শনিবার, ২৭ জুলাই ২০২৪, ০৬:২৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
দিবারাত্রির কাব্য: মানিক বন্দোপধ্যায় ( ৪২ তম কিস্তি )
- Update Time : শুক্রবার, ১৯ এপ্রিল, ২০২৪, ১২.০০ পিএম

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে আরেকটি নতুন যুগ সৃষ্টি হয়েছিলো। ভাষাকে মানুষের মুখের ভাষার কাছে নিয়ে আসা নয়, সাহিত্যে’র বিষয়ও হয়েছিলো অনেক বিস্তৃত। সাহিত্যে উঠে এসেছিলো পরিবর্তিত মন ও সমাজের নানান প্রাঙ্গন। সময়ের পথ ধরে সে যুগটি এখন নিকট অতীত। আর সে সাহিত্যও চিরায়ত সাহিত্য। দূর অতীত ও নিকট অতীতের সকল চিরায়ত সাহিত্য মানুষকে সব সময়ই পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে। চিরায়ত সাহিত্যকে জানা ছাড়া বাস্তবে মানুষ তার নিজেকে সম্পূর্ণ জানতে পারে না।
সারাক্ষণের চিরায়ত সাহিত্য বিভাগে এবারে থাকছে মানিক বন্দোপধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্য।
দিবারাত্রির কাব্যে’র ভূমিকায় মানিক বন্দোপধ্যায় নিজেই যা লিখেছিলেন …..
দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।
দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক,- তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection-মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।
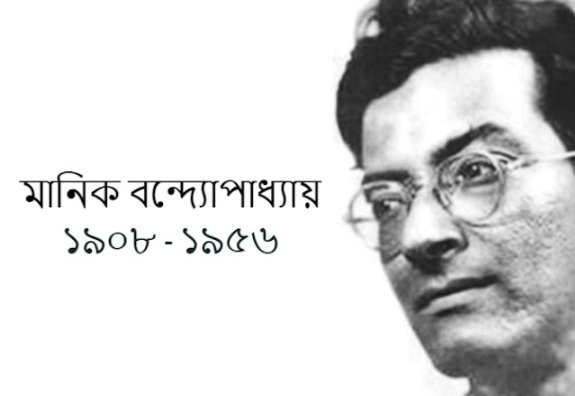
দিবা রাত্রির কাব্য
মানিক বন্দোপাধ্যায়
বলে আনন্দ চোখ মুছতে লাগল। হেরম্ব তাকে একটি সান্ত্বনার কথাও বলতে পারল না। বাতাসের নাড়া খেয়ে গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে, আনন্দ প্রায় ভিজে গিয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে হেরম্ব ঘরে গেল। জানালা কেউ বন্ধ করেনি। বৃষ্টির জলে মেঝো ভেসে গিয়েছে। হেরম্বের বিছানাও ভিজেছে। বিছানাটা উল্টে নিয়ে হেরম্ব তোশকের নিচে পাতা শুকনো শতরঞ্জিতে বসল।
বলার অপেক্ষা না রেখে আনন্দও তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। সে অল্প অল্প কাঁপছিল, জলে ভিজে কিনা বলবার উপায় নেই। হেরম্বের মনে হল, সান্ত্বনার জন্য যত নয়, নির্ভরতার জন্যই আনন্দ ব্যাকুল হয়েছে বেশী। এরকম মনে হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ভেবে না পেয়ে হেরম্ব তাকে সান্ত্বনাও দিল না, নির্ভরতাও দিল না। সে বরাবর লক্ষ্য করেছে এরকম অবস্থায় ঠিকমতো না বুঝে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়।
আনন্দ বলল, ‘মা কি করেছে জান? বাবাকে টাকা দিয়েছি বলে আমাকে মেরেছে।’ হেরম্বের দিকে পিছন ফিরে পিঠের কাপড় সে সরিয়ে দিল, ‘দ্যাখো কি রকম মেরেছে। এখনো ব্যথা কমেনি। ঘষা লেগে জ্বলা করে বলে জামা গায়ে দিতে পারিনি, শীত করছে, তবু। কি দিয়ে মেরেছে জান? বাবার ভাঙা ছড়িটা দিয়ে।’
তার সমস্ত পিঠ জুড়ে সত্যই ছড়ির মোটা মোটা দাগ লাল হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিশ্বাস রোধ করে বলল, ‘তোমায় এমন করে মেরেছে!’
আনন্দ পিঠ ঢেকে দিয়ে বলল, ‘আরও মারত, পালিয়ে গেলাম বলে পারেনি। বৃষ্টির সময় মন্দিরে বসে ছিলাম। তুমি যত আসছিলে না, আমি একেবারে মরে যাচ্ছিলাম। তিনি বুঝি আসতে দেননি, যাঁর সঙ্গে গেলে?’ ‘হ্যাঁ, তার স্বামী আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না। পিঠে হাত বুলিয়ে
দেব আনন্দ ?’
‘মা, জ্বালা করবে।’
হেরম্ব ব্যাকুল হয়ে বলল, ‘একটা কিছু করতে হবে তো, নইলে আলা কমবে কেন? আচ্ছা সেঁক দিলে হয় না?’ বলে হেরম্ব নিজেই আবার বলল, ‘তাতে কি হবে?’
‘এখন জ্বালা কমেছে।’
‘কমেনি, জ্বালা টের পাচ্ছ না। তোমার পিঠ অসাড় হয়ে গেছে। বরফ ঘষে দিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হত।’
‘তা হত। কিন্তু বরফ নেই। তুমি বরং আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েই দাও।’
‘বস, বরফ নিয়ে আসছি।’
আনন্দের প্রতিবাদ কানে না তুলে হেরম্ব চলে গেল। শহর পর্যন্ত হেঁটে যেতে হল। বরফ কিনে সে ফিরে এল গাড়িতে। আনন্দ ইতিমধ্যে মেঝের জল মুছে ভিজে বিছানা বদলে ফেলেছে। সে যে সোনার পুতুল নয় এই তার প্রমাণ।
এত কষ্ট করে বরফ সংগ্রহ করে এনেও এক ঘণ্টার বেশী আনন্দের পিঠে ঘষে দেওয়া গেল না। বরফ বড় ঠাণ্ডা। আনন্দ চুপ করে শুয়ে রইল, হাত গুটিয়ে বসে রইল আনন্দ। যে কোন কারণেই হোক আনন্দকে মালতী যে এমনভাবে মারতে পারে সে যেন ভাবতেই পারছিল না।
মেঘ কেটে গিয়ে এখন আবার কড়া রোদ উঠেছে। পৃথিবীর উজ্জ্বল মৃতি এখনো সিক্ত এবং নম্র। আনন্দকে শুয়ে থাকতে হুকুম দিয়ে হেরম্ব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।
মালতী কখন থেকে বারান্দায় এসে বসে ছিল। হেরম্বকে সে কাছে ডাকল। হেরম্ব ফিরেও তাকাল না। মালতী টলতে টলতে কাছে এল। বেশ বোঝা যায়, মাত্রা রেখে আজ সে কারণ পান করেনি। কিন্তু নেশায় তার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে বলে মনে হল না।
‘সাড়া দাও না যে!’
‘কারণ আছে বই কি।’
মালতী বোধহয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সেখানে দুপ করে বসল। ‘শুনি, কারণটা শুনি।’
‘সেটুকু বুঝাবার শক্তি আপনার আছে, মালতী-বৌদি।’
দিবারাত্রির কাব্য: মানিক বন্দোপধ্যায় ( ৪১ তম কিস্তি )
More News Of This Category









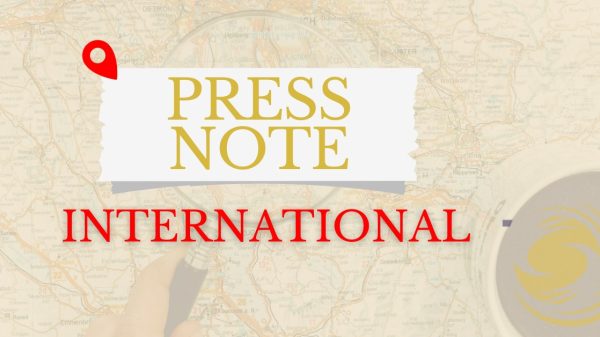



Leave a Reply