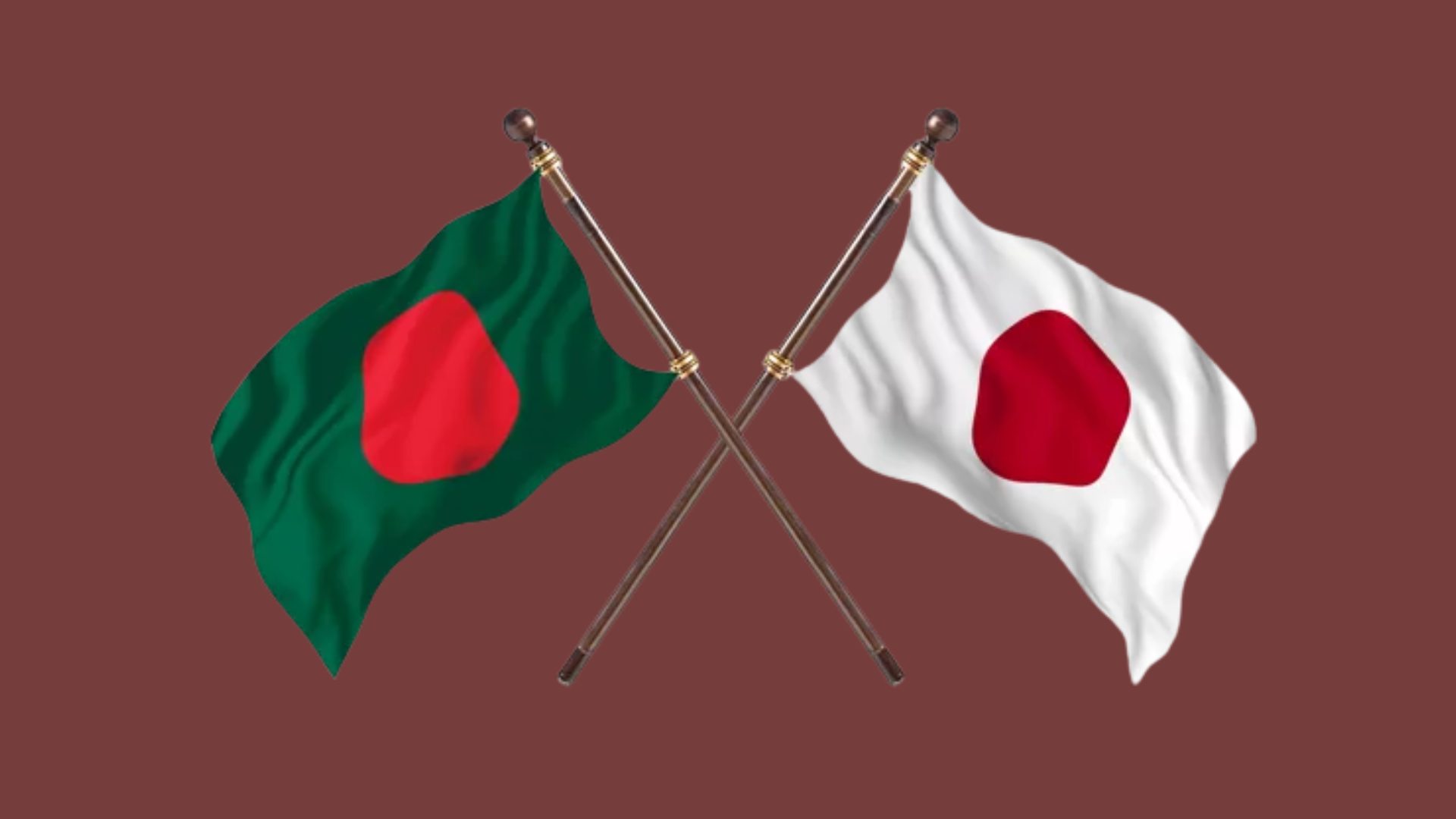শীতের সন্ধ্যা, ঘড়িতে বাজে পাঁচটা, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনাসদস্যের আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটছে রমনা রেসকোর্স (সোহরাওয়াদী উদ্যান)-এ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে স্বাধীন দেশে উদিত হওয়ার প্রস্তুতি নিতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিল’ (Instrument of Surrender) স্বাক্ষর করার সাথে সাথে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। একই সাথে প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য- যার মধ্যে প্রায় ৭৯,০০০ ইউনিফর্মধারী সৈন্য এবং ১২,০০০ এরও বেশি বেসামরিক নাগরিক, তারা যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটককৃত হয়, যার মধ্য থেকে আনুমানিক ৩,০০০ যুদ্ধবন্দী আবার যুদ্ধকালীনই বন্দী হয়েছিল। তাদের দেখভাল ও নিরাপত্তা বাংলাদেশী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের তত্ত্বাবধানে চলে যায়। এখানেই বাংলাদেশের বিজয় একটি নৈতিক ও সভাতার পরীক্ষায় প্রবেশ করে। সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্র, যার জনগণ নৃশংস গণহত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এসেছে-তাদের সামনে ছিল প্রতিশোধের সহজ পথ। কিন্তু বাংলাদেশ সেই পথ বেছে নেয়নি।
মিত্রবাহিনীর তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া
ভারতের ইস্টার্ন আর্মির চিফ অব স্টাফ লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব তাঁর ‘সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা’ গ্রন্থে লিখেছেন, ১৬ই ডিসেম্বর ‘আত্মসমর্পণের দলিল’ স্বাক্ষরের আগে বিকেল তিনটার দিকে তিনি নিয়াজির গাড়িতে করে ঢাকা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হন জেনারেল অরোরাকে রিসিভ করার জন্য। পথিমধ্যে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে এয়ারফিল্ডে যেতে বাধা দেয়। চতুর্দিক থেকে হালকা অস্ত্রের বিচ্ছিন্ন গোলাগুলির শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছিল। নিয়াজীর নিরাপত্তা নিয়ে ভারতীয়রা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে তারা এয়ারফিল্ডে পৌঁছান। সামান্য পরে এক ট্রাক বোঝাই মুক্তিবাহিনী রানওয়ের অন্য পাশে এসে থামে। মুক্তিবাহিনীর দুজন সৈন্যের পিছনে কাঁধে মেজর জেনারেল র্যাঙ্কের ব্যাজ লাগিয়ে একজন ব্যক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসেন। জেকব তাঁকে চিনতে পারেন- তিনি ‘বাঘা’ সিদ্দিকী। বিপদের গন্ধ পেয়ে নিয়াজীকে আড়াল করার জন্য দুজন প্যারাট্রুপারকে নির্দেশ দিয়ে জেকব কাদের সিদ্দিকীর দিকে এগিয়ে যান; আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করার জন্যই নিয়াজিকে বেঁচে থাকতে হবে। জেকবের চাপাচাপিতে সিদ্দিকী শেষ পর্যন্ত রানওয়ে থেকে ট্রাকটি নিয়ে চলে যান। মিত্রবাহিনীর বোঝার বাকি থাকে না প্রতিশোধের আগুনে ফুঁসছে বাংলাদেশ। তা দাবানল হয়ে ওঠার আগেই পাকিস্তান সেনা সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ‘আত্মসমর্পণের দলিলে উল্লেখ করা হয়, ‘লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা দৃঢ়তার সাথে আশ্বাস দিচ্ছেন যে আত্মসমর্পণকারীদের জেনেভা কনভেনশনের বিধান অনুসারে সৈন্যদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সমস্ত পাকিস্তান সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করা হবে।’ বাংলাদেশ জুড়ে পাকিস্তানি সেনাসদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাদেরকে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর যৌথ কমান্ডের (মিত্র বাহিনী) অধীনে রাখা হয়। ঢাকা ও এর আশেপাশে অবস্থানরত পাকসেনাদের ঢাকা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। ঢাকার বাইরের পাকসেনাদের নিকটস্থ (যেমন: ময়নামতি, যশোর, রংপুর, চট্টগ্রাম) সেনানিবাসের হেফাজতে নেয়া হয়। ভারতে যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্পে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সেখানেই নিরাপদে ছিলেন।
দেশে দেশে জেনেভা কনভেনশন
১৯৪৯ সালের জেনেভা ৩য় কনভেনশনের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ (যেমন ১৩-১৬, ১৭, ২১-২৪, ৫৭, ১০৯ ১১৭ ইত্যাদি। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি পূর্ণ মানবিক প্রোটোকল অনুসরণ করে। এই কনভেনশন অনুযায়ী (সংক্ষেপে):
যুদ্ধবন্দীদের হত্যা, নির্যাতন বা অপমান করা যাবে না
খাদ্য, চিকিৎসা ও নিরাপদ আবাস নিশ্চিত করতে হবে
যুদ্ধ শেষ হলে তাদের যথাসময়ে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে কিন্তু ইতিহাসে বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘিত হয়েছে, বিজয়ী শক্তি পরাজিতদের সাথে নির্মম আচরণ করেছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানরা বিশেষ করে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে। আনুমানিক ৩০-৩৫ লক্ষ সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী অনাহার ও হত্যায় মারা গিয়েছিল। অপরদিকে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান যুদ্ধবন্দীদের দীর্ঘকাল আটকে রাখা হয়েছে, লক্ষাধিক যুদ্ধবন্দী শ্রমশিবিরে মৃত্যুবরণ করেছেন, যুদ্ধ শেষে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার এ বিষয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়। ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সম্প্রচারিত হয়: ‘বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে আমার আহ্বান কোন অবস্থাতেই নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। মনে রাখবেন যে অপরাধীকে আইন মোতাবেক শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আপনার সরকারের এবং সে দায়িত্ব সরকার পালন করবেন। যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিকেও জয় করে আনতে হবে।
২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ যখন প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিপরিষদ স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন তখন ঢাকা বিমানবন্দরে তাজউদ্দিন আহমদে স্পষ্ট করে বলেন যে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সৈন্যরা যৌথ কমান্ডের অধীনে ছিল এবং বাংলাদেশ তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনকে সম্মান করবে।
যুদ্ধবন্দীদের ভারতে স্থানান্তর
তিন ধরণের পাকিস্তানিদের আটক করা হয়
১) যুদ্ধবন্দী (Prisoner of War-POW): ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সামরিক কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট বেসামরিক লোক। এদের মধ্যে ৭৯,৬০০-৮১,০০০ জন ইউনিফর্মধারী কর্মী, যাদের মধ্যে সেনাবাহিনী (প্রায় ৫৫,০০০), নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পশ্চিম পাকিস্তান রেঞ্জার্স এবং আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত। বেসামরিক ব্যক্তি প্রায় ১২,০০০-১৩,০০০, যার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, বেসামরিক কর্মচারী এবং সামরিক কর্মীদের পরিবার (মহিলা ও শিশু) অন্তর্ভুক্ত।
২) বেসামরিক অন্তরীণ (Civilian Internee-CI সিআই): বেসামরিক পাকিস্তানি নাগরিক যারা আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে নিরাপত্তার কারণে আটক ছিলেন।
৩) বেসামরিক নিরস্ত্র পাকিস্তানি নাগরিক (Civilian Unarmed Pakistani Citizens-CUPC সিইউপিসি): পাকিস্তানি বেসামরিক নাগরিক যারা যোদ্ধা ছিলেন না, যেমন বেসামরিক কর্মচারী, তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি যারা সরাসরি সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন না। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবন্দী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ছিলেন না, তবে সনাক্তকরণ, সুরক্ষা বা প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্যে আটক ছিলেন। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নাটের গুরু মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর লেখা ‘হাও পাকিস্তান গট ডিভাইডেড’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়- জেনারেল নিয়াজি, নৌবাহিনীপ্রধান অ্যাডমিরাল শরীফ, বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডোর এম ইনামুল হক, মেজর জেনারেল জামশেদ, রাও ফরমান আলী, নজর, আনসারী, কাজী মজিদ প্রমুখ শীর্ষ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীগণ ২০শে ডিসেম্বর বিমানযোগে কোলকাতা পৌঁছান। তারা যখন টারম্যাকে অবতরণ করেন তখন অ্যাডমিরাল শরীফ জেনারেল নিয়াজির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবিতে বলেন, ‘আপনি বলতেন আমি কোলকাতা যাবো। এখন আপনি সেখানে পৌঁছে গেছেন।’ বিদ্রূপাত্মক কথাটি এসেছিল জেনারেল নিয়াজীর এই দাম্ভিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে, তিনি কলকাতা আক্রমণ করবেন এবং দখল করে নেবেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতে তাদের জীবন শুরু হয়।
বাকি যুদ্ধবন্দীদের ভারতীয় ট্রেনে করে ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে দিতে তিন সপ্তাহ সময় লেগেছিল। ভারত জুড়ে (প্রধানত: ফিরোজপুর, রামগড়, লক্ষ্ণৌ। এক ডজনেরও বেশি জেল এবং ৫০টি আটক শিবিরে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়।
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও জেনেভা কনভেনশন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২-এ বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ৫দিন পর অর্থাৎ ১৫ই জানুয়ারি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-র সাথে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানিদের বর্বর হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন, লুটতরাজের করুণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন সাংবাদিক বলেন যে, ‘স্যার, আপনারা তো খুবই সভ্য মানুষ এবং বিশ্ব আশা করবে যে আপনি জেনেভা কনভেনশনের শর্তাবলী অনুসারে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ করবেন।’ বঙ্গবন্ধু নির্দ্বিধায় জবাব দেন, ‘অবশ্যই আমরা জেনেভা কনভেনশন অনুসরণ করব। আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন, আমরা জেনেভা কনভেনশন অনুসরণ করব। ঐ সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে জানান যে জেনারেল মানেকশও একই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন; বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘আমি খুশি যে তারা এটা করছে, তারা এটা করছে’। তবে একই সাথে তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সুরক্ষা দিলেও, যারা গুরুতর অপরাধ করেছে তাদের সুরক্ষা প্রদান করে না। তিনি বস্তুত জেনেভা ৩য় কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৩০ যেখানে ‘গুরুতর লঙ্ঘন’ (grave breach) এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং ৪টি কনভেনশনে ছড়িয়ে থাকা অনুচ্ছেদ ৪৯/৫০/১২৯/১৪৬ যেখানে ঐ ‘গুরুতর লঙ্ঘনে’র কারণে যুদ্ধবন্দীদেরও বিচার করার বিধান রাখা হয়েছে, সে দিকে নির্দেশ করছিলেন।
স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারের তৎপরতা
১৯৭১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মুক্ত ঢাকায় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রিপোর্ট করা হয় যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৮৯,০০০ নিয়মিত সদস্য বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাদের মধ্যে পাঁচ হাজারকে ইতোমধ্যে ভারতে পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগীরা (রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রমূখ। বিচার থেকে রেহাই পাবে না। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন গভর্নর ড. এএম মালিক এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ৩০ জন শীর্ষ পাকিস্তানি বেসামরিক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং শীঘ্রই তাদের গণহত্যার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।
সরকার একই সঙ্গে স্পষ্টভাবে জানায়- পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধে সরাসরি জড়িত। ৩১শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার মাত্রা ও ব্যাপ্তি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১২ই জানুয়ারী ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪ই জানুয়ারী ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমি ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের কাছে আবেদন করেছি যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কীভাবে আমার জনগণকে হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের নির্যাতন করেছে, আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এবং আমাদের সম্পত্তি লুট করেছে তা তদন্ত করার জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হোক। যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের আবেদনে সাড়া না দেয়, তাহলে সরকারকে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে যেন আমাদের জনগণ ন্যায়বিচার পেয়েছে বলে মনে করে।
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ২৪শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ‘বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২’ (The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972) জারি করেন।
১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির এই ৮ নং আদেশের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং শান্তি কমিটির সদস্যদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত অর্থে এটি ছিল বাংলাদেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রথম আইনি পদক্ষেপ। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় আসেন। ১৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ২৯শে মার্চ বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধের জন্য প্রায় ১,১০০ পাকিস্তানি সামরিক বন্দীর বিচারের আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ১৪ই জুন ভারত প্রাথমিকভাবে ১৫০ জন যুদ্ধবন্দীকে বিচারের জন্য হস্তান্তর করতে সম্মত হয় যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নৃশংসতার ‘প্রাথমিক মামলা’ (prima facie) উপস্থাপন করেছিল। ভারত ও পাকিস্কানের মধ্যে ঐতিহাসিক ‘সিমলা চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হওয়ার দশ দিন আগে অর্থাৎ ১৯শে জুন, ১৯৭২ শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের বিচারের জন্য তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। ২৯-৩০শে জুন ভারতের সিমলায় জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি পকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়। ইন্দিরা গান্ধী ১২ই জুলাই নয়াদিল্লিতে বলেন যে তিনি যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে ‘দ্বিপাক্ষিক’ বিষয় বলে মনে করেন। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচারের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।
১৭ই এপ্রিল ১৯৭৩ সালে সরকার সরাসরি গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত বা নেতৃত্বদানকারী ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং ভারতকে অবহিত করে যে যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবাসনের সময় যেন এদেরকে আলাদা করা হয়। একটি কমিশনের মাধ্যমে তদন্ত, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, নথিপত্র এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে এই তালিকা প্রণয়ন করা হয়। পূর্বোক্ত দালাল আইন ১৯৭২-এর মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশীয় দোসরদের বিচার করা সম্ভব হচ্ছিল, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধবন্দীদের এ আইনের আওতাভুক্ত করা যাচ্ছিল না। সেজন্য সংবিধান সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৭৩ সালের ১৫ই জুলাই জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের সংবিধানে ‘প্রথম সংশোধনী’ আনা হয়, যার ধারা ৪৭(৩)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয় … গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না..।’ সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন প্রণয়ন করা। ৪ দিন পর (১৯শে জুলাই) জাতীয় সংসদে ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩’ (International Crimes (Tribunal) Law 1973) খধি ১৯৭৩) পাশ হয় এবং ২০শে জুলাই আইন জারি হয়। ২৬শে জুলাই ১৯৭৩ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ (ICT) গঠন করে।
কারা সেই ১৯৫ জন
১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর পূর্ণ তালিকা কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ পায়নি। তবে গণমাধ্যম সূত্রে বেশ কয়েকজনের নাম ঘুরে ফিরে এসছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ; এ ছাড়া ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পদমর্যাদার আরও অনেক কর্মকর্তা ছিলেন, যাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অঞ্চলে গণহত্যা ও দমন-পীড়নের অভিযোগ ছিল। গণহত্যা তদন্ত এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য বাংলাদেশে ‘ওয়ার ক্রামইস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি (WCFFC) দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছে। WCFFC-এর গবেষণার ফলাফল নিয়ে সংগঠনটির আহ্বায়ক ডা. এম এ হাসান রচিত ‘পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন’ বইটিতে এই যুদ্ধাপরাধীদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। বিভাগওয়ারি যুদ্ধাপরাধীদের নাম, পদবী, অপরাধের ধরণ, ঘটনা স্থান ও কাল, সাক্ষীদের পরিচয় ও সাক্ষ্য বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকা বিভাগের তালিকায় রয়েছেন লে. জে. টিক্কা খান, মে. জে. রাও ফরমান আলী খান, ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব, রাজা, আসলাম, শরীফ, কর্নেল তাজ, মেজর আসলাম প্রমূখ। চট্টগ্রাম বিভাগের তালিকায় উপরোক্ত কয়েকজন ছাড়াও রয়েছেন লে. জে. নিয়াজি, ইয়াকুব মালিক, ব্রিগেডিয়ার বেগ, আনসারী, কর্নেল জানজুয়া, ভাদী প্রমুখ। সিলেট বিভাগের তালিকায় রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা, কর্নেল সরফরাজ মালিক প্রমূখ। খুলনা বিভাগের তালিকায় রয়েছেন কমান্ডার গুলজারিন, মেজর ইশতিয়াক, বেলায়েত খান, একরাম, জাফর, বানোরি, ক্যাপ্টেন আকরাম প্রমুখ। বরিশাল বিভাগের তালিকায় রয়েছেন ক্যাপ্টেন মুনির, সুবেদার সিদ্দিক, ইয়ামিন প্রমূখ এবং রাজশাহী বিভাগের তালিকায় রয়েছেন লে. কর্নেল আব্দুল্লাহ খান, সাফায়েত, মেজর শেরওয়ানী, আখতার শাহ, আব্দুল মজিদ প্রমূখ।
কূটনৈতিক বাস্তবতা: যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি ও প্রত্যাবাসন পরাজয়ের দায় স্বীকার করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭১ রাষ্ট্রপতি, সামরিক শাসক ও সেনাবাহিনী প্রধান (Commander-in-Chief, সি-ইন-সি)-এর পদে ইস্তফা প্রদান করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ২০শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সংক্ষুব্ধ সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ঐদিনই জেনারেল টিক্কা খানকে অপসারিত করে লে. জেনারেল গুল হাসান খানকে সি-ইন-সি পদে নিযুক্ত করেন। গুল হাসান তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে লিখছেন- একদিন রাষ্ট্রপতি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং আশ্বাস দিলেন যে যুদ্ধবন্দীদের বিচারের প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমানের চোখ রাঙানির কাছে তিনি হার মানবেন না। যাদের বিচার হবে তাদের তালিকায় তিনি গুল হাসানের নাম অন্তর্ভুক্ত হতে দেবেন না। যাহোক, মার্চেই তাঁকে অপসারণ করা হয়, স্থলাভিষিক্ত হন ঐ জেনারেল টিক্কা খান। গুল হাসানকে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো নয়। ৯ই মে বিদায়ী সাক্ষাতে গেলে ভুট্টো আবারও তাকে যুদ্ধবন্দীদের বিচার নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেন। ভুট্টোর সামনে গুল হাসান ভাবলেশহীন থাকলেও তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারেননি। ভিয়েনায় যোগ দিয়ে ১৪ই মে তিনি জেনারেল এমএজি ওসমানীকে চিঠি লিখে জানতে চান যে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কী অভিযোগ আনা হয়েছে। ওসমানী দ্রুতই জবাব দেন। চিঠির শুরুতে এক অনুচ্ছেদ জুড়ে তিনি উল্লেখ করেন যে পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী বাংলাদেশের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের ওপর চরম অমানবিক ধরণের গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও লুণ্ঠন চালিয়েছে। তবে তিনি এও জানান যে গুল হাসানের নাম যুদ্ধপরাধীদের তালিকায় নেই। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে তৎপর ছিল এবং সে কারণে পাকিস্তান সেনাসদস্যরা মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। সেই চাপ উপেক্ষা করার সুযোগ রাষ্ট্রপতি ভুট্টোরও ছিল না। পাকিস্তান সেনাসদস্যদের বিচার প্রতিহত না করতে পারলে তাঁর মসনদ আক্রান্ত হতে পারে এ আশঙ্কা তিনি করতেন। তবে ভুট্টোর হাতে বেশ কয়েকটি দাবার গুটি ছিল:
১. পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী ৪,০০,০০০ বাংলাদেশির অনেকেই পাকিস্তান সরকারের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে ছিলেন ২৮ হাজার সেনা। ১৬,০০০ বাংলাদেশি সরকারি কর্মচারীকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং দেশ ত্যাগে বাধা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি (IRC) জানায় যে, অনেক বাংলাদেশিকে কেবল ‘পাকিস্তান ত্যাগ করার অভিপ্রায়ের জন্য’ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং হাজার হাজারকে কোনও অভিযোগ ছাড়াই জেলে পাঠানো হয়েছিল। এতে আরও বলা হয় যে পাকিস্তানে বেসামরিক বাংলাদেশিরা গুরুতর বৈষম্য এবং হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের সাথে ‘নিগ্রো’ হিসেবে আচরণ করা হচ্ছে। ব্যাপক নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে শত শত বাংলাদেশি আফগানিস্তানের দুর্গম দিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় আটক প্রতিটি বাংলাদেশির জন্য ১,০০০ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল। ২. ভুট্টো গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অন্তত ২০০ বাংলাদেশি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাকে বন্দি করেন। বন্দি বাঙালি কর্মকর্তাদের অবস্থা কেমন ছিল তা জানা যায় পাকিস্তানের কনসেনস্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী মে. জেনারেল এম. খলিলুর রহমানের লেখা ‘কাছে থেকে দেখা ১৯৭৩-১৯৭৫’ বই থেকে: ‘সত্যি বলতে কি ওই সময়ে আমরা কেমন প্রাণ হাতে নিয়ে ও মেয়েদের ইজ্জতের ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে সে বন্দিশালায় ছিলাম, তা বর্ণনা করা যায় না।’ ভুট্টো হুমকি দেন যে বাংলাদেশ যদি ১৯৫ জন পাকিস্তানির বিচার করে, তাহলে পাকিস্তানও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে একই ধরণের ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে। ২৭শে মে, ১৯৭৩ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো বলেন, ‘জনমত এখানে। বাংলাদেশীদের। বিচার দাবি করবে… আমরা জানি যে বাঙালিরা যুদ্ধের সময় তথ্য দিয়েছিল। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকবে। কতজনের বিচার হবে, আমি বলতে পারছি না।’ এদিকে তাদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে বঙ্গবন্ধুর সরকারের ওপর প্রবল চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন স্বজনরা।
১০ আগস্ট, ১৯৭২ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো বলেন যে বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে ‘আমাদের বন্দীদের মুক্তির ক্ষেত্রে তাদের এক ধরণের ভেটো রয়েছে’, কিন্তু ‘আমাদের হাতেও একটি ভেটো রয়েছে।’ পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধুরাষ্ট্র চীনকে তার ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ থেকে বিরত রাখার জন্য অনুরোধ করে। ফলে বাংলাদেশ যখন জাতিসংঘে আবেদন করে, তখন চীন ১৯৭২ সালের ২৫শে আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সদস্যপদ গ্রহণে ভেটো প্রদান করে।
8. পাকিস্তান তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান না করায়, মানবিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় (বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান) আলোচনা সম্ভব ছিল না; সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে ছাড়া বাংলাদেশ এই ধরণের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারত না।
৫ যুদ্ধবন্দীদের ভরণ-পোষণের জন্য ভারতকে লাখ লাখ ডলার খরচ করতে হচ্ছিল, যা দেশটির অর্থনীতিতে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল।
দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতি ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারপ্রক্রিয়াকে সরল পথে এগোতে দেয়নি। ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল ভারত ও বাংলাদেশ উপমহাদেশে পুনর্মিলন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার বৃহত্তর স্বার্থে প্রস্তাব করে যে আটক ও আটকে পড়া ব্যক্তিদের সমস্যা মানবিক বিবেচনায় সমাধান করা উচিত- একই সাথে সকলকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে, তবে সে সকল পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী ব্যতীত, যাদেরকে নির্দিষ্ট অভিযোগে বিচারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজন হতে পারে।
২৮শে আগস্ট ১৯৭৩ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক ‘দিল্লি চুক্তি’ (Delhi Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। যদিও বাংলাদেশ এটি স্বাক্ষর করেনি (কারণ পাকিস্তান তখনও বাংলাদশকে স্বীকৃতি দেয়নি), কিন্তু চুক্তিটি বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ সম্মতিতে (indirect concurrence) করা হয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে:
পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ভারত থেকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর পথ খুলে যায়
পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশের নাগরিকদের (সেনাসদস্য সহ) প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হয়
বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের (অবাঙালি/বিহারি) প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হয়
পাকিস্তান ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে অগ্রসর হয়
এটিকে ‘প্রত্যাবাসন চুক্তি’ (Repatriation Agreement) বলা যেতে পারে, তবে কেবল আংশিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে। এই চুক্তির আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল- এটি ঐ ১৯৫ জন পাকিস্তানি সামরিক অফিসারকে সাধারণ প্রত্যাবাসন থেকে পৃথক করেছিল। অনুচ্ছেদ ৩(৫)-এ বলা হয়েছিল যে ১৯৫ জন ভারতে থাকবেন এবং তিন পক্ষের মধ্যে পরবর্তী কোনও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রত্যাবাসন করা হবে না।
৯ই এপ্রিল, ১৯৭৪ নয়াদিল্লিতে প্রত্যাবাসনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি চুক্তি (New Delhi Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। প্রথমবারের মতো এটি ছিল বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ পাকিস্তান ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ (লাহোরে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের সময়) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই চুক্তির ১৩-১৫ অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী (আংশিক): বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা সংঘটিত বাড়াবাড়ি রকমের বহুমুখী অপরাধ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলুশন এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যা হিসেবে বিবেচিত এবং সর্বজনীন ঐকমত্য ছিল- যে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী এ ধরণের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং আইনের যথাযথ প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে। পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, তার সরকার যে কোনো অপরাধের নিন্দা জানিয়েছে এবং গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিন মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, বিষয়টিকে তিনটি দেশের পুনর্মিলনের জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত। মন্ত্রীরা আরও উল্লেখ করেছেন যে স্বীকৃতির পর, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সফর করবেন এবং পুনর্মিলনকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে অতীতের ভুল ক্ষমা করার এবং ভুলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশের জনগণের কাছে অতীতের ভুল ক্ষমা করে ভুলে যাওয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশ সরকার ক্ষমার দৃষ্টিতে বিচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিল্লি চুক্তির অধীনে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াধীন অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো যেতে পারে বলে একমত হয়েছে। এই সমঝোতার কারণেই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত পাকিস্তানি সেনাকে বিচারের আওতায় আনা যায়নি- যা বাংলাদেশের জন্য ছিল একটি কঠিন কিন্তু কৌশলগত সিদ্ধান্ত।
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ থেকে ত্রিমুখী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৭৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে প্রক্রিয়াটি কার্যত সম্পন্ন হয়। আত্মসমর্পণকারী প্রথম সৈনিক লে. জেনারেল নিয়াজি ‘প্রথমে প্রবেশ, সবশেষে বহিরাগমন’ নীতি অনুসরণ করে শেষ যুদ্ধবন্দী হিসেবে প্রত্যাবাসিত হন। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক (পূর্ব পাকিস্তানে জেনারেল নিয়াজির সাথে ছিলেন) তার বই ‘হামাহ ইয়ারান দোজখ’ (The Wounded Pride) (১৯৮৪) গ্রন্থে স্মরণ করেন: শত্রু সৈন্যদের অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি আমাদের অস্থির করে তোলেনি। বরং পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের বোঝাই আমাদের হতাশ করেছিল।’ কেউ কেউ ওয়াঘা সীমান্তে পৌঁছানোর আগেই তাদের ‘যুদ্ধবন্দী পোশাক’ (PXW) ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, লজ্জায়-অপমানে তারা তা করেছিল।
হামুদুর রহমান কমিশন
পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিশন গঠন করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান থেকে শুরু করে নৌ, সেনা, বিমান বাহিনীর প্রধান, মন্ত্রী, আমলা আর বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাসহ ২৮৬ জনের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনর প্রথম অংশ ১৯৭২ সালের জুলাইয়ে ও দ্বিতীয় অংশ ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করে কমিশন। ৬৭৫ পৃষ্ঠার এই বিশাল প্রতিবেদনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে লে. জে. এএকে নিয়াজি, মে. জে. রাও ফরমান আলী, ক. জে. জামশেদ খান, রি. এ. শরীফ এবং কমান্ডার এনামের জবানবন্দী। রিপোর্টে বলা হয় কমিশনের তদন্তে প্রমানিত হয়েছে যে যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের জন্য সুস্পষ্টভাবে সশস্ত্র বাহিনী দায়ী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, নিপীড়ন, গণহত্যা এবং সামরিক ব্যর্থতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্যও সশস্ত্র বাহিনীই দায়ী। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অযাচিত এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে অগ্নিসংযোগ, সারাদেশে হত্যাকাণ্ড ঘটায়, হিন্দু জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হত্যা এবং আক্রমণ করে, বুদ্ধিজীবী এবং পেশাজীবী হত্যা করে এবং নিহতদের গণকবর দেয়া হয়। তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়টিও (মদ, নারীআসক্তি) প্রমানিত হয়।
কমিশন সুপারিশ করে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, লে. জে. এস.জি.এম.এম. পীরজাদা, লে. জে. গুল হাসান, মে. জে. উমর এবং মে. জে. মিঠা, আর্মি এসএস গ্রুপের কমান্ডারের প্রকাশ্যে বিচার হওয়া উচিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের জন্য। আরও ৫ জন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের বিচারের সুপারিশ করা হয় কর্তব্যে ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য; এদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী, মোহাম্মাদ জামসেদ, এম. রহিম খান, ইরশাদ আহমদ খান, বি. এম. মুস্তফা এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি.এম. বাকুইর সিদ্দিকি, মোহাম্মদ হায়াত এবং মোহাম্মদ আসলাম নিয়াজী। ভুট্টো বা পরবর্তী পাকিস্তান সরকার প্রধানগণ সেই সুপারিশগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। দোষীদের বিচারের জন্যও কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি, ভুট্টো কর্তৃক প্রতিশ্রুত নিজস্ব ট্রাইবুনালের মাধ্যমে তাদের বিচারেরও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
বাংলাদেশ শুধু যুদ্ধ জয় করেনি
বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে জেনেভা কনভেনশন অনুসরণ করে বন্দীদের নিরাপত্তা, খাদ্য, চিকিৎসা ও মর্যাদা নিশ্চিত করে। যুদ্ধ শেষের দিন থেকে বন্দীদের ওপর কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিশোধ নেমে আসেনি। এই সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিকও, আবার গভীরভাবে নৈতিকও। নয় মাস ধরে গণহত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হওয়া একটি জাতির এমন আচরণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে নৈতিক উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করে। এই সময় পর্ব প্রমাণ করে- বাংলাদেশ শুধু যুদ্ধ জয় করেনি, সে জয় করেছে নৈতিকতা, আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় পরিপক্কতার পরীক্ষাও। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের পরিণতি এবং ১৯৫ জনের বিচার প্রশ্নটি তাই কেবল অতীতের নয়; এটি রাষ্ট্র, ন্যায়বিচার ও বাস্তব রাজনীতির টানাপোড়েনের প্রতীক। এই অধ্যায় আমাদের শেখায়-যুদ্ধের বিজয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ, যুদ্ধের পর রাষ্ট্র কীভাবে আচরণ করে-তা ইতিহাসে আরও গভীর ছাপ ফেলে। যে জাতি নিজে গণহত্যার শিকার হয়েছে, সেই জাতিই আন্তর্জাতিক আইন মেনে পরাজিত বাহিনীর অধিকার রক্ষা করেছে- এটি ইতিহাসে বিরল।

 বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ
বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ