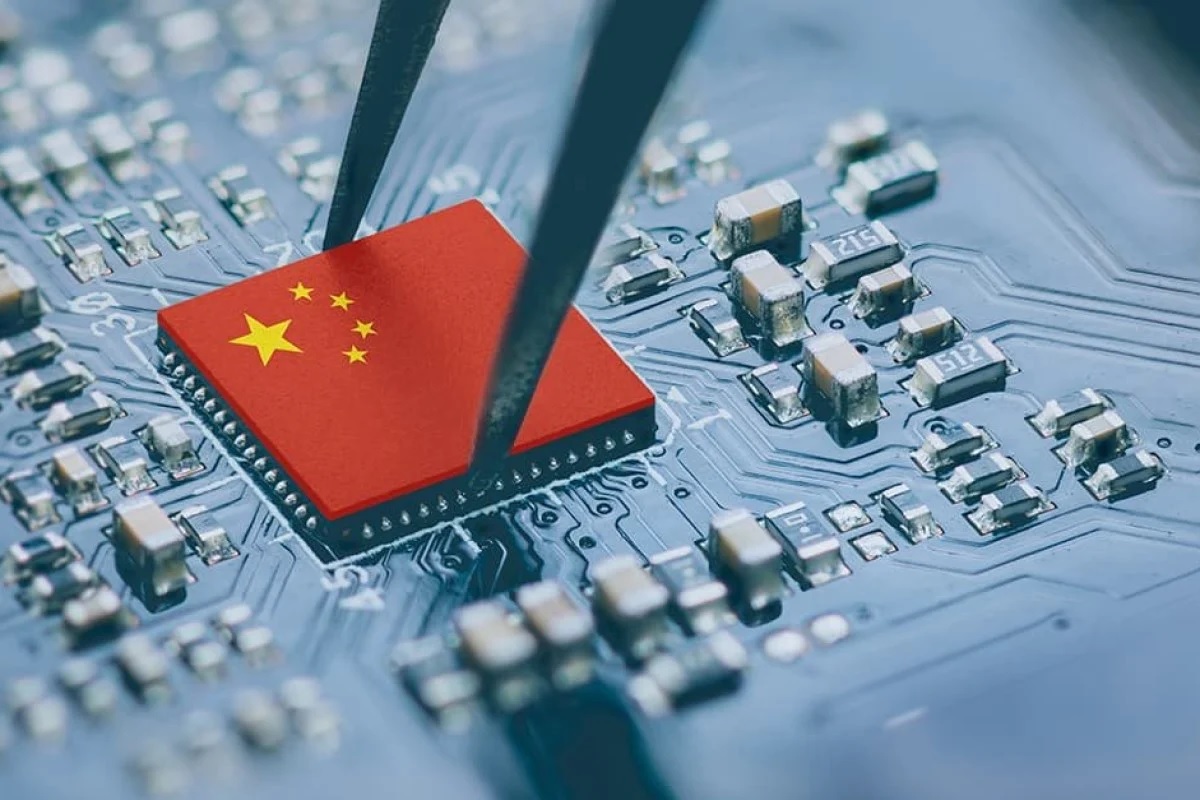মৃত্যু ও পরিসংখ্যান: গত তিন মাসে প্রাণ হারিয়েছে শতাধিক
২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাস ধরে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অপ্রতিরোধ্য হারে বাড়ছে। বিশেষ করে শেষ তিন মাস—মে, জুন ও জুলাইয়ে—ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র তিন মাসেই ডেঙ্গুতে মারা গেছে প্রায় ১৪০ জন মানুষ। ইতোপূর্বে ঢাকাসহ ঢাকার শহরতলীতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলেও এবার মফস্বল এলাকাতেও মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
গত বছরের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা। অধিকাংশ মৃত্যুই হয়েছে শক সিনড্রোম বা ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের কারণে—যেখানে সময়মতো প্লাজমা বা পর্যাপ্ত স্যালাইন না পেলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে।
কোন অঞ্চল সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত?
বর্তমানে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল—বিশেষ করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী ও বান্দরবান—ডেঙ্গু সংক্রমণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। ঢাকা শহর বরাবরের মতোই ডেঙ্গুর মূল কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গেছে, বিশেষ করে পুরান ঢাকা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এছাড়া খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, এমনকি রংপুরেও এবার ডেঙ্গু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।
সাধারণত বর্ষাকালে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ে, কারণ এ সময় জমে থাকা পানিতে এডিস মশা সহজেই বংশবিস্তার করে। কিন্তু এবারের মতো এমন বিস্তার অতীতে দেখা যায়নি। একাধিক জেলায় সতর্কাবস্থা জারি থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতির কারণে তা খুব একটা কার্যকর হয়নি।

সরকারের ব্যর্থতা: কেন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না স্বাস্থ্য বিভাগ?
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনগুলো প্রতি বছর এডিস মশা নিধনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে—যেমন ফগার মেশিনে কীটনাশক ছিটানো, লার্ভা ধ্বংস অভিযান, সচেতনতামূলক প্রচার ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
প্রথমত, অধিকাংশ অভিযান নিয়মিত না হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলভাবে পরিচালিত হয়—অর্থাৎ মৃত্যুর খবর বা গণমাধ্যমে সংবাদ ছড়ালে তৎপরতা শুরু হয়, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়।
দ্বিতীয়ত, ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও রয়েছে অভিযোগ। অনেক এলাকাবাসীর দাবি, ফগার মেশিন চালানো হলেও মশা মারা পড়ছে না; বরং ওষুধের গন্ধও টের পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে পুরনো, মেয়াদোত্তীর্ণ বা মানহীন কীটনাশক ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে।
তৃতীয়ত, এলাকাভিত্তিক ডেঙ্গু হটস্পট চিহ্নিত করার পরেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর বা টেকসই কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। বরং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে দায় এড়ানোর প্রবণতা স্পষ্ট। যেমন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দায় চাপায় সিটি করপোরেশনের ওপর, আবার সিটি করপোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগের অকার্যকারিতা তুলে ধরে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব
ডেঙ্গু এখন আর শুধুমাত্র মৌসুমি রোগ নয়; এটি একটি সারাবছরের জনস্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে একে প্রতিরোধে এখনো কোনো সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। অধিকাংশ উদ্যোগই স্বল্পমেয়াদি ও সংকটকেন্দ্রিক। মশা নিধনে একবার অভিযান চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়; বরং বছরের সব সময়ই নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নগর পরিকল্পনায় বড় ধরনের সংস্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নির্মাণাধীন ভবনে পানি জমে থাকা রোধ, নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়—এই সকল উপায়েই ডেঙ্গুর মতো মহামারি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি
ডেঙ্গু এখন শুধু একটি স্বাস্থ্যগত সংকট নয়; এটি একটি সামাজিক, পরিবেশগত এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। প্রতিবারের মতো এবারও কর্তৃপক্ষ দেরিতে তৎপর হয়েছে। কিন্তু বারবার এই সংকট ফিরে আসা মানে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে। মৃত্যুহার ও রোগীর চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এখনই সময় একটি জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ কৌশল গ্রহণের—যা হবে বিজ্ঞানভিত্তিক, সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি। অন্যথায়, এই ব্যাধি প্রতি বছর আরও প্রাণঘাতী রূপ নিয়ে ফিরে আসবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট