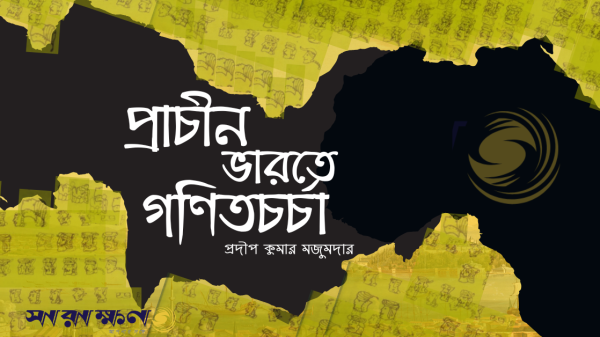গণতান্ত্রিক বিশ্বজুড়ে যখন কর্তৃত্ববাদী নেতারা প্রভাব বাড়াচ্ছে—শুধু হাঙ্গেরি বা তুরস্কতেই নয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও—তখন বিংশ শতকের একটি প্রশ্ন একবিংশ শতকে আবার ফিরে এসেছে। প্রশ্নটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান—সবার জন্যই চাপ সৃষ্টি করে: কে স্বৈরশাসকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, আর কে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে?
এই প্রশ্নের একটি ইঙ্গিত মেলে তৃতীয় রাইখের ভেতরে ঘটে যাওয়া এক অসাধারণ ঘটনায়, যা প্রায় ৮০ বছর ধরে প্রায় বিস্মৃত। ঘটনাটির কেন্দ্রে ছিলেন জার্মান উচ্চসমাজ থেকে আসা প্রায় দশজন বন্ধু ও পরিচিত—অভিজাত বংশ ও পেশাজীবী এলিট উভয়ই। তাদের বৃত্তে ছিলেন দুইজন কাউন্টেস, একজন রাষ্ট্রদূতের বিধবা, এক কূটনীতিক, বর্তমান ও সাবেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, এক চিকিৎসক, একজন অগ্রগামী নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং এক সাবেক মডেল—প্রমুখ। তাদের মিলিত বৈশিষ্ট্য ছিল হিটলারের বিরুদ্ধে—বড় ও ছোট—বিভিন্ন রকম অবাধ্যতা দেখানোর প্রস্তুতি।
কিন্তু তাদের সেই অভিন্ন উদ্দেশ্যের ধারণাটি মারাত্মকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরের এক চা-আড্ডায় তারা মিলিত হন—না জেনেই যে তাদেরই একজন বাকিদের বিরুদ্ধে গেস্টাপোর কাছে গোপনে খবর দিতে যাচ্ছে। সেই বিশ্বাসঘাতকতা গ্রেপ্তার ও কারাবন্দিত্ব ডেকে আনে—এবং সেদিন উপস্থিত কয়েকজনের পরিণতি হয় মৃত্যুদণ্ডে, কারও গিলোটিনে, কারও ফাঁসিতে। এর প্রভাব শেষ পর্যন্ত নাৎসি রাষ্ট্রযন্ত্রের চূড়ান্ত শীর্ষে গিয়ে ঠেকে।
এই কাহিনির মূল রহস্য কেবল বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় নয়; বরং কেন বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ—যারা চাইলে সহজেই মাথা নিচু করে থাকতে পারত—সবকিছু ঝুঁকিতে ফেলেছিল। তারা যদি ধারা মেনে চলত, তাদের সম্পদ, পেশাজীবন ও দেশীয় সম্পত্তি সম্ভবত অক্ষুণ্ণ থাকত। যুদ্ধোত্তর সময়ও তারা অক্ষতভাবে পার করতে পারত। তবু তারা অন্য পথ নিয়েছিল।
ভাবুন অট্টো কিপকে—চা-আড্ডার সময় যার বয়স ছিল ৫৭—এক কূটনীতিক, যিনি ওয়াইমার প্রজাতন্ত্রের শেষ বছরগুলোতে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জার্মান কনসাল জেনারেলের মর্যাদাপূর্ণ পদে ছিলেন। ১৯৩৩ সালে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এক নৈশভোজে—বিশিষ্ট স্বদেশী আলবার্ট আইনস্টাইনের সম্মানে; তিনিই তখন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ইহুদি। আমন্ত্রণ গ্রহণ মানে সদ্য ক্ষমতায় বসা নাৎসি শাসকদের রোষ ডেকে আনা; অস্বীকার মানে তাদের ইহুদিবিদ্বেষী নিপীড়নের পাশে দাঁড়ানো। কিপ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং আইনস্টাইনের সম্মানে টোস্টও দেন। ফলত, তাকে বার্লিনে তলব করা হয়—ফ্যুরারের সামনেই হাজিরা দিতে।

আরও দেখুন মারিয়া ফন মাল্টজানকে—তরুণ কাউন্টেস—যিনি নিজের বার্লিনের অ্যাপার্টমেন্টকে গোপন আশ্রয়ে পরিণত করেছিলেন “সাবমেরিনদের” জন্য—অর্থাৎ যারা আড়াল-আবডালে বেঁচে থাকা বাধ্য ইহুদি; যাদের নিরাপত্তা নির্ভর করত নীরব ও অদৃশ্য থাকার ওপর। (তাদের একজন ছিলেন মাল্টজানেরই নিষিদ্ধ ইহুদি প্রেমিক।) কিংবা তার সহকর্মী কাউন্টেস লাগি জল্ফ; তিনি ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা ভেঙে তাদের জন্য বাজার-সদাই করতে যেতেন। দুই হাতে ঠাসা বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরোনো ছিল তার বহুদিনের অভ্যাস—এভাবে পথে কারও সঙ্গে দেখা হলেও বাধ্যতামূলক ‘হাইল হিটলার’ স্যালুট দিতে হাতে ফাঁকা থাকত না।
আর্কাইভ ঘেঁটে—দলের সদস্যদের রেখে যাওয়া চিঠি, ডায়েরি ও আদালতের সাক্ষ্য, এবং তাদের পরিবারের জীবিত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে—আমি কেন কয়েকজন মানুষ এক ভয়ংকর শক্তিশালী শাসনের সামনে ‘না’ বলতে পেরেছিলেন, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিবেশী কেন মাথা নত করেছিলেন—তার একটি উত্তরের খোঁজ পেয়েছি।
কয়েকজন ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খ্রিস্টান—বিশ্বাস করতেন, শেষ বিচারে তারা জবাব দেবে হিটলারের কাছে নয়, যিশু খ্রিস্টের সামনে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন সেই ভাগ্যনির্ধারক চা-আড্ডার আয়োজক, উদ্ভাবনী শিক্ষাবিদ এলিজাবেথ ফন থাডেন। তার স্কুল—তৃতীয় রাইখ শুরুর ছয় বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ইভানজেলিকাল রুরাল এডুকেশন হোম ফর গার্লস—নিঃশব্দে ইহুদি ছাত্রীদেরও আশ্রয় দিত, যখন তাদের পরিবার পাগলের মতো দেশ ছেড়ে পালানোর কাগজপত্র জোগাড়ে ব্যস্ত। ঈশ্বরের কাছেই যে তার জবাবদিহি—এই বিশ্বাসই তাকে সাহস দিয়েছিল, যখন এক গেস্টাপো পরিদর্শক স্কুলে এসে “বিশ্বাসগত ঘাটতি” খুঁজতে শুরু করেছিল—কারণ কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিল, তিনি একবার পুরাতন নিয়মের একটি গীতসংহিতা আবৃত্তি করেছিলেন; তাদের কাছে যা ‘হিব্রু ধর্মগ্রন্থের কলঙ্ক’ বহন করত। (১৩ বছর বয়সী এক ছাত্রীই ছিল তথ্যদাতা।)
দলের আরও কয়েকজন ছিলেন অভিজাত বংশোদ্ভূত, যারা মনে করতেন তাদের সর্বোচ্চ আনুগত্য জাতীয় সমাজতন্ত্রের নয়, বরং নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রতি। হিটলার হাজার বছরের রাইখের স্বপ্ন দেখলেও, এসব পরিবার তো শতাব্দীর পর শতাব্দী জার্মানিকে শাসন করেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল—তাদের শ্রেণিই জার্মানির গভীর ও প্রকৃত সত্তা, যার অংশ হলো দুর্বলদের প্রতি পিতৃতান্ত্রিক সদয়তা। নাৎসিবাদ এক ক্ষণস্থায়ী মোহ; টিকে থাকবে তারা এবং তাদের অভিজাত উত্তরাধিকার।

এই বিশ্বাস থেকেই মারিয়া ফন মাল্টজান এমন ঔদ্ধত্যভরা অস্থিরতায় গেস্টাপো কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলেন, যখন তারা তার অ্যাপার্টমেন্টে হানা দেয়। তারা যখন সোফা-বেডের নিচে কাঠের খোপটি খুলতে বলেন—যার ভেতরে তার প্রেমিক নিঃশ্বাস বন্ধ করে লুকিয়ে ছিলেন—তিনি জানান, খোপটি খোলা যায় না; যদি সত্যিই সন্দেহ থাকে, তবে গুলি চালিয়ে দেখুক। যেন প্রায় উস্কে দিলেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন—কোনো ক্ষতি হলে তাদের আগেভাগে লিখিতভাবে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তার এই কৌশল—নিজ শ্রেণির অহংকারে মোড়া—কাজ করে। তার প্রেমিক বেঁচে যায়।
এই নাটকের কয়েকজন মুখ্য নায়ক ছিলেন নারী—যাদের বেড়ে ওঠায় আরেকটি মিল ছিল: দৃঢ়চেতা পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এলিজাবেথ ফন থাডেন, এবং দুই কাউন্টেস—মারিয়া ও লাগি—তিনজনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা শুধু পিতৃস্নেহ পাননি; তাদের ওপর পিতার আস্থা ছিল অগাধ। আধুনিক নারীবাদের আগের যুগেই তাদেরকে কোনো পুরুষের সমান ধরে যেকোনো কাজের যোগ্য বলে মনে করা হতো। বহু বছর পর, পিতারা মৃত, কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস তারা বয়ে নিয়ে চলেছেন। নাৎসি শাসনের সময় সেই আত্মবিশ্বাসই সাহসে রূপ নেয়।
এই নারীদের শক্তি আরেক গভীর বিশ্বাসে বলীয়ান হয়—যা সম্ভবত নির্ধারণ করে দেয় কে নিপীড়ক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে আর কে চাপের মুখে ভেঙে পড়বে: দিনের সরকারের ঊর্ধ্বে কোনো কর্তৃত্বে আস্থা। চা-আড্ডার বেশিরভাগ বিদ্রোহীই বুঝতে পেরেছিলেন—এমন বিশ্বাস কেবল মনে রাখা নয়, কাজেও প্রতিফলিত করতে হয়।
কারও ক্ষেত্রে তা ছিল ছোট ছোট অবাধ্যতা—লাগি জল্ফের বাজারের ব্যাগের মতো। আবার অট্টো কিপের মতো কারও ক্ষেত্রে তা ছিল দুর্দান্ত প্রতিরোধ—হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের একেবারে নাগাল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। বড় ও ছোট এসব কাজে তারা নিজেদের কাছে এবং একে অপরের কাছে প্রমাণ করেছেন—আজ্ঞাপালনই একমাত্র বিকল্প নয়।
স্পষ্ট করে বলা দরকার—অভিজাত জার্মানদের অধিকাংশই হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। উল্টো, ওয়াইমার যুগে বিলুপ্ত উপাধি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্যুরার যে টান দিয়েছিলেন, তাতে জার্মান অভিজাত শ্রেণির বড় অংশ নাৎসিদের পাশেই দাঁড়ায়। আর অবশ্যই, সেই সময় ও স্থান থেকে সরল রেখায় শিক্ষা নিয়ে আজকের যুগে বসিয়ে দেওয়াও যায় না।
তবু যদি ওই নারী-পুরুষদের প্রাণঘাতী পরিণতি থেকে কোনো শিক্ষা নিতে হয়, তা হতে পারে—স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা হলো এমন মানুষের বিস্তৃত বাহিনী, যারা যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি, রাজপুত্র—অথবা রাষ্ট্রপতির চেয়েও উচ্চতর এক কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে।

 জোনাথান ফ্রিডল্যান্ড
জোনাথান ফ্রিডল্যান্ড