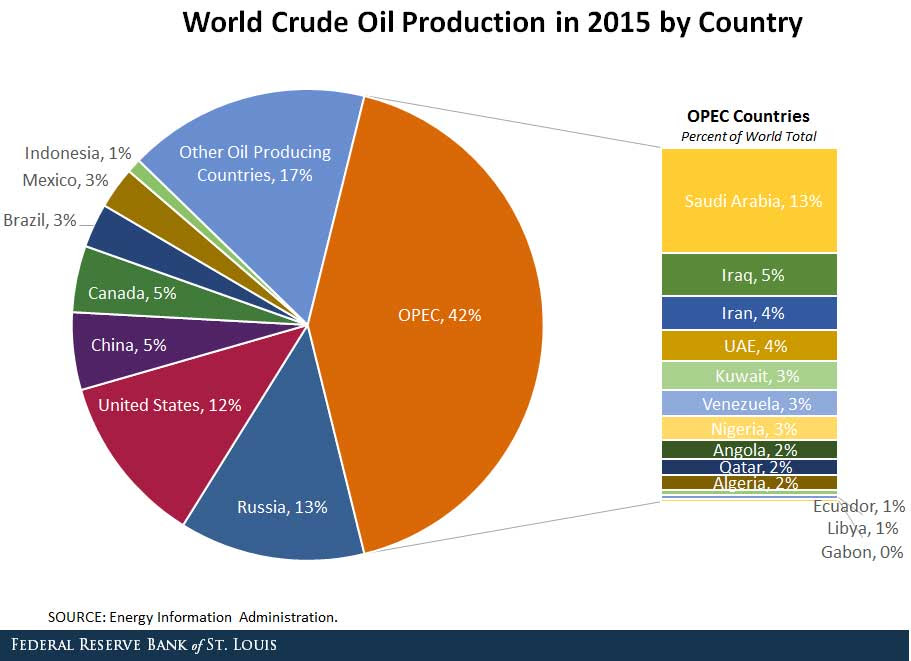কিছুদিন আগে কয়েকজন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল—তাদের সবচেয়ে বড় ভয় কী। উত্তরে কেউ বলেছিল, ভুল করে কিছু করলে বকা খাওয়া, কেউ বলেছিল বন্ধুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, কেউ বলেছিল আমি ফেল করব, কেউ বলেছিল নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, আবার কেউ বলেছিল বাবা-মাকে হতাশ করার ভয়।
এই বিষয়গুলো কি কখনও শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করা হয়েছে—এই প্রশ্নে নেমে এসেছিল নীরবতা।
শিশুদের প্রয়োজন তাদের দুশ্চিন্তা ও সন্দেহের কথা বলার সুযোগ, কেন তারা রেগে যায় বা কেন নিজেকে সামলাতে পারে না—তা নিয়ে কথা বলা। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কই জানেন, মানসিকভাবে স্থিতিশীল শিশু পড়াশোনায়ও বেশি মনোযোগী হয়। তবু প্রত্যাশার এমন এক দমনমূলক চাপ রয়েছে যে অধিকাংশ শিক্ষকই অতিরিক্ত কাজ ও ক্লান্তিতে জর্জরিত হয়ে তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালকদের বলতে পারেন না—একটি শিশুর নিজের সম্পর্কে বোঝাপড়া একাডেমিক বিষয়ের জ্ঞানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।
যখন আমাদের মতো মৌখিক ও ঐতিহ্যনির্ভর সমাজে পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষা চালু হয়েছিল, তখন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সহায়ক দিকনির্দেশনার কোনো জায়গা রাখা হয়নি। কেউ ভাবেনি যে শিশুদের শৃঙ্খলা, নিয়ম আর পাঠের বাইরেও কিছু প্রয়োজন হতে পারে। যত বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনায় ডুবে গেছে, ততই সে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ ও নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে গেছে। শিশুর পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত পুরো প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন বস্তুগত জগতেই কেন্দ্রীভূত থেকেছে, আর সেই পরিকল্পনাই আজও চলমান।

উচ্চস্তরের চিন্তাশক্তি—কেউ চাইলে একে আধ্যাত্মিক বিকাশও বলতে পারেন—যা গভীর ও ঘনিষ্ঠ এক অভিজ্ঞতা, ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন হলেও আলোচনার প্রয়োজন ছিল, তা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেছে। শিক্ষা এখন পরীক্ষায় পাস করার একটি পদ্ধতিতে রূপ নিয়েছে। গত এক দশক বা তার বেশি সময়ে কিশোর আত্মহত্যা ও শিশুদের মধ্যে সহিংসতা বাড়তে থাকায় একটি প্রশ্ন বারবার ফিরে এসেছে—একাডেমিক উৎকর্ষের পথে আমরা কি কিছু হারিয়ে ফেলেছি? আমরা জানি, এই ব্যবস্থাকে পুরোপুরি উল্টে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে শিক্ষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্রিয় সহযোগিতায় নিশ্চয়ই একে সংশোধন করা যায়, যাঁরা সবাই আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।
একটি সভ্য সমাজে—এবং আমরা নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে নিরন্তর গর্ব করি—প্রতিটি প্রজন্মের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সমাজকে আরও ভালো ও নিরাপদ করে তোলা। সেই কারণেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বিপুল। সহযোগিতামূলক বিকাশের মূল্য, সহমর্মিতা, অনুভূতি ও পার্থক্য ব্যবস্থাপনার শিক্ষা জীবনের শুরুতেই দিতে হয়। সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিকতার একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক রূপান্তর কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে বহু ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষককে জাগরণের দূত হিসেবে গড়ে তুলতে কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন—সে বিষয়ে প্রায় কিছুই বলা হয়নি।
সবকিছুই যে অন্ধকার, তা নয়।
সম্প্রতি আমি একটি ভিডিও দেখেছি, যেখানে সহস্রাব্দ প্রজন্মের সামাজিক ও আবেগগত সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। সেখানে যে শীতল করা ত্রুটিগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল অধিকারবোধ, আত্মমগ্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, কম সহনশীলতা এবং দীর্ঘ সময় কোনো বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখতে না পারা। এটি হয়তো তাদের কারও ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে নয়। বিশ্বজুড়ে বহু তরুণ সাহায্যের আহ্বানে আন্তরিক সাড়া দিচ্ছে। বিপদে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য সাহায্যের অনুরোধ বা পশু আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য খাদ্য ও অনুদানের আবেদন জানানো মাত্রই ফোনকল ও আশ্বাসের ঢল নামে। এদের অনেকেই স্কুলপড়ুয়া। এর অর্থ কী? কেউ তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কিছুর স্পর্শে তাদের ভেতরের সেরাটা বেরিয়ে এসেছে।

মূল্যবোধ শেখানো যায় না, কেবল আত্মস্থ করা যায়—এই ধারণার একটি প্রচলিত পাল্টা যুক্তি হলো, আমরা তা শিখেছি আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু পরিবার যদি এতটাই ব্যস্ত থাকে যে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে না পারে, তবে শিশুরা কার সঙ্গে কথা বলবে, কার কাছ থেকে শিখবে? বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এমন একটি নীতি বাস্তবায়ন করা যায়, যা ক্রমশ বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের গুরুত্ব ও দায়িত্বের ধারণা গড়ে তোলে। এতে অন্তত সেই শিশুদের প্রভাবিত করা সম্ভব, যারা স্কুলে যেতে পারে এবং একদিন নিজেদের সমাজ ও সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেবে। তারাই লিখবে ও শেখাবে, শহর গড়বে, নতুন ওষুধ ও প্রযুক্তির পেটেন্ট করবে, নীতি ও আইন প্রণয়ন করবে।
এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন এক বাস্তবতায়, যেখানে দশ বছরের নিচে বয়সী লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শিশুর শিক্ষার কোনো আশা নেই। অশিক্ষার কারণে তারা বঞ্চিত এবং চারপাশের সব নেতিবাচক শক্তির সামনে অসহায়। তাহলে কি আমাদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় না—ঐতিহ্য ও পূর্বধারণাভিত্তিক সীমিত জ্ঞান অতিক্রম করার? আধুনিক জীবনের তীব্র প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই বহু তরুণকে এমন অবস্থায় ফেলেছে, যেখানে উদ্বেগ, ভয় ও ক্রোধ মোকাবিলার মতো কোনো ভেতরের শক্তি তাদের নেই। কিছু ছোট শিশু এতটাই একাকী ও অস্থির যে ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে, পছন্দের পোশাক না পেলে বা ইংরেজি ভাষার ক্লাসে নিজেকে অযোগ্য মনে করলে তারা নিজের জীবন শেষ করে দেয়।
শান্তির জন্য শিক্ষা বলতে পরিবার, সমাজ, জাতি ও বিশ্বে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করাকে বোঝায়। ছয় বছরের একটি শিশু সামাজিক ন্যায়ের ধারণা বুঝতে পারবে না। কিন্তু চৌদ্দ বছরের একটি কিশোর তা বুঝতে পারে এবং বুঝতেই হবে। ছয় বছরের শিশুকে বলা যায়, মজা করার জন্য একটি কুকুরছানার দিকে পাথর ছোড়া যাবে না। পনেরো বছরের কিশোর বুঝতে পারে—পাতা, পাখি, পোকামাকড়, মানুষ ও জলবায়ু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।
যদি আমাদের এমন এক দরিদ্র হয়ে পড়া পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়, যা তার খাদ্যভাণ্ডার বা দুর্ভিক্ষ, জলসম্পদ বা বন সামলাতে পারছে না, তবে যত দ্রুত সম্ভব শিশুদের এই বোধে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে যে পৃথিবীর এক প্রান্তে একটি গোষ্ঠীর ওপর যা ঘটে, শেষ পর্যন্ত তা সবার ওপরই প্রভাব ফেলে। আমরা শিশুদের সুস্থ রাখার কৌশল শিখেছি, কিন্তু তাদের হৃদয় ও মনের দিকে কম মনোযোগ দিয়েছি। নিঃসন্দেহে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষকে অর্থবহ জীবন যাপনের যোগ্য করে তোলা, কেবল জীবিকা নির্বাহের উপায় শেখানো নয়।

 মিনি কৃষ্ণান
মিনি কৃষ্ণান