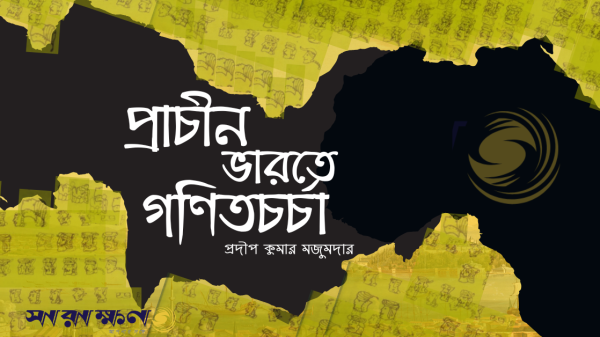মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “আমেরিকা ফার্স্ট” নীতিভিত্তিক প্রতিদানমূলক শুল্ক ব্যবস্থার ফলে যে অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে এবং ক্রমাগত পরিবর্তিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন করার যে তাড়াহুড়া চলছিল, তা আপাতত স্থিত হলেও এর প্রভাব এখনো শেষ হয়নি। নতুন মার্কিন শুল্ক এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চুক্তি আদায়ের প্রবণতা দীর্ঘস্থায়ী হবে—এমন ধারণা স্পষ্ট হওয়ায় দেশগুলো বিকল্প বাজারের খোঁজে নেমেছে। এতে কিছুটা আশাবাদ তৈরি হলেও এই আশাবাদ এখনই বাস্তবে রূপ নেবে না। নিয়মনির্ভর বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থার ভাঙনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাক্কা সামনে রয়েছে; আরও বড় ধরনের ব্যাঘাত ও বাজার-অস্থিরতার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
আমেরিকার শুল্ক ও চীনের উদ্বৃত্ত সক্ষমতা
চীনের ওপর মার্কিন শুল্কের প্রাথমিক প্রভাব স্পষ্ট: যুক্তরাষ্ট্রগামী কিছু রপ্তানি কমবে। মহামারির পর চীনের পুনরুদ্ধার ধীরগতির, রিয়েল এস্টেট খাতও টালমাটাল। তাই ভর্তুকি ও বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে উৎপাদন খাতকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলবে। অতীতে অতিরিক্ত শিল্পক্ষমতার পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকত, ফলে সেখানকার উৎপাদনভিত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখন চীন সেই পণ্য অন্যত্র বিক্রি করতে চাইবে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সস্তা আমদানির চাপ
ইতোমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে চীনের উদ্বৃত্ত উৎপাদন কমদামে ঢুকে দেশীয় শিল্পের টিকে থাকা কঠিন করে তুলছে। থাইল্যান্ডে গত দুই বছরে ইলেকট্রনিক্স, আসবাব, পোশাক ও গাড়িসহ বিভিন্ন খাতে চার হাজারের বেশি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে—সস্তা চীনা আমদানিকে বড় কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার টেক্সটাইল খাতেও একই চাপের মুখে বহু চাকরি হারিয়েছে। ফলে দেশগুলো সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে: ভিয়েতনাম চীনা হট-রোলড স্টিলের ওপর সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক বসিয়েছে; ইন্দোনেশিয়া চীনা নাইলন ফিল্মের ওপর চার বছরের অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক ঘোষণা করেছে; থাইল্যান্ড চীনা অ্যালয় হট-রোলড কয়েলে ৩০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়ে ফাঁকফোকর বন্ধ করেছে। এমন আরও পদক্ষেপ বাড়বে বলেই ধারণা।

চীনের পাল্টা প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী
কোনো পূর্বাভাসেই চীনের নীরবতা ধরে নেওয়া উচিত নয়। বাণিজ্য ও বিনিয়োগক্ষেত্রে পাল্টা ব্যবস্থা আসবেই।
ভিয়েতনামের ‘প্লাস ওয়ান’ থেকে ‘মাইনাস ওয়ান’?
দীর্ঘদিন ‘চায়না প্লাস ওয়ান’ কৌশলে নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে ভিয়েতনাম সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু যদি যুক্তরাষ্ট্র-চীন কোনো চুক্তিতে চীনের ওপর শুল্ক কমে ভিয়েতনামের সমপর্যায়ের কাছে চলে আসে, তবে সেই সুবিধা হারিয়ে যেতে পারে। ট্রাম্প ইঙ্গিত দিচ্ছেন চুক্তির দিকে—তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের যুক্তরাষ্ট্র ট্রানজিট পরিকল্পনা বাতিল, ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি সামরিক সহায়তা আটকে রাখা, চীনের দিকে সংবেদনশীল প্রযুক্তি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা বিরতি—যদিও প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে দ্ব্যর্থক বার্তা এসেছে। যদি শুল্ক-সুবিধা কমে, তবে ‘ভিয়েতনাম প্লাস ওয়ান’ হারিয়ে ‘ভিয়েতনাম মাইনাস ওয়ান’ হতে পারে—কারখানা ও প্রবাহ আবার চীনে ফিরতে পারে। সরবরাহচেইনের পুনর্বিন্যাস ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।
‘এশিয়া ফর এশিয়া’: যুক্তিযুক্ত কিন্তু সময়সাপেক্ষ
সরকার, ব্যবসা ও বিনিয়োগকারীরা এখন ‘এশিয়া ফর এশিয়া’—অর্থাৎ এশিয়ার মধ্যেই উৎস, উৎপাদন ও সেবার জাল গড়ে তোলা—এ দিকে ঝুঁকছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত উত্থান-পতনের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতা গড়তে এটি যৌক্তিক। কিন্তু বহু দেশের জন্য মার্কিন বাজার এখনো অপরিহার্য। ২০২৪ সালে কেবল ভিয়েতনামের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল রেকর্ড ১২৩ বিলিয়ন ডলার; গোটা অঞ্চলের উদ্বৃত্ত ২২৭ বিলিয়ন ডলার। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কিছুটা কমতে পারে, তবে এতে বছর লেগে যাবে।
অধিক সরবরাহ, কম মুনাফা—নতুন বাস্তবতা
সবাই যদি ‘এশিয়া ফর এশিয়া’ গ্রহণ করে, তবে তুলনামূলক ছোট ও উন্নয়নশীল বাজারে সরবরাহ দ্রুত বাড়বে; প্রতিযোগিতা তীব্র হবে, মুনাফার হার কমবে। আবার যুক্তরাষ্ট্র-নির্ভর কোম্পানিগুলোর গ্রাহকরা খরচ কমাতে পারে—ফলে দেশীয় কোম্পানির আয় আরও চাপে পড়বে।
সামনের ঝড়: উৎসদেশ জালিয়াতি ও খাতভিত্তিক শুল্ক
যুক্তরাষ্ট্রে ‘ট্রানশিপমেন্ট’ ঠেকাতে নকল উৎসদেশ নথি দেওয়া কোম্পানিগুলোকে শাস্তি দিতে বিচার বিভাগ ক্রমবর্ধমানভাবে ‘ফলস ক্লেইমস অ্যাক্ট’ প্রয়োগের ঘোষণা দিয়েছে—নজিরবিহীন কড়াকড়ি আসতে পারে। পাশাপাশি খাতভিত্তিক ‘জাতীয় নিরাপত্তা’ শুল্ক—যেমন গাড়ি, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামে ২৫–৫০ শতাংশ; ওষুধে সম্ভাব্য ২৫০ শতাংশ—শিগগিরই কার্যকর হতে পারে। এ অবস্থায় প্রতিদানমূলক শুল্কগুলো কেবল ‘ওয়ার্ম-আপ’ মনে হতে পারে।

‘ড্যামোক্লেসের তলোয়ার’ হয়ে শুল্কের হুমকি
নতুন চুক্তিগুলোর বিনিয়োগ বা ক্রয়-অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট না হলে, অংশীদারদের মাথার ওপর উচ্চ শুল্কের হুমকি ঝুলে থাকবে। এমনকি বাণিজ্য-বহির্ভূত ইস্যুতেও (যেমন ব্রাজিল বা ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে) শুল্কের চাপ আসতে পারে। শুধু ওয়াশিংটন থেকেই নয়, অস্থিরতা ও চাপ আসবে অন্য দিক থেকেও।
বেইজিংয়ের চাপ ও দ্বিমুখী ঝুঁকি
চীনও কোম্পানিগুলোর ওপর চাপ বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে। তাদের ‘অ্যান্টি-ফরেন স্যাংশনস’ আইন অনুযায়ী, যারা চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মানবে—বিশেষত জোরপূর্বক শ্রমবিরোধী মার্কিন আইনের প্রয়োগে—তাদের শাস্তির মুখে পড়তে হবে। ফলে কোম্পানিগুলো দুই দিক থেকেই ঝুঁকিতে পড়বে।
নতুন বৈশ্বিক নিয়ম—এখনই নয়
ট্রাম্প-পরবর্তী ভাঙা ব্যবস্থার জায়গায় নতুন বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থা গড়তে বহু দেশ আগ্রহী। কিন্তু তা নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব নয়। ধরে নিলেও যে একমত হওয়া গেল, বহু দেশ ও কোম্পানির জন্য মার্কিন ভোক্তাকে কেউ প্রতিস্থাপন করতে পারবে না—এই কার্ডটি ট্রাম্পের হাতেই রয়েছে।
করণীয়
ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ নিয়ে অভিন্ন অনীহা এশিয়াকে কিছুটা একতাবদ্ধ করলেও কেবল অনুভূতি দিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়া যাবে না। সরকার, করপোরেট নির্বাহী ও বিনিয়োগকারীদের এখনই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ঢেউয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে—ঝুঁকি চিহ্নিত করে কৌশল সাজাতে হবে। ট্রাম্পের এই নীতিগুলো শিগগিরই কাউকে—না আমেরিকা, না এশিয়াকে—‘মহান’ করে তুলবে না; তাই আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই।

 স্টিভেন ওকুন ও স্টিফেন ওলসন
স্টিভেন ওকুন ও স্টিফেন ওলসন