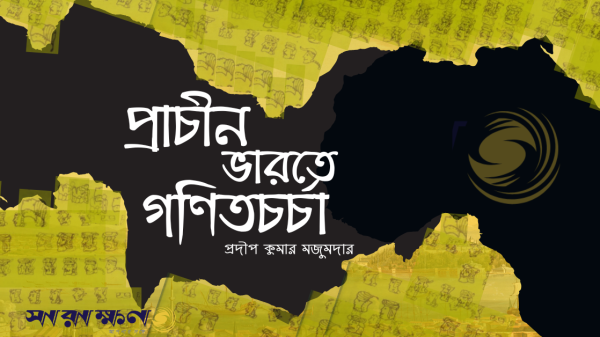ট্রাম্প যদি আজ থেকে দশ বছর আগে তার এই ট্যারিফ যুদ্ধটা শুরু করার সুযোগ পেতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেত, আমেরিকা জিতত এই অর্থনৈতিক যুদ্ধে। কারণ, তখন এশিয়া ছিল শুধুমাত্র প্রোডাকশন হাউস। সস্তা শ্রমিকের কারণে কম মূল্যে পণ্য তৈরি করা যেত, আর সে পণ্য পশ্চিমে বিক্রি করতে হতো। বাজার ছিল পশ্চিমই একমাত্র।
এখন এশিয়ার বড় অংশের বাস্তবতা ভিন্ন। এখন এশিয়ার বড় অংশ শুধু প্রোডাকশন হাউস নয়, তাদের নিজস্ব বড় মার্কেটও আছে। তাছাড়া এশিয়ায় উৎপন্ন পণ্যের এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বড় বাজার সৃষ্টি হয়েছে।
তাই এমন সময়ে ট্রাম্পের বা আমেরিকার এই ট্যারিফ যুদ্ধ পৃথিবীতে কাকে কোন অবস্থানে নিয়ে যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।
আমেরিকার অবস্থান ও এশিয়ার উত্থান
অনেকে হয়তো মনে করছেন, ট্রাম্প ব্যবসায়ী, কথাবার্তার ধরনে একটু খ্যাপাটে মনে হয় বলেই তিনি এমন একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধে নেমেছেন। বাস্তবে এমন চিন্তা খুব বেশি যুক্তিযুক্ত নয়।
আমেরিকা দিন দিন তার অর্থনৈতিক শক্তি হারাচ্ছে, এবং তার বিপরীতে চায়না, ভারত, রাশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ মিলে বিকল্প অর্থনীতির শক্তি হিসেবে নানা কেন্দ্র হয়ে উঠছে। পাশাপাশি ছোট ছোট অনেক এশীয় দেশও অর্থনীতিতে ভালো করছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের সম্ভাবনা ও বিপর্যয়
মধ্যপ্রাচ্য যদি যুদ্ধের কবলে না পড়ত— যদি ইরাক, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া ধ্বংস না হতো— তাহলে মধ্যপ্রাচ্য শুধু তেল বিক্রির অর্থনীতি নয়, আরও বহুমাত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারত।
মধ্যপ্রাচ্যের নতুন প্রজন্ম যারা বিদেশে পড়াশোনা করেছে, আধুনিক বিশ্ব ও আধুনিক জীবনযাত্রা তাদের কাছে পরিচিত— তারাও দেশে ফিরে উৎপাদনমুখী অর্থনীতি তৈরির কাজে যুক্ত হতো।
প্রায় পঁচিশ বা তিরিশ বছর আগে কোন একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বইয়ে বা পত্রিকায় মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজন তরুণের সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। তারা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। ছুটিতে দেশে ফেরার পথে প্লেনে তাদের সঙ্গে ওই লেখক ও সাংবাদিকের আলাপ হয়। ওই ছাত্ররা বলেছিল, মধ্যপ্রাচ্যের ধনীদের ছেলেদের মতো তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে না আমেরিকায়; বরং তারা বাস্তব জীবন জানার চেষ্টা করছে এবং ভবিষ্যতে দেশে ফিরে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা করছে। তাদের দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আছে, তাছাড়া তারা রপ্তানির বাজারও জানে।
আরব বসন্ত ও তার ফলাফল
এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, ওই ছেলেরা এখন কোথায় আছে, কী করছে? কারণ, গত তিরিশ বছরে ইরাকের অর্থনীতি ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে বায়োলজিক্যাল অস্ত্র খোঁজার নামে। ইরান নিষেধাজ্ঞার কবলে— সেখানে পরমাণু অস্ত্র তৈরি হচ্ছে এমন অভিযোগে।
আর তিউনিসিয়ায় এক শিক্ষিত ফল বিক্রেতার গায়ে আগুন দেওয়ার মাধ্যমে যে রঙিন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অর্থনীতি ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব বড় বাজারে।
শুধু তাই নয়, এই দেশগুলোর শক্তিশালী নেতারাও নিহত হয়েছেন— কারণ, “লিডার ইজ দ্য লাইট অফ এ কান্ট্রি।” তাদের নিহত হওয়া শেষ বিচারে অনেক কিছু।
মিশরের আরব স্প্রিংয়ের খবর প্রতিদিন পেতাম তাজউদ্দিন আহমদের পালিত কন্যা রিপি ও তার মিশরীয় ব্রাদারহুড নেতা স্বামীর মাধ্যমে। খবরগুলো ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, ওই সময়ে যে সংবাদপত্রে কাজ করতাম তার জন্যও সুবিধাজনক, তবু বিস্মিত হতাম— কেন মিশরে ডানপন্থীরা এভাবে গণতন্ত্র চাইছে, আর বিকল্প নেতা কে?

রঙিন বিপ্লবের প্রভাব
এখন দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া এমনকি আফ্রিকার ছোট ছোট দেশ— যেগুলো বাজার গড়ে তুলছে বা অভিজ্ঞ নেতৃত্ব পাচ্ছে— সেগুলোতেও গণতন্ত্রের এই রঙিন ছোঁয়া লাগছে।
২৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ‘ডন’ পত্রিকায় আসিম সাজ্জাদ আখতার তিউনিসিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়ার এই রঙিন বিপ্লব নিয়ে একটি দীর্ঘ লেখা লিখেছেন। লেখার প্রায় শুরুতেই তিনি লিখেছেন:
“In 2011, the much feted Arab Spring was triggered by the self-immolation of a well-educated street vendor in Tunisia, spreading to Egypt, Bahrain and many other countries. Millions of people came out onto the streets in defiance of dictators and monarchs who had ruled with an iron fist for decades.
The people had their victory, deposing hated figures like Zine El Abidine Ben Ali and Hosni Mubarak. But ultimately, the Arab Spring left a bitter taste. Authoritarian regimes and an even more exploitative capitalist order were restored in almost all of the Middle East and North Africa. Countries like Syria and Libya were ravaged by imperialist-sponsored proxy wars. Almost 15 years on, the status quo has not only been restored but appears even more entrenched.”
(২০১১ সালে বহুল প্রশংসিত ‘আরব বসন্ত’-এর সূচনা হয়েছিল তিউনিসিয়ার এক শিক্ষিত পথবিক্রেতার আত্মাহুতির মাধ্যমে। সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মিসর, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে। লাখো মানুষ নেমে আসে রাস্তায়— দশকের পর দশক লোহার মুঠোয় দেশ শাসন করা একনায়ক ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয় তারা।
শুরুতে জনগণ জয়ী হয়েছিল। পতন ঘটে তিউনিসিয়ার জিন এল আবিদিন বেন আলি ও মিসরের হোসনি মোবারকের মতো নিন্দিত শাসকদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘আরব বসন্ত’ এক তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার প্রায় সব দেশেই পুরনো স্বৈরশাসন ফিরে আসে, সঙ্গে আরও শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়া ও লিবিয়ার মতো দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পরিচালিত প্রক্সি যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রায় পনেরো বছর কেটে গেলেও, আরব বিশ্বের সেই পুরনো ক্ষমতাকাঠামো শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠিতই হয়নি— বরং আগের চেয়েও গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে পড়েছে।)
প্রক্সি যুদ্ধ ও অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু
আসিম সাজ্জাদ আখতারের লেখায় যেমন জানা যায়, তেমনি গোটা পৃথিবী জানে— ওই দেশগুলো প্রক্সি যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ যারা বিদেশে পড়াশোনা শেষে দেশে এসে শিল্প গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল, তারা এখন দূরে বসে আমাদের মতোই ধ্বংসস্তূপ দেখছে, চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি বা সংবাদে।
এই সব ধ্বংসস্তূপ ও প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে আরও কিছু বাজার ও অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হওয়া ঠেকানো হয়েছে। ফলে এখন ট্যারিফ যুদ্ধ চলছে এশিয়ার কয়েকটি বড় দেশসহ রাশিয়ার মতো কিছু দেশের সঙ্গে। যদিও রাশিয়া নিষেধাজ্ঞার কবলে।

ট্যারিফ যুদ্ধের ধারাবাহিকতা
বর্তমানে যে ট্যারিফকে “ট্রাম্পের ট্যারিফ” বলা হচ্ছে, এটি কোনো হঠাৎ আসা অর্থনৈতিক যুদ্ধ নয়— বরং একটি ধারাবাহিক অর্থনৈতিক যুদ্ধের অংশ।
রাইজিং ইকোনমিগুলো সফলভাবে ফলিং ইকোনমির সঙ্গে কূটনৈতিক খেলা খেলে বিষয়টি দীর্ঘায়িত করেছে। তাই যখন ট্যারিফ যুদ্ধ শুরু হয়েছে, ততদিনে এশিয়ার অনেক দেশ নিজস্ব বাজার বড় ও শক্তিশালী করতে পেরেছে। ফলে রাইজিং ইকোনমিগুলো ফলিং ইকোনমির সঙ্গে এখন বেশ শক্ত হাতে লড়ছে।
সামরিক ব্যয় ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ
তবে প্রশ্ন হলো, রাইজিং ইকোনমিগুলো কি তাদের সব শক্তি নিজস্ব অর্থনীতি ও বাজার তৈরিতে দিতে পারবে? কারণ, পাকিস্তানের লেখক ও ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ— “প্রক্সি ওয়ার”।
বাস্তবে অর্থনীতির এই খেলায় প্রত্যেকটি দেশকে সামরিক খাতে ব্যয় করতে বাধ্য করছে এই প্রক্সি ওয়ার— সেটা অস্ত্র উৎপাদন হোক বা কেনা হোক। এছাড়া, যেমন পাকিস্তানের আসিম সাজ্জাদসহ অনেক লেখক উল্লেখ করেছেন, প্রক্সি ওয়ারের আরেকটি বিশেষ শক্তি হলো দেশের ভেতরের সোশ্যাল ফোরামনির্ভর এক শ্রেণির তরুণ ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা।
তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, যাদের মোকাবেলায়ও বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে।
যে দেশগুলোর অর্থনীতি ভেঙে গেছে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়েছে রঙিন বিপ্লবের মাধ্যমে— সেখানে যে নেতারা বসেছেন, তাদের অধিকাংশই বিতর্কিত এবং মৌলবাদের সঙ্গে যুক্ত। সর্বোপরি তারাও খাদ্য ও কর্মসংস্থানের বদলে অস্ত্র কিনছে, যা গ্লোবাল সাউথের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।
আশার দিক
তবে এসব বাধা সত্ত্বেও এশিয়াসহ গ্লোবাল সাউথের বড় অর্থনীতিগুলো বেশ শান্ত মাথায় এগিয়ে চলছে। অনেক দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে সময়মতো যুদ্ধ থেকে রেবিয়ে আসার দক্ষতা দেখাচ্ছে। এমনকি ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও জাপান সমুদ্রসীমা নিয়ে বড় কোনো সংঘর্ষে যাচ্ছে না।
চায়নাকেও সাউথ চায়না সি নিয়ে আগের মতো আগ্রাসী অবস্থায় দেখা যাচ্ছে না; তারা সরে এসেছে ‘উলফ ওয়ারিয়র’ কূটনীতি থেকে। ভারতও নানা প্রতিকূলতার পর গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার পথে এগোচ্ছে।
শেষ বিচারে ট্যারিফ যুদ্ধের বড় অংশই ভারত ও চীনের বিরুদ্ধে, কারণ এ দুটোই বিশ্বের বড় বাজার এবং ভবিষ্যতের রাইজিং ইকোনমি। অন্যদিকে রাশিয়া এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে যা তার অর্থনীতিতে একটি বড় ঘূন পোঁকা।
পরমানু শক্তি
পাকিস্তানের কিছু থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মনে করছে, পাকিস্তান বর্তমানে কূটনৈতিক সাফল্যের উজ্জল সূর্যের আলোয় আছে। তবে অনেকেই সতর্ক করেছেন— এই ট্যারিফ যুদ্ধের সময় পাকিস্তান যে পথে হাঁটছে, তাতে সে ভেতরে ও বাইরে উভয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।
এমনকি যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যও তাকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে অস্ত্র কিনতে, এবং দেশেও ঘটতে পারে রঙিন বিপ্লব। কারণ, অনেকগুলো শক্তি এক প্লেটে নিয়ে খেলছে পাকিস্তান।
পরমাণু শক্তিধর এই ভঙ্গুর রাজনীতির পাকিস্তান তাই ট্যারিফ যুদ্ধের আরেকটি শেষ মারাত্মক ধাপ— যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণু শক্তি ব্যবহারে বিশ্ব উল্টে পাল্টে গিয়েছিল— তেমনই বিপজ্জনক অবস্থার দিকে যেতে পারে।
সব মিলিয়ে ট্যারিফ যুদ্ধ পৃথিবীকে এক ভয়াবহ সময়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে আশার বিষয় হলো, এশিয়ার রাইজিং ইকোনমিগুলো— যারা মূলত এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু— তারা খুব শান্ত মাথায়, প্রকৃত প্রেমিকের মতো এগোচ্ছে এবং নিজেদের অবস্থান ও জনগণকে শক্তিশালী করছে। তাদের এই শান্ত, ধৈর্যশীল অবস্থানই বর্তমান বিশ্বের ভরসা।
সবুরে মেওয়া ফলে
কূটনীতিতেও মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে হয়, যেমন তিনি লিখেছেন, — “ক্রুদ্ধ প্রভূর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।” শান্ত প্রেমিকের সবুরেই মেওয়া ফলুক— এটাই বর্তমান পৃথিবীর আশা ও ভরসা।
লেখক: সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সম্পাদক, সারাক্ষণ, The Present World
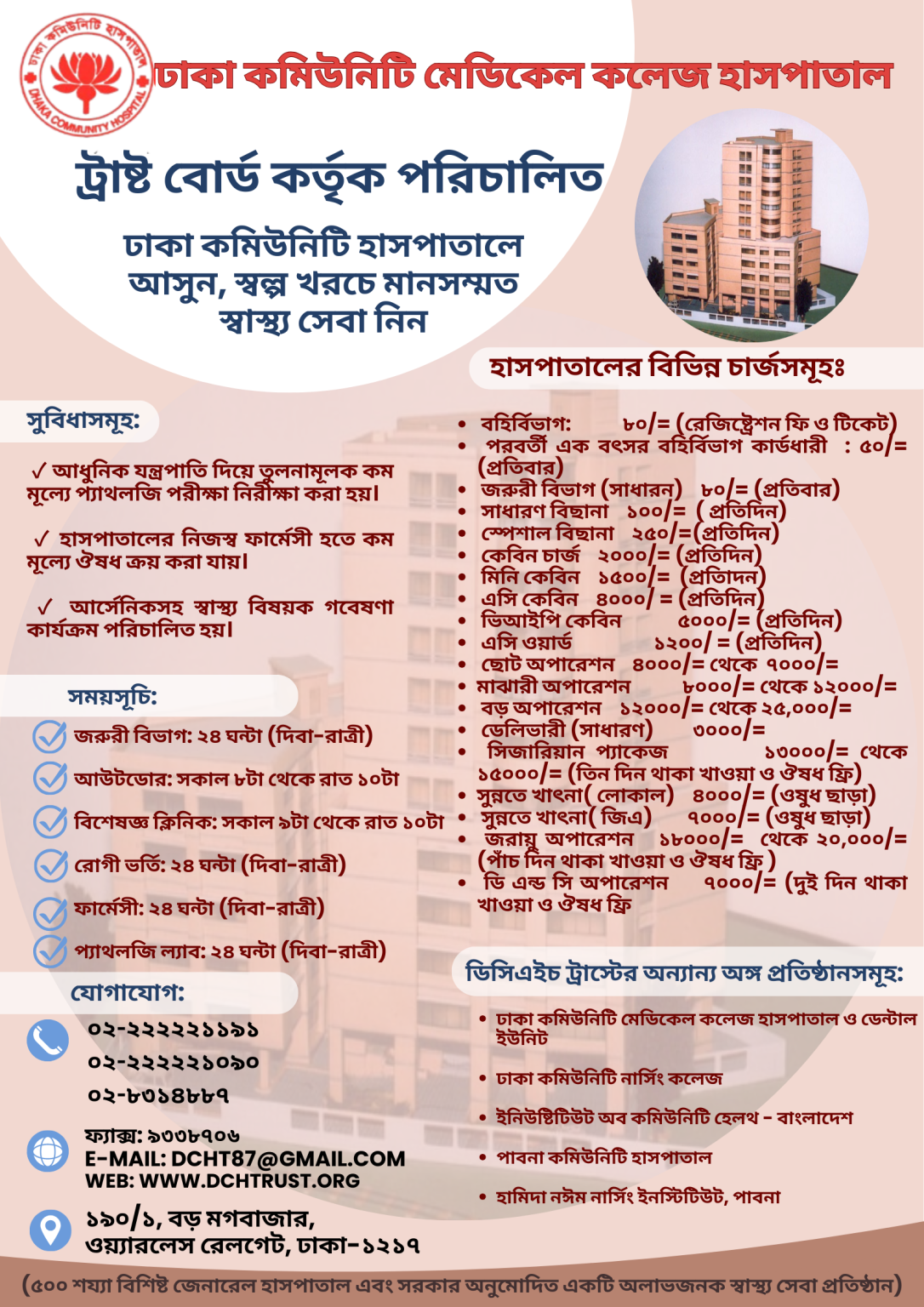

 স্বদেশ রায়
স্বদেশ রায়