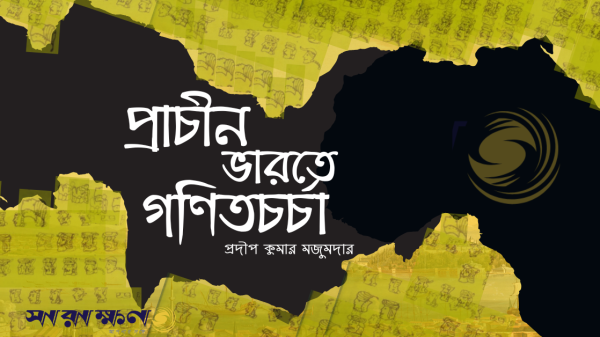মুহাম্মদ ইউনূস ও তারেক রহমানের লন্ডনে যে মিটিং হয়, ওই মিটিং-পরবর্তী যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়, ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের রমাদান ফাস্টিং শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। এখনও ইন্টারিম ব্যবস্থার সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে এমন কথাই বলা হচ্ছে।
নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ
বর্তমান ইন্টারিম ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যে রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের মধ্যে নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও অনান্য মৌলবাদী দলগুলো চায় প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পি আর) পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচন হোক। অন্যদিকে দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি চায়, সংবিধানের নির্দেশিত পদ্ধতিতেই নির্বাচন হতে হবে। ইমিডিয়েট পাস্ট পার্লামেন্টের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও বিএনপির দাবির সঙ্গে একমত। অন্যদিকে, দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখন নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ, তাই তাদের কোনো অফিসিয়াল মতামত জানার উপায় নেই।
ইন্ট্রারিম ব্যবস্থার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা
বর্তমান ইন্টারিম ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি যাই থাকুক না কেন, তারা বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে উপদেষ্টা (মন্ত্রী বা নির্বাহীর সমতুল্য) হিসেবে শপথ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির কাছে নেওয়া ওই শপথে তারা বলেছেন, “ আমি সংবিধানের রক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিব”( “That I will preserve, protect and defend the constitution,”) যা সংবিধানের আর্টিকেল ১৪৮-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই বর্তমান ইন্টারিম ব্যবস্থা মূলত ওথ-বাউন্ডেড। তাদের সংবিধানের বাইরে গিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচন করানোর আইনগত বা শপথ অনুযায়ী কোনো উপায় নেই। যে কারণে এই ইন্টারিম ব্যবস্থাকে সংসদ নির্বাচন করাতে হলে সংবিধানে যা বলা আছে সেভাবেই করতে হবে।
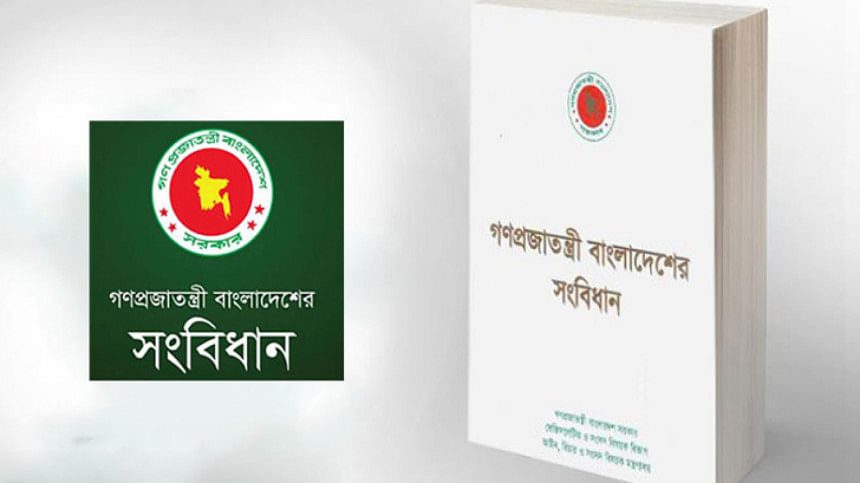
সংবিধানের ধারা অনুযায়ী নির্বাচন
বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের আর্টিকেল ৬৫-এর ক্লজ (২)-এ সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বলা আছে, “ একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এই অুনচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকারতারকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগন সংসদ সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন”। (“Parliament shall consist of three hundred members to be elected in accordance with law from single constituencies by direct election and, for so long as clause (3) is effective, the members provided for that clause; the members shall be designated as members of parliament।” ) এখানে অবশ্য clause (3)-এ মনোনীত মহিলা পার্লামেন্ট মেম্বরদের কথা বলা হয়েছে।
যেহেতু বর্তমান ইন্টারিম ব্যবস্থাকে সংবিধানের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকেও সংবিধানের অধীনেই নির্বাচনে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে সংবিধান নির্ধারিত আসনভিত্তিক প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এ অবস্থায়, ‘পি আর’ পদ্ধতি না সংবিধানে বিদ্যমান পদ্ধতি—এই বিতর্ক নির্বাচন নিয়ে সময়ক্ষেপণের কৌশল হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
আপার হাউস প্রস্তাব ও নতুন বিতর্ক
বর্তমান ইন্টারিম ব্যবস্থার সৃষ্ট কিছু সংবিধান ও নির্বাচন-সংক্রান্ত কমিশন এবং সরকারের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক দলগুলো আরেকটি বিতর্ক সামনে এনেছে—তারা পার্লামেন্টে আপার হাউস করতে চায়। বাংলাদেশের সংবিধানের পার্ট-১-এর রিপাবলিক অংশে বলা হয়েছে, “ বাংলাদেশ একটি একক ….যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে”। (“Bangladesh is Unitary … to be known as the People’s Republic of Bangladesh।”) যেহেতু ইউনিটারি কান্ট্রি, তাই এর পার্লামেন্টে আপার হাউস করার কোনো সাংবিধানিক পথ নেই।
বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা—যারা এখনও কিছুটা মুহাম্মদ ইউনূসের সমর্থক, প্রথম দিকে প্রায় শতভাগ ছিল—তারাও ৯ অক্টোবরের এক আলোচনা সভায় বলেছে, পার্লামেন্টের আপার হাউস করার এই অহেতুক বিতর্ক থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কিন্তু ইন্টারিম ব্যবস্থার সমর্থক জুলাই মুভমেন্টের ছাত্রদের প্রতিনিধি সেখানে (যিনি ইউনূসের সফরসঙ্গী হিসেবে নিউইয়র্কে গিয়েও মাতৃসম এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে হাত মেলাননি, যা সাধারণত আফগানিস্তানের তালেবানদের মধ্যে দেখা যায়) জোর দিয়ে বলেছে, তারা পার্লামেন্টে আপার হাউস চায়।

মৌলবাদী জোটের অবস্থান ও কমিশনের ভূমিকা
মুহাম্মদ ইউনূস-সমর্থক কট্টর মৌলবাদী সংগঠনগুলো—অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, হেফাজতে ইসলাম এবং ইউনূসের নিয়োগদাতা ছাত্রনেতাদের দল এনসিপি—নির্বাচন নিয়ে সংবিধানের বাইরে গিয়ে বিতর্ক করছে। তাদের এই বিতর্কের সুযোগ করে দিচ্ছে ইউনূসের তৈরি কিছু কমিশন। তারা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে বৈঠক করে এবং এসব বিতর্ক সামনে আনার সুযোগ দেয়।
বাস্তবে এই বিতর্কগুলো শুধু মিডিয়ার খাদ্য ছাড়া সাংবিধানিকভাবে অর্থহীন। যেহেতু সংবিধানে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, ইন্টারিম ব্যবস্থারও সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।
জুলাই চার্টার ও রেফারেন্ডাম দাবির পটভূমি
এরপরেও এই মৌলবাদী দলগুলো এবং তাদেরই সমমতের জুলাই আন্দোলনের ছাত্রদের নিয়ে তৈরি দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ইন্টারিম ব্যবস্থাকে বারবার চাপ দিচ্ছে—নির্বাচনের আগে তাদের তৈরি জুলাই চার্টারকে সংবিধানের অংশ করতে হবে। এ কাজের জন্য ইন্টারিম ব্যবস্থা ও তার তৈরি কমিশনগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা পন্থা সামনে আনছে। সর্বশেষ বিএনপি, মৌলবাদী দলগুলো ও এনসিপি ইন্টারিম ব্যবস্থার কমিশনের সঙ্গে বসে একমত হয়েছে—জুলাই চার্টার সংবিধানের অংশ করতে হলে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠান করতে হবে।
মৌলবাদী দলগুলো ও সমমনা এনসিপি এই রেফারেন্ডাম সংসদ নির্বাচনের আগে চায়। অন্যদিকে, বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, পার্লামেন্ট নির্বাচনের দিনে দুটি ব্যালটের মাধ্যমে পার্লামেন্ট নির্বাচন ও রেফারেন্ডাম একসঙ্গে করা যেতে পারে।
সংবিধানে রেফারেন্ডামের বিধান নেই
কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে রেফারেন্ডামের কোনো বিধান নেই। সংবিধান যখন প্রথম প্রণয়ন করা হয়, অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধানেও ছিল না। মাঝখানে রেফারেন্ডামের সুযোগ সংবিধানের পার্ট-১০-এর আর্টিকেল ১৪২-এ যোগ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৫তম সংশোধনীতে সেটা বাদ দেওয়া হয়।
এই বাদ দেওয়ারও যৌক্তিক কারণ ছিল। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান এবং ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ সামরিক শাসক এরশাদ তাদের প্রতি জনগণের আস্থা যাচাইয়ের জন্য রেফারেন্ডাম আয়োজন করেন। যা পরে ৫ম ও ৭ম সংশোধনী হিসেবে পার্লামেন্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট দুটোই পরবর্তীতে বাতিল করে দেয়।
এছাড়া ১৯৯১ সালে দেশ আবার প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি থেকে পার্লামেন্টারি বা ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতিতে ফিরলে পার্লামেন্টের সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সেপ্টেম্বর একটি রেফারেন্ডাম করা হয়। এটা আদালতে চ্যালেঞ্জ হয়নি। তবে তখন আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, এর প্রয়োজন ছিল না। পার্লামেন্টের সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া সিদ্ধান্তের পরে রেফারেন্ডাম অপ্রয়োজনীয়। আদালতে চ্যালেঞ্জ হলে সেটি অপ্রয়োজনীয় বলেই পর্যবেক্ষণ দিত।

ইনডেমনিটির দাবি ও নতুন ভয়
এখন ছাত্রদের দল ও মৌলবাদী দলগুলো তাদের জুলাই চার্টারের আইনগত ভিত্তির জন্য রেফারেন্ডামকে শেষ অস্ত্র হিসেবে সামনে এনেছে। তাদের এই তাগিদের পেছনে কারণ আছে। যেহেতু জুলাই আন্দোলনের পরে মৌলবাদী দলের অনেক সদস্য ও জুলাইয়ের ছাত্রনেতারা মিডিয়ায় ও প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে—তারা পুলিশ হত্যা করেছে, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ধ্বংস করেছে “বিপ্লবের” নামে। সে সময় তারা মনে করেছিল, তারা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। এখন তাদের জনবিচ্ছিন্নতা তাদেরকে ভীত করছে।
যে কারণে তারা জুলাই চার্টারের নামে মূলত ইনডেমনিটি চায়। এজন্য রেফারেন্ডামকে নতুন অস্ত্র হিসেবে সামনে এনেছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী রেফারেন্ডাম আয়োজনের কোনো সুযোগ নেই—এটা তারা কেন বুঝতে পারছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কোনো ইনডেমনিটি দেওয়ারও সুযোগ নেই। এর আগে অনেক ইনডেমনিটি বিচার বিভাগের মাধ্যমে বাতিল হয়েছে।
“সেইফ এক্সিট” প্রসঙ্গ
এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন, ক্ষমতার উন্মাদনার বাতাসে এক বছর পার করে এখন কি তারা বাস্তবতার আইনগত মাটি দেখতে পাচ্ছে? এজন্যই রেফারেন্ডাম, নির্বাচন এসব কথা বলার একদিন পরেই তাদের বক্তব্যে আলোচিত শব্দ—“সেইফ এক্সিট”, বা “আরও খারাপ কিছু” ।
বাস্তবে রাজনীতি যেহেতু অনেকটা জীবন্ত সত্তার মতো চলমান, সময় যত খারাপ হয়, তার গতি ততই দ্রুত হয়। মাত্র এক বছর আগে শেখ হাসিনার সময়ের শেষদিকে এমনই দ্রুতগতি দেখেছিল বাংলাদেশের মানুষ।
লেখক: সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সম্পাদক, সারাক্ষণ ও The Present World.
( লেখাটি India Today তে প্রকাশিত হয়েছে, এখানে তার বাংলা অনুবাদ দেয়া হল, India Today এর link https://www.indiatoday.in/opinion/story/bangladesh-interim-government-muhammad-yunus-election-crisis-july-charter-referendum-constitutional-impasse-2802789-2025-10-14
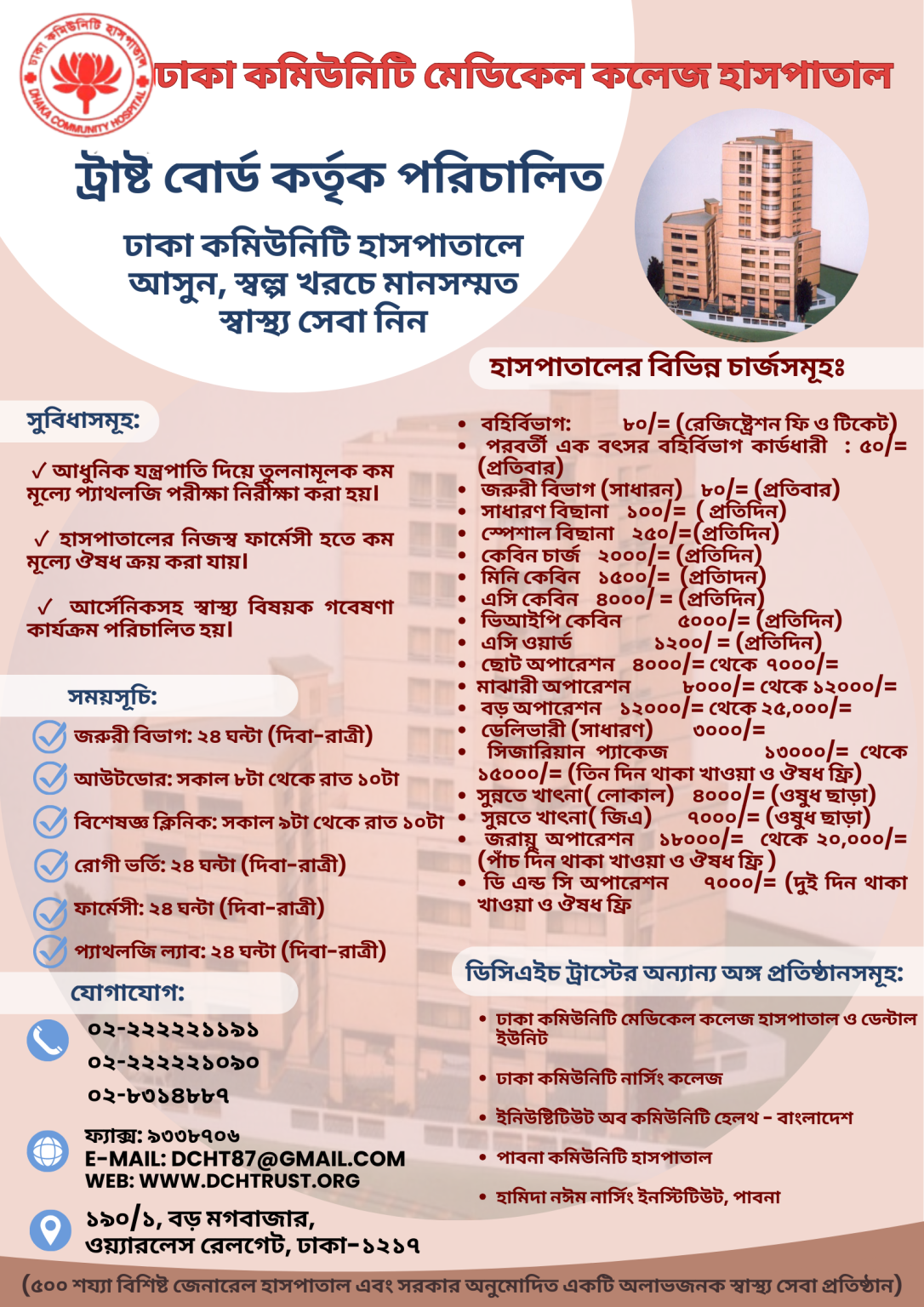

 স্বদেশ রায়
স্বদেশ রায়