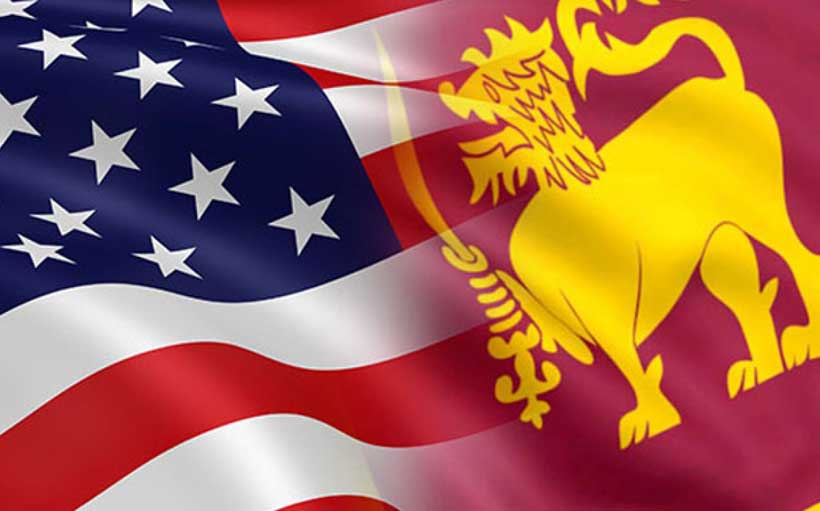সালমান রফি শেখ
শ্রীলঙ্কার রপ্তানির ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের ৪৪ শতাংশ ‘পারস্পরিক’ শুল্ক ইতিমধ্যেই সার্বভৌম ঋণখেলাপি ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল দেশটির ভঙ্গুর অর্থনীতিকে কঠিন ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। তাই কলম্বোর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি পণ্যে নিজস্ব শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দেওয়া। এপ্রিলের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কার একটি প্রতিনিধি দল মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে, যদিও এখনও কোনও চুক্তি হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য—মূলত তৈরি পোশাক, চা ও রাবারজাত জিনিস—রপ্তানি হয়, যা দেশটির মোট রপ্তানির প্রায় এক-চতুর্থাংশ। বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি মাত্র ৪৪৩ মিলিয়ন ডলার, যা ট্রাম্পকে ক্ষুব্ধ করা বাণিজ্য ঘাটতি নির্দেশ করে।
এই শুল্ক বহাল থাকলে কিছু অনুমান অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার রপ্তানি ২০ শতাংশের বেশি কমে যেতে পারে, যা অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার প্রচেষ্টাকে বিপদে ফেলবে। তবে কোনও সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রধান সমস্যা শ্রীলঙ্কার বাণিজ্যিক ভঙ্গুরতা—একটি মাত্র বাজারে অতিনির্ভরতা; বৈচিত্র্য বাড়ানো একান্ত জরুরি।

শ্রীলঙ্কার ব্যবসায়ীরা বলেন, উচ্চ আমদানি শুল্ক ও সীমিত বাণিজ্য চুক্তির কারণে বিকল্প বাজারে প্রবেশ কঠিন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কে শ্রীলঙ্কার দুর্বল সংযুক্তি—এটি এশিয়ার কম একীভূত অর্থনীতিগুলোর একটি।
২০০৫ সাল থেকে শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ-এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকার (সাফটা) সদস্য। তবে সার্ক কার্যকর না থাকায় সাফটাও অগ্রসর হয়নি। ভারতের ও পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পরিসর সীমিত; উৎস-দেশের কঠোর নিয়ম ও সংবেদনশীল পণ্যের দীর্ঘ তালিকা লাভ কমিয়ে দিয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কলম্বো নতুন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে বাণিজ্য জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। ২০২৩-এ সিঙ্গাপুরের সঙ্গে স্থগিত চুক্তি পুনরায় চালু করা হয় এবং ২০২৪-এ থাইল্যান্ডের সঙ্গে নতুন চুক্তি হয়। এগুলো ভারতে-পাকিস্তানে করা চুক্তির সাধারণ সীমাবদ্ধতা এড়ালেও সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড তুলনামূলক ছোট অংশীদার, আর উভয়ের সঙ্গেই শ্রীলঙ্কার বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।
এখন ভিন্ন কী করা যায়? উত্তর লুকিয়ে আছে বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক একীকরণে—বিশেষ করে আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে (আরসিইপি)। ২০০৭-এ আসিয়ান কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো পর্যন্ত সদস্যপদ সীমিত করেছিল, কিন্তু আরসিইপির তেমন ভৌগোলিক বাধা নেই। আসিয়ান রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া—বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য ব্লকটির অংশ।

সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহে ২০২৩-এ কলম্বোর ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাসে বক্তৃতায় স্বীকার করেন, ১৯৬০-এর দশকে আসিয়ানে যোগ দেওয়ার সুযোগ শ্রীলঙ্কা হাতছাড়া করেছিল। সেই জানালা বন্ধ হলেও আরসিইপি নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে, যা উপেক্ষা করার উপায় নেই।
আরসিইপি-তে যোগ দিলে শ্রীলঙ্কা বড় অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে। অংশীদারত্বটি আঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খল জোরদার এবং ‘নেটওয়ার্ক ট্রেড’—একই পণ্যের বিভিন্ন উৎপাদন ধাপ একাধিক দেশে ছড়িয়ে—কে উৎসাহ দেয়। এতে শ্রীলঙ্কা এই অঞ্চলের বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে রপ্তানি খাতকে বিস্তৃত করতে পারবে।
এখন আরসিইপি দেশগুলোতে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি জিডিপির মাত্র ১০ শতাংশ; সামগ্রিকভাবে রপ্তানি ২০০০-এর ৩৩ শতাংশ থেকে ২০২০-এ নেমে এসেছে ১২ শতাংশে। গভীরতর একীকরণ এ প্রবণতা উল্টাতে পারে—বিশেষত লোহা-ইস্পাত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক এবং মোটরসাইকেল-হুইলচেয়ারের যন্ত্রাংশ খাতে।
চা রপ্তানিতেও উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা আছে। সঠিক আরসিইপি বিনিয়োগ পেলে শ্রীলঙ্কা বৃহৎ ভরচা কাঁচা চা বিক্রি ছেড়ে উন্নত মূল্য-সংযোজিত পণ্যে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে উৎপাদন কম হলেও উচ্চ মূল্য-সংযোজন ও ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে আয় বেশি।
তবে আঞ্চলিক একীকরণই যথেষ্ট নয়। আরসিইপি-র পূর্ণ সুবিধা তুলতে শ্রীলঙ্কাকে ঘরোয়া সংস্কার করতে হবে—আরও উদার অর্থনীতি, শুল্ক সরলীকরণ এবং ১৯৭০-এর দশকের শেষ থেকে চলে আসা খাপখাইয়া নীতি-নির্ধারণের অবসান। ধারাবাহিক ও স্বচ্ছ নীতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে ও বিদেশি পুঁজি আনবে।
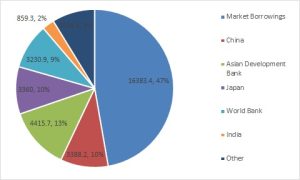
আরও উদার বাণিজ্যিক পরিবেশ সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে, যা স্থানীয় শিল্পকে দক্ষতা বাড়াতে, ব্যয় কমাতে ও তুলনামূলক সুবিধা-সম্পন্ন খাতে কেন্দ্রীভূত হতে বাধ্য করবে—ফলে উৎপাদনশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাবে।
শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক কৌশলের মধ্যমণি হওয়া উচিত নয়। একটি মাত্র রপ্তানি গন্তব্যে অতিনির্ভরতা—বিশেষত বর্তমান অস্থির বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশে—বিপজ্জনক। অগ্রগতির পথ হলো গতিশীল আঞ্চলিক অর্থনীতির সঙ্গে ব্যাপক একীকরণ ও দেশের কাঠামোগত সংস্কারের দিকে অবিচল প্রতিশ্রুতি।
লেখক: সালমান রফি শেখ লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেসের মুশতাক আহমদ গুরমনি স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের রাজনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report