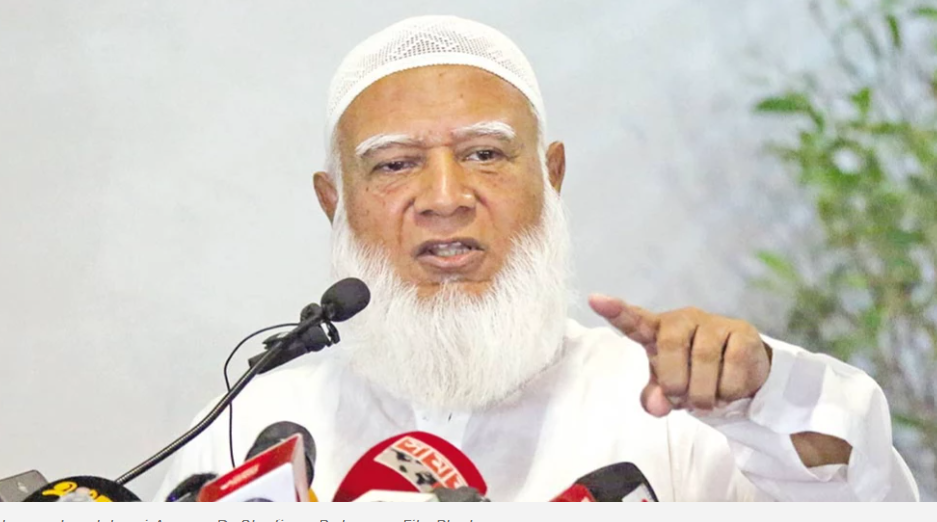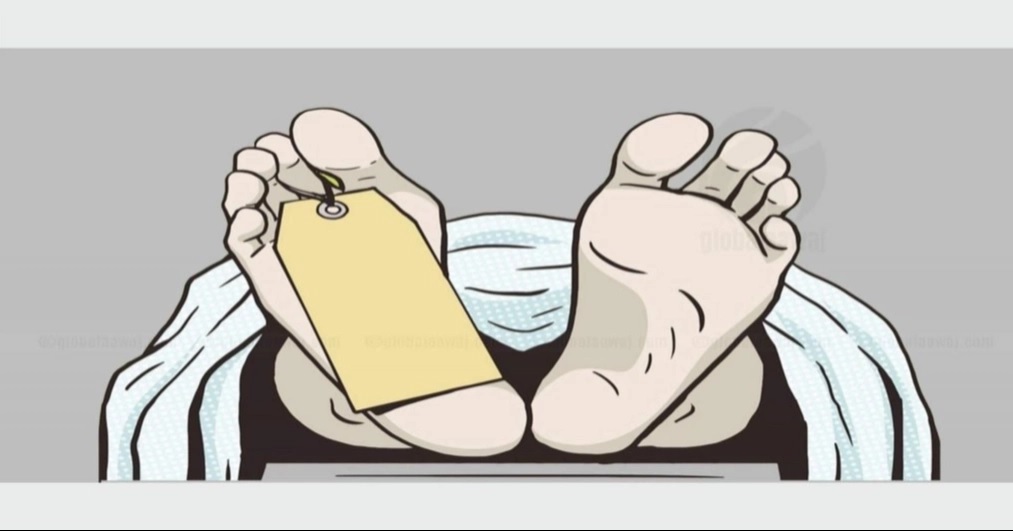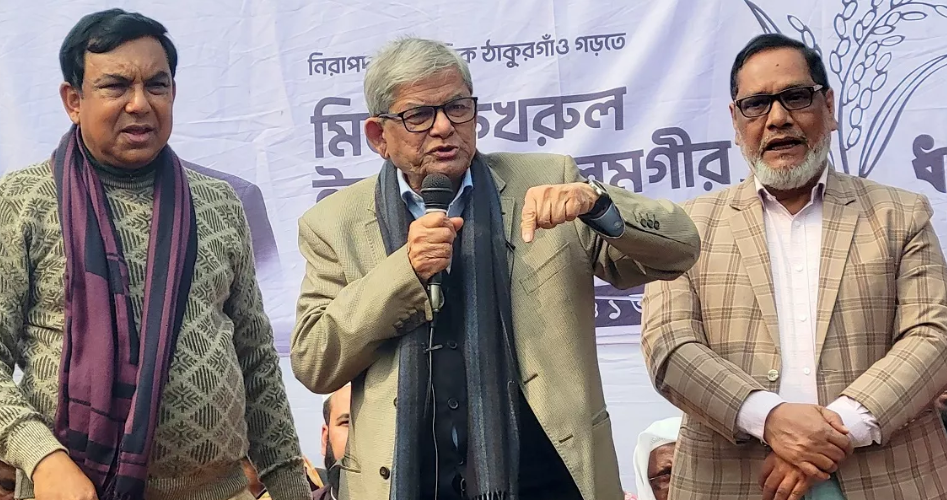ওআরএস: এক সাধারণ দ্রবণের অসাধারণ ইতিহাস
পানিশূন্যতা বা ডায়রিয়ার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ছিল ভয়াবহ। শিশু এবং বৃদ্ধরা বিশেষভাবে আক্রান্ত হতেন। চিকিৎসা ব্যবস্থার দুর্বলতা, বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং দ্রুত চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাতেন প্রতিবছর। কিন্তু এক সাধারণ লবণ-গুড়ের দ্রবণ—ওআরএস (Oral Rehydration Solution)—পরিস্থিতি বদলে দেয় চিরতরে।
এই জাদুকরি দ্রবণের আবিষ্কারের পেছনে আছে দীর্ঘ গবেষণা, সাহসিকতা, এবং এক অমানবিক মানব বিপর্যয়ের মধ্যে কাজ করার অনন্য উদাহরণ।
আবিষ্কারের পেছনের বিজ্ঞান: গ্লুকোজ আর সোডিয়ামের সঠিক সংমিশ্রণ
১৯৬০-এর দশকে বিজ্ঞানীরা খুঁজছিলেন এমন একটি সহজ চিকিৎসা, যা ডায়রিয়াজনিত পানিশূন্যতা মোকাবিলা করতে পারে সহজে, সস্তায় এবং হাসপাতালের বাইরে। সেই সময়ের প্রচলিত চিকিৎসা ছিল ইনট্রাভেনাস (IV) স্যালাইন, যা ব্যয়বহুল এবং চিকিৎসা-কেন্দ্রিক ছিল।

কলকাতার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ এবং ঢাকা, তখনকার পাকিস্তানের একটি স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআরবি (তখনকার Cholera Research Laboratory)-র যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, গ্লুকোজ ও সোডিয়ামের নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রণ অন্ত্রের মধ্যে সোডিয়াম শোষণ বাড়ায় এবং সাথে পানি শোষণকেও গতি দেয়।
এভাবে জন্ম নেয় ওআরএস – পানি, লবণ এবং চিনি মিশিয়ে তৈরি করা এক প্রাণরক্ষাকারী দ্রবণ।
১৯৭১: উদ্বাস্তু সংকট আর ওআরএস-এর সাহসী প্রয়োগ
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, বিশেষ করে ভারতের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় হাজার হাজার শরণার্থী জীবনযাপন করছিলেন অস্থায়ী শিবিরে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপর্যাপ্ত পানি এবং খাদ্যের অভাবে কলেরা ও ডায়রিয়া ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যু হার ছিল রীতিমতো ভয়াবহ।
এই সময় সাহসী পদক্ষেপ নেন দুই গবেষক—ডাঃ রিচার্ড কাশ ও ডাঃ ডেভিড নালিন। তাঁরা তখন আইসিডিডিআরবিতে গবেষণা করছিলেন ওআরএস নিয়ে। ১৯৭১ সালের শরণার্থী সংকট তাঁদের গবেষণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার এক বিরল সুযোগ দেয়।
তাঁরা ওআরএস সরবরাহ করতে থাকেন উদ্বাস্তু শিবিরে—প্রথমে হাতে হাতে তৈরি করে, পরে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ছোট প্যাকেটের মাধ্যমে। শুধু শিশু নয়, বড়দের মধ্যেও এটি অভাবনীয় কার্যকার্যিতা দেখাতে শুরু করে।
ডাঃ নালিন পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “ওআরএস প্রয়োগ করার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর হার ৩০%-এর বেশি থেকে ৫% এর নিচে নেমে আসে।”

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিপ্লব: শিশু মৃত্যুর বিরুদ্ধে এক নিঃশব্দ অস্ত্র
১৯৭১ সালের সফল প্রয়োগের পর ওআরএস-কে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির অংশ করা হয়। ব্র্যাক এবং অন্যান্য এনজিও সংগঠন দেশের গ্রামে-গঞ্জে ওআরএস পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করে।
“ঘরে তৈরি স্যালাইন খাওয়ান”—এই সহজ বার্তা পৌঁছে যায় বাংলার ঘরে ঘরে।
১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে শিশু মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমে আসে। বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ডায়রিয়া। ওআরএস এর প্রতিষেধক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।
ভারতের সাফল্য এবং আফ্রিকার বিপ্লব
বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দেখে ভারতেও ওআরএস ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সরকারের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ব্যাপক গণসচেতনতা চালায়। সস্তা ও সহজে উৎপাদনযোগ্য এই দ্রবণ অল্প সময়েই ভারতের গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় স্থান পায়।
এরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইউনিসেফ ওআরএস-কে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেয়। বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকায় যেখানে কলেরা এবং ডায়রিয়া ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, ওআরএস লক্ষ লক্ষ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ককে বাঁচিয়ে তোলে।

নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া—এইসব দেশেও ওআরএস ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ইউনিসেফের হিসেবে, ওআরএস বিশ্বব্যাপী বছরে অন্তত ৫ লক্ষ শিশুর প্রাণ বাঁচায়।
এক পরিণতির সূচনা: ‘মিরাকল অফ দ্য সেঞ্চুরি’
২০০১ সালে দ্য ল্যান্সেট ম্যাগাজিন ওআরএস-কে আখ্যা দেয় “possibly the most important medical discovery of the 20th century।”
এটি ছিল এমন এক আবিষ্কার যা অস্ত্রোপচার ছাড়াও, হাসপাতালের বাইরে, গ্রামীণ চৌকাঠে দাঁড়িয়েও প্রাণ রক্ষা করতে পারে। বাংলাদেশ, ভারত, ও আফ্রিকার মানুষের জন্য এটি ছিল এক নিঃশব্দ বিপ্লব।
লবণ-চিনির ঘরে ঘরে বেঁচে থাকা
ওআরএস প্রমাণ করে, সব স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের জন্য কোটি কোটি টাকার গবেষণাগার নয়, দরকার বাস্তবমুখী চিন্তা এবং মানবিক প্রয়োগ। বাংলাদেশের ইতিহাসে ওআরএস শুধু এক চিকিৎসা নয়, এটি এক মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর যুগে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতীক।
আজও, একটি শিশুর ডায়রিয়া হলে মায়েরা বলেন—“সালাইন খাওয়াও।” এই কথাটি শুধু এক চিকিৎসার পরামর্শ নয়, এটি একটি জনগণের বিজয়ের কাহিনী।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট