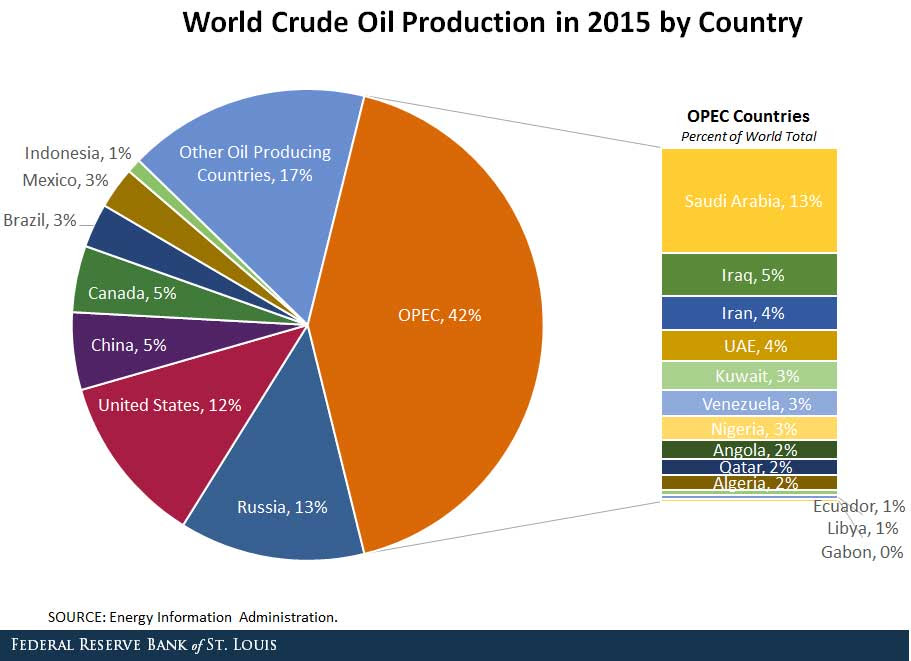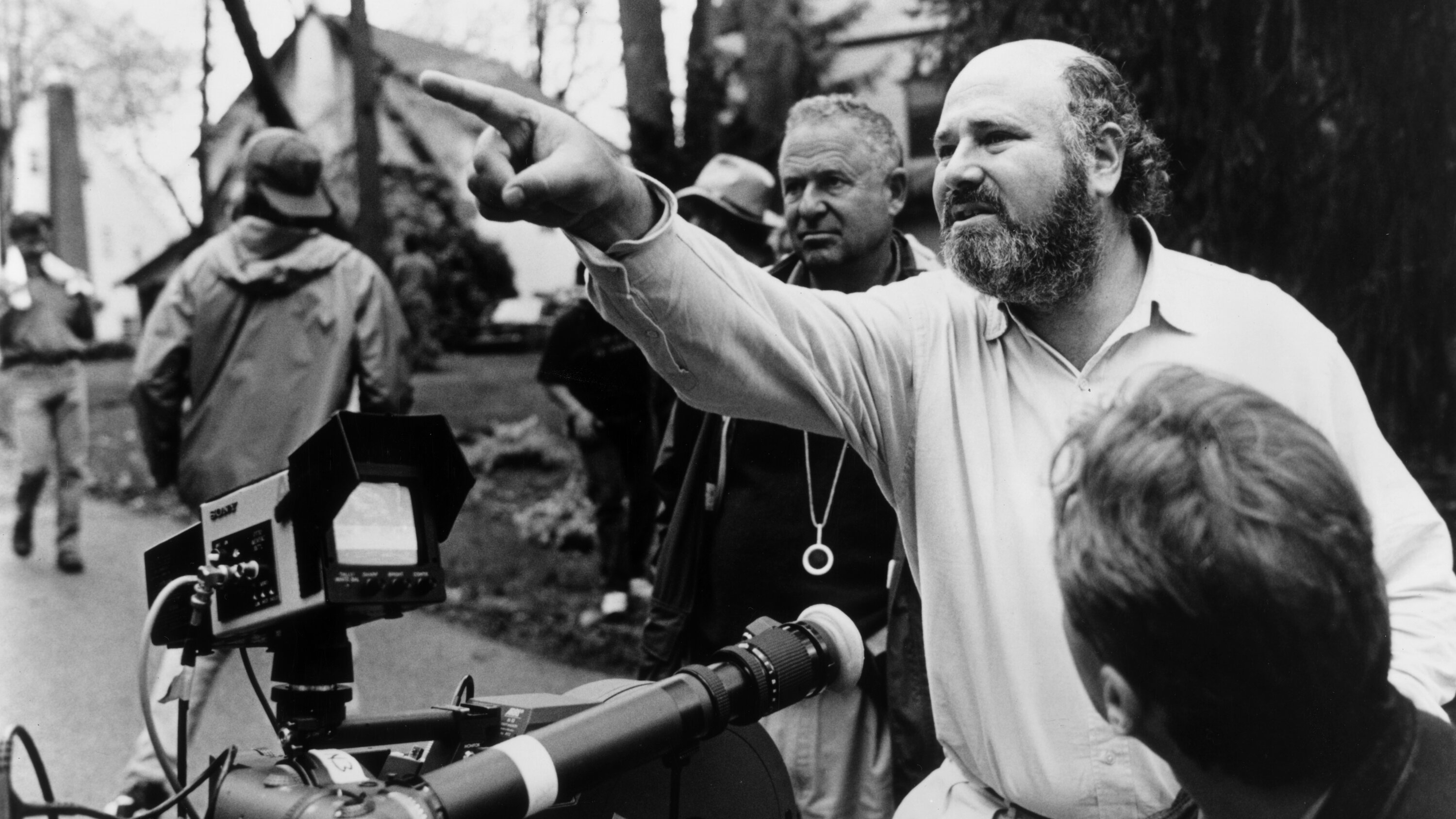বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ। তবুও চলতি মৌসুমে দেখা যাচ্ছে—কলকাতার বাজারে ইলিশের দাম ঢাকার তুলনায় অনেক কম। ঢাকায় ৫০০ গ্রাম আকারের ইলিশ কেজি ১,৪৫০–১,৬০০ টাকায় বিক্রি হলেও কলকাতায় একই আকারের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ৬০০–৭৫০ রুপিতে (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৮৩৪–১,০৪২ টাকা)। এক কেজি আকারের ইলিশ ঢাকায় ২,৬০০–৩,২০০ টাকা পর্যন্ত উঠলেও কলকাতায় তা ১,৫০০–১,৮০০ রুপি (প্রায় ২,০০০–২,৫০০ টাকা)। ফলে প্রশ্ন উঠছে—যে দেশ মূল উৎপাদক, সেখানে দাম বেশি আর আমদানিকারক শহরে কম কেন?
বাংলাদেশের উৎপাদন বাস্তবতা
সরকারি ও গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ধরা ইলিশের প্রায় ৭৫–৮৬ শতাংশই আসে বাংলাদেশ থেকে। উৎপাদনে এ আধিপত্য সত্ত্বেও বাজারে সেই বাড়তি জোগানের সুবিধা ভোক্তারা পুরোপুরি পাচ্ছেন না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে দামের স্বস্তি মিলছে না।
দুই শহরের দামের তুলনা
ঢাকা: জুলাই–আগস্টের প্রথম ভাগে ঢাকার বাজারে ৫০০ গ্রাম ইলিশ কেজি ১,৪৫০–১,৬০০ টাকা, ৭৫০–৮০০ গ্রাম ১,৮৫০–২,০০০ টাকা এবং এক কেজি বা তার বেশি আকার ২,৬০০–৩,২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
কলকাতা: একই সময়ে কলকাতা–হাওড়া বাজারে ৫০০ গ্রাম ইলিশ কেজি ৬০০–৭৫০ রুপি, ৭০০–৮০০ গ্রাম ১,২০০–১,৩০০ রুপি এবং এক কেজি আকার ১,৫০০–১,৮০০ রুপিতে বিক্রি হয়েছে—যা টাকায় রূপান্তরে ঢাকার তুলনায় অনেক কম। গড়ে ঢাকার দাম কলকাতার তুলনায় ১৫৩–১৭৪ শতাংশ পর্যন্ত বেশি।

কলকাতায় দাম নিয়ন্ত্রিত থাকার কারণ
১) বিকল্প উৎস: কলকাতায় মিয়ানমারের ইরাবতী নদী ও ভারতের গুজরাট–মুম্বাই উপকূল থেকে প্রচুর ইলিশ এসেছে। প্রতিদিন গুজরাট থেকে প্রায় ৬০ টন ইলিশ বাজারে পৌঁছেছে, পাশাপাশি মিয়ানমারের ৬২৫ টন ইলিশ শীতঘরে মজুত থাকায় সরবরাহ বেড়েছে।
২) স্থানীয় ধরা: বর্ষার শুরুর বৃষ্টি ও সময়মতো ট্রলার নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের ফলে পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৌসুমের শুরুতেই রেকর্ড পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়েছে—যা গত দুই বছরের মোট ধরা থেকেও বেশি।
৩) বাংলাদেশি ইলিশের অনুপস্থিতি: রিপোর্ট প্রকাশের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশি ইলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় পৌঁছেনি। ফলে দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
ঢাকায় দাম চড়ার কারণ
১) সরবরাহ শৃঙ্খলের জট: উপকূল থেকে ঢাকার খুচরা বাজারে পৌঁছাতে ইলিশ কয়েক দফা হাতবদল হয়, যেখানে প্রতিটি স্তরে মার্জিন যোগ হয়। ‘দাদন’–ঋণ ও মজুতদারি দামের উপর চাপ বাড়ায়।
২) খরচ বৃদ্ধি: জ্বালানি, বরফ, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং ও পরিবহন খরচ কয়েক বছরে বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বরিশাল থেকে ঢাকায় ট্রাকভাড়া এখন ২৫–৩০ হাজার টাকা, বরফ–প্যাকেজিং খরচ কেজিপ্রতি ১৫০–২০০ টাকা।
৩) বাজার স্থিতিস্থাপকতার ঘাটতি: মৌসুমে সরবরাহ বাড়লেও ঢাকায় দামের পতন ধীর—যা অনেকের মতে বাজার কারসাজির লক্ষণ।

নিষেধাজ্ঞার সময়সূচি পরিবর্তন
এ বছর বাংলাদেশ ১৫ এপ্রিল–১১ জুন সমুদ্র মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা মেনেছে, যা ভারতের সময়সূচির সাথে মিলে গেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন—শুধু সময় মিললেই সব সমস্যার সমাধান হয় না; বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে, না হলে মৌসুমি ধরা ও বাজারে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।
রাজনীতি ও রপ্তানি পরিস্থিতি
পূজার আগে প্রতিবছর বাংলাদেশ সীমিত পরিমাণ ইলিশ ভারতে পাঠায়। গত বছর প্রায় ৩,০০০ টনের অনুমতি ছিল, কিন্তু এ বছর এখনো আনুষ্ঠানিক রপ্তানি হয়নি। ফলে কলকাতা বিকল্প উৎসে ভর করছে এবং দাম তুলনামূলক কম রয়েছে। সিদ্ধান্ত হলে কলকাতার বাজারে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে।
ঢাকায় দামের সামান্য পতন
সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার বাজারে মাঝারি ও বড় আকারের ইলিশের দামে কিছুটা পতন দেখা গেছে, তবে কলকাতার তুলনায় দাম এখনও অনেক বেশি।

সমাধানের পথ
১) স্বচ্ছ নিলাম: ডিজিটাল দরপত্র, মূল্য ও কমিশন প্রকাশ।
২) ‘দাদন’ ঋণ কমানো: সুদহীন ঋণ বা সহায়ক তহবিল দিয়ে জেলেদের অর্থায়ন।
৩) পরিবহন–সংরক্ষণ ভর্তুকি: বরফ, ঠান্ডা সংরক্ষণ ও পরিবহন খাতে সহায়তা।
৪) বাজার মনিটরিং: মজুত ও কারসাজি রোধে টাস্কফোর্স এবং আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন।
৫) বৈজ্ঞানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা সমন্বয়: ধরা, প্রজনন, লবণাক্ততা ও স্রোতের তথ্যভিত্তিক সময়সূচি।
৬) দেশীয় দামের শর্তে রপ্তানি: নির্দিষ্ট সীমার ওপরে দাম হলে রপ্তানি কোটা সমন্বয় করে ভোক্তাকে সুরক্ষা দেওয়া।
বিকল্প উৎস
বাংলাদেশ উৎপাদনে শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও ভোক্তার কাছে সাশ্রয়ী দামে ইলিশ পৌঁছাতে না পারা বড় ঘাটতি। কলকাতায় বিকল্প উৎস ও নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ চেইন দাম স্থিতিশীল রেখেছে, কিন্তু ঢাকায় জটিল সরবরাহ ব্যবস্থা, খরচ ও বাজার কারসাজির কারণে দাম চড়া। সঠিক নীতি, বাজার স্বচ্ছতা ও লজিস্টিক সহায়তাই এ বৈপরীত্য কমাতে পারে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট