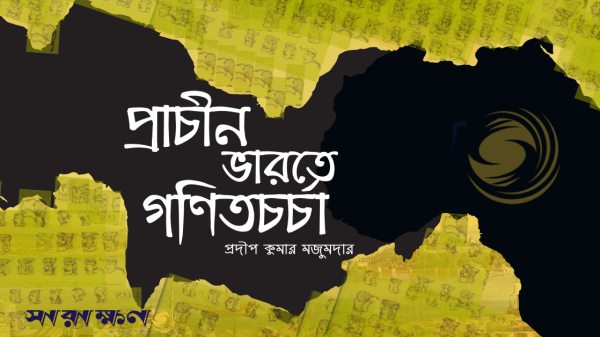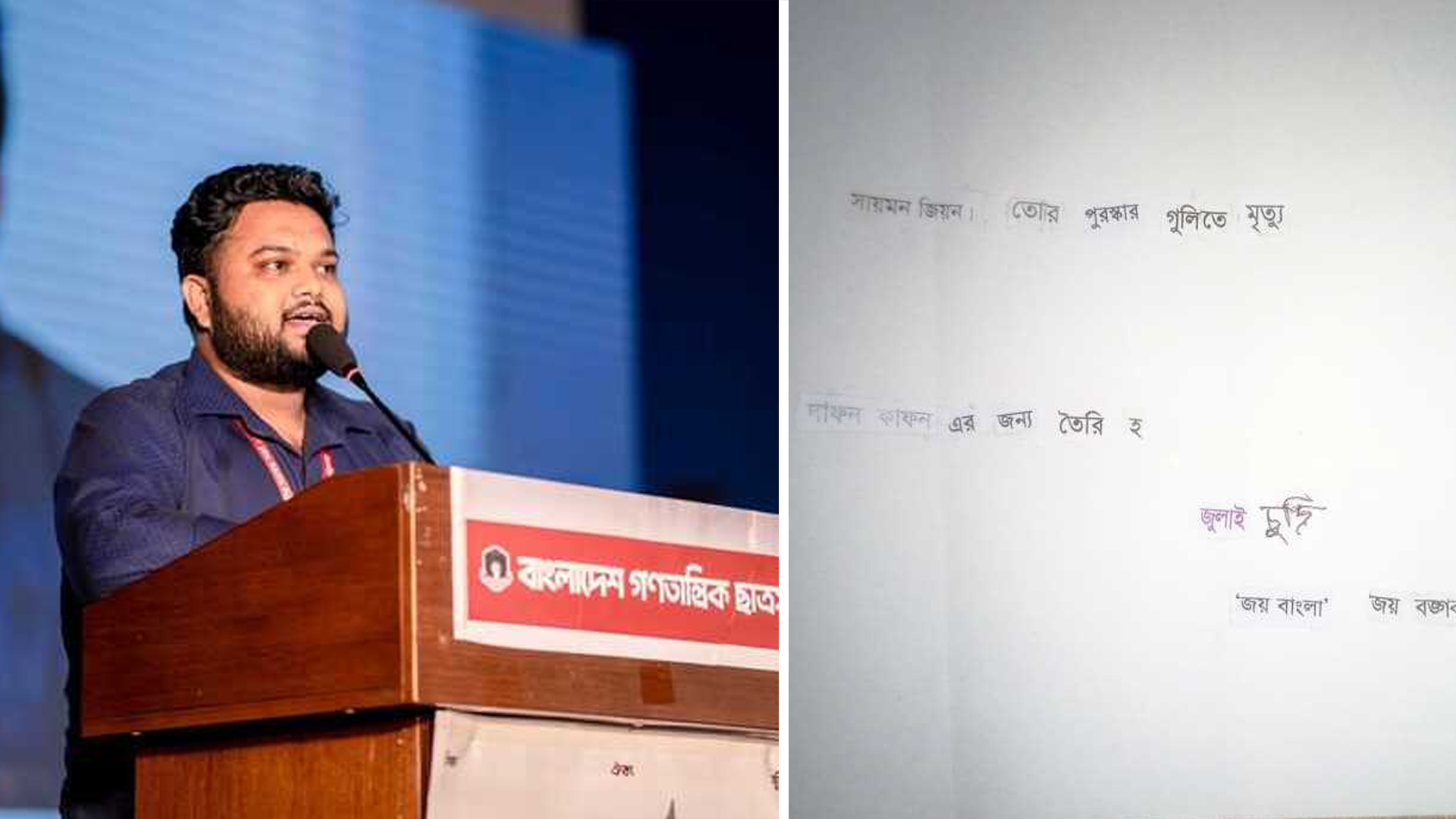কোন চিল চিল না? চার্চিল। শৈশবে এই ধাঁধার মাধ্যমে উইনস্টন চার্চিলের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। দ্বিতীয় বিশ^যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। নাৎসি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের গুঞ্জন যখন জোরেশোরে চলছে তখন তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য তিনি বেশি বিখ্যাত। সমরনায়ক হয়েও চার্চিল ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন; দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডওয়্যার এবং অ্যা হিস্টোরি অব ইংলিশ স্পিকিং পিপল তার রচিত বহুলালোচিত দুটি গ্রন্থ। লিখতে হলে পড়তে হবে। আরেক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ টিবি ম্যাকোলি বলেছিলেন, ‘ছয় লাইন লিখতে হলে ছয় হাজার লাইন পড়তে হবে’। চার্চিল অতৃপ্ত পাঠক ছিলেন; তার বহুলপঠিত গ্রন্থের ভেতরে রয়েছে— দ্য টাইম মেশিন (এইচ জিওয়েলস), দ্য ব্যালাড অফ রিডিং গাওল (অস্কার ওয়াইল্ড), কাউন্টার—অ্যাটাক এবং অন্যান্য কবিতা (সিগফ্রিড স্যাসুন), মেজর বারবারা (জর্জ বানার্র্ড শ), দ্য গুড আর্থ (পার্লর্র্ এস.বাক) ইত্যাদি। এবার নিজেদের দিকে তাকাই।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আয়ুষ্কাল ৫৫ বছরের মধ্যে ১২ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। এই দীর্ঘ কারাকাল তিনি বৃথা যেতে দেননি, অলস সময় পার করেননি। কারাগারে থেকে আন্দোলনের কলকাঠি নেড়েছেন, প্রচুর গ্রন্থ পাঠ এবং লেখালেখি করেছেন। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের নিজ বাড়িটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। ঐ বাড়ি থেকে যেমন তিনি বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি করেছেন আবার ঐ বাড়িতে জ্ঞানবিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে নিজেকে আরো সংস্কৃত, পরিণত ও শানিত করে গড়ে তুলেছেন। বই পড়া ছিল তার নেশা। কারগারে, বাড়িতে, ভ্রমণে বই পড়ার পরিবেশ করে নিয়েছিলেন।
১৯৫২ সালের মে মাসের ঘটনা। শেখ মুজিব পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে প্রথমবারের মতো এসেছেন। এর আগে একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদেরকে গুলি করে হত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেছে। গোটা পাকিস্তান জুড়ে তখনও সেই উত্তেজনা। শেখ মুজিব করাচিতে এসেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। শেখ মুজিব তার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করলেন, একই সাথে আওয়ামী লীগকে বিরোধী দল হিসেবে তার স্বীকৃতি আদায় করলেন। এরপর তিনি হায়দারাবাদ গেলেন হোসেন শহীদ সেহারাওয়াদীর্র সাথে দেখা করতে। তার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে বিকেলে গাড়ি করে করাচির উদ্দেশে ফিরছিলেন। সোহরাওয়াদীর্ নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, শেখ মুজিব তার পাশের আসনে, পেছনে ‘পিন্ডি ষড়যন্ত্র’ মামলার কয়েকজন অ্যাডভোকেট। এর পরেরটুকু বঙ্গবন্ধুর ভাষায় শুনি,‘রাস্তায় অ্যাডভোকেট সাহেবরা আমাকে পূর্ব বাংলার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বাংলা ভাষাকে কেন আমরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাই? হিন্দুরা এই আন্দোলন করছে কিনা? আমি তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম। শহীদ সাহেবও তাদের বুঝিয়ে বললেন এবং হিন্দুদের কথা যে সরকার বলছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা তিনিই তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। আমার কাছে তারা নজরুল ইসলামের কবিতা শুনতে চাইলেন। আমি তাদের ‘কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধূ’, ‘নারী’,‘সাম্য’— আরো কয়েকটা কবিতার কিছু অংশ শুনলাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতার দু’একটার কয়েক লাইন শুনালাম । শহীদ সাহেব তাদের ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিলেন।’ এই যে যখন তখন নজরুল—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করে শোনানো, তা শুধুামাত্র একজন সাহিত্যনুরাগী পাঠকের দ্বারাই সম্ভব। বক্তৃতা—বিবৃতি, সাক্ষাৎকার এমনকি সাধারণ আলাচারিতাতেও তিনি প্রায়শ মনীষীদের উদ্ধৃতি দিতেন।

কারাগারে তিনি বই পেতেন বেগম মুজিবের কাছ থেকে। তার পাঠ্যাগ্রহ সম্বন্ধে বিদেশি বন্ধুরাও অবহিত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে ‘ন্যাটোর ১৫ জাতি’ শীর্ষক ম্যাগাজিনের ২য় সংখ্যা কারাবন্দি শেখ মুজিবের কাছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল। ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল (ডিপিআর) ক্যাটাগরির বন্দী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বন্দীরা সপ্তাহে একটি চিঠি আর ১৫ দিনে একবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত। কিন্তু সেখানেও বাধা নিষেধ ছিল। সাক্ষাতের সময় গোয়েন্দা ও জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত থাকত। বঙ্গবন্ধু দুঃখ করে লিখেছেন: ‘নিষ্ঠুর কর্মচারীরা বোঝে না যে স্ত্রীর সাথে দেখা হলে আর কিছু না হউক একটা চুমু দিতে অনেকেরই ইচ্ছে হয়, কিন্তু উপায় কী? আমরা তো পশ্চিমা সভ্যতায় মানুষ হই নাই। তারা তো চুমুটাকে দোষণীয় মনে করে না। স্ত্রীর সাথে স্বামীর অনেক কথা থাকে কিন্তু বলার উপায় নাই।’ ডিপিআর বন্দীর কাছে সবকিছু সেন্সর করে পাঠানো হতো। বেগম মুজিব কারাগারে যে বই নিয়ে যেতেন তা ডিআইজি পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে সেন্সর করে আপত্তিকর কিছু পাওয়া না গেলে তবেই কারা কতৃর্পক্ষের কাছে পাঠানো হতো। ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ শীর্ষক গ্রন্থমালার ১২শ খণ্ড থেকে জানা যায়— ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেগম মুজিব কারাগারে এই বইগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন: ব্রিটিশ লেখক সিএস ফরেস্টারের উপন্যাস ‘দ্য আফ্রিকান কুইন’, ত্রিশের দশকে আইরিশ লেখক কেট মর্টনের ঐতিহাসিক থ্রিলার ’হোমকামিং, ইংরেজ লেখক ডিএইচ লরেন্সের উপন্যাস ‘দ্য বয় ইন দ্য বুশ,’ স্কটিশ লেখক—ইতিহাসবিদ স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রেমের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আইভেনহো’ ও যোগযোগ দক্ষতা বিষয়ক গ্রন্থ ‘অ্যাসপেক্টস অব কনভারসেশন’। বইগুলোর বিষয় বৈচিত্র এবং ভাষা লক্ষ্যণীয়। এই বইগুলো কারাগারে বঙ্গবন্ধুর হাতে পেঁৗছলেও সব বই কিন্তু পেঁৗছাতো না। আত্মজীবনীমূলক ‘সুকর্ন’ তেমন একটা গ্রন্থ। সুকর্ন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি; স্বাধীতার নায়ক তথা জাতির পিতা। ওলন্দাজদের ৩৫০ বছরের ্ঔপনিবেশিক শাসন এবং জাপানিজদের বছর পাঁচেকের দখলদারিত্ব থেকে ইন্দোনেশিয়া তারই সংগ্রামী নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করে। বেগম মুজিবের হাতে ধরে সুকর্ন নামের বইটি ১৯৬৭ সালের ১৪ই জুন কারা কতৃর্পক্ষ এসবি অফিসে পাঠালে তারা ২০শে জুন এই লিখে ফেরত পাঠায়, ‘বইটিতে ড. সুকর্নর শৈশব থেকে সম্পূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। এতে লেখক বর্ণনা করেছেন ওলন্দাজ শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি কীভাবে সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জন্য স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। তিনি তার ১৩ বছরের কারাগার এবং নির্বাসিত জীবনের কথাও উল্লেখ করেছেন। বইটি যদি শেখ মুজিবুর রহমানের মত বন্দীর কাছে পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে তিনি এই বই পড়ে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন।’ কারা কতৃপক্ষ বইটি বঙ্গবন্ধুকে দেয়নি। সেরকম আরেকটি বই ‘পাকিস্তান—অ্যা পলিটিক্যাল স্টাডি’, কিথ কোলার্ড রচিত। এ বইটিতে পাকিস্তানের জন্মসময় থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের ১০ই জানুয়ারি গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিবেদনে বইটির বিভিন্ন আপত্তিকর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে। যেমন প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে লেখক বলেছেন যে, ‘পাকিস্তানের ইতিহাস জাতীয় ঐক্য ধারণ করে না । এর কোন কমন ভাষা বা সংস্কৃতি নেই, ভৌগলিক এবং অর্থনৈতিকভাবেও এটি একক সত্ত¦ার নয়।’ বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র নন, এটাও অজুহাত হিসেবে উল্লেখ করে বইটি তার কাছে আর দেওয়া হয়নি।
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে ঢুকে নিচতলার বারান্দা সংলগ্ন একবারে ডানদিকের ঘরটাই ছিল তার ব্যক্তিগত পাঠাগার। জাদুঘর হিসেবে এতদিন আগের মতই সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু ৫ই আগস্ট ২০২৪ তা জ¦ালিয়ে পুরিয়ে ছারখার করে দেয়া হয়েছে এবং গত ৫ই ফ্রেব্রুয়ারি ভবনের ধ্বংসাবশেষ বুলযোজার দিয়ে ধূলায় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনদিনই আর সেই অবকাঠামোর ঐতিহাসিক রূপ ফিরে পাওয়া যাবে না।
বঙ্গবন্ধু ঐ বাড়ির পাঠাগারে বই পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। দর্শনার্থী ও সহকমীর্দের সাথে সচরাচর এখানে বসতেন না। তাদের জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা ছিল। পাঠাগারটি ছিল সুপরিসর, খোলামেলা। দখিনা জানালা। পূর্বদিকেও তাই। কাঠের ফ্রেমের কাঁচের জানালা ভেদ করে চোখ চলে যেত বাগানে, সবুজ ঘাসের গালিচায়। দিনের বেলা সূর্যের আলো ঘরটাকে ঝলমল করে রাখতো। রাতে জোছনার আঁচল নেমে আসতো। চারিদিকে সারি সারি কাঠের আলমারি, তাকে তাকে সাজানো বই স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে উঁকি দিত। জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ধরণের শো পিস। এর মধ্যে ছিল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী কাঠের বা ব্রোঞ্জের নৌকা, হাতপাখা, পাখি ইত্যাদি। কয়েকটি ছবি আলমারির ওপরে, একটিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর্র সাথে যুবক মুজিব; এছাড়াও বাবা লুৎফর রহমন, বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, সাইকেলে হাসিমুখে বসা শেখ রাসেলের বহুল পরিচিত ছবি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা ছড়া বাঁধাই করে উপহার দিয়েছিলেন কোন এক গুনগ্রাহী, তাতে কালি কলমে লেখা— ‘পুষ্প তোমায় দিতে নারিলাম, দিলাম একটা ছড়া, আল্লাহ করুন তোমার হাতেই দেশ যেন হয় গড়া’।

ঘরের মাঝখানে ছিল আয়তাকৃতির পড়ার টেবিল। তার পাশে একটি উঁচু স্ট্যান্ডের ওপর বৃহদাকারের একটি কোরআন শরীফের দিকে যে কারো দৃষ্টি চলে যেত। মিশর সফরকালে ধর্মগ্রন্থটি তাকে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত উপহার দিয়েছিলেন। এর নিচের তাকগুলোতে কয়েকটি অভিধান ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য গ্রন্থ। পড়ার টেবিলের ওপর রাখা কয়েকটি বই, তন্মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বড় একটা সংবিধান যা তিনি স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই আমাদের উপহার দিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি যা পড়েছেন তা গভীরভাবে তার রাজনৈতিক দর্শনে আকৃতি গড়ে দিয়েছিল। ধমার্ন্ধতা, শ্রেণি—বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সংবিধানে লিখেছেন, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অধিকার থাকবে, কিন্তু ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না। পচাত্তরের ১৫ই আগস্টেও পাঠাগারটি ঘাতকের বুলেট থেকে রেহাই পায়নি। বইয়ের আলমারিতে বুলেটের ক্ষতচিহ্নগুলো ঐ কালরাত্রির নির্মমতাকে ধরে রেখেছিল। পড়ার টেবিলে গুলিবদ্ধ কয়েকটি বই; তন্মধ্যে কবি নজরুল বিষয়ক শ্রদ্ধাঞ্জলি নামের বইটি বিদ্ধ করে যেন কবিকেই বীতশ্রদ্ধ করেছে একটি বুলেট। হূমায়ূন আহমেদের নন্দিত নরকে বইটিতেও ছিল সেই নারকীয় হামলার চিহ্ন।
আলমারিতে রবীন্দ্র রচনাবলির সবগুলো খণ্ড ছিল, আবার আলাদা করে উপন্যাস গোরা, চার অধ্যায়, ছোটগল্পের সংকলন গল্পগুচ্ছ, কাব্য সংকলন সঞ্চয়িতাও ছিল, যেটি বেগম মুজিব প্রায়শ জেলখানায় নিয়ে যেতেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে পা দিয়ে রবিঠাকুরের পঙ্ক্তি ‘সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি’ স্মরণ করে জনসমুদ্রের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু অশ্রম্নবিজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, ‘কবিগুরু তোমার উক্তি ভুল প্রমানিত হয়েছে। তুমি দেখে যাও তোমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।’ ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার প্যারেড গ্রাউন্ডে সমবেত ১০ লাখ ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ তিনি প্রথমে হিন্দিতে শুরু করেছিলেন। একটু পর জনতাই বাংলা বাংলা বলে শোর তোলে, তখন ইন্দিরা গান্ধিও তাকে বাংলায় বলতে বলেন। কৃতজ্ঞতা জানাতে বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রসাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন, ‘নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা দিলাম আমি তাই’। আরেক আলমারিতে নজরুল রচনাবলি, কাব্য সংকলন সঞ্চিতা। বঙ্গবন্ধু ভারতের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সেদেশ থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন, আবাসনের ব্যবন্থা করেছিলেন, দেশসেরা চিকিৎসকদের মাধ্যমে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করেছিলেন, সবোর্পরি জাতীয় কবির মযার্দা প্রদান করেছিলেন। ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বারের মত রেকর্ডকৃত কলিম শরাফী, সানজিদা খাতুন প্রমুখের গাওয়া ১২টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আফসোস করে বলেছিলেন,‘পাকিস্তান স¦াধীন হওয়ার ২২ বছর পরও রবীন্দ্রসাহিত্য পূর্বপাকিস্তানে পাওয়া যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং শত দমনপীড়ন করেও তা থেকে বাঙালি জাতিকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কদিন আগে শাহাজাদপুরে কুঠিবাড়ির জীর্ণদশা দেখে আমার কষ্ট লেগেছে।’ তিনি আরো বলেছিলেন,‘কবি নজরুলকে ভালোভাবে যত্ন নেয়া হচ্ছে না। যৎসামাণ্য মাসিক ভাতা নজরুলের মত অসামান্য প্রতিভাবানের জন্য যথেষ্ট নয়’।
মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ ও দলিল—দস্তাবেজ তার সংগ্রহে ছিল, যেমন: বালাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস। সাহিত্য সাময়িকীর প্রতি আকর্ষণ ছিল। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় কতৃর্ক প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার অনেকগুলো সংখ্যা দৃশ্যমান ছিল। শওকত ওসমানের জাহান্নাম হইতে বিদায়, সৈয়দ মুজতবা আলীর শবনম, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের কত ছবি কত গান, আবুল ফজলের দুর্দিনের দিনলিপি পাঠাগারের অমূল্য সম্পদ ছিল। জলবায়ু সংকট নিয়ে উচ্চকিত এত আলোচনা তখন ছিল না। তবু এক্সপ্লোরিং দ্য ওয়েদার (গ্যালেন্ট এবং হেজ), দ্য ওয়ান্ডাফুল ওয়ার্ল্ড অব এয়ার (জেমস ফিশার), ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড অব লাইফ (জুলিয়ান হাক্সলে), রিভারস অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি গ্রন্থ এ বিষয়ে তার পাঠাগ্রহের সাক্ষ্য ছিল। প্লেয়িং দ্য গিটার বইটি হয়তো শেখ কামালের জন্যই এনেছিলেন।
বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ^সাহিত্যের পাঠক। ধ্যান—ধারণায় ছিলেন সমাজতন্ত্রের অনুবতীর্। সংবিধানে রাষ্ট্রের ৪ মূলনীতির একটি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে সমাজতন্ত্রের চৈনিক বা রুশ বা বৈজ্ঞানিক কোন মডেলই কপি—পেস্ট না করে তিনি নিজের মত কায়েম করতে চেয়েছিলেন। আলমারিতে শোভিত কার্ল মার্কসের দুনিয়া কাঁপানো ক্যাপিটাল, মার্কস—অ্যাঙ্গেল, লেনিনের নির্বাচিত রচনাসমগ্র, ফানডামেন্টালস অব সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম ইত্যাদি গ্রন্থ তার সমাজতান্ত্রিক মানস গঠনে ভূমিকা পালন করেছিল। রুশ সাহিত্যের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, সেটাও তাকে প্রভাবিত করেছিল। পাঠাগারে আছে ম্যাক্সিম গোর্কির মা, লিও টলস্টয়ের ছোটগল্প সমগ্র, দস্তয়ভস্কির দ্য ইডিয়ট, নিকোলাই অস্ত্রভস্কির ইস্পাত ইত্যাদি বইয়ের সমাহার। ইংরেজ কবি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা, লংফেলোর নির্বাচিত কবিতাও জায়গা করে নিয়েছে তার পাঠাগারে।

বিশ^রাজনীতির জন্য ইতিহাস জানা আবশ্যক। তিনি হিস্টরি অব সোভিয়েত ফরেন পলিসি, অরিজন অব অ্যামেরিকান পলিটিকাল থট, ক্রশ সেকশন—অ্যাসেইজ অব কনটেম্পোরারি অ্যামেরিকা, গ্লিমসেস অব ফ্রিডম অব ইন্ডিয়া (জওহরলাল নেহরু), হিস্টরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (তারা চাঁদ), পাকভারত যুদ্ধ, পূবে আবার সূর্য উঠলো ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতেন। গুগলের যুগ তো তখন ছিল না যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর এখনকার মত আঙুলের ডগাতে পাওয়া যেত। আলমারিতে রক্ষিত ব্রিটানিকা’স কনসাইজড পিকচারড এনসাইক্লোপেডিয়ার সবহুলো খণ্ডে তার জ্ঞানতৃষ্ণার নিবারণ হতো। আজকের মৌলিক বিজ্ঞান সিরিজ বই, স্থাপত্যকলা এমনকি জাদুর বইও আছে। মনীষীদের জীবনী তাকে অনুপ্রেরনা জোগাতো; তাই হযরত মোহাম্মদ (সা.), যীশুখ্রিষ্ট, জর্জ বার্নার্ড শ, আব্রাহাম লিঙ্কন, কলম্বাস, হিটলার, নেপোলিয়ান, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রমূখের জীবনীগ্রন্থের উপস্থিতি ছিল আলমারিতে। একদিকে ধর্মগ্রন্থ তফসীরে আশরাফী, বোখারী শরীফের খণ্ডসমূহ যেমন আছে, আবার পৌরানিকীও ছিল। বিদ্যাসাগর রচনাবলি. বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলি, সমরেশ বসুর দুই অরণ্য, মানুষ, বিশ^াস সহ সত্যজিৎ রায়, শির্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবতীর্, সাগরময় ঘোষ প্রমূখ প্রখ্যাত ভারতীয় লেখকের উপন্যাস বা গল্পগ্রন্থ তার পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করেছিল।
কোন আলমারিতে কোন বই আছে তা খুঁজে পাওয়ার জন্য লাইব্রেরিতে ক্যাটালগ বক্স থাকে; এতে ড্রয়ারের মধ্যে থরে থরে সাজানো ছোট ছোট কার্ডে বই ও লেখকের নাম, আলমারি নম্বর, তাক নম্বর, বইটির অবস্থান উল্লেখ করা থাকে। বঙ্গবন্ধুর পাঠাগারে সক্রিয় ক্যাটালগ বক্সও ছিল। বইগুলো বিষয়ের ভিত্তিতে গুচ্ছ গুচ্ছ করে সেভাবেই সাজানো ছিল। আন্দোলন, সংগ্রাম, সংগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু বই পড়তে বা নিজের একান্ত চিন্তাভাবনার জন্য পাঠাগারে যথেষ্ট সময় কাটাতেন। বিভিন্ন বইয়ে ছোট ছোট চিরকুট সাঁটানো ছিল, কোন কোনটায় তার স্বহস্তে লেখা নোট, যেগুলো তিনি যে বইগুলো পড়েছেন তার প্রমাণক ছিল।
বেগম মুজিব জেলে কেবল বই না, খাতা—কলমও দিতেন, লেখার জন্য। বারবার তাগাদা দিতেন। আবার বঙ্গবন্ধু যখন জেল থেকে ছাড়া পেতেন তখন বেগম মুজিব জেল গেটে যেতেন বঙ্গবন্ধুকে আনতে আর বঙ্গবন্ধুর লেখাগুলো যেন আসে তা নিশ্চিত করতেন। রুলটানা এসব খাতা অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছে ‘অসমাপ্ত আত্মীজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’ ও ‘আমার দেখা নায়াচীন’। ভাষাভঙ্গি থেকে শুরু করে লেখার ভেতরে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে বঙ্গবন্ধুর পড়াশোনা কত গভীর ছিল। কবি না হয়েও তিনি কবি হয়ে উঠেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিন নিউজউইকের সাংবাদিক লোবেন জেঙ্কিন্স তার লেখায় বঙ্গবন্ধুকে ‘রাজনীতির কবি’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। নির্মলেন্দু গুণ তার ‘স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদেও হলো’ কবিতায় তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবি বলে সম্বোধন করেছেন। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন বঙ্গবন্ধুর লেখা বইগুলোকে ‘সময়ের দলিল’ বলেছেন; তিনি আরো বলেছেন, ‘সহজ ভাষাভঙ্গি, বিভিন্ন ঘটনাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও লেখার মধ্যে সরস প্রবাহ— এই সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য রচনশৈলীর প্রতীক, যা লেখক হিসেবে তাঁর সার্থকতাকেই প্রকাশ করে। রাজনীতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে দার্শনিক যোগ, সেগুলো বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ পায়।’
চার্চিল বলেছিলেন ‘আমি শুধু সেই মানুষদের ভয় পাই যারা ভাবতে পারে না’। আমাদের নেতাদের দৈনন্দিন যে রুটিন তাতে তাদের ভাবার সময়, পড়ার সময় কতটুকু! ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু এমন কজনই বা আছেন! একজন সংসদ সদস্য তো একবার ছাত্রদের সাথে এক সভায় বলেই বসেছিলেন ‘তোমরা শেক্সপিয়ারের মত বিজ্ঞানী হও’। ক’জনের বাড়িতে ব্যক্তিগত পাঠাগার দূরে থাক, নিজের পড়ার একটা টেবিল আছে? ক’জনের বক্তব্য শুনলে সুপাঠকের পরিচয় পাওয়া যায়?
মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, গীতিকবি ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

 বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ
বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ