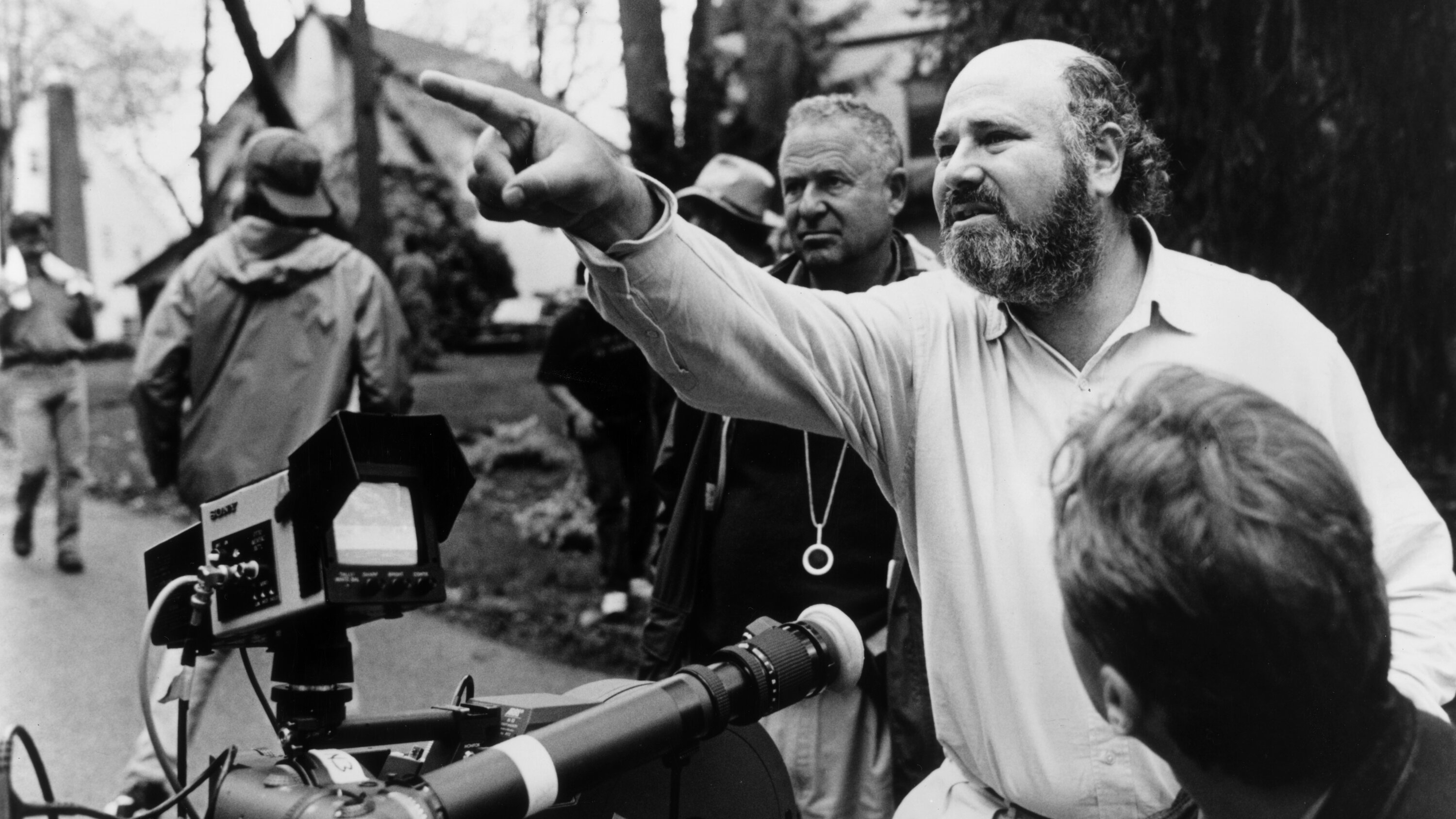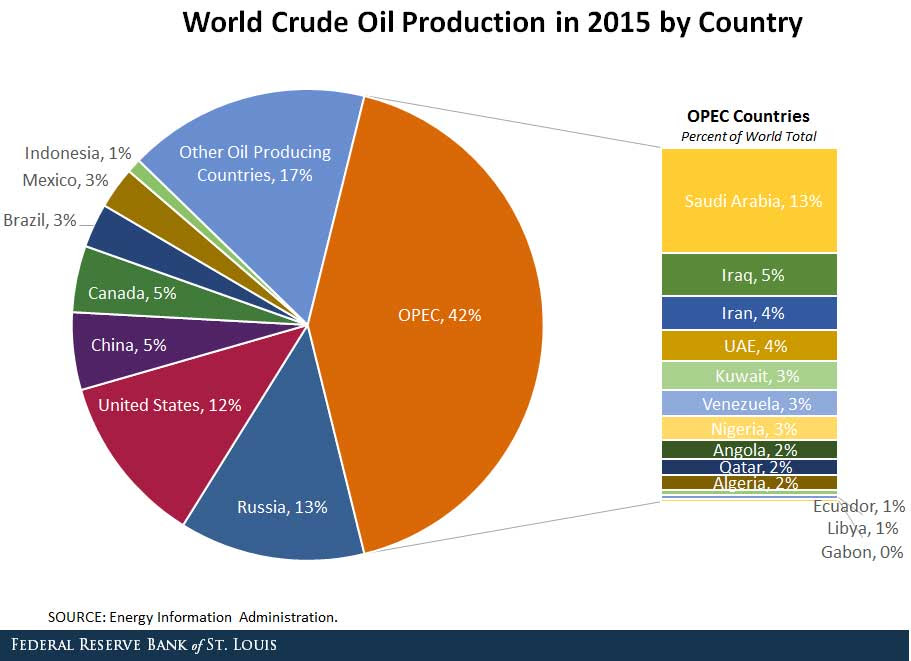পশ্চিমবঙ্গের মালদা আর মুর্শিদাবাদ, জেলা-দুটির অর্থনীতির অন্যতম মূল ভিত্তি হলো এখানকার পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। তবে নানা রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ‘অবৈধ বাংলাদেশি’ সন্দেহে যেভাবে হেনস্থা হতে হচ্ছে, তাতে ভীত হয়ে বহু মানুষ গ্রামে ফিরে এসেছেন। তাদের রোজগার নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় তার নেতিবাচক ফল দেখা যাচ্ছে জেলা দুটির হাট-বাজারেও।
ওই দুই জেলা ঘুরে এসে এই প্রতিবেদন:
ভর দুপুরে কাঁধে একটা কোদাল নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ধানক্ষেতের মাঝ বরাবর আল পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল হক।
মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুরে তার গ্রামে নিজের জমি জায়গা বিশেষ নেই – তিনি চলেছিলেন বাবার ক্ষেতে কোনও কাজে। চাষ আবাদ অবশ্য তার পেশা নয়।
তখনই একটা যাত্রী ট্রেন হুইসল বাজিয়ে ছেড়ে চলে গেল পাশের মিলনগড় স্টেশন থেকে। ওই রেললাইনটা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণ আর বিহারের সঙ্গে অন্যতম মূল রেল লাইন।

ওরকমই ট্রেনে তো তিনি সেই ছোটবেলা থেকেই যাতায়াত করতেন – হরিশচন্দ্রপুরের মিলনগড় থেকে সুদূর ওড়িশা পর্যন্ত। সেখানকার গ্রামে গ্রামে প্লাস্টিকের ঘর-সংসারের জিনিষ, খেলনা – এসব বেচতেন এরা, কয়েক মাস আগে পর্যন্তও।
“ছোট থেকে আমি বাইরে ওড়িশাতেই থাকি। আগে বাবারা, চাচারা করছিল, এখন বাবার বয়স হয়ে গেছে, তাই আর যাচ্ছে না, আমরা কাজ করি। আমি ওখানেই প্লাস্টিকের জিনিস ফেরি করি।” বলছিলেন মি. হক।
তিনি বলছিলেন, “এর আগে আমরা কাজ করেছি, এরকম আক্রমণ তো হয় নি, বা এরকম সমস্যায় পড়ি নি। এই যখন থেকে বিজেপি ওখানে সরকারে এসেছে, তারপর থেকেই আমাদের ওপরে অত্যাচার হচ্ছে। আমাদের মারধর করল, জেলে আটকিয়ে রাখল, তারপর বাড়ি ফিরে এলাম। এখানে তো কোনও কাজ-কাম নেই, কী করব! বাবার কিছু আর আমার কিছু জমি জায়গা আছে, সেখানেই কাজ করছি এখন।”
মি. হকদের মতো পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওড়িশায় যাওয়া কয়েকজন পরিযায়ী ব্যবসায়ীকে কী বীভৎসভাবে মারধর করা হয়েছে, আটক রাখা হয়েছিল, সেই সংবাদ আগেই প্রচার করেছে বিবিসি বাংলা।
সেখানকার স্থানীয়রা যেভাবে মারধর করেছেন এই পরিযায়ীদের, তার কয়েকটি ছবি বিবিসি দেখেছে। তবে ওই বর্ণনা পাঠকদের অস্বস্তির কারণ হতে পারে, তাই তা থেকে আমরা নিজেদের বিরত রাখলাম।

‘একবার তো বেঁচে ফিরে এলাম’
আশরাফুল হকের মতোই কয়েক মাস আগে পর্যন্ত, মুম্বাইতে ভূগর্ভস্থ পাইপ বসানোর কাজ করতেন ওই মিলনগড় গ্রামেরই মোহাম্মদ খায়েরুল ইসলাম।
এখন কাজ ছেড়ে ফিরে এসেছেন গ্রামে। অলস দিনের শেষে বিকেলবেলায় স্টেশনের লাগোয়া এলাকায় বছর দশেকের মধ্যে গজিয়ে ওঠা ছোট্ট বাজারে এসেছিলেন চা খেতে। সেখানেই কথা হচ্ছিল মি. ইসলামের সঙ্গে।
“আমরা যেখানে থাকতাম, সেখানে কোনও সমস্যা হয় নি ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য জায়গা থেকে খবর পাচ্ছিলাম যে বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলছে, ডকুমেন্ট দেখতে চাইছে। তখনই ঠিক করি যে এখানে থাকব না। তাই ফিরে এসেছি,” বলছিলেন মি. ইসলাম।
আবার গঙ্গা-পদ্মা নদী-ধারার যে অংশ ভারত থেকে বাংলাদেশ হয়ে ফের ভারতে ঢুকেছে পদ্মা নামে, তার পাশের জেলা মুর্শিদাবাদেরও বহু পরিযায়ী শ্রমিক গত তিন চার মাসে ঘরে ফিরে এসেছেন।
এরকমই কয়েকজন চর কৃষ্ণপুরের রাহুল শেখ আর নয়ন শেখ।

তাদের গ্রাম ওই চর এলাকা থেকে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ খুবই কাছে। পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে নৌকা চেপে ওই চর এলাকার দিকে যাওয়ার সময়ে দূরে দেখাও গেল বাংলাদেশের ভূমি।
ওই চর এলাকা থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানা এলাকার মেহবুব শেখও ফিরেছেন তার গ্রামে। কিন্তু সরাসরি আসতে পারেন নি তিনি।
মহারাষ্ট্রের পুলিশ তাকে অবৈধ বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পুশ-আউট করে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তার ভারতীয় পরিচয় নিশ্চিত করার পরে সেদেশ থেকে পরিবারের কাছে ফিরতে পেরেছেন তিনি।
তবে এখনও কাজে ফিরতে ভয় পাচ্ছেন তিনি।
মি. শেখ বলছিলেন, “ভয় লাগছে, যদি আবারও হেনস্থা করে!”
“সব ডকুমেন্ট থাকার পরেও তো হেনস্থা করছে, তাই ভয় লাগছে। একবার তো ফিরে এলাম বেঁচে, আবার যদি মনে করেন কোথায় ফেলে দেবে নিয়ে, তখন তো মরণ ছাড়া.. ..”, বাংলাদেশে পুশ আউটের অভিজ্ঞতা মনে করে বলছিলেন মেহবুব শেখ।

পরিযায়ীদের রেমিট্যান্সেই বদলে গেছে গ্রাম
“এই গাছতলা থেকে ওদিকটা আর এদিকে হাই মাদ্রাসা অবধি – পুরোটাই বিল ছিল একসময়ে,” বলছিলেন হরিশচন্দ্রপুরের কোবাইয়া গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা আব্দুল কাইয়ূম।
মিলনগড় স্টেশনের পাশে এসেছিলেন বিকেলের চা খেতে।
মিলনগড়ের ওই বিল এলাকাতেই এখন গ্রামের দোকান বাজার – চায়ের দোকান থেকে শুরু করে ব্যাংকের এটিএম যেমন হয়েছে, তেমনই আছে ঘড়ি আর জামাকাপড়ের দোকানও।
আর রয়েছে নির্মাণ সামগ্রীর দোকান।
এই নির্মাণ সামগ্রীর প্রচুর দোকান মালদা আর মুর্শিদাবাদ জেলা দুটির গ্রামাঞ্চলে দেখা যাচ্ছিল।
মালদার বাসিন্দা মি. কাইয়ূম বলছিলেন, “বছর ১৫-র মধ্যেই এগুলো বদলিয়ে গেছে। বেশিরভাগ মানুষই বাইরে থেকে খেটে পয়সা রোজগার করে এনে এগুলো করেছে।”

বদলিয়ে গেছে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা অঞ্চলের গ্রামগুলোও। চাষের জমির মধ্যেই অনেক নির্মীয়মাণ বাড়ি যেমন চোখে পড়ছিল, তেমনই দেখছিলাম তৈরি হয়ে যাওয়া বিশালাকার দোতলা-তিনতলা বাড়িও। কাঁচা বাড়ি প্রায় নেই-ই।
গ্রামের এক প্রবীণ কৃষক জয়নাল বলছিলেন, “যারা মজুর খাটে, তারাই ভাল আছে। আগে ওদের অবস্থা ভাল ছিল না। আর যাদের জমি জিরেত আছে, তারা খায় ডাল-ভাত, আর ওরা খায় মাংস ভাত। জমিওয়ালাদের চিন্তা করে খেতে হয়।”
মুর্শিদাবাদ আর মালদার এই গ্রামগুলির যে ছবি উপগ্রহের মাধ্যমে পাওয়া যায়, সেগুলো দেখলেই বোঝা যাবে কত নতুন বাড়ি হয়েছে গত এক-দেড় দশকে।
আবার পদ্মাপারের গ্রাম আখেরিগঞ্জের মতো জায়গাতে ‘অনলাইন ডেলিভারি বয়’-এরও দেখা পেলাম।
পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বলছিলেন, “ভিন রাজ্য থেকে অর্থ উপার্জন করে পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন গ্রামে ফিরে আসে, তার ওপরে গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভর করে। এখানে ছোট ছোট দোকান বা বাজারে সেই অর্থ খরচ করে শ্রমিক পরিবারগুলো।
“আবার অনেক রেস্তোঁরা হয়েছে, গৃহসজ্জার দোকান হয়েছে এইসব অঞ্চলে। একই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বেসরকারি স্কুলের হোস্টেলে রেখেও পড়াশোনা করাচ্ছে এই পরিবারগুলো,” বলছিলেন মি. ফারুক।
দুই জেলাতেই চোখে পড়ছিল প্রচুর বেসরকারি স্কুলের বিজ্ঞাপন জ্বলজ্বল করছে রাস্তার ধারে। মি. ফারুক বলছিলেন এই সব স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশই পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের ছেলে মেয়ে।
যতগুলো পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে, সকলেই বলেছেন যে তারা সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে সচেতন।
মিলনগড় গ্রামের মোহাম্মদ খায়েরুল ইসলাম বলছিলেন, “ছেলেকে স্কুলে পড়াচ্ছি যাতে বড় হয়ে আমার মতো অন্য রাজ্যে তাকে কাজ করতে যেতে না হয়। পরিশ্রম করে রোজগার করছি তো সেজন্যই।”
দোকান-বাজার, বিভিন্ন পরিসেবা, নির্মাণ সামগ্রীর বিক্রি – এসব যেমন একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিহ্ন, তেমনই আবার যখন পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিনাখরচের সরকারি স্কুলের বদলে বেসরকারি স্কুলে পাঠানো হয়, সেটা দেখেও বোঝা যায় যে পরিবারগুলিতে অর্থায়ন হয়েছে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।
তবে গত কয়েক মাস ধরে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে এসেছে ভাঁটার টান।

‘ছেঁড়া চটি সেলাই করে পরছি’
পদ্মা নদীর মাঝে জেগে ওঠা চর কৃষ্ণপুরের মহিষমারী এলাকার গৃহবধূ হাসিবা খাতুন তখন রাতের রান্না চাপিয়েছিলেন।
তার স্বামী রাহুল শেখ অনেক বছর ধরেই অন্য রাজ্যে কাজ করেন। সবশেষ কাজ করতে গিয়েছিলেন ওড়িশায়। স্থানীয় মানুষরা তাদের হেনস্থা করতে শুরু করায় ফিরে এসেছেন গ্রামে। কখনও দিনমজুরির কাজ পান, কোনও দিন সেটাও জোটে না।
এদিকে জমানো অর্থও প্রায় শেষ, শখ-আহ্লাদ তো বাদ দিতেই হয়েছে, কমাতে হয়েছে সংসার খরচও।
“আগে মাছ-ভাত, মাংস-ভাত খেতাম, এখন সবজি বেশি আসছে। রোজগারপাতি থাকলে বাচ্চাকে ভাল ডাক্তার দেখাতাম, এখন সরকারি হাসপাতালে লাইন দিতে হচ্ছে,” বলছিলেন মিসেস খাতুন।
তার আক্ষেপ, “ছেঁড়া চটি সেলাই করে পরছি, জামা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে পরছি – এভাবেই চলছে। আগে তো একটা জামা দরকার হলে দুটো বা তিনটে জামাও কিনতে পেরেছি।”
মিসেস খাতুনের মতোই সংসারের খরচে রাশ পড়াতে হয়েছে ভগবানগোলার মেহবুব শেখে স্ত্রী সোরেনা বিবি বা তারই প্রতিবেশী নাসিয়া বিবিদের মতো হাজার হাজার পরিবারকে।
আর তাদের খরচে রাশ টানার প্রভাব পড়েছে এলাকার হাটে বাজারে।

ফাঁকা দোকানপাট, ব্যবসা নেই
পদ্মা পাড়ের আখেরিগঞ্জের হাট ব্রিটিশ আমলে বিরাট অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র ছিল।
এলাকারই বাসিন্দা সারাফ আবেদিন বলছিলেন, “আখেরিগঞ্জের হাটে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গের রাজশাহী থেকে শুরু করে বিরাট অঞ্চলের মানুষ কেনাবেচা করতে আসতেন। এর একটা মূল পণ্য ছিল পাট। তবে সময়ের বিবর্তনে হাটটা এখন খুবই ছোট হয়ে এসেছে।”
যেদিন আখেরিগঞ্জের হাটে গিয়েছিলাম, সেটা ছিল এক বুধবার। ওইদিনই ছিল হাটবার।
সন্ধ্যাবেলাতেও বেশ ভিড় চোখে পড়ছিল। তবে সবজির দোকানেই বিক্রিবাটা বেশি হচ্ছে দেখছিলাম। তুলনামূলক-ভাবে শাড়ি বা জুতো

হাটবারে সারাদিনই কেনাবেচা চলে, তবে গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য বাজারে ভিড় মূলত বিকেলের পর থেকেই শুরু হয়।
ভগবানগোলা বাজারেও এক সন্ধ্যায় ভিড় দেখা যাচ্ছিল বেশ ভালই। কিন্তু রাস্তার দুইপাশে দোকানগুলো প্রায় ফাঁকাই। কখনও সখনও কোনও ক্রেতা আসছেন।
ওই বাজারে বছর দশেক ধরে খেলনা, গৃহসজ্জা, ঘরকন্না আর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের নানা সামগ্রীর দোকান চালান আজমল হক।
“পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের স্ত্রী পরিবারের কাছে টাকা পাঠালে তা দিয়েই আমাদের ব্যবসাটা চলে। ওরা টাকা না পাঠালে আমাদের সেই ব্যবসা হয় না। এখন ওরা কাজ পাচ্ছে না, তাই আমাদের ব্যবসার অবস্থাও খুব খারাপ,” বলছিলেন মি. হক।
আবার মালদার হরিশচন্দ্রপুরের দৌলতপুর গ্রামে নির্মাণ সামগ্রীর দোকান-মালিক আব্দুল মালিক বলছিলেন, “আমার ব্যবসার প্রায় ৭০ শতাংশই চলে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঠানো টাকায়। পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে থেকে রোজগার করে না আনলে তো আমাদের জিনিষও বিক্রি হবে না।”
“বিগত চার-পাঁচ মাসে বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বলা পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপরে অত্যাচার শুরু হওয়ার পর থেকে তারা যখন রাজ্যে ফিরে এল এবং তাদের কাজকর্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হল, তার প্রভাব গ্রামীণ অর্থনীতিতেও পড়েছে,” বলছিলেন আসিফ ফারুক।
তবে এর মধ্যেই আবারও অনেক পরিযায়ী শ্রমিক ফিরেও যাচ্ছেন কাজের জায়গায়।
আর যারা থেকে গেছেন তারাও ভাবতে শুরু করেছেন যে কবে কাজে ফিরতে পারবেন।
বাংলাদেশে পুশ-আউট হয়ে গিয়ে আবারও ফিরে আসা শ্রমিক মেহবুব শেখ বলছিলেন, “কাজে তো যেতেই হবে। আবার যখন আবহাওয়া ভাল হবে, যখন দেখব যে পশ্চিমবাংলার লোককে আর ধরছে না, বাঙালীদের কিছু বলছে না, তখন আবার যাব।”
ফিরে তো যেতেই হবে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের, না হলে যে সংসার চালানো দুষ্কর।
BBC News বাংলা

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট