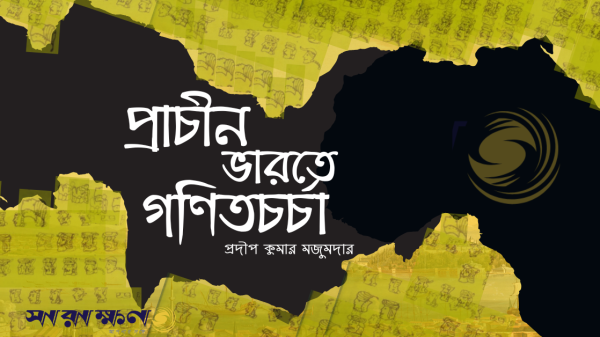“রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসে ইসপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলো নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন”। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার অনূদিত ইসপের গল্পের ভূমিকা এইভাবেই শুরু করিয়াছেন।
বিদ্যাসাগর ইসপ অপেক্ষা বাঙালি জাতির জন্য আরো অনেক বড় মাপের ছিলেন। যাহা বাঙালির পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে তাহা বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে বলিয়া গিয়াছেন।
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “ প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো; আর, মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বব্যাপী স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ; আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিয়া রাখে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশত লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না”।
বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই কথা বহুপঠিত। তাহার পরেও আজ বাংলাদেশে বিদ্যাসাগারের ২০৫তম জন্মদিবসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেরুদণ্ডের মতো একটি মেরুদণ্ড বড়ই প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে। আর এ কারণেই এই লেখার শুরুতেই তাহার অনুবাদিত ইসপের গল্পের বইটির ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে ইসপের ৭৪টি নীতি গল্প তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আজ বাংলাদেশের চারপাশে তাকাইলে তাহার অনুবাদিত ইসপের ‘ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর’ গল্পটি বার বার মনে আসে। যেখানে ব্যাঘ্রটি কুকুরের গলায় মালিকের দেয়া বকলসের দাগ দেখিয়া ভালো খাবারের আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়া স্বাধীন জীবনে চলিয়া যায়।
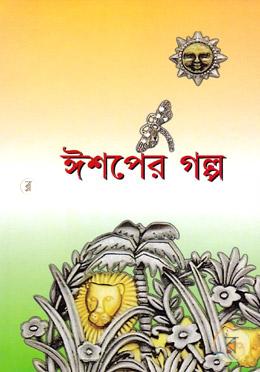
আজ যখন স্বাধীনতার প্রতীকগুলো এবং স্বাধীনতার নেতার ভাস্কর্য, এমনকি জাতির ইতিহাসের জন্যে তাহার আইকনিক বাড়িটিও বুলডোজার দিয়া গুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা লইয়া উল্লাস নৃত্য শুধু নয় ভূরিভোজ হইয়াছে। আর ইহার পরিবর্তে যাহার দাপাইয়া বেড়াইতেছেন, তাহাদের কলার খুলিলেই বেশির ভাগের গলায় মালিকের দেয়া বকলসের দাগ দেখা যাইবে।
আর যাহারা ওই পালিত কুকুরের মতো খাদ্যলোলুপ তাহারা যে অর্থলোলুপ তাহাতে তো কোন সন্দেহ নাই। এই অর্থলোলুপদের ও কৌশলী ভিক্ষাবৃত্তিধারীদের প্রতি বিদ্যাসাগরের সব সময়ই একটা ঘৃণা ছিলো। যাহা রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও শম্ভূচন্দ্র প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে পাওয়া যায়, “ বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিলো। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেই জন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, “ এখানে আছেন বলিয়া, আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই” ।
ইহাই মেরুদণ্ড। কালভেদে কখনও কখনও অর্থলোলুপ, হীন-চরিত্রের মানুষেরা উচ্চস্থান বা পবিত্রস্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগকে মান্য করিয়া নিজেকে নরাধমে পরিণত করার কোন যৌক্তিকতা নাই। আজ হইতে, ২০৫ বছর আগে এই শঠ ও কপট ক্ষীণকায়, পর-অনুগ্রহে সম্মানপ্রার্থী লোভী বাঙালি জাতির মধ্যে বৃহৎ বনস্পতির মতো মাথা উঁচু করিয়া এই সাহসের শিক্ষা বিদ্যাসাগরই বাঙালি জাতিকে দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য হইলো, তাহার জাতিটি অতবড় পাত্র নয় যে তাহা গ্রহণ করিবে। বরং তাহার জাতিগোষ্টির বেশিভাগই অপরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া বাকচাতুর্যের মধ্যে দিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেই বেশি পছন্দ করিয়া থাকে। তাহার মতো সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিয়া তাহার জাতিতে খুব কম মানুষই দীর্ঘকায় হইয়াছেন। আর যাহারা দীর্ঘকায় হইয়াছেন- খর্বকৃত্তিরা দল বাধিয়া কুকুরের মতো পা উঁচু করিয়া সেই সব পর্বতসম উঁচু মূর্তি বা বৃহৎ বৃক্ষে মূত্র ত্যাগ করিয়া ইতরের আনন্দ ভোগ করিয়াছে- যাহা তাহাদের স্বভাব বা জন্মজাত। স্বভাব বলিতে হইবে এই কারণে, বিদ্যাসাগরের মত মানুষ যাহা ধারণ করিয়া চলিয়াছিলেন বা চলেন তাহা সংস্কৃতি ও পরমার্থ আর পশু যাহা ধারণ করিয়া চলিয়া থাকে তাহা স্বভাব মাত্র।

আর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমাদের মূল পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ আরো বিশদ করিয়া বলিয়াছেন, “ সেইজন্য তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাহার কার্যপ্রণালী আমাদের মত ছিলো না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি; তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগুলো ছিল, কিন্তু তাহার উপরেও ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই সুখদুঃখ লাভক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদুঃখ লাভক্ষতি কিছুই নহে।
আমাদের বর্হিজীবনের একটা লক্ষ্য আছে, তাহাকে সমস্ত জড়াইয়া এক কথায় স্বার্থ বলা যায়। আমাদের খাওয়া- পরা শোওয়া কাজকর্ম করা – সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ। ইহাই আমাদের বর্হিজীবনের মূলগ্রন্থি।
মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম -মহল ও খাস- মহলের দুই কর্তা- স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্য করিয়া চলাই মানব জীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারে বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় ‘ অধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ’ তখন পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থকে পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল অবলীলাক্রমে তিনি সেই কাজ করিয়া থাকেন।
অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃপুতুলি যন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে এক প্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি, – ভক্তি করি না, পূজা করি- চিন্তা করি না, কর্ম করি- বোধ করি না সেই জন্যই কোনটা ভালো ও কোনটা মন্দ তাহা। অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব- দেবতা- স্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড় প্রতিমা কোনমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে”।

এই যাহারা আমরা কোনমতে ঠাট বজায় রাখিয়া চলি, তাহার কখনই পারমার্থিক নহে। “ গতানুগতিকো লোকো না লোকঃ পারমার্থিকঃ” আমাদের দেশের কবির এই কথাই সত্য, গতানুগতিক লোক, গতানুগতিকই তাহারা কখনই বীর হইতে পারে না।
এই অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু গতানুগতিকের বাইরে গিয়া পরমার্থ অর্জন করিয়া ছিলেন তাহা নহে, তিনি সত্যিকার বীরও ছিলেন। তাই ভাষা ও মানব সমাজ যে দুইটাই প্রচণ্ড গতিশীল- সেই বিষয় দুইটাকে তিনি সংস্কার করিবার জন্যে আপন স্বার্থ বিসর্জন দিয়া জীবনপণ কাজ করিয়াছিলেন।
যাহারা জীবদ্দশায় বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াছিলেন, তাহার কাজ দেখিয়াছিলেন তাহারা আমাদের অধিক ভাগ্যবান। কারণ, জীবদ্দশায় দেখা আর তিনি পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার পরে তাহার কাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাহাকে জানার ভেতর একটি পার্থক্য তো থাকিয়াই যায়।
এই হিসাবে আমাদের প্রজন্ম আমরা কিছুটা ভাগ্যবান, আমরা বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখিয়াছি। যিনি আপন স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশ ও মানুষের মুক্তিকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া জীবনপণ লড়িয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যেমন সফল হইয়াছিলেন এবং তাহার স্বজাতির ইতরগণ কর্তৃক পরিত্যাজ্য হইয়াছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্যেও তেমনি ঘটিয়া থাকে। বাঙালির মতো তৃণ ভূমিতে বিশাল বৃক্ষ জন্মাইলে ইহার ব্যতিক্রম কিছুই ঘটিবে না। বাঙালির সকল বৃক্ষের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটিয়াছে। কারণ বাঙালির একটি অংশ সব সময়ই তাহার ছাগ-চরিত্র লইয়া তৃণকেই ভালোবাসে- দীর্ঘকায় বৃক্ষ তাহার স্বভাবজাত নহে। যে কারণে বিদ্যাসাগর তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার স্বজাতি কর্তৃক নিহত হন নাই বটে, তবে অপমানিত ও পরিত্যাজ্য হইয়াছেন।

তাহার পরেও আমাদের যেমন দেশরক্ষা করিতে হইলে, আপন বাঙালি সত্ত্বাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধারণ করিতে হইবে। তেমনি আমাদের সমাজ ও সন্তানদের চরিত্র তৈরি করিতে হইলে এই সকল বৃক্ষের কাছে বার বার যাইতে হইবে। তৃণভূমিতে মানব সন্তান বড় হয় না। মানব সন্তানকে অন্তরে বৃক্ষ বা পাহাড়ের মত দীর্ঘ হইতে হয়।
বিদ্যাসাগর হইতে শুরু করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই তৃণভূমিময়, নিষ্ফলা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া খুব বেশি মানুষ তাহাদের সঙ্গী হিসাবে পাইবেন, এমনটি আশা করা নিতান্তই মূর্খতা। ভাবিলে শরীর শীতল হইয়া আসে, বাঙালির আরেক বৃহৎ বৃক্ষ নজরুল যে কবিতা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, আজ এই তৃণভোজী চালিত সমাজ ও রাষ্ট্রে বসিয়া তিনি কী তাহা লিখিতে পারিতেন! বরং পাঠ্য হইতে তিনি পরিত্যাজ্য হইয়াছেন দীর্ঘদিন যাবত্। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সমাজে খোঁজ নেওয়া হইলে দেখা যাইবে -নজরুলের অবস্থা বিদ্যাসাগরের হইতে তাঁহার বাঙালি স্বজাতি সমাজে খুব ভালো নহে।
তবে তারপরেও রবীন্দ্রনাথের পথকে অনুসরণ করতেই হইবে- যাহারা এখনও বিদ্যাসাগর হইতে নজরুল হইয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপরিচয় হিসাবে ধারণ করেন- তাহাদের জন্যে পথ হইলো, “ ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয় বাদ্য”।
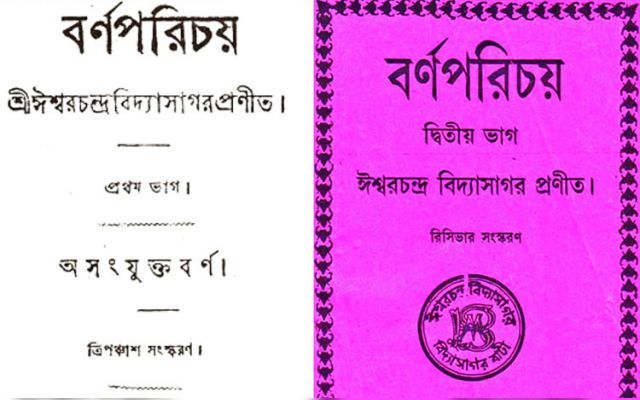
যেমন বিদ্যাসাগর যে বাল্য শিক্ষার বইকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন, শুধু নিজে লেখেননি, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, সীতানাথ বসাক সবাইকে তিনিই আপনার বক্ষে লইয়া বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। তাইতো শামসুর রাহমান ৫২ তে আসিয়া লিখিয়াছিলেন,
“ কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলি শৈশবে ‘ পাখি সব করে রব’ বলে মদনমোহন
তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। ….’
ক্ষুদ্র চেষ্টা ও অভিজ্ঞতা শেষে এ তৃণভূমিতে এ সত্য বুঝিয়াছি, সহসা কেহই শিশু শিক্ষা বা বাল্যশিক্ষার বইয়ের যে অভাব বিদ্যাসাগর দূর করিবার পথে নামিয়াছিলেন – এই পথে রাষ্ট্র ও সমাজকে চালিত করিবেন না। তবে যাহাদের ভগ্ন ঢাক আছে তাহারা আগাইয়া আসিয়া যথাসাধ্য জয়বাদ্য বাজাইতে পারেন। যেমন তরুণ প্রকাশক রবীন আহসানকে দেখিয়াছি, তিনি ৫০ হাজার সুকুমার রায় রচনাবলী প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে শিশুদের মধ্য দিয়াছেন। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনেকে আগাইয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মবার্ষিকীতে তিনি বা তাঁহার মতো যাঁহারা আছেন, তাঁহারা শিশু শিক্ষার জন্য ‘প্রথমভাগ’ ‘দ্বিতীয় ভাগ’ লইয়া এমন উদ্যোগ লইতে পারেন। কারণ যাহারা এ ভূমি হইতে ঘাস খাইয়া যাইতেছে বার বার- তাহারা যাহাই করুক না কেন, এ ভূমি তো আমাদের। এ ভূমিতে আমাদের সন্তানরা কতকাল তৃণ থাকিবে, তাহাদের বৃহৎ বৃক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা যে কোন স্থান হইতে শুরু হইতে পারে। আর প্রকৃত অর্থে, ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, আমরা ভক্তি করি না -পূজা করি- বিদ্যাসাগর দেবতা নন, তিনি মর্তের মানুষ- তাহাকে পূজা করিয়া দায় সারিবার কাজটি সঠিক নয়। বরং ভক্তি করিয়া তাহার কাজকে কাজে লাগাইলেই তাহার মাধ্যমেই তাহার সংগ্রাম ও আদর্শকে আগাইয়া নেওয়া হইবে। মনে রাখিতে হইবে তাহার হাত ধরিয়া বাংলা ভাষার নবজন্ম ঘটিয়াছে- আর বাঙালির রাষ্ট্রটি সৃষ্টির সঙ্গে ভাষা অনেক বেশি মিশিয়া আছে।
লেখক: সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সম্পাদক, সারাক্ষণ, The Present World.


 স্বদেশ রায়
স্বদেশ রায়