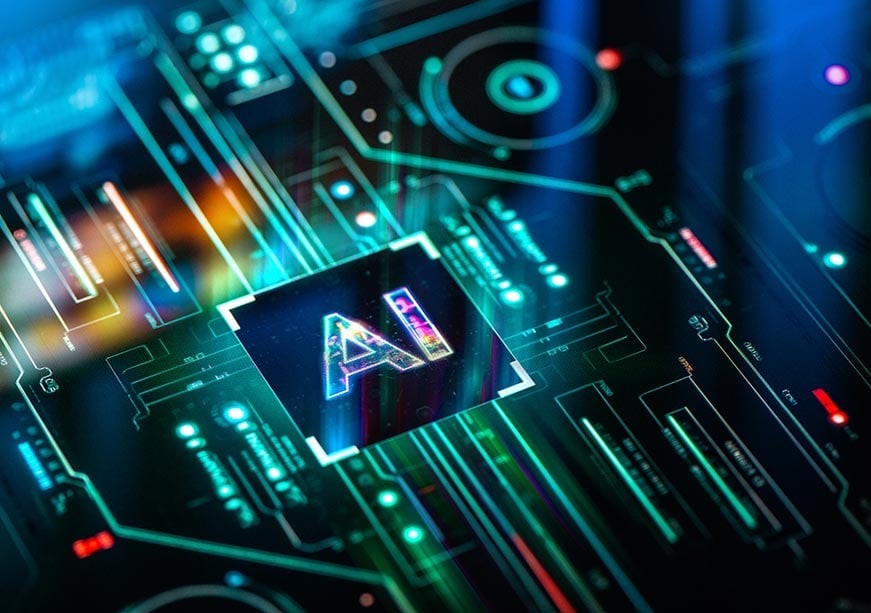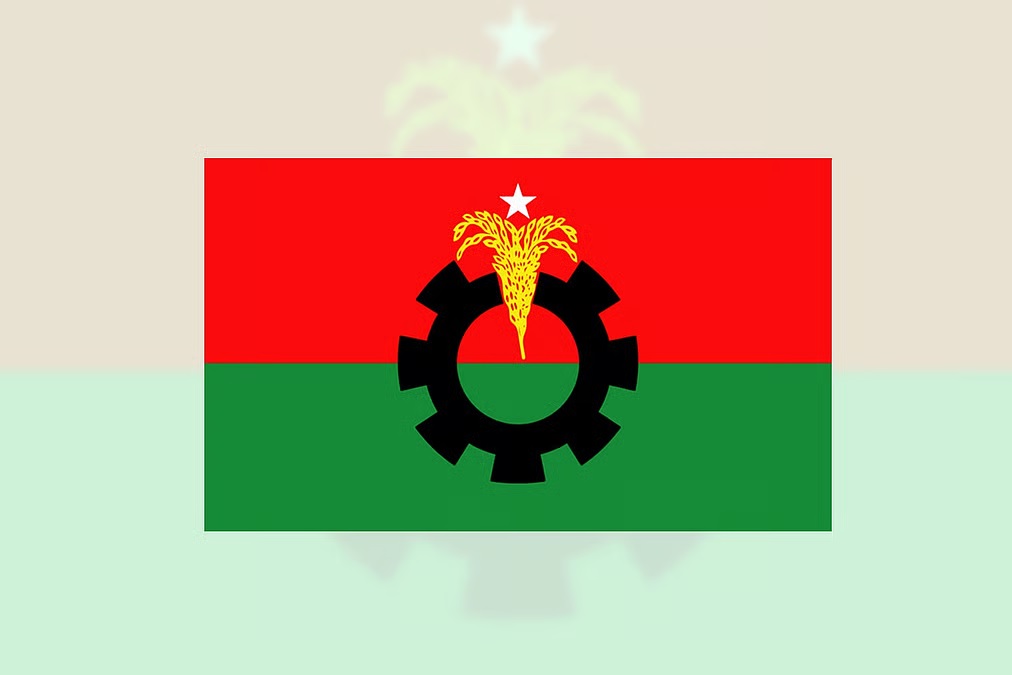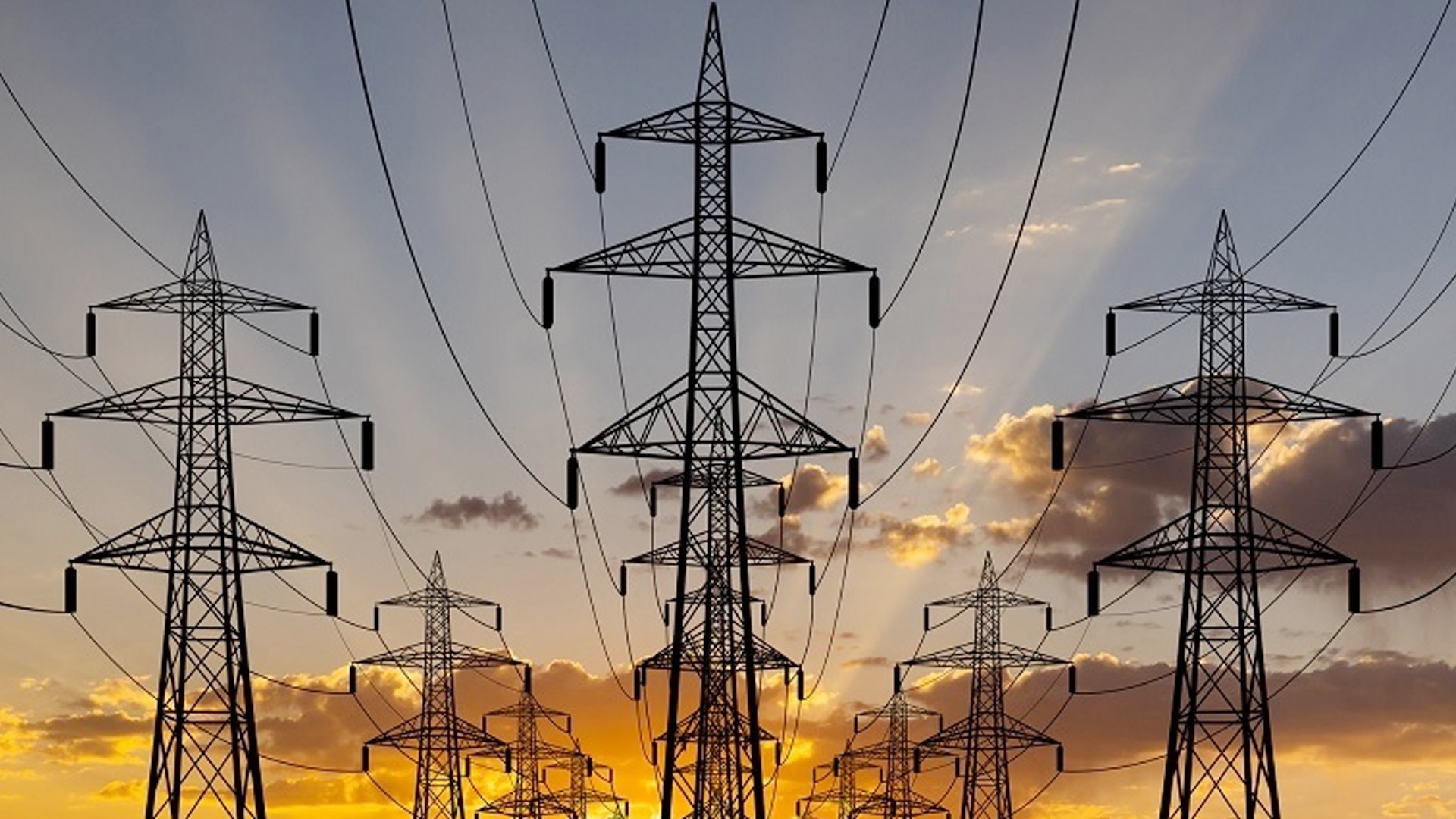বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ধরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করেছে। মেগা প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাজেট ঘাটতি পূরণে আন্তর্জাতিক ঋণ হয়ে উঠেছে প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সাম্প্রতিক কড়াকড়ি দেখাচ্ছে—এই মডেল আর আগের মতো কার্যকর নয়। আইএমএফ এবার বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে সুনির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিয়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কঠিন বাস্তবতার ইঙ্গিত বহন করছে।
নতুন শর্তের কাঠামো
আইএমএফ জানিয়েছে, বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ আট দশমিক চার চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ নিতে পারবে। এর মধ্যে প্রথম তিন মাসে সর্বোচ্চ এক দশমিক নয় এক বিলিয়ন এবং অর্থবছরের প্রথমার্ধে সর্বোচ্চ তিন দশমিক তিন চার বিলিয়ন ডলারের সীমা থাকবে। অর্থাৎ ঋণ ব্যবস্থাপনা এখন থেকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে সংস্থাটি।
মূল উদ্দেশ্য হলো ঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং দেশের অর্থনীতিকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই পথে আনা।

কেন আইএমএফ কঠোর হলো
আইএমএফ প্রথমে বাংলাদেশকে চার দশমিক সাত বিলিয়ন ডলারের প্রোগ্রাম দিয়েছিল। পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন। কিন্তু সর্বশেষ ঋণ টেকসইতার বিশ্লেষণে দেখা গেছে—বাংলাদেশ আর ‘কম ঝুঁকি’র পর্যায়ে নেই, বরং ধারাবাহিকভাবে ‘মধ্যম ঝুঁকি’র তালিকায়।
গত অর্থবছরে ঋণ-রফতানি অনুপাত দাঁড়িয়েছে একশো বাষট্টি শতাংশের বেশি, যেখানে অনুমান ছিল সর্বোচ্চ একশো আঠারো শতাংশ। একইভাবে ঋণ-রাজস্ব অনুপাতেও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে। আইএমএফ বলছে, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ঋণ টেকসইতার ঝুঁকি আরও বাড়বে।
বৈদেশিক ঋণের বর্তমান চিত্র
বাংলাদেশের ইতিহাসে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ এখন সর্বোচ্চ।
- সর্বশেষ হিসাবে ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় একশো বারো বিলিয়ন ডলারে।
- স্থানীয় মুদ্রায় এর অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় তেরো লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা।
- এক দশক আগে ঋণের পরিমাণ ছিল বিশ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি; অর্থাৎ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতামত
অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

- অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান (সিপিডি): “প্রকল্পগুলো কঠোরভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি ঋণের ব্যবহার সুশাসন ছাড়া সম্ভব নয়।”
- ড. জাহিদ হোসেন (সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক ঢাকা): “ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার না হলে ভবিষ্যতে এটি বড় বোঝায় পরিণত হবে।”
- ড. সেলিম রায়হান (সানেম): “রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বল আর্থিক শৃঙ্খলা আইএমএফকে কড়াকড়ি আরোপে বাধ্য করেছে।”
- ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক): “বর্তমানে হাতে যে ডলার আছে, তা আপৎকালীন সময়ের জন্য যথেষ্ট নয়। ঋণের পরিবর্তে নিজস্ব আয়ের ভিত্তি বাড়ানো জরুরি।”
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও তুলনা
শ্রীলঙ্কা
শ্রীলঙ্কা দীর্ঘদিন বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করেছে। অবশেষে দেশটি ঋণ খেলাপি হয়, কারণ রিজার্ভ ফুরিয়ে যায় এবং ঋণ-রফতানি অনুপাত অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এরপর আইএমএফ থেকে বেইলআউট প্যাকেজ নেয় দেশটি, যার শর্তে সরকারি ব্যয় হ্রাস, কর বৃদ্ধি এবং মুদ্রানীতি কড়াকড়ি করা হয়।
পাকিস্তান
পাকিস্তানও আইএমএফ থেকে জরুরি ঋণ নিয়েছে। শর্ত ছিল ভর্তুকি কমানো, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো এবং কর সংগ্রহ বাড়ানো। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বল রাজস্ব কাঠামোর কারণে দেশটি বারবার শর্তপূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।
ভিয়েতনাম ও ভারত
অন্যদিকে ভিয়েতনাম ও ভারত ঋণনির্ভরতা কমিয়েছে। রাজস্ব আহরণ বাড়ানো, রফতানি বৈচিত্র্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ টেনে এনে তারা ঋণ টেকসইতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।
বাংলাদেশের শিক্ষা: প্রতিবেশী দেশগুলোর অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে—ঋণ সঠিকভাবে কাজে না লাগলে তা সংকটে পরিণত হয়। আর সঠিকভাবে ব্যবহার করলে প্রবৃদ্ধি বাড়ে।

নন-কনসেশনাল ঋণের উদ্বেগ
সম্প্রতি বাংলাদেশ যে ঋণ অনুমোদন দিয়েছে তার বেশিরভাগই “নন-কনসেশনাল”— অর্থাৎ বাজারভিত্তিক সুদে। যেমন:
- এডিবি থেকে ছয়শো ঊনপঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার
- ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে দুইশো একচল্লিশ মিলিয়ন ডলার
- এআইআইবি থেকে চারশো মিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা
- ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে দুটি পানি প্রকল্পে একশো ষাট মিলিয়ন ইউরো
এসব ঋণে ভর্তুকি কার্যত নেই বললেই চলে। ফলে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যাবে এবং পরিশোধের চাপ আরও তীব্র হবে।
রিজার্ভ ও রেমিট্যান্স
রিজার্ভ কিছুটা বেড়েছে—
- আইএমএফের হিসাবে প্রায় ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার
- বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে একত্রিশ বিলিয়নের বেশি
প্রবাসী আয়ও বাড়ছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকেই এসেছে দুই বিলিয়নের বেশি ডলার, যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। তবে বিনিয়োগ খাত স্থবির হয়ে পড়ায় এর ইতিবাচক প্রভাব সীমিত।
সামনের চ্যালেঞ্জ
ঋণনির্ভরতা কমানো
রাজস্ব আহরণ বাড়াতে হবে। বর্তমানে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম।
রফতানির বৈচিত্র্য
তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আইটি, ফার্মাসিউটিক্যালস, কৃষি ও হালকা প্রকৌশল খাতে প্রবৃদ্ধি আনতে হবে।
বিনিয়োগ টানা
বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতির স্বচ্ছতা ও কর কাঠামো সংস্কার ছাড়া বিনিয়োগকারীরা আসবে না।

সুশাসন নিশ্চিত করা
মেগা প্রকল্পে দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ না করলে ঋণের চাপ আরও বাড়বে।
আইএমএফের নতুন শর্ত কেবল একটি সীমাবদ্ধতা নয়—এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার কঠিন বার্তা। বৈদেশিক ঋণনির্ভর উন্নয়ন মডেল এখন প্রশ্নবিদ্ধ। সামনের দিনে যদি সরকার নিজস্ব আয় বাড়াতে না পারে, তবে বৈদেশিক ঋণ আর ভরসা হবে না—বরং হয়ে উঠতে পারে নতুন সংকটের উৎস।
প্রতিবেশী দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বলছে—ঋণ টেকসইতা বজায় রাখতে হলে রাজস্ব সংগ্রহ, রফতানি বৈচিত্র্য এবং সুশাসন ছাড়া বিকল্প নেই। বাংলাদেশ কি সময়ের এই সতর্ক বার্তাকে কাজে লাগাতে পারবে? সেটিই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট