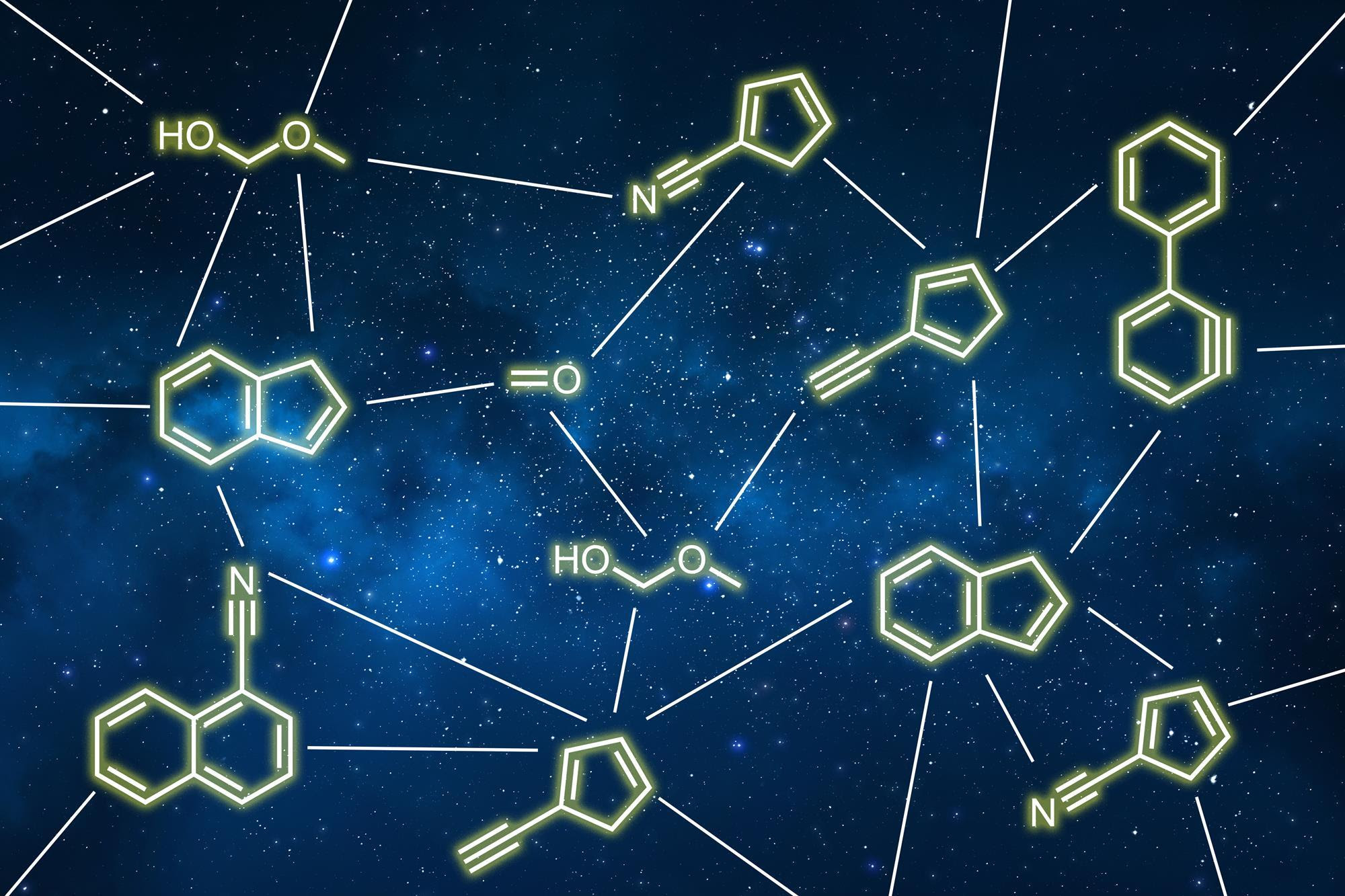আমেরিকায় ওষুধের দাম কেন এত বেশি?
আমেরিকানদের কাছে সবচেয়ে বড় ক্ষোভের একটি হলো ওষুধের দাম। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয়েই মনে করেন, অসুস্থ রোগীদের কাছ থেকে মুনাফার লোভে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো। যুক্তরাষ্ট্রে ব্র্যান্ডেড ওষুধের দাম অন্যান্য ধনী দেশের তুলনায় গড়ে চার গুণ বেশি।
ডোনাল্ড ট্রাম্পও এই সমালোচনার সঙ্গে একমত। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, ওষুধ কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করা হবে তাদের দাম “সর্বনিম্ন দেশের দামের সমান” করতে। যদি তা না হয়, তবে “সব ধরনের উপায়” ব্যবহার করে তিনি দাম কমাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি এবং এটি উল্টো আমেরিকার স্বাস্থ্যসেবাকে আরও খারাপ করতে পারে।
আসল মুনাফা কার হাতে যাচ্ছে?
আমেরিকার জটিল স্বাস্থ্যসেবায় অদক্ষতা ও বাড়তি ব্যয়ের মূল উৎস ওষুধ কোম্পানি নয়। বরং এর বড় অংশ জমা হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের অন্য অংশে—হাসপাতাল, বীমা কোম্পানি, ওষুধ সরবরাহকারী, এবং “ফার্মেসি বেনিফিট ম্যানেজার” (PBMs)-এর হাতে।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্যসেবার তালিকাভুক্ত ২২০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফার তিন ভাগের দুই ভাগ নিয়েছে এই মধ্যস্বত্বভোগীরা। তিনটি PBM প্রতিষ্ঠানই গত বছর প্রায় ৮০% প্রেসক্রিপশন দাবি নিয়ন্ত্রণ করেছে, যাদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক প্রতিযোগিতার অভিযোগ তদন্তাধীন।
কেন আমেরিকানরা বেশি দাম দেয়?
ইউরোপীয় দেশগুলো জাতীয় পর্যায়ে ওষুধ কিনে থাকে এবং মূল্য নির্ধারণ করে রোগীর আয়ুষ্কাল ও জীবনমান কতটা বাড়াবে তার ভিত্তিতে। ফলে অনেক ওষুধ ইউরোপ বা জাপানে অনুমোদনই পায় না, কিংবা অনেক দেরিতে আসে।
২০১৪ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে আমেরিকায় অনুমোদিত পাঁচটির মধ্যে একটি ওষুধ ইউরোপে কখনো অনুমোদন পায়নি, আর প্রায় অর্ধেক ওষুধ জাপানে অনুমোদিত হয়নি। যেসব ওষুধ তিন জায়গাতেই অনুমোদিত হয়েছে, তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ আগে অনুমোদন পেয়েছে আমেরিকায়—গড়ে ইউরোপের চেয়ে ছয় মাস এবং জাপানের চেয়ে প্রায় তিন বছর আগে।
অর্থাৎ, আমেরিকানরা বেশি দাম দিলেও নতুন ওষুধের প্রাপ্যতায় তারা এগিয়ে থাকে।
ট্রাম্পের পরিকল্পনার সম্ভাব্য বিপদ
ট্রাম্প চাইছেন অন্য দেশের দামের সঙ্গে আমেরিকার দাম সমান করতে। কিন্তু এর মানে দাঁড়ায় ইউরোপ বা জাপানের মতো মূল্যায়ন আমেরিকায় প্রয়োগ করা, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবার মান কমিয়ে দিতে পারে।

তাছাড়া, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো দাম বাড়িয়ে বিপুল মুনাফা করছে—এমন ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। নতুন ওষুধ উদ্ভাবনে ঝুঁকি নিতে হয়, আর প্রায় ৯০% গবেষণা ব্যর্থ হয়। যদি মুনাফা কমে যায়, তবে ঝুঁকি নেওয়ার আগ্রহও কমে যাবে।
ফলে তারা হয়তো নতুন ওষুধ উদ্ভাবনে কম বিনিয়োগ করবে, কিংবা অন্য দেশে ওষুধ ছাড়ার সময় আরও দেরি করবে যাতে দাম সর্বনিম্ন স্তরে না নেমে যায়। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব পড়বে রোগীদের ওপরই।
বিকল্প সমাধান কী হতে পারে?
বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপের দামের কপি না করে তাদের পদ্ধতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ইউরোপে ওষুধের দাম নির্ধারণ হয় এর কার্যকারিতা ও রোগীর জীবনের মান উন্নত করার ওপর ভিত্তি করে।
আমেরিকায়ও কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:
- মেডিকেয়ার এখন কয়েকটি ওষুধের দাম নিয়ে সরাসরি আলোচনা করতে পারে।
- মেডিকেইড ব্যয়বহুল জিন থেরাপির জন্য রোগীর ফলাফলের সঙ্গে অর্থ প্রদানের শর্ত যুক্ত করছে।

যদি মূল্য-ভিত্তিক এই পদ্ধতিকে বিস্তৃত করা যায়, তবে তা স্বচ্ছতা বাড়াবে এবং উদ্ভাবনকে কার্যকর চিকিৎসার দিকে পরিচালিত করবে। এতে খরচ থাকলেও তা হবে আরও কার্যকর এবং রোগীদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী।
যদিও দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও বেশি থাকবে, তবু আমেরিকানরা উন্নত চিকিৎসা সুবিধা পাবে, যা তারা সবসময়ই চায়।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট