২১শ শতকের সংস্কৃতি নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। গানকে বলা হয় সুরহীন, কথামালাকে বলা হয় অর্থহীন। সিনেমা ভরে গেছে রিবুট, সিক্যুয়েল আর সুপারহিরোতে। একসময় টিভি নাটকে ছিল সৃজনশীল বিস্ফোরণ। আর এখন প্রতিটি ঝকঝকে নতুন শোকে বলা হয় ‘অবশ্যই দেখার মতো’, যদিও বেশিরভাগই সাধারণ মানের। অনেকে মনে করেন—অ্যালগরিদম সৃজনশীলতাকে গ্রাস করে ফেলেছে।
ডব্লিউ ডেভিড মার্কসের নতুন বই “Blank Space” এই থেমে থাকা, শব্দে ভরা শূন্যতার ব্যাখ্যা দেয়। তবে তাঁর বিশ্লেষণ যতই তীক্ষ্ণ হোক, পরিস্থিতি নিয়ে তিনি (হয়তো আপনিও) বরং অতিমাত্রায় হতাশ।
সংস্কৃতির স্থবিরতা: অভিযোগ ও তুলনা
মার্কস মূলত পপ সংস্কৃতি, ফ্যাশন, ভিজ্যুয়াল আর্ট এবং ইন্টারনেট–চালিত zeitgeist — এই বিষয়গুলোই বিশ্লেষণ করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, একসময় সমাজ নতুন শিল্প উদ্ভাবনে উৎসাহ দিত এবং তার সুযোগও তৈরি করত। কিন্তু ২০শ শতকের শুরুতে কিউবিজম–সুররিয়ালিজম কিংবা ১৯৬০ – এর দশকের প্রতিসংস্কৃতির বিস্ফোরণ আজ দেখা যায় না। বর্তমান সময়কে তিনি বলেন “একটি ফাঁকা জায়গা”— Blank Space।
অর্থের প্রভাব: বাণিজ্যিকতার কাছে শিল্পের হার
মার্কস মনে করেন, পপ সঙ্গীতে “সেলিং আউট” বলে আর কোনো ধারণাই নেই। শিল্পের মূল্য এখন নির্ধারিত হয় অর্থে, ফলে ভিন্ন ভিন্ন ঘরানা মিশে একধরনের চকচকে ‘বাজারযোগ্য’ পপ সাউন্ডে পরিণত হয়েছে।
খ্যাতি মেলে প্রতিভা দিয়ে নয়, বরং ব্যবসায়িক কৌশল ও প্রচারণা দক্ষতায়— যেমন প্যারিস হিলটন প্রজন্মের ওঠান। রিয়েলিটি টিভি এই প্রবণতাকে আরও তীব্র করেছে, যেখানে সংস্কৃতি নেমে এসেছে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণের লড়াইয়ে।
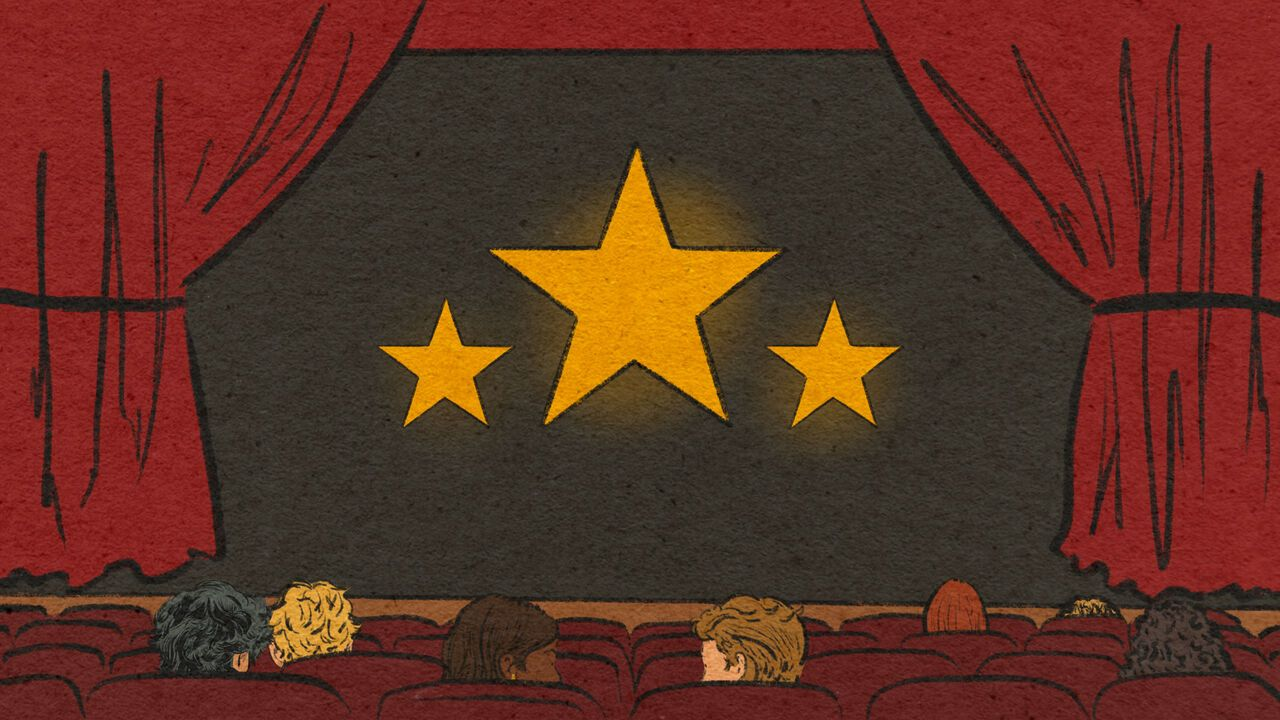
শ্রেণিবিন্যাস ও সমালোচনার সংকট
বামপন্থী চিন্তায় শ্রেণিবিন্যাসের প্রতি অনীহাও আজকের সংস্কৃতির স্থবিরতার একটি কারণ। কারও কাছে রোলিং স্টোনসকে মারায়া কেরির চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া ‘শ্বেত, পুরুষতান্ত্রিক’ পক্ষপাত হিসেবে দেখা হয়। পুরনো ধাঁচের সমালোচকদের বলা হয় এলিট বা ‘গেটকিপার’।
অন্যদিকে, নারীবাদ ও যৌনতার উন্মুক্ত আলোচনার বিপরীতে এক ধরনের বিদ্রূপাত্মক, নৈরাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, যেখানে লজ্জা বা শিষ্টাচারকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়।
প্রযুক্তি: ইন্টারনেটের উত্থান, পতন ও বিভ্রম
ইন্টারনেট শুরু হয়েছিল উৎসাহীদের খেলাঘর হিসেবে। পরে “গ্যাংনাম স্টাইল” – এর মতো ভাইরাল ঘটনা এবং নতুন প্রজন্মের তারকারা সমাজজুড়ে প্রভাব বিস্তার করে।
এরপর ২০১০ – এর দশকের শেষ দিকে এটি হয়ে ওঠে গুজব, ষড়যন্ত্র, দ্রুত অর্থ উপার্জনের ফাঁদ ও বিষাক্ত প্রচারের জায়গা।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্রূপাত্মকভাবে শান্ত— যেহেতু বেশিরভাগ মানব–সৃষ্ট শিল্পই ব্যর্থ হয়, তাহলে এআই–এর প্রভাব নিয়ে এত উদ্বেগ কেন?
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি: পুরোনো অভিযোগ, নতুন রূপ
অনেক সমালোচনা নতুন নয়— অতীতেও ‘বাজারি সংস্কৃতি’ বা সামাজিক খ্যাতির অভিযোগ ছিল। সময়ের ছাঁকনি সবসময় সেরা জিনিসগুলো রেখে দেয়— হলিউডের ক্লাসিকগুলো থাকে, বি–মুভিগুলো হারিয়ে যায়; জয়েস – ফিৎসজেরাল্ড টিকে থাকেন, সস্তা পাল্প ফিকশন মিলিয়ে যায়।
ডিজিটাল স্রোতের ভেতর এখনই বলা কঠিন কোন সৃষ্টিই বা দীর্ঘমেয়াদে মূল্যবান হবে।

রেট্রোম্যানিয়া: সব পুনরাবৃত্তিই কি খারাপ?
পুরোনো ধারণার পুনরাবৃত্তি সত্যিই সৃজনশীল সংকটের ইঙ্গিত দেয়। তবে মার্কস যখন বলেন যে বিটলসের দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা সংস্কৃতির স্থবিরতার পরিচয়, তখন তিনি ভুল করেন।
কিছু শিল্প অন্যগুলোর তুলনায় সত্যিই ভালো— যেমন The Wire – এর তুলনায় Emily in Paris।
যেমন ১৯৬০ – এর রক’এন’রোল বা ভিক্টোরিয়ান উপন্যাস আজও অতুলনীয়। পুরোনো শিল্পকর্ম সহজলভ্য হওয়াই আধুনিক সংস্কৃতির সৌন্দর্য— তা কোনো ত্রুটি নয়।
শান্ত সময়ের সংস্কৃতি: আরাম ও পুনরাবৃত্তির গল্প
২১শ শতকের ক্ষুদ্র ভিন্নতা, পুনরাবৃত্তি ও আত্মতুষ্টি তুলনামূলক শান্ত সময়ের প্রতিচ্ছবি হতে পারে। বড় রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপর্যয়ই প্রায়শই শিল্পকে নতুন রূপ দিয়েছে— যেমন ২০শ শতকের শুরুতে হয়েছিল।
আজকের শিল্পীরা কি একই মাত্রার সৃজনশীল ঝাঁকুনি দিতে পারতেন? বরং আশা করা যায় — সেই পরীক্ষা আমাদের সামনে না আসুক।
#সংস্কৃতি #সৃজনশীলতা #বইপর্যালোচনা #সমসাময়িকশিল্প #২১শ_শতক

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট 



















