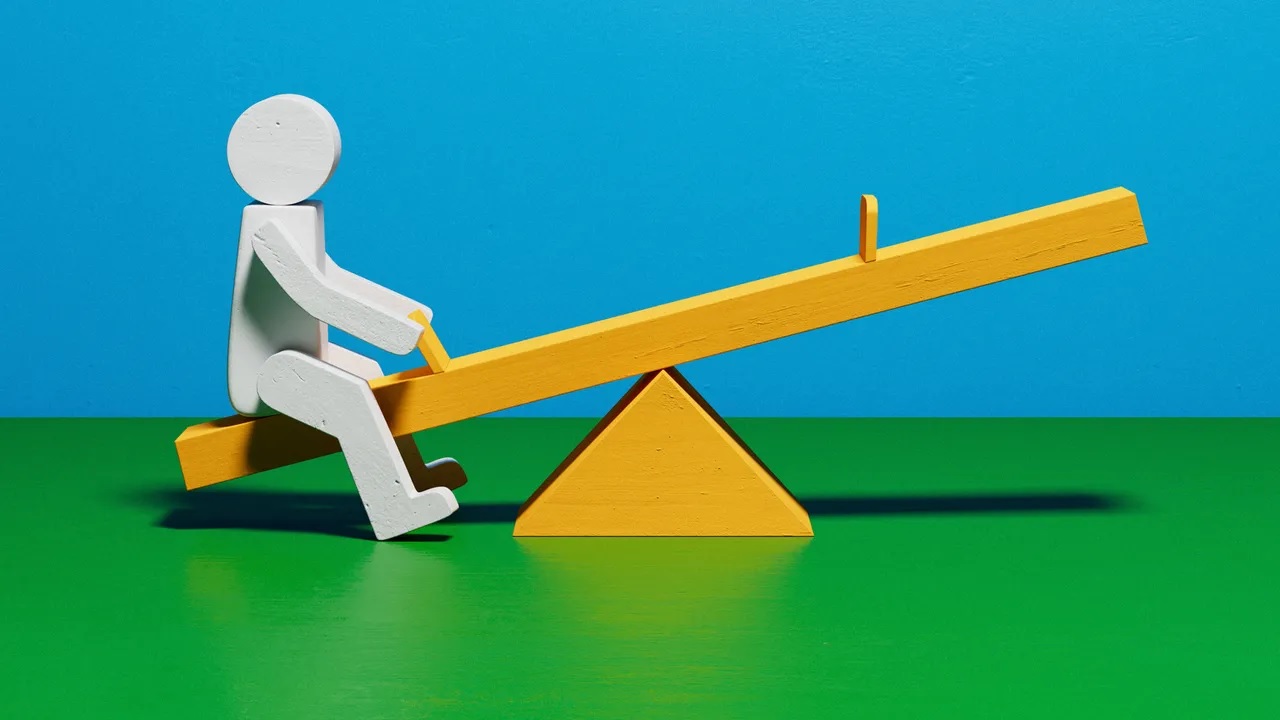আমাদের সময়ের শিশুরা যেন খনির ভেতর ক্যানারি পাখির মতো—সমাজের বিষাক্ততা প্রথমে তাদেরই ছুঁয়ে যায়। সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে ৯ থেকে ১৬ বছর বয়সী একের পর এক শিশুর আত্মহত্যার ঘটনা তাই আমাদের বাধ্য করছে স্কুলকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে। এই লেখা বিদ্যালয়কে দোষারোপ নয়—বরং কঠিন এক সত্যের সামনে দাঁড় করায়: আমরা কি সত্যিই শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি?
শৃঙ্খলার নামে নির্যাতন, লেবেল আর লজ্জার ভারে ভেঙে পড়া শিশুরা
অনেক স্কুলে “ডিসিপ্লিন” মানে হচ্ছে অপমান আর শাস্তির বুনো সংস্কৃতি। ছোট্ট বয়স থেকেই বাচ্চারা শুনতে পায়—‘লেজি’, ‘ডাফার’, ‘ফেলিওর’, ‘পাগল’, ‘স্লো’, ‘গুড ফর নাথিং’।
যাদের লক্ষ্য করা হয় সবচেয়ে বেশি, তারা সাধারণত সমাজের সবচেয়ে ভঙ্গুর—দৃষ্টিগোচর বা অদৃশ্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন শিশু, কম নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থী, আর নিম্ন-আয়ের বা নন-সাভর্না পরিবারের সন্তানরা।
ভয়াবহ সব কাহিনি ভেসে আসে—অন্ধকার বাথরুমে আটকে রাখা, টিফিন কেড়ে নেওয়া, বাথরুমে যেতে না দিয়ে ভিজিয়ে ফেলা পর্যন্ত বাধ্য করা।
সংবাদে আসে আরও নির্মম উদাহরণ—শতবার উঠবস করিয়ে অজ্ঞান করা, গরম লোহার দাগ, রোদের তাপে দাঁড় করিয়ে রাখা, টয়লেট পরিষ্কার করানো, বা ক্লাসে পুরো অপমানজনক শাস্তি।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, শাস্তির এই সংস্কৃতি অস্ত্র বানিয়ে ফেলে ঠিক সেই মানুষদের—যাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ছিল: সহপাঠী ও অভিভাবকদের।
সোনার ঘটনাটি যেমন—শেল্টার হোমে থাকা এই মেয়েটির খাতা শিক্ষকই ছিঁড়ে ফেললেন, তাকে “ডাফার” বললেন, অন্য বাচ্চাদেরও হাসাহাসি করতে উসকে দিলেন।
আনন্দকে ক্লাসে জোর করে প্যান্ট খুলতে বাধ্য করা হলো; সে কাঁদতেই পুরো ক্লাস তাকে নিয়ে উল্লাস করল।
শহানা, দশম শ্রেণির ছাত্রী, সংক্ষেপে বলে—“স্কুলগুলো হাঙ্গার গেমসের মতো। আমাদের একে অন্যের বিরুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়।”
অভিভাবকদেরও এই খেলায় নামানো হয়—বারবার অভিযোগ, অপমান, প্রিন্সিপালের রুমে লজ্জা—যা শেষ পর্যন্ত বাচ্চার ওপরই ফিরে আসে।
কোনো শিশু হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত নেয় না যে সে বাঁচতে চায় না। তারা ধরে থাকে ভালোবাসার ঘর, স্কুলে belonging, আত্মমর্যাদা আর নিজের জীবনে ভূমিকা আছে এই বিশ্বাসের মতো সূক্ষ্ম সুতোয়।
যখন এসব সুতো একের পর এক ছিঁড়ে যায়—থেকে যায় লজ্জা, একাকিত্ব আর আশা-হীনতা। তখন ক্ষুদ্র একটি ধাক্কাও হতে পারে শেষ সীমা।
অনেকে বলে—“এখনকার বাচ্চারা খুব নাজুক।”
কিন্তু সত্য হলো—বিষাক্ত পরিবেশের দায় শিশুদের নয়। সমস্যাটা কাঠামোর, ব্যবস্থার, আর সেই সংস্কৃতির যা সহিংসতাকে স্বাভাবিক করে দিয়েছে।

নিরাপদ স্কুল গড়তে লাগে বোঝাপড়া, জবাবদিহি, আর একসঙ্গে হাঁটার মন
শিশুর জীবন রক্ষা মানবাধিকার—এটাই প্রথম নীতি হওয়া উচিত।
শিক্ষাকে সাজাতে হবে নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে—ফলাফল, সিলেবাস, পারফরম্যান্স এগুলো পরে আসবে।
ভারতের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বলছে পাঁচটি ভিত্তি—অ্যাক্সেস, ইকুইটি, কোয়ালিটি, অ্যাফোর্ডেবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি।
কিন্তু প্রশ্ন হলো—এর মাঝখানে শিশুর মর্যাদা কি সত্যিকারের অঙ্গীকার হিসেবে আছে?
মর্যাদা যদি কেন্দ্র হয়, তবে চাই বাস্তব নির্দেশিকা—
কীভাবে কথা বলা হবে, কীভাবে সম্মান দেখানো হবে, কঠিন সময়ে কীভাবে পাশে দাঁড়ানো হবে, কীভাবে ইনক্লুসিভ ক্লাসরুম তৈরি হবে।
অনেকে ভাবতে পারে—এতে তো আরও সময়, আরও সম্পদ লাগবে।
কিন্তু নীতি একটাই—আগে নিরাপত্তা, পরে শিক্ষা।

জবাবদিহির জায়গায় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শিক্ষক দেখেন সহকর্মীদের নিষ্ঠুর আচরণ, কিন্তু ভয় বা চাকরি হারানোর আতঙ্কে কিছু বলেন না।
শুধু শাস্তি দিয়ে শিক্ষক বদলানো যাবে না—তাতে সহিংসতার সংস্কৃতি আরও পোক্ত হয়।
বরং দরকার সহমর্মিতার প্রশিক্ষণ, দ্রুত ন্যায়সঙ্গত প্রতিক্রিয়া, আর এমন এক কাঠামো যা শিক্ষককেও যত্ন করে।
যে স্কুল শিক্ষককে যত্ন করে—সেই স্কুলই শেষ পর্যন্ত শিশুকে রক্ষা করে।
পিয়ার মেন্টরিং হতে পারে আরও একটি শক্তিশালী উপায়।
অনেক সময় শিশুরা তাদের বয়সী আরেকজনের কাছে মন খুলে বলতে পারে বেশি।
প্রশিক্ষিত সিনিয়র শিক্ষার্থীরা হতে পারে সেই নিরাপদ জায়গা—যারা বিচারহীনভাবে শুনবে, প্রয়োজন হলে বিশ্বস্ত বড়দের কাছে পথ দেখাবে।

সবশেষে, যখন কিশোর-কিশোরীদের জিজ্ঞেস করা হয়—“নিরাপদ স্কুল কেমন?”
তাদের উত্তর সরল, অথচ গভীর—
“আমাদের মূল্যকে শুধু গ্রেডে মেপো না।”
“দেখাও যে তুমি সত্যিই কেয়ার করো।”
তারা চায়—বোঝাপড়া, কৌতূহল, পাশে হাঁটার মন।
এক তরুণের কথাটি আজও আমাদের কানে বাজে—
“আমাদের থামাতে চাইবে না, আগে আমাদের বুঝতে চেষ্টা করো। যখন বুঝবে—তখন একসাথে আমরা নিজেদের থামাতে পারব।”
এই বোঝাপড়ার দিকেই শুরু হয় ‘নিরাপদ স্কুল’-এর পথচলা।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট