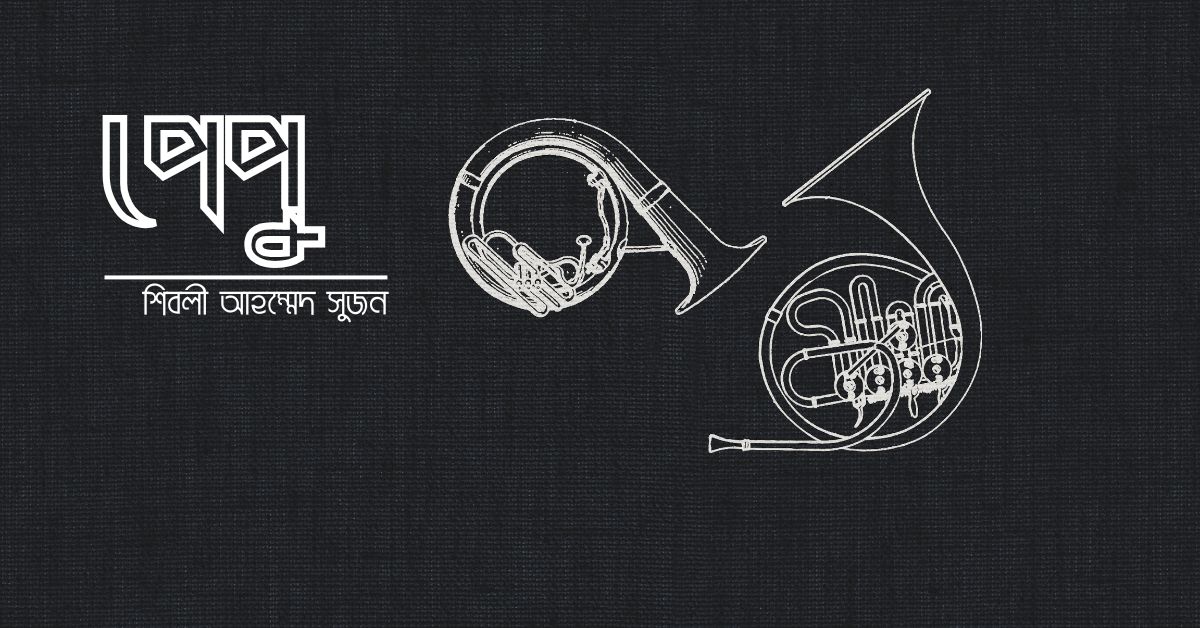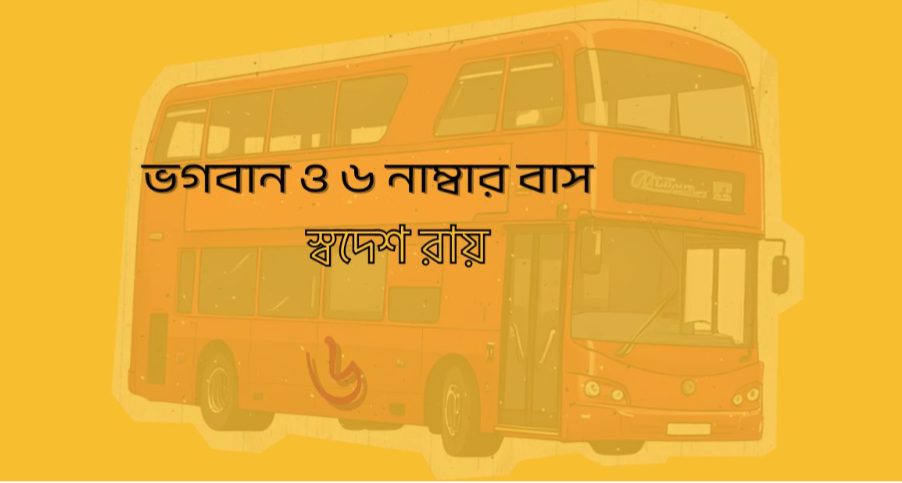শশাঙ্ক মণ্ডল
শিল্প-বাণিজ্য
তৃতীয় অধ্যায়
ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে আমাদের দেশে বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে গ্রামীণ সমাজ ছিল তার কুটিরশিল্পীরা নিজেদের ঘরে বসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কুটিরশিল্পের পণ্য তৈরি করত। মাল বাজারে আসত নানা হাত ঘুরে-এরা ছিল বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ফড়ে পাইকার বণিক। শেষ পর্যন্ত এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করত বড় বড় ব্যবসায়ীরা। কুটির শিল্পের পাশাপাশি কৃষিজাত পণ্যাদি বাজারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল। কৃষির ক্ষেত্রেও মূলধন আগাম হিসাবে অথবা ঋণের ছদ্মবেশে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রবেশ করছিল।
অভাবের সময় চাষীকে ধার পাবার জন্য মহাজনদের নিকট হাত পাততে হত এবং ফসল উঠলে সুদ সমেত ঋণ শোধ দিতে হত। ফসল ওঠার সময় শস্যের দাম পড়ে যেত। ধানের সুদ বাবদ বাড়ি আদায় করা হত এবং অনেক সময় তা আসলের তিনগুণ হয়ে যেত। এক বস্তা ধান খঋণ নিলে ফসলের সময় সুদে আসলে তিনবস্তা দিয়ে তা শোধ করতে হত। সুতরাং সুদের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে ২০০% এর মতো গিয়ে দাড়াত (১)। গ্রামের সাধারণ কৃষক ঋণজালে জড়িয়ে পড়ত। কৃষি-অর্থনীতি ছিল সমাজের চালিকা শক্তি।
অবস্থাপন্ন চাষীরা ফসল ওঠার সময় ধান, গুড়, সরষে প্রভৃতি সস্তায় কিনে রাখত। পরে দাম বাড়লে বিক্রয় করত। এদের মূলধন খুব বেশি হলে বছরে দুবার তিনবার আবর্তিত হত। (খ) অন্যদিকে পাইকাররা বছরে ৩ বার থেকে ৮ বার মূলধনকে আবর্তিত করতে পারত। এই গৃহস্থ ব্যাপারীরা গ্রামের মোড়ল। এরা অভাবের সময় চাষিকে দাদন বা বাড়ি দিত। পরে ফসল উঠলে সুদ সমেত তা আদায় করে নিত। তার ফলে উৎপন্ন শস্যের একটা বড় অংশ খামারেই বিক্রি হয়ে যেত। বুকানিন হ্যামিলটনও বলেছেন ধনী চাষিরা এভাবে বিপুল টাকা আগাম লগ্নী করত কৃষিতে এবং শতকরা ২৫ ভাগ লাভ করত।
নিজের উদ্যোগে মূলধন নিয়োগ করে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কারখানার পণ্য উৎপাদন করার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের কোনও আগ্রহ ছিল না বা কোন রেওয়াজ ছিল না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূলধন বিনিয়োগ করে পরিবর্তন ঘটানোর কোন চেষ্টা হয়নি। কেবল বাজারের চাহিদা ও যোগানের খেলা; দামের উঠানামায় কৃষি-অর্থনীতি জড়িয়ে পড়েছিল এবং এখনও তার চিহ্ন লক্ষ করা যাবে। পাইকার ছিল দাবার গুটি প্রকৃষ্পক্ষে বড় ব্যবসায়ীরা পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করত; নৌকার মালিকানা তাদের হাতে ছিল।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report