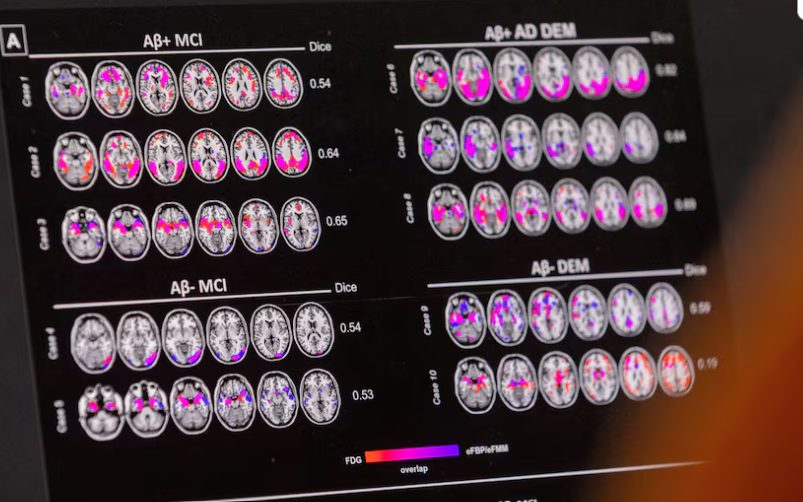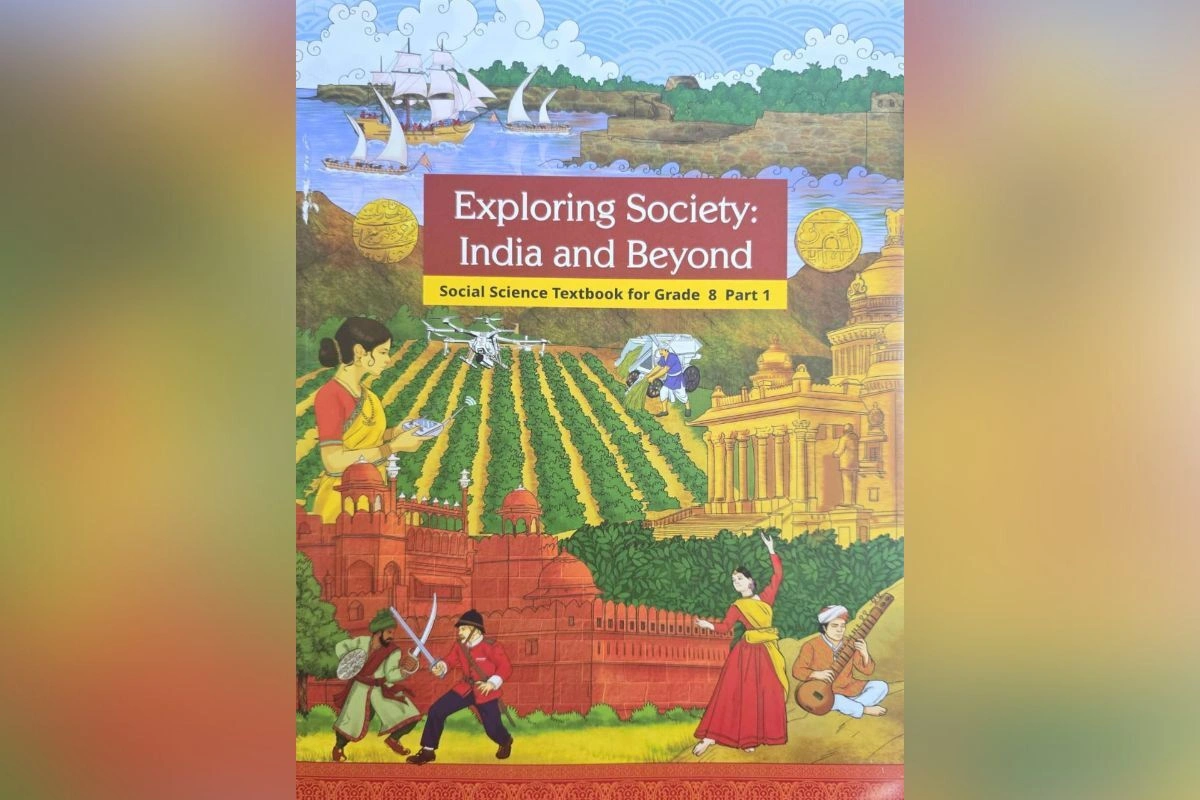শশাঙ্ক মণ্ডল
সাহিত্য
পঞ্চম অধ্যায়
পরবর্তীকালের ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের শিক্ষার অহমিকা প্রকাশ করতে গিয়ে সগর্বে ঘোষণা করতেন ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শিখিনি। পণ্ডিতমশাই ফসল উঠলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রদের বেতন বাবদ ধান সংগ্রহ করতেন। এই ধান সংগ্রহ করাটা ছিল অনেক কঠিন কাজ। সারা বছর ছাত্র পড়ানোর পর ধান কম দেবার সময় অনেকে কম দেবার চেষ্টা করত।
পাঠশালার শিক্ষার ব্যাপারে জমিদার বা সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকম সাহায্য করার রীতি ছিল না। গ্রামের মানুষেরা নিজেদের উদ্যোগে এ কাজ করতেন। সুতরাং শিক্ষকের জীবন ছিল দৈন্যপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্থ। পূজাপার্বণে উৎসবে নানাধরনের উপহার পেতেন পণ্ডিতমশাইরা। উপহারের মধ্যে কাপড় থেকে শুরু করে রান্নার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকে গুড় নারকেল অনেক কিছুই হতে পারত। সব কিছু মিলিয়ে গুরুমশাইদের বেতন মাসিক দু টাকা থেকে তিন টাকা ছিল। এ্যডমস্ সাহেব তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের এসব শিক্ষকরা যে বেতন পেতেন তা কলকাতার গৃহভৃত্যদের বেতনের চাইতেও কম।(১) স্বভাবতই এই গুরুগিরিতে আসতেন অর্ধশিক্ষিত অনেকক্ষেত্রে কিছু সহায়-সম্বলহীন মানুষ।
দীর্ঘকাল ধরে বর্ণশাসনের নিয়মানুযায়ী কায়স্থ বা করণিকরা লেখাপড়া শেখানো হিসাব নিকাশের কাজ করত। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ক্ষত্রিয়রা এই কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। পাঠশালার শিক্ষকদের অধিকাংশ হিন্দুসমাজ অন্তর্ভুক্ত কায়স্থ ছাড়াও অন্যান্য বর্ণের মানুষ। বছরে সবসময় পাঠশালার কাজ চলত না। পাঠশালার নিজস্ব ঘর না থাকায় বর্ষাকাল থেকে শুরু করে শীতকাল পর্যন্ত পাঠশালা বন্ধ থাকত-অনেকটা মরশুমি ব্যবস্থা; শীতের শেষে ফাল্গুণ চৈত্র মাস থেকে আবার পঠন পাঠন শুরু হত বর্ষাকাল এলে আবার পাঠশালা বন্ধ ‘চৈতে গুরুর মৈতে শিষ্য’ প্রবাদটির উৎস লুকিয়ে আছে এখানে। ছাত্ররা তালপাতার ওপর গাঢ় কালির লেখা দাগের ওপর কঞ্চির কলম দিয়ে লেখা অভ্যাস করত।
কালি ছিল সেদিন হাতে তৈরি, সীমের পাতার রস ও হাড়ির তলার কালি মিশিয়ে একধরনের কালো কালি তৈরি করা হত। সে যুগে অন্যভাবেও কালি তৈরি করা হত; এ কালি দিয়ে পুঁথি লেখার কাজ চলত; অনেক সময় বালির ওপরেও লেখা অভ্যাসের কাজ চলতো। পাঠশালায় সর্দার পড়োদের একটা বড় ভূমিকা থাকত বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে পঠন পাঠনে শিক্ষক মশাইকে সাহায্য করা, পাঠশালার ছুটির আগে সকল ছাত্রকে নিয়ে ডাক পড়ানোর ব্যাপারে এরা উদ্যোগী হত এবং পরিচালনা করত। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে প্রাধান্য পেত লিখতে শেখা এবং পড়তে শেখা।
এ ছাড়া প্রাথমিক জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করা। অঙ্কের প্রাথমিক নিয়ম, যোগ-বিয়োগ, গুন-ভাগ পাঠশালায় শেখানো হত। ধারাপাত মানসাঙ্ক, ২০ পর্যন্ত নামতা, শুভঙ্করের আর্যা, ক্ষেত্রফল, কাঠাকালি, খনার বচন, মণ-সের-টাকাপয়সার হিসাব শেখানো হত। লিখিত পুঁথির কোন প্রচলন পাঠশালার ক্ষেত্রে ছিল অপ্রচলিত। শ্লেট-পেন্সিল কাগজ প্রভৃতির কোন চলন ছিল না।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report