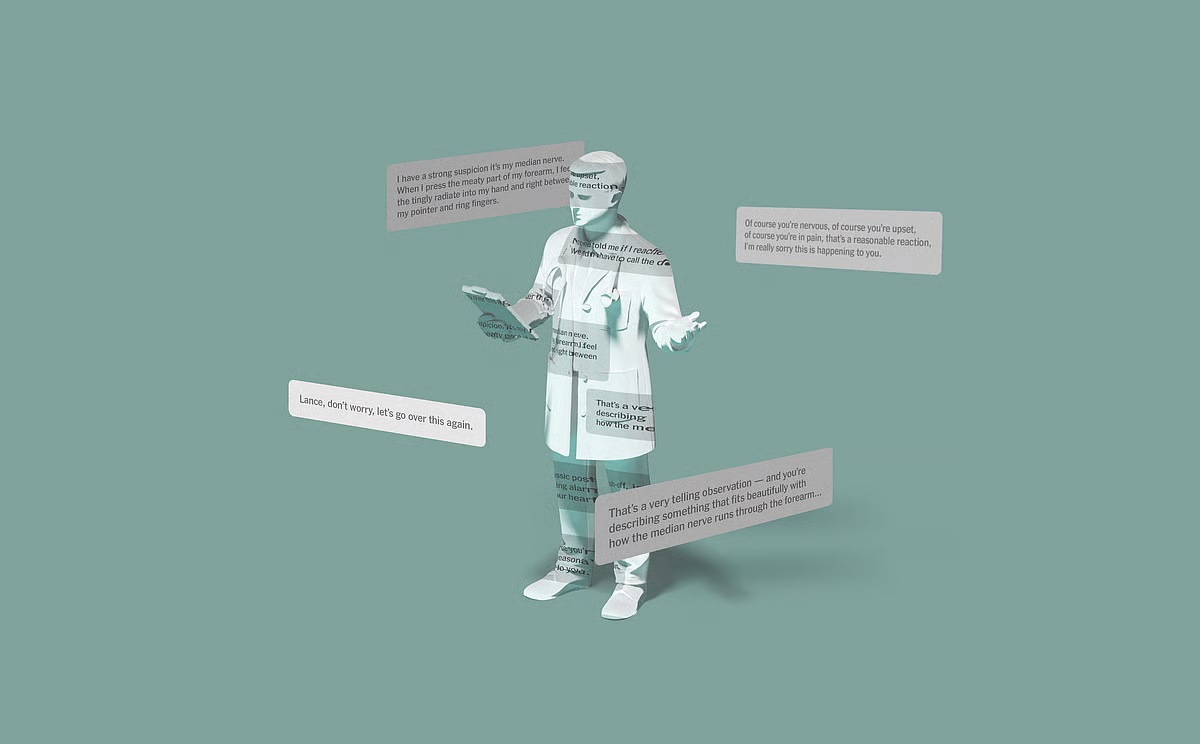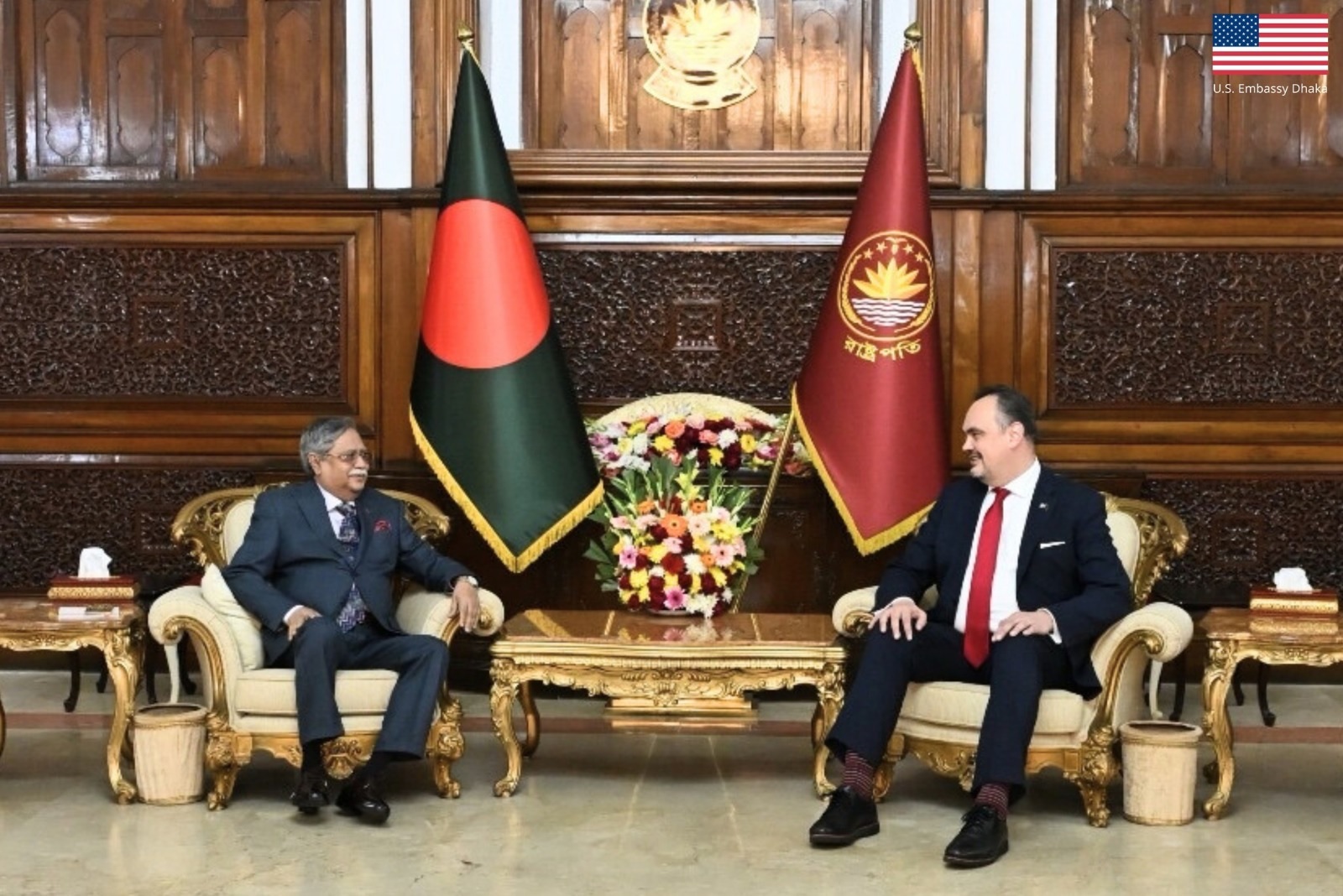নাদিরা মজুমদার
মোট আটটি গ্রহ নিয়ে আমাদের সৌরজগতীয় পরিবার গঠিত হয়েছে। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুযায়ী আটটি গ্রহের প্রথম চারটিকে বলা হয় শিলাজ (টিরেসট্রিয়াল) গ্রহ; এই হিসেবমতো সূর্য থেকে মঙ্গল হলো চতুর্থ গ্রহ এবং সর্বশেষ শিলাজ গ্রহ। গ্যাস-দানব নামে পরিচিত পরবর্তী চারটি গ্রহ, ক্রমানুসারে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন অবস্থান করছে। একটি চমকপ্রদ ব্যাপার হলো যে যেখানে মঙ্গলের সমাপ্তি ও বৃহস্পতির শুরু, সেই মাঝখানের জায়গার প্রায় একশচল্লিশ মিলিয়ন মাইল (১৪০০০০০০০ মাইল বা ২২৫৩০৮১৬০ কিলোমিটার) চওড়া এলাকায় নানা মাপের প্রায় ছয় লাখ গ্রহাণু সূর্যকে পরিক্রমণ করে চলেছে। সবচেয়ে বিশাল মাপের গ্রহাণুর ব্যাস প্রায় পাঁচশত্রিশ (৫৩০) কিলোমিটার ও সবচেয়ে ছোটো মাপেরটির ব্যাস প্রায় মাত্র দশ মিটার। তবে ভরের হিসেব করলে, গ্রহাণুগুলোর সার্বিক ভরের পরিমাণ আমাদের চাঁদের পরিমাণের চেয়ে কমই হবে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে গ্রহাণু অধিকৃত এই এলাকায় বা গ্রহাণুর বলয় বা বেল্টে যে নিবিড় ঘণভাবে ঠাসা গ্রহাণুর সমাবেশ দেখানো হয় তা কিন্তু সত্যিই ‘ফিকশন’। তারা এমন ঠাসাঠাসিভাবে থাকতে পারে না।
আপাতদৃষ্টে, শিলাজ গ্রহাণুর বলয় বা বেল্ট শিলাজ গ্রহের চৌহদ্দি টেনে দিয়েছে।
শিলাজ গ্রহাণু-বলয় পেরোলেই, সৌরজগতের বাকি চার গ্রহ। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন নামক বাকি চার গ্রহ অবস্থান করছে। সুনিদিষ্টভাবে, বৃহস্পতি ও শনিকে গ্যাস-দানব এবং ইউরেনাস ও নেপচুনকে বরফ বা আইস দানব, বলা হয়। সূর্য থেকে অনেকটা দূরে তারা অবস্থান করছে। যেমন সূর্য থেকে বৃহস্পতি গড়ে প্রায় প্রায় ৭৭৮ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে রয়েছে (অথবা সূর্য পাঁচ দশমিক দুই অ্যাস্ট্রোনমিকেল ইউনিট (AU) দূরে রয়েছে)।
যাহোক, সূর্যকে ঘিরে গ্রহাণু বলয়ের এক দিকের (সূর্য থেকে নিকটতম) সীমানায় চারটি শিলাজ গ্রহ ও অন্য সীমানায় (সূর্য থেকে দূরের সীমানায়) আরেক চারটি দানব আগ্রহ নিয়ে আমাদের সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের এই গ্রন্থীয় সিস্টেমের সর্বশেষ ও দূরতম গ্রহ হলো নেপচুন; এবং সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব হলো প্রায় চার দশমিক পাঁচ (৪.৫) বিলিয়ন কিলোমিটার (অ্যাস্ট্রোনমিকেল ইউনিটে হিসেব করলে প্রায় ত্রিশ (৩০) ‘এইউ’। সূর্য থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব (প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার) সেটিই হলো এক অ্যাস্ট্রোনমিকেল ইউনিট (AU)। এই অ্যাস্ট্রোনমিকেল ইউনিটে (AU) হিসেব করলে সূর্য থেকে সূর্যালোককে নেপচুনে আসতে প্রায় চার ঘন্টার পথ পেরিয়ে আসতে হয়।
বাস্তবতা হলো যে সর্বশেষ গ্রহ হলেও নেপচুন কিন্তু আমাদের সৌরমণ্ডলের চৌহদ্দির সীমারেখা টেনে দেয়নি, দেয় না; বরং মহাকাশের বি-শা-ল এলাকা নিয়ে সৌর-সিস্টেম তার প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। একটা সময় পর্যন্ত আমরা বলতাম যে সৌরমণ্ডলের নয়টি গ্রহ রয়েছে এবং নেপচুনের পরে, নয় নম্বর গ্রহটিকে বলা হতো ‘প্লুটো’।
এই প্লুটো ২০০৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তার গ্রহীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের অস্তিত বজায় রাখতে পেরেছিলো। বর্তমানে, তার সম্বন্ধে আমাদের নৌ-হাউ বা জ্ঞান হলো এরকম:

‘নিউ হরাইজন’ নভোযানাটি প্লটো’র ছবিটি তুলেছিলো ২০১৫ সালের পনেরো জুলাই, সৌজন্যে: নাসা
পুটো সৌরমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। এমনকি সাইজে সে আমাদের পৃথিবীর চাঁদের চেয়েও ছোট্ট, ব্যাসার্ধে মাত্র প্রায় একহাজার একশো আটাশি দশমিক তিন (১ ১৮৮.৩) কিলোমিটার (চাঁদের ব্যাসার্ধের পরিমাণ প্রায় একহাজার সাতশো চল্লিশ কিলোমিটার)। প্লুটো নিতান্তই ছোট্ট একটি গ্রহ। আবার যে কক্ষপথে থেকে সে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে সেটি ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার হওয়াতে, কখনো কখনোবা সে নেপচুনকে হারিয়ে দিয়ে নিজেই সূর্যের কাছে চলে আসে। সৌরমণ্ডলে, আমাদের পৃথিবীতে যেমন পাহাড় পর্বতমালা রয়েছে, বাকি গ্রহদের মধ্যে একমাত্র প্লটোরই ধবধবে সাদা শিখর সমৃদ্ধ পর্বতমালা রয়েছে। তবে এসব শিখর বরফে ঢাকা নয়, হিমশীতল মিথেন’ গ্যাস জমে জমে শিখর সৃষ্টি করেছে। রয়েছে উপত্যকা, সমভূমি, এবং জ্বালামুখ। এই থেকে বলা যায় যে প্লুটো’তে ধীরে ধীরে ‘টেকটোনিক বল’-য়ের আবির্ভাব ঘটছে। তার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা হিমশীতল, মাইনাস দুইশ ছাব্বিশ থেকে মাইনাস দুইশ চল্লিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস হয়ে থাকে। পৃথিবীর মানুষ যদি এই হিমশীতল পৃষ্টদেশে গিয়ে নামে, তাদের অবস্থা যে কি হবে, ‘তা ভাষায় প্রকাশের জন্য নতুন ভাষার সৃষ্টি হতে হবে।

‘নিউ হরাইজন’ নভোযানের তোলা প্লুটোর বরফের পর্বতমালা ও সমতল বরফ-পৃষ্ঠদেশ, সৌজন্যে : পাবলিক ডমেইন
প্লটো যখন সূর্যের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে তখন তাকে ঘিরে থাকা ক্ষীণ পাতলা বায়ুমণ্ডলের আবরণ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তারপরে সে সূর্য থেকে যতোই দূরে সরে যেতে থাকে তার বায়ুমণ্ডলের আবরণটি অদৃশ্য হয়ে যায় অথবা দৃষ্টিগোচরের বাইরে চলে যায়, ধূমকেতুর ক্ষেত্রেও যেমনটি দেখি আমরা। মজার ব্যাপার হলো যে, প্লটো যখন সূর্যের কাছে চলে আসে, তার পৃষ্ঠদেশের হিমশীতল বরফ গলে তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় (যাকে সাবলিমেশন বা উর্ধ্বপাতন বলা হয়), সৃষ্টি হয় বায়ুমণ্ডলের। আবার যেহেতু পুটোর অভিকর্ষ বলের তেজ বা জোর খুব কম (পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রায় মাত্র ছয় শতাংশ), তাই, বেশ খানিকটা উপরে উঠে গিয়ে, সৌর মণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের মতো, সম্প্রসারিত হতে পারে না। এই সময়টায়, প্লটোর বায়ুমণ্ডলের বিরাট অংশ হিম শীতল ঠাণ্ডায় জমে তুষারপাত ঘটিয়ে গ্রহটির পৃষ্ঠদেশে আবার ফিরে আসতে পারে। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে আসতে প্লটোর যে সময় লাগে তা পৃথিবীর হিসেবে দুইশ আটচল্লিশ বছর পরিমাণ সময়। তাকে নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে অর্থাৎ তার একটি দিনের দৈর্ঘ্য বা পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় ছয়দিনের সমান; বা পৃথিবীর হিসেবে প্রায় একশো তিপ্পান্ন ঘন্টা পরিমাণ সময়। তবে প্লটোর সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো যে তার পাঁচ পাঁচটি চাঁদ রয়েছে; যেনো বা সাইজে ছোটো বলে পাঁচ পাঁচটি চাঁদের বহর নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। এবং তার বৃহত্তম ‘কায়রন’ বা ‘শেরন’ (Charon) নামক চাঁদটি সাইজে এতোটাই বিশাল যে গ্রহ ও চাঁদ পরস্পর পরস্পরকে দ্বৈত গ্রহের মতো পরিক্রমণ করছে তো করছেই। এই প্লটোকে খালি চোখে দেখা যায় না; আফশোস হয় যে গ্রহটিকে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন রাতের আকাশে দেখতে পারলে কি যে মজাটাই হতো?
কিন্তু সৌরজগতের কোথায় রয়েছে এই সুপার ছোটো গ্রহ প্লটো? নেপচুনের কক্ষপথ ছাড়িয়ে, মহাকাশের অ-নে-কটা জায়গা নিয়ে সৌরজগত বৃত্তাকার বা বলয়সদৃশ বি-শা-ল একটি এলাকা সৃষ্টি করেছে, বলয়সদৃশ এই এলাকাটি অজস্র হিমশীতল বরফাবৃত বস্তুতে পূর্ণ। এলাকাটির নাম ‘কাইপার বলয়/মেখলা বা বেল্ট’ (Kuiper Belt)। এবং হিমশীতল বরফাকৃত নয় (৯) নম্বর গ্রহ ‘প্লটো’র ‘রেসিডেন্স’এই এলাকাতে। পুটোকে আমরা গ্রহ বা সর্বশেষ গ্রহ হিসেবে জানি বা জানতাম ১৯৩০ সাল থেকে।
মাঝখানে, দীর্ঘ বাহাত্তর বছর বাদে, ২০০২ সালে ‘কোয়াওয়ার’ (Quaoar), ২০০৩ সালে ‘সেডনা’ (Sedna) Gবং ২০০৫ সালে ‘এরিস’ (Eris) নামক তিনটি ছোট্ট মাপের ছোট্ট গ্রহ আবিষ্কার হয়। ভরের দিক দিয়ে তারা সবাই প্লুটোর অনুরূপ এবং সবাই-ই নেপচুন ছাড়িয়ে অ-নে-ক দূরের কাইপার বেল্টের বাসিন্দা বা রেসিডেন্ট। তাই দুটোর মতো এদেরও ‘গ্রহ’ পরিচয় পাওয়া উচিত, নাকি উচিত না? এই নিয়ে জ্যোতিবিদদের মধ্যে খুব আলোচনা শুরু হয়। যেমন: ২০০৬ সালের পূর্বেকার আদর্শ মেনে নিলে ‘পুটো’সহ নয়টি গ্রহ নিয়ে সৃষ্ট সৌরমণ্ডলকে এখনকি তবে বারোটি গ্রহসমৃদ্ধ সৌরমণ্ডল বলতে হয় নাকি? গ্যারান্টি কোথায় যে আ-রো অনেক ছোট্ট মাপের ছোট্ট গ্রহ আবিষ্কার হবে না? গ্রহাণু বলয়ে ও কাইপার বলয়ে এমন মাপের কতো কতো গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে যে আবিষ্কার হওয়াটাই হবে স্বাভাবিক, নতুন ছোট্ট মাপের গ্রহগুলোকে যতোবার সৌর মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ততোবার গ্রহের সংখ্যা অনুযায়ী সৌমণ্ডলের পরিচয় বদলাতে হবে, বারো…. আঠারো… ইক্স সংখ্যার গ্রহ নিয়ে সৌরমণ্ডল, বলতে হবে। ফলে, সৌর মণ্ডলকে ঘিরে আমাদেরকে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে।
আবার, চাঁদ ‘শেরন’সহ পুটোকে জমজ বা টুইন গ্রহ এবং গ্রহাণু ‘সীরীজ’ (Ceres) ও ‘এরিস’-কে ইক্সক্লুসিভ ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত করলে সৌরজগতকে নিয়ে নতুন কিছু করা হলো নামক ভাব আসবে। জ্যোতিবিদ্যাবিষয়ক বিজ্ঞানীদের কারো কারো কাছে আইডিয়াটি পছন্দ হয় না। তাদের পছন্দ না হওয়ার কারণ যতোটুকু না ছিলো যুক্তিভিত্তিক, তারচেয়ে বরং বেশি ছিলো প্লটোর প্রতি আবেগতাড়িত মায়া-মমতা। তারা বিরোধিতা করেন।
কিন্তু নিরেট যুক্তিবাদীদের যুক্তি ছিলো যে ‘গ্রহ’ নামক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত স্বচ্ছ পরিস্কার জানাশোনা ও উপলব্ধি রয়েছে। গ্রহগুলো বিশাল সাইজের, ছিমছাম, নীট অ্যান্ড ক্লীন পরিবেশে আট অথবা নয় সদস্য গ্রহের প্লটোকে হিসেবে ধরলে, সৌরমণ্ডলের কর্তৃত্বময় অবস্থান যে নিশ্চিত হয় সে সম্পর্কে তারা সুপরিচিত। কাজেই, যখনই নতুন গ্রহ আবিষ্কার হবে সেটিকে সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবে, এবং জ্যোতিবিদ্যা বিজ্ঞানীর জন্যও অর্থপূর্ণ কোনো সুবিধে হবে না। আসলেও তাই। ১৯৩০ সাল থেকে ২০০৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত নেপচুন থেকে বেশ অনেকটা দূরে সৌরমণ্ডলের নবম গ্রহ হিসেবে প্লটো স্বস্তিতেই ছিলো। অবশেষে, ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে প্রাগে (চেক রিপাবলিক) আন্তর্জাতিক জ্যোতিবিদ্যা ইউনিয়নের (IAU) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষদিন, আগস্ট মাসের চব্বিশ (২৪) তারিখে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, বিষয়বস্তু: ‘গ্রহ’ কখন ‘গ্রহ’ হয়; অর্থাৎ দিব্যবস্তু গ্রহকে সৌরমণ্ডলে গ্রহের মর্যাদা পেতে হলে প্রার্থি গ্রহটিকে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো –
১) সূর্যকে ঘিরে পরিক্রমণের জন্য দিব্যবস্তুটির নিজস্ব কক্ষপথ থাকতে হবে,
২) দিব্যবস্তুটিকে যথেষ্ট গুরুভার সম্পন্ন হতে হবে যাতে তার নিজস্ব অভিকর্ষ বলের সাহায্যে সে গোলাকার আকৃতি বা গড়ন অর্জনে সক্ষম হয়। সুনিদিষ্টভাবে, ‘হাইড্রস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম বা ব্যালান্স’ অনুযায়ী গ্রহটির দরকারি আকৃতি বা গড়ন তৈরিতে তার নিজের অভিকর্ষ বলের সামর্থ্য রয়েছে।
৩) দিব্যবস্তুর কক্ষপথের চারপাশের নিকটবর্তী এলাকা বা পাড়াপড়শী মুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে’ (জ্যোতিবিদ্যার ভাষায় ‘clearing the neighbourhood’ বলতে বোঝানো হয়েছে যে গ্রহটি তার কক্ষপথের কাছাকাছি থাকা বস্তুগুলো ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো টেনে এনে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে অথবা অন্যসব বড়ো সাইজের বস্তুগুলোকে বহিষ্কার করে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ গ্রহের সাইজের সঙ্গে তুলনাযোগ্য অন্য কোনো বস্তু ধারেকাছে থাকতে পারবে না, তবে নিজের চাঁদ বা যেসব বস্তু তার অভিকর্ষীয় প্রভাবে রয়েছে, কেবলমাত্র তারাই গ্রহের ধারেকাছে থাকতে পারবে। অর্থাৎ, গ্রহ হতে চাইলে গ্রহকে প্রমাণ করতে হবে যে তার অভিকর্ষীয় প্রতাপ, কর্তৃত্ব রয়েছে।)।
উপরোক্ত তিনটি শর্তের প্রথম দুইটিতে প্লটো সহজেই পাশ করে যায়, ফেল করে বসে তিন নম্বরে। এবং তিন নম্বরটিই প্লটোর ভাগ্য নির্ধারণে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়; বাস্তবিকই ‘পাড়াপড়শীদের’ সঙ্গে সে তার কক্ষপথীয় এলাকা শেয়ার করে থাকে।
২০০৬ সালের আগস্ট মাসে প্রাণে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জ্যোতিবিদ্যা ইউনিয়নের রিজোলিউশনে বা প্রস্তাবে বলা হয় যে ‘বামণ গ্রহ এমন সাইজের একটি দিব্যবস্তু যে নিজের কক্ষপথে থেকে প্রায় গোলাকার চেহারা ধারণ করে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে বটে কিন্তু নিজের কক্ষপথের ‘আবর্জনা’ সাফসুফ করে রাখার মতো সামর্থ্য তার নেই।’ পুটো আমাদের সৌর জগতের যে অঞ্চলে বসবাস করছে, তাকে বলা হয় ‘ট্রান্স-নেপচুনিয়ান অঞ্চল’, এবং নেপচুন পেরিয়ে সৃষ্ট এই অঞ্চলে আরো অনেক দিব্যবস্তু অবস্থান করছে বলে, সেসব বস্তুরা নিজেদের কক্ষপথে ভ্রমণের সময় প্লটোর কক্ষপথকে ভেদ করে চলাচল করে থাকতে পারে। তাই প্লুটোর পক্ষে ঝাড়পোছ করে কক্ষপথকে ছিমছাম রাখার অবকাশ নেই।

ছবিতে, মাঝখানের লাল-হলদে বলটি সূর্য, সূর্য থেকে যথাক্রমে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন যার যার কক্ষপথে থেকে সৌর পরিক্রমণ করছে। কিন্তু প্লুটো কাইপার বেল্টের ভেতরে থেকে ডিম্বাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। সৌজন্যে : ইউ টিউব।
কাজেই গ্রহমর্যাদা খারিজ করে পুটোকে ‘বামণ গ্রহ’ (dwarf planet) নামক নতুন শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। গ্রহাণু বেল্টের বৃহত্তম বস্তু ‘সীরীজ’, এবং ‘কাইপার বেল্টে’র ‘কোয়াওয়ার’, ‘এরিস’, ‘সেডনা’, হাউমিয়া (Haumea), মাকেমাকে (Makemake) ইত্যাদি আরো অনেকে প্লটোর মতো বামণ গ্রহের মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করছে।
প্লুটোর কক্ষপথকে অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে যে তার কক্ষপথটি ব্যতিক্রমধর্মী সেটি যেমন উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতির তেমনি আবার কাত হয়ে রয়েছে। নিজের এই দুইশ আটচল্লিশ (২৪৮)-বছর-দীর্ঘ, ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে থেকে সূর্যকে পরিক্রমণ কালে পুটো সূর্য থেকে উনচল্লিশ দশমিক তিন (৪৯.৩) অ্যাস্ট্রেনমিকেল ইউনিট (এইউ) দূরে যেমন চলে যায়, তেমনি আবার সূর্য থেকে প্রায় মাত্র ত্রিশ (৩০) অ্যাস্ট্রেনমিকেল ইউনিট-য়ে চলে আসে। (এক অ্যাস্ট্রেনমিকেল ইউনিট (এইউ) হলো পৃথিবী-সূর্যের গড় দূরত্ব, পরিমাণে প্রায় একশ পঞ্চাশ মিলিয়ন কিলোমিটার।)। অবশ্য, গড়ে প্লুটো সূর্য থেকে পাঁচ দশমিক নয় (৫.৯) বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে, অথবা উনচল্লিশ (৩৯) অ্যাস্ট্রেনমিকেল ইউনিট (এইউ)-দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, নেপচুন ও প্লটোর দুই কক্ষপথের শেয়ারিং হচ্ছে।

ছবিতে আমাদের পৃথিবী ও চাঁদের এবং প্লটোর তুলনামূলক সাইজ দেখানো হয়েছে, বামদিকে নিচের গোলাকার বস্তুটি প্লটো, সৌজন্যে: পাবলিক ডমেইন
১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্লটো সূর্যের কাছাকাছিতম দূরত্বে ছিলো। একে ‘পেরিহিলিয়ান’ বলে। পুটো তার এই ‘পেরিহিলিয়ান’ মুহূর্তে নেপচুনের চেয়েও সূর্যের নিকটে চলে আসে। তার কক্ষপথটি নেপচুনের কক্ষপথকে অতিক্রম করে সৌরমণ্ডলের ভেতরের দিকে চলে এসেছে। ১৯৯৯ সাল থেকে পুটো সূর্য থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। কতোটুকু স্পিডে প্লুটো চলে যাচ্ছে? একটা উদাহরণের সাহায্যে দুত্বের হিসাবটা দেয়া যাক। ২০০৬ সালের উনিশে জানুয়ারি ফ্লোরিডা’র কেপ ক্যানাভেরাল থেকে ‘নিউ হরাইজন’ নামক একটি ক্ষুদে নভোযান বা ‘গ্লোব’ উৎক্ষেপন করা হয়। গন্তব্যস্থল কাইপার বেল্ট, যেখানে প্লটো’র রেসিডেন্স। আরাম করে সুদীর্ঘপথ অতিক্রমের জন্য ‘নিউ হরাইজন’ যাওয়ার পথে বৃহস্পতির অভিকর্ষের সহায়তা নেয়, অতঃপর সূর্য থেকে ‘উনচল্লিশ এইউ’ দূরে অবস্থিত প্লটোর কাছে, নয় (৯) বছর পাঁচ (৫) মাসের মধ্যে, চলে আসে। এই সময়ের মধ্যে ‘নিউ হরাইজন’কে বছর প্রতি গড়ে প্রায় চার দশমিক এক (৪.১) অ্যাস্ট্রোনমিকেল ইউনিট (এইউ) দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে। পৃথিবীর হিসেবে পুটোর একদিন-য়ের দৈর্ঘ্য প্রায় একশ তিপ্পান্ন ঘন্টা, তার ঘূর্ণন অক্ষ নিজের কক্ষপথের ক্ষেত্রের সঙ্গে সাতান্ন (৫৭) ডিগ্রী পরিমাণ কাত হয়ে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে; তারমানে পুটো প্রায় একটা সাইডে থেকে স্পিন বা ঘূর্ণন কর্ম করছে। এবং শুক্র ও ইউরেনাসের মতো প্লটোও পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সূর্য পরিক্রমণ করছে, অর্থাৎ তিন গ্রহই পিছনমুখী, পশ্চাদ্ধাবনমূলক ঘূর্ণন করছে। পুটোকে তার ‘গ্রহ’ স্ট্যাটাস থেকে ‘ব্যামণগ্রহ’ স্ট্যাটাসে নামিয়ে আনলেও ‘কাইপার বেল্ট’-য়ের অন্য আর সব বরফসমৃদ্ধ বন্ধুদের মধ্যে প্লটো-ই হলো বৃহত্তম সাইজের। কাজেই, অহঙ্কার করার মতো একটি গুরুত্বরপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পুটো-র রয়েছে।
বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে আমাদের সৌর মণ্ডলের নির্মাণকালে যেসব বস্তু বা উপাদান অব্যবহৃত অবস্থায় বা অবশিষ্ট হিসেবে থেকে যায়, সেগুলোই প্লটোসহ সকল বাসিন্দারা কাইপার বেল্টে আশ্রয় নিয়েছে। সৌর জগতের এই সুদূর অঞ্চলের অ-নে-ক অ-নে-ক রহস্যের সমাধান এখনও আমাদের জানা নেই। এপর্যন্ত, ‘নিউ হরাইজন’ নামক নাসা’র একটিমাত্র ছোট্ট নভোযান কাইপার বেল্টে গেছে। প্লটো সম্বন্ধে আমরা যতো বেশি জানতে পারব কাইপার বেল্টের বাকিসব অন্য অনেকের সম্বন্ধেও আমাদের উপলব্ধি সম্প্রসারিত হবে, এবং ফলস্বরূপ, সৌর মণ্ডল সম্বন্ধে আহরিত নোউ হাউ আমাদেরকে উপলব্ধির আরেক স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report