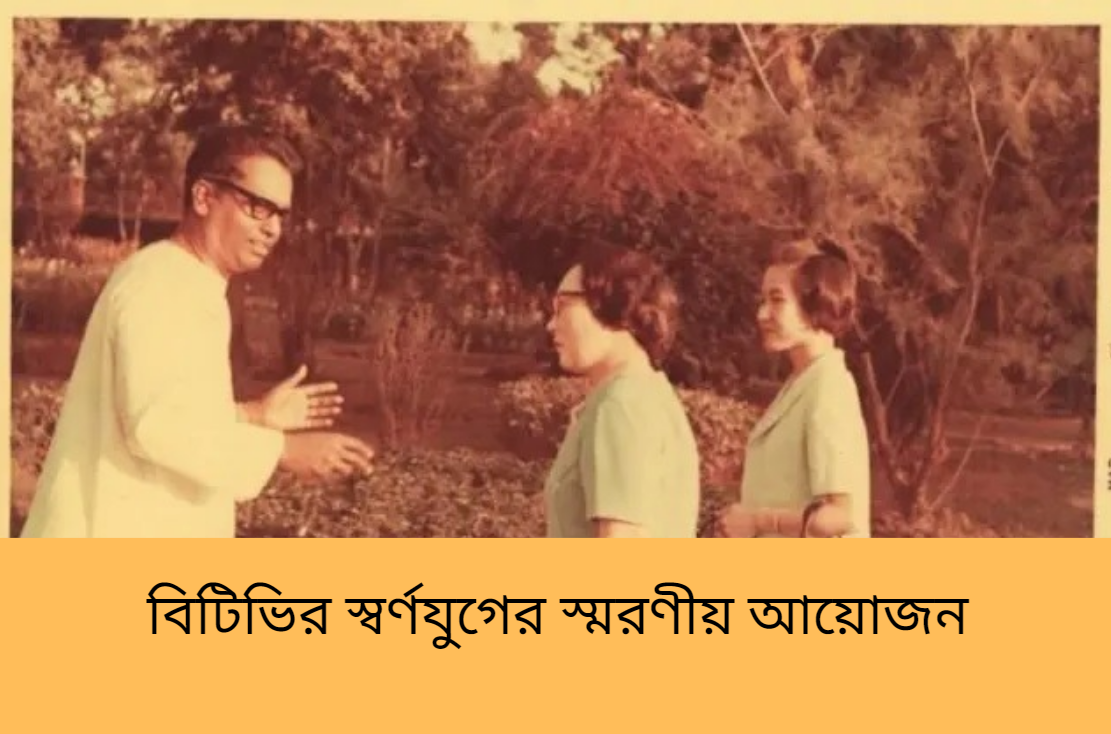নাটকের নাম: কবর
প্রচারকাল: ঈদুল ফিতর, ১৯৮০ (বাংলাদেশ টেলিভিশন)
নির্দেশনা: আবদুল্লাহ আল মামুন
রচনা: মুনীর চৌধুরী
প্রধান চরিত্র: গোর খোঁড়েনি
অভিনয়: আতাউর রহমান, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, আবুল খায়ের, মামুনুর রশীদ
স্মরণীয় পার্শ্বচরিত্র: আতাউর রহমানের ‘মাওলানা’
নাটকের সারসংক্ষেপ ও প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যা
বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইতিহাসে যেসব ঈদের নাটক শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়, ‘কবর’ তাদের অন্যতম। মুনীর চৌধুরীর রচিত এই নাটকটি প্রথম লেখা হয় ১৯৫৩ সালে, পাকিস্তানি শাসনামলে ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদে। তখন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। এই নাটকটি তখনকার দমননীতির বিরুদ্ধে এক সাহসী সাহিত্যিক প্রতিবাদ। যদিও এটি লিখিত হয়েছিল স্বাধীনতার বহু আগে, তবে ১৯৮০ সালে ঈদুল ফিতরে বিটিভিতে প্রচারিত হলে তা নতুন করে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার আলো জ্বালায়।

নাটকের ঘটনাপ্রবাহ একটি কবরস্থানে আবর্তিত হয়, যেখানে মৃত তিনটি চরিত্র—একজন মাওলানা (ধর্মের প্রতিনিধি), একজন রাজনৈতিক কর্মী বা বিপ্লবী (জনগণের প্রতিনিধি) এবং একজন বুদ্ধিজীবী (শিক্ষিত শ্রেণির প্রতিনিধি)—মৃত্যুর পরেও নিজেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এই বিতর্ক শুধু কথার খেলা নয়, বরং এটি একটি জাতির আত্মসমালোচনার রূপক। তারা জীবিত অবস্থায় যেসব দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিল, সেগুলোর ব্যর্থতা তাদের আলোচনায় ফুটে ওঠে। এটি এমন এক নাটক, যেখানে দর্শক শুধু কাহিনী নয়, বরং নিজের মনেও প্রশ্ন তোলে—”আমরা কি যথার্থ দায়িত্ব পালন করছি?”
অভিনয়ের গভীরতা ও চরিত্র বিশ্লেষণ
নাসির উদ্দীন ইউসুফ ‘বিপ্লবী’ চরিত্রে ছিলেন দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ। তার সংলাপ বলার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি এবং শরীরী ভাষা নাটকে এক তীব্রতা এনেছিল। তিনি ছিলেন নাটকের যুক্তির মেরুদণ্ড, যে প্রশ্ন তোলে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় এবং প্রতিবাদ করে।

আতাউর রহমানের ‘মাওলানা’ চরিত্রটি ছিল সবচেয়ে জটিল ও অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ। তিনি একাধারে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু একইসঙ্গে নিজের দায় এড়িয়ে যাওয়ারও প্রতীক। তার দ্বিধা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যর্থতা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপিত হয়। যখন তিনি নিজের অবস্থান রক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, তখন তার চেহারায় ও কণ্ঠে যে অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে, তা দর্শককে এক প্রকার নীরব অনুশোচনায় ফেলে দেয়।
মামুনুর রশীদের চরিত্র ছিল সংক্ষিপ্ত, তবে তার সংলাপ—“আমরা সবাই এই কবরেরই অংশ”—নাটকের সারকথা হয়ে দাঁড়ায়। এই সংলাপ দর্শককে মনে করিয়ে দেয় যে, কেউই নিজের ব্যর্থতার দায় এড়িয়ে যেতে পারে না।
নির্দেশনা ও চিত্রভাষার শক্তি
আবদুল্লাহ আল মামুন নাটকটিকে শুধুমাত্র একটি সাহিত্যনির্ভর মঞ্চনাটক হিসেবে উপস্থাপন করেননি, বরং তাতে এমন এক ভিজ্যুয়াল ভাষা সংযোজন করেছিলেন যা টেলিভিশনের পর্দায় এক অনন্য মাত্রা তৈরি করে। মিনারের আজানের ধ্বনি, অন্ধকারের মধ্যে হালকা ছায়া, মৃতদের ধীরগতির চলাফেরা—সব মিলিয়ে নাটকটি হয়ে ওঠে এক ধরনের পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা।

তিনি যেভাবে আলোছায়া ব্যবহার করেন, তা যেন মৃত চরিত্রগুলোর অস্তিত্বকে ধূসর ও অনির্দিষ্ট করে তোলে—যেমন তাদের অবস্থান সমাজেও অস্পষ্ট। একইসঙ্গে ঈদের দিন প্রচলিত হাস্যরসাত্মক নাটকের বাইরে গিয়ে এমন একটি দর্শনচিন্তায় মোড়ানো নাটক পরিবেশন করাও ছিল এক ধরনের সাহসী সাংস্কৃতিক প্রয়াস।
নাটকটির প্রভাব ও উত্তরাধিকার
‘কবর’ নাটকটি শুধুমাত্র একটি চেতনানির্ভর নাটক নয়, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাট্যধারার একটি মাইলফলক। ঈদের মতো উৎসবের দিনে এমন একটি গভীর দর্শনসমৃদ্ধ নাটক প্রচারের মাধ্যমে বিটিভি একটি সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছিল। অনেক নাট্যবোদ্ধা ও সমালোচক মনে করেন, এটি বিটিভির ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ঈদ নাটকগুলোর একটি, যা ঈদের বিনোদনের পরিধিকে শুধু হাস্যরসের গণ্ডি থেকে বের করে এনে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চেতনার জায়গায় উন্নীত করেছিল।
আজও এই নাটকটি স্মরণ করা হয় সেইসব সময়ের স্মারক হিসেবে, যখন নাটক ছিল প্রতিবাদের হাতিয়ার, এবং টেলিভিশন ছিল জাতির আয়না।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট