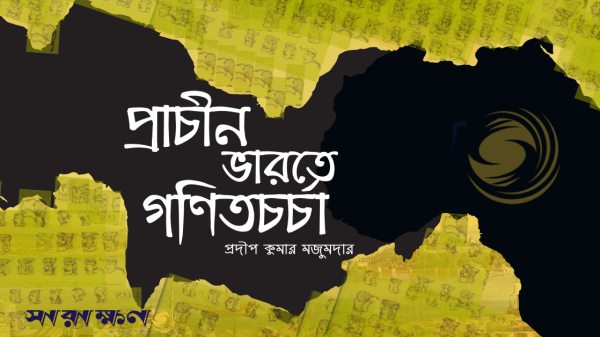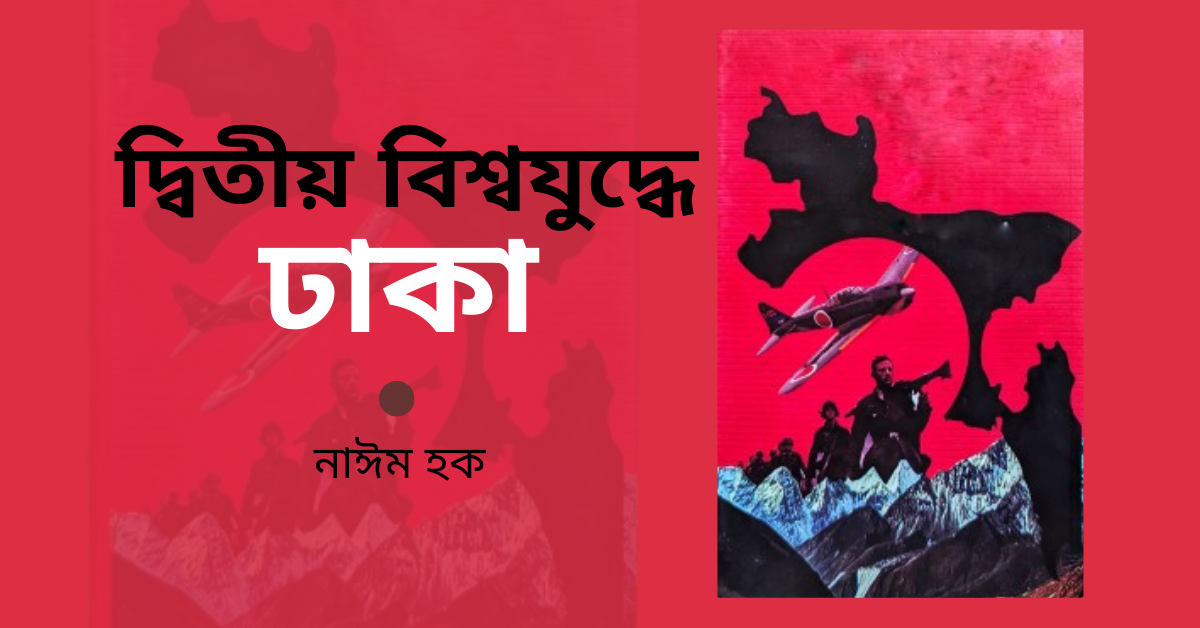আমাদের সমাজে একটি নৃশংস বাস্তবতা আছে—ধর্ষণ নামক জঘন্য অপরাধের শিকার হওয়ার পরও ভুক্তভোগীকে নানা ভাবে অপমান, সন্দেহ ও দোষারোপ করা হয়। এর পেছনে রয়েছে সমাজব্যবস্থার গভীর ও বিকৃত মানসিকতা।
ভুক্তভোগীকে দোষারোপের সংস্কৃতি
ধর্ষণের পর স্বাভাবিক সহানুভূতি বা সহায়তা পাওয়ার বদলে অনেক নারীকে শুনতে হয়—“তুমি ওরকম পোশাক পরলে কেন?”, “তুমি ওখানে গিয়েছিলে কেন?”, “তুমি হয়তো রাজি ছিলে!”। এই দোষারোপের মাধ্যমে মূল অপরাধীকে আড়াল করা হয় এবং ভুক্তভোগীকেই অপরাধী হিসেবে তুলে ধরা হয়।
এটি কেবল ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যা নয়—সমাজের রীতিনীতির মধ্যে রক্তের মতো মিশে থাকা এক বিকৃতি। সমাজ যেন ধর্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে বলে—“তোমার কিছু দোষ নেই, দোষ ছিল তার।” ফলে ধর্ষকের অপরাধ আরও বৈধতা পায়।
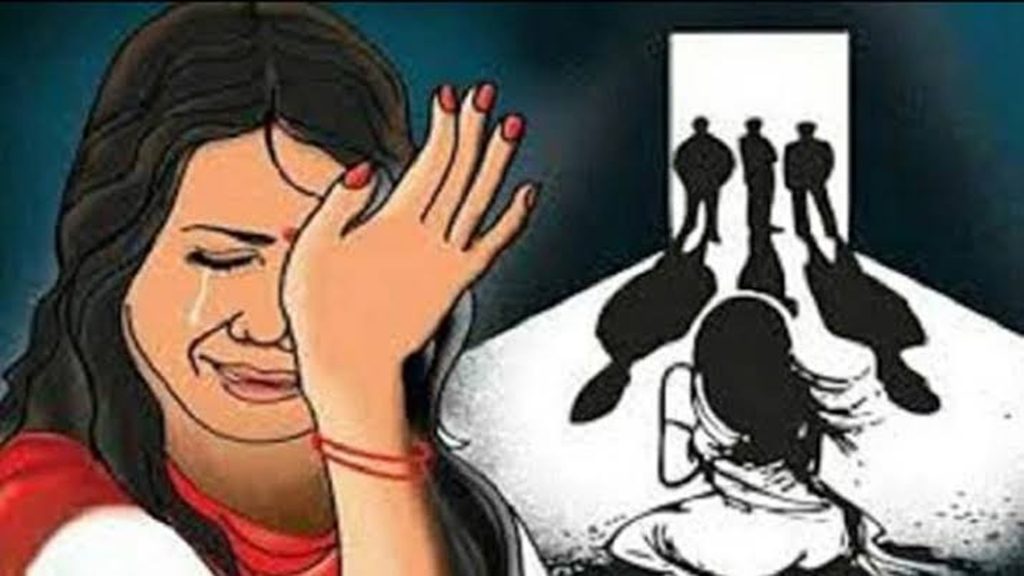
পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা
এই দোষারোপের শিকড় পিতৃতান্ত্রিক চিন্তায়। যেখানে নারীর মর্যাদা, স্বাধীনতা বা শরীরকে পরিবারের ‘ইজ্জত’ হিসেবে দেখা হয়। ধর্ষণকে নারী নয়,পরিবারের বা সমাজের মানহানির বিষয় বানিয়ে ফেলা হয়। ফলে পরিবার বা সমাজ চায় ঘটনা চেপে যেতে, যাতে তাদের তথাকথিত সম্মান রক্ষা পায়। ভুক্তভোগীর জীবন তখন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।
ভয়, নিয়ন্ত্রণ এবং নীরবতা চাপিয়ে দেওয়া
ভুক্তভোগীর মুখ বন্ধ করতে, তাকে লজ্জায় ফেলতে সমাজ ইচ্ছাকৃতভাবে দোষারোপের কৌশল বেছে নেয়। এর উদ্দেশ্য—নারীদের শাসন করা, তাদের স্বাধীন চলাফেরা বা মত প্রকাশে বাধা দেওয়া। নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ধর্ষণকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আইনি ও সামাজিক ব্যর্থতা
যখন ধর্ষণের শিকার কেউ অভিযোগ করে, তখনও পুলিশি তদন্তে, হাসপাতালে পরীক্ষায়, আদালতের ভাষায়—সবখানেই সেই একই মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। ভুক্তভোগীকে প্রমাণ করতে বলা হয় যে সে সত্যিই ‘ভালো মেয়ে’ ছিল। ফলে অনেকে ন্যায়বিচারের আশা ছেড়ে দেয়।
এটা কেবল মানসিকতা নয়—এটি একটি অপরাধ
ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করা মানে তাকে দ্বিতীয়বার নির্যাতন করা। এটি এক ধরনের মানসিক সহিংসতা। এটিও অপরাধের অংশ। সমাজ যখন ভুক্তভোগীকে চুপ করিয়ে দেয়, অপমান করে, সন্দেহ করে—তখন সেটি ধর্ষকেরই হাত শক্ত করে।
পরিবর্তনের কী দরকার?
শিক্ষা: যৌন সম্মতি, মানবাধিকার এবং সমান মর্যাদা নিয়ে শিক্ষা দেওয়া।

আইনি সংস্কার: ভুক্তভোগীর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সম্মানজনক আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।
মিডিয়ার ভূমিকা: ভুক্তভোগীকে অপরাধী না বানিয়ে প্রকৃত অপরাধীর নাম, চেহারা, পরিচয় স্পষ্ট করা।
পারিবারিক সমর্থন: পরিবারকে শেখাতে হবে—লজ্জা ভুক্তভোগীর নয়, ধর্ষকের।
সমাজকে বুঝতে হবে—ধর্ষণ কোনো “দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা” নয়, এটি একটি পরিকল্পিত অপরাধ, যেখানে ভয় দেখিয়ে, শক্তি প্রয়োগ করে নারীর স্বাধীনতা, সম্মান ও নিরাপত্তা হরণ করা হয়। আর এর পর ভুক্তভোগীর ওপর দোষ চাপানো সেই অপরাধেরই অংশ। এই মানসিকতা ভাঙা না গেলে ধর্ষণ থামবে না—বরং আরও বৈধতা পাবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট