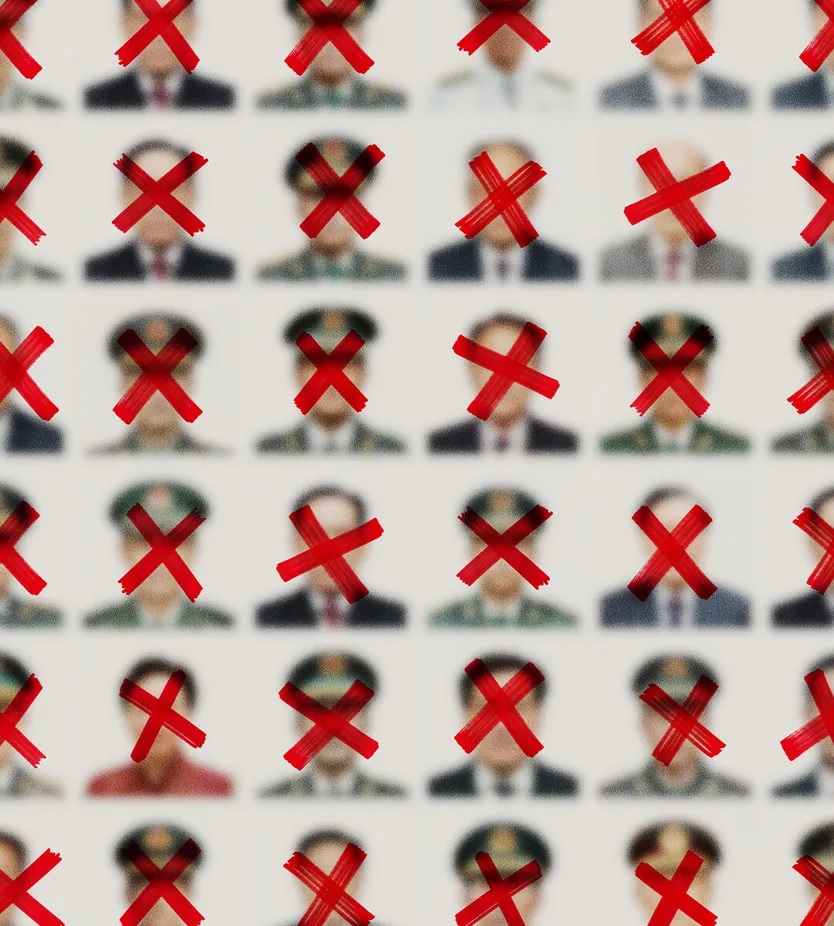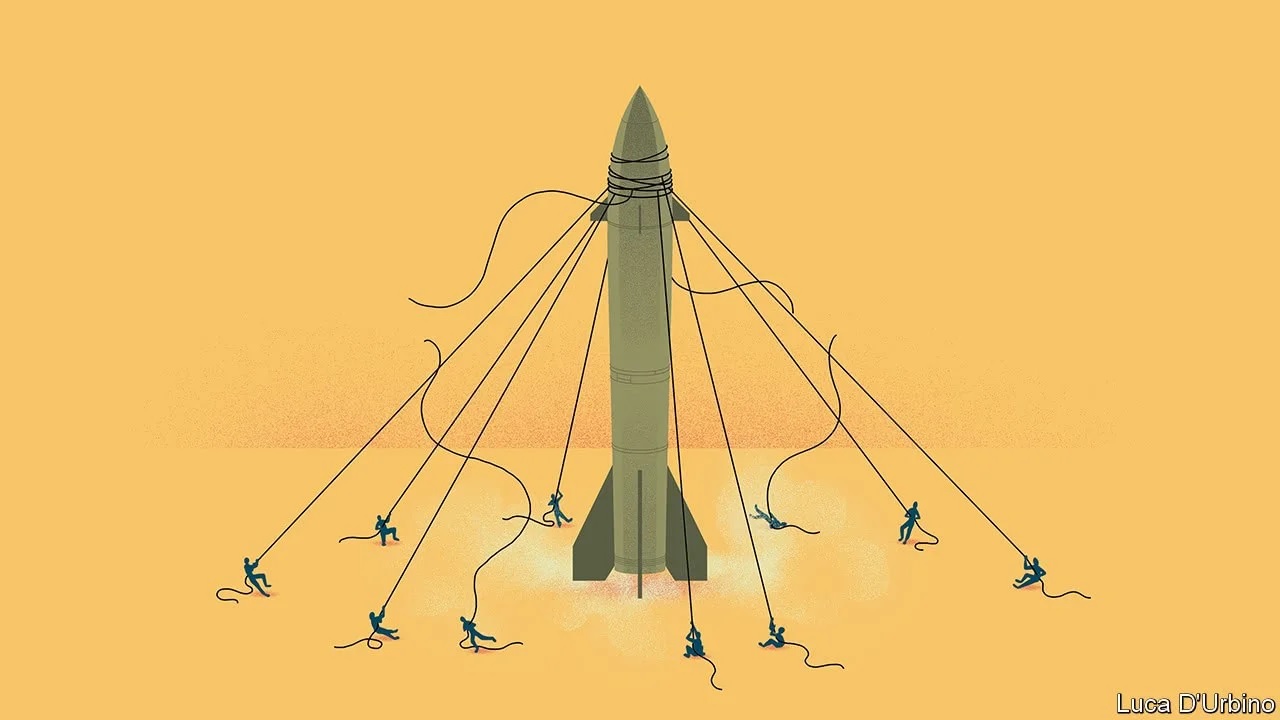দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ চিত্রা নদী আজও যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও খুলনা ঘিরে বসবাসকারী মানুষের জীবন, অর্থনীতি ও পরিবেশের প্রাণস্রোত। ইতিহাস, প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈভব—সবকিছুরই এক নিবিড় মিশেল এই নদীর দুই পাড়।
উৎস ও পথপরিক্রমা
চুয়াডাঙার নিচু চর থেকে উৎপন্ন হয়ে দারসানা, কালীগঞ্জ, যশোর, শালিখা ও কালীপাড়ার ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে চিত্রা গাজীরহাটে নবগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়; এরপর যৌথ প্রবাহ ভৈরব ও রূপসা ছুঁয়ে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে। অতীতে এ প্রবাহ ছিল ইছামতীর শাখা, কিন্তু মুখ ভরাটের কারণে আজ তা নবগঙ্গার উপধারা।
উপনিবেশিক যুগে বাণিজ্যপথ: কলকাতা থেকে খুলনা
উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার (তৎকালীন ক্যালকাটা) সঙ্গে চিত্রা–নবগঙ্গা–ভৈরব–রূপসা ধারায় গুরুত্বপূর্ণ নৌরুট গড়ে ওঠে; চাল, পাট, ধান ও কাঠসহ নানা পণ্য এ পথেই পৌঁছত ক্যালকাটায়। কলকাতা ঘাটে রিভার স্টিমার ‘রকেট’-এর মতো প্যাডেল জাহাজগুলো খুলনা পর্যন্ত যাত্রী ও পণ্য আনা–নেওয়া করত, যা ছিল দ্রুতগতির ‘কলোনিয়াল এক্সপ্রেস’।

খুলনার শিল্পোদ্যোগে চিত্রার ভূমিকা
বন্দরনগর খুলনা যখন কুঠিভিত্তিক সুতার মিল ও জুট প্রেস খুলে শিল্পশহরে রূপ নিচ্ছিল, তখনই কাঁচামাল আনা- নেয়াতে চিত্রা–রূপসা নৌপথের ব্যবহার বেড়ে যায়। ১৯১০-এর দশকে খুলনার জুট প্রেস, কাঠ-করাত মিল ও বরফকলের কাঁচামাল নদীপথেই আসত, যা পরে খুলনা–রূপসার গঙ্গাবক্ষে বৃহৎ ‘সামুদ্রিক লাইটার’-এ তুলে সমুদ্রগামী জাহাজে পাঠানো হতো।
যশোর: ব্রিটিশ ভারতের প্রথম জেলা সদর
১৭৮৬-তে যশোর কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসন প্রথম পূর্ণাঙ্গ জেলা কার্যালয় গড়ে তোলে। এই ঐতিহাসিক সদর এবং তার আশপাশে গড়ে ওঠা কাসবা, সদর বাজার ও মৃৎশিল্পসমৃদ্ধ মুড়ালি—সবকিছুর বিকাশেই চিত্রা ছিল মূলে।
তীরবর্তী সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ
- পাইকগাছা ও কালীশংকর মেলা: নববর্ষ ও অগ্রহায়ণের রাশমেলায় দূরদূরান্ত থেকে নৌকাভর্তি লোকজন আসত।
- পণ্ডিতপুরের তালপাতা-পুঁথি: নদীপথেই সুদূর কাঁঠালপাড়া, বাগেরহাট হয়ে কলকাতার বইবাজারে পৌঁছে যেত।
- কবিগান ও মসলিন: নৌকার ছইয়ে বসে কবিয়ালরা গাইত ‘চিত্রার পাড়ে গঙ্গা-জলে’, আর মসলিন-মহাজনেরা রাতের আঁধারে সূক্ষ্ম বস্ত্রের নিলাম করত।

দুই পাড়ের বনজগত
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদীর লবণত্ব বাড়ায় কিছু অংশে ছোট ছোট ম্যানগ্রোভের ঝুঁটি দেখা যাচ্ছে—গেওয়া, সুন্দরী, গোলপাতা পর্যন্ত জন্ম নিয়েছে বলে গবেষকেরা জানান।
বানর ও অন্যান্য প্রাণী
চিত্রার তীরে গ্রামাঞ্চলের রেসাস বানরের দল খেজুর-কাশবন ঘিরে ঘুরে বেড়ায়; কৃষকের ক্ষেত-বাগানেও এদের দেখা মেলে। দেশের রেসাস জনগোষ্ঠী মূলত এমন নদীবেষ্টিত অঞ্চলেই সবচেয়ে নিবিড়ভাবে মানুষের সহাবস্থানে টিকে আছে।
‘হিপো’-এর গল্প
স্থানীয় লোকগাথায় বড় আকারের ‘জল-গরু’ জাতীয় প্রাণীর কথাও শোনা যায়—যা আদিতে হেক্সাপ্রোটোডন (প্রাগৈতিহাসিক জলহস্তী)-এর জীবাশ্ম ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়ার ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সাযুজ্য রাখে, যদিও সমসাময়িক বাস্তবে এ অঞ্চলে জলহস্তী নেই।

মাছের স্বর্গ: ৫৩ প্রজাতির সমাহার
২০১১–১২ সালের এক গবেষণায় চিত্রা নদীতে ১০টি বর্গের মোট ৫৩টি মাছের প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে কার্প (রুই, মৃগেল, কালবসু) ৩৩.৯৬%, ক্যাটফিশ (বোয়াল, শিং, বাগাড়) ২২.৬৪%, পার্চ ও টেংরা জাতীয় পার্সিফর্ম ২৪.৫৩%—নদীর জৈববৈচিত্র্যের অনন্য প্রমাণ।
সংকট ও টেকসই ভবিষ্যৎ
চিত্রার প্রবাহ আজ সঙ্কুচিত; উজানে সেচ, ড্রেজিংয়ের অভাব, শিল্পবর্জ্য ও পলিমাটির কারণে শুকনো মৌসুমে খরা ও পানিকষ্ট, বর্ষায় আকস্মিক প্লাবন দেখা দেয়। স্থানীয়রা খাল-বিল পুনঃখনন, অংশীজনকেন্দ্রিক নদী কমিটি ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দাবি তুলেছেন। মতান্তরে, ‘একটি নদীর আরোগ্যের সূচক তার তীরে দাঁড়িয়ে বানরের মুখে হাসি দেখা যায়’—এমনটাই বলেন পরিবেশবিদেরা।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট