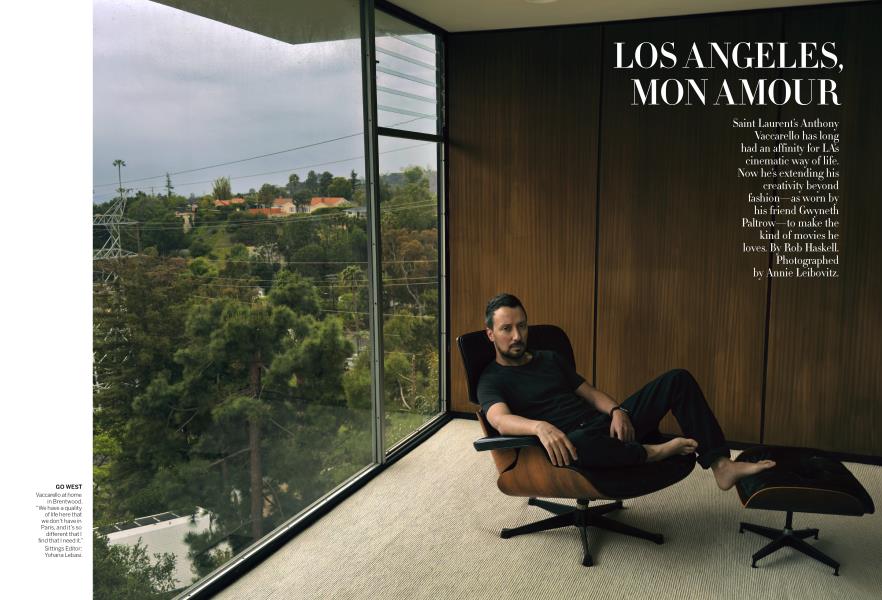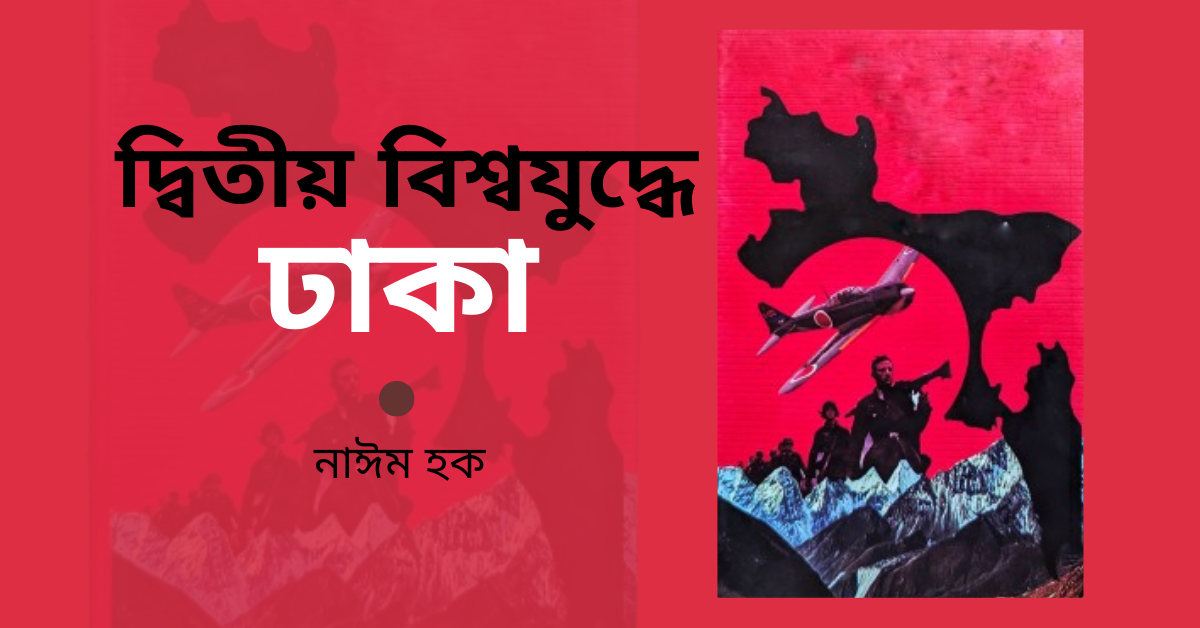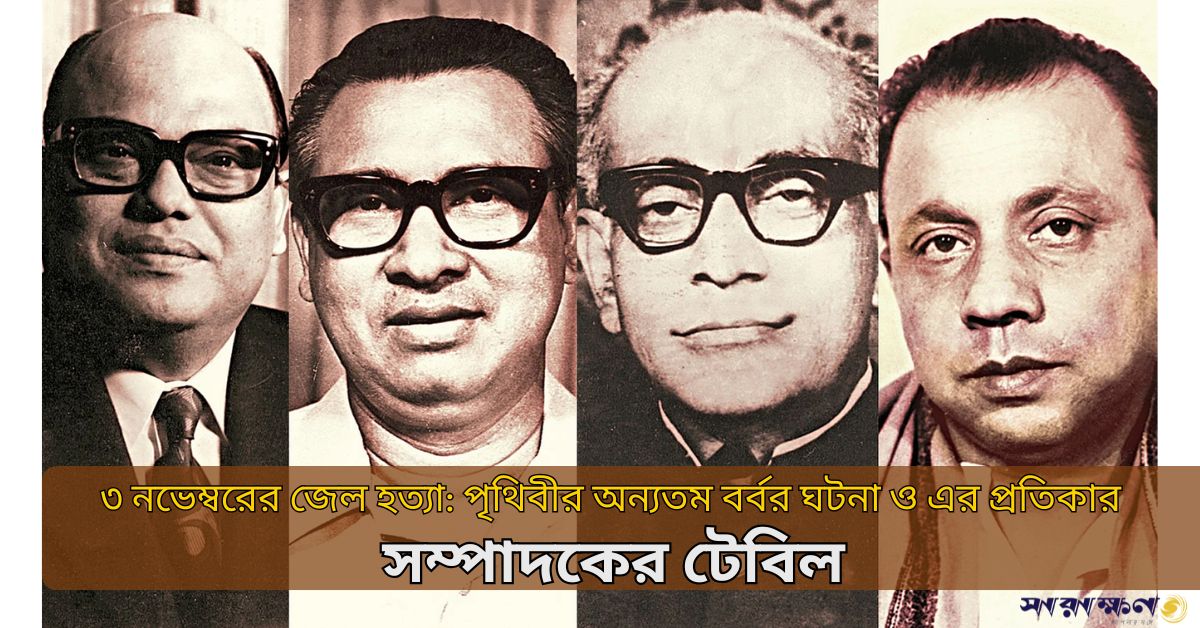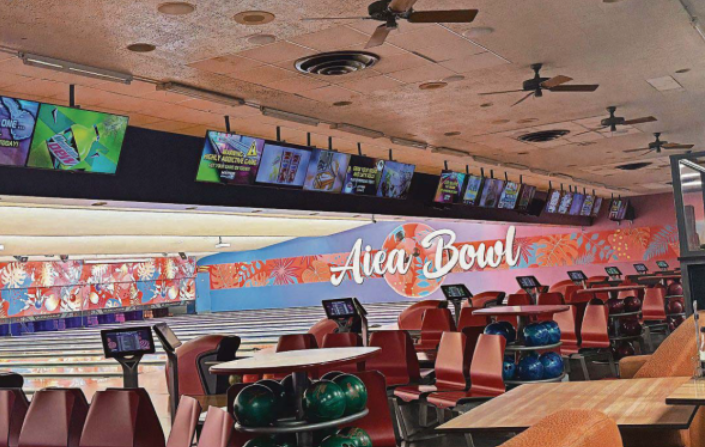বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল কোলে নেওয়া ধলেশ্বরী নদী শুধু একখণ্ড জলধারা নয়—এটি ইতিহাস, জনপদ, শিল্প–বাণিজ্য, বন–জীববৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক সত্তার পরিপূর্ণ বহমান দলিল। প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ধলেশ্বরী পদ্মা–যমুনার জলরাশি বহন করে ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বুড়িগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং এই ভূখণ্ডের অর্থনীতি, পরিবেশ ও জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। পূর্ববর্তী লেখাগুলোতে ‘ধোলেশ্বরী’ বানানটি ভিন্ন ছিল; শুদ্ধ রূপ ধলেশ্বরী—এখানে তাই সংশোধিত হয়েছে।
উৎপত্তি, গতিপথ ও ভূ-প্রকৃতি
ধলেশ্বরী আদতে পদ্মা নদীর একটি প্রাচীন শাখা। মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর–সিঙ্গাইর সন্নিকট থেকে শাখাটি বেরিয়ে এসে নবাবগঞ্জ, দোহার, কেরানীগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ অতিক্রম করে বুড়িগঙ্গায় মিশে যায়।

• দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা: মৌসুমি বৈচিত্র্যে ভরা—বর্ষায় কোথাও ৪–৫ কিমি প্রশস্ত, শুষ্কে ন্যূনতম ২০০–৩০০ মি পর্যন্ত সরু হয়ে আসে।
• ভূ-প্রকৃতি: দুই তীরে বালুকাময় চর, পলিমাটির ধূসর দ্বীপ, মাঝেমধ্যে বালির চরে গাছগাছালি। পলি-সঞ্চয়ের গুণে মাটি উর্বর—ধান ও পাটের জন্য আদর্শ।
• হাইড্রোলজি: পদ্মা ও যমুনার প্রবাহ-সমন্বয়ে ধলেশ্বরী ঢাকার প্রাকৃতিক বন্যা-প্রশমক হিসেবে কাজ করত; পানি বৃদ্ধির সময় অতিরিক্ত চাপ সামলে রাখত।
ঔপনিবেশিক নৌ-বাণিজ্য: কাঁচা পাট থেকে কলকাতা বন্দর
১৯শ শতকের মাঝামাঝি, বিশেষ করে ১৮৫০–১৯৩০—এই আট দশকে ধলেশ্বরী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম কাঁচামাল রুট ছিল।
• কাঁচা পাট: মানিকগঞ্জ–সিঙ্গাইর অঞ্চলের পাট ধলেশ্বরীর খেয়াঘাট ধরে বড় বজরায় লোড হয়ে সদরঘাট, সেখান থেকে স্টিমারে কলকাতা পৌঁছাত।
• চাল ও গুড়: নবাবগঞ্জ–দোহার এলাকার খোলা জলে ভেসে আসত বস্তাবন্দি চাল, গুড় ও তিলের খৈ।
• কাস্টমস ও ঘাট: ব্রিটিশরা “কুন্ডু ঘাট কাস্টমস” নামে একটি শুল্কঘর বসিয়েছিল নবাবগঞ্জে—সেখানেই রাজস্ব আদায় হতো।

জনপদ গড়ে ওঠা ও নগর বিকাশ
- মানিকগঞ্জ সদর ও সিঙ্গাইর:নদীকেন্দ্রিক গঞ্জ; চৌমুহনী হাট ধলেশ্বরীর ডাঙাপাড়ে সাপ্তাহিক বাণিজ্যের প্রাণ ছিল।
• নবাবগঞ্জ ও দোহার: ১৮৬০-এর দশকে নানাবিধ ঘাট স্থাপনার কারণে “নৌ-বাজার শহর” নামে পরিচিতি পায়।
• কেরানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল: ১৯৫০-৬০-এর দশকে চামড়া, ইট ও ধাতুব্যবসা গড়ে ওঠে—নদীপথে মালামাল আনা-নেওয়া সহজ ও সস্তা ছিল।
• স্বয়ং ঢাকা শহর: ধারাবাহিক যোগাযোগের ফলে সদরঘাট রূপ নেয় পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম নৌ-টার্মিনালে, যা নগরায়ণের ছাঁচ বদলে দেয়।
নৌযান, লঞ্চ ও বাজরার কথকতা
ধলেশ্বরীর জাহাজ-সংস্কৃতিকে বুঝতে ‘বাজরা’ শব্দটির দিকে তাকাতে হয়—চওড়া তলা ও অগভীর ড্রাফটের এই নৌযানই পাট-চালের প্রধান বাহক।
• বাজরা: ২৫–৪০ মি দীর্ঘ, ২০০–৩০০ টন ধারণক্ষমতা।
• লঞ্চ ও স্টিমার: পাকিস্তান আমলে পেট্রল-চালিত লঞ্চ আসে; ১৯৮০-এর পর ডিজেল স্টিমার জনপ্রিয়।
• খেয়া নৌকা: দুই তীরের গ্রামীণ যাতায়াতের মেরুদণ্ড—মাছ, সবজি, খড়, গবাদিপশু পারাপারে অনন্য।
কৃষি ও চরজীবন: পলি, ফসল, লোনাপানি-পরিবর্তন
প্রতি বর্ষায় নদী বয়ে আনা পলিতে চর সৃষ্টি হয়—এসব চরে মৌসুমি চাষ আজও টিকে আছে।
• ধান ও পাট: প্রধান ফসল; পলি-সঞ্চয়ে ধানের ফলন ১২–১৫ মণ/বিঘা পর্যন্ত বাড়ে।
• সবজি বাগান: শীতকালে ভুট্টা, গাজর, মরিচ; গ্রীষ্মে কাঁঠাল, লাউ, কুমড়া।
• চরবাসীদের জীবন: নদীর ওঠানামা মানেই স্থানান্তরিত ঘর-বসতি; বাঁশের মাচায় টাঙানো বসতঘর, ভাসমান সবজি-ক্ষেত ‘ধাপ’—চর-সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বন ও জীববৈচিত্র্যের নন্দন
ঈদ-খ্রিস্টমাসের আগেই দোহার–নবাবগঞ্জের বনাঞ্চলে শোনা যেত শিয়ালের ডাক; শীতকালে চর জুড়ে কানাডিয়ান বারহাঁস, সারস, গ্রেবি হাঁসের আনাগোনা।
• উদ্ভিদ: কড়ই, বাবলা, হিজল, বরুণ—গভীর শিকড় পলি ক্ষয় ঠেকাত।
• স্তন্যপায়ী: শিয়াল, বেজি, জংলি বিড়াল; মাঝেমাঝে গুঁইসাপও দেখা যেত।
• পাখি: দেশি মাছরাঙা, ধলাপেট কাস্তেচরা, শীতকালীন সরালি।
দুঃখজনকভাবে অনিয়ন্ত্রিত বন-উচ্ছেদ, ইটভাটা ও স্থায়ী বসতির চাপে ১৯৫০–২০২৫—এই ৭৫ বছরে প্রায় ৬০–৭০% গাছগাছালি হারিয়েছে।
মাছ ও জলজ অর্থনীতি
ধলেশ্বরীর দেশি মাছ একসময় ঢাকাইয়া সেলিব্রিটিদের দাওয়াতের বিশেষ পদ ছিল।
| প্রজাতি | ধরার মৌসুম | বাজার-সুনাম |
| রুই, কাতলা, মৃগেল | বর্ষা শেষে | ‘স্থুল মাপের নদী-রুই—সেরা’ |
| চিতল, বোয়াল | ভাদ্র-আশ্বিন | অভিজাত হোটেল-রেস্তোরাঁয় প্রিমিয়াম |
| শোল, গজার, আইড় | শীতকালে | কেরানীগঞ্জের ‘টাটকা শোল ভুনা’খ্যাত |
১৯৯০-এর পর শিল্পবর্জ্য, প্লাস্টিক ও অপরিকল্পিত কালভার্ট-বাঁধের কারণে মৎস্যসম্পদ ৪০–৫০% কমে যায়। ‘জল-আটকানো ঢাকা প্রকল্প’ (২০১৮) অনুযায়ী ৩ কোটি চারা মাছ প্রতি বর্ষায় অবমুক্ত হচ্ছে, তবু দূষণ-নিয়ন্ত্রণের অভাবে পুনর্জন্ম ধীর।

সাহিত্য, লোকগাথা ও ধর্মীয় আচার
- গান-বাউল:নবাবগঞ্জের পালাগানে “ধলেশ্বরীর ঢেউ” উপমা প্রেম-বিরহে ভাসে।
• লোককথা: কেরানীগঞ্জে প্রচলিত ‘ধলেশ্বরীর সোনালি নুলি’—নদীতে নেমে সোনা কুড়ানোর রূপকথা।
• ধর্মীয় মেলা: সিঙ্গাইরের ‘বরুণ দেবতা স্নান’—বর্ষার প্রথম পানিতে হিন্দুদের পুণ্যস্নান; ঈদ উপলক্ষে নদীপাড়ে মুসলিম ‘নৌকা বাইচ’ ঐতিহ্য।
নদীর পরিবর্তন: বাঁধ, দখল ও দূষণ
গত ৫০ বছরে ধলেশ্বরী তিনটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—
দখল: অবৈধ বাঁধ-মাটি ভরাট; ২০২০-এর জরিপে ৭৩ কিমির মধ্যে ১৮ কিমি অংশে ৩,২০০-এরও বেশি অবৈধ স্থাপনা।
দূষণ: চামড়াশিল্প, প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ও ইটভাটার বর্জ্যে পানির BOD-COD ২–৩ গুণ বেড়েছে।
নাব্যতা হ্রাস: অপরিকল্পিত কালভার্ট-সেতু, চিনামাটির ভরাট, বালু উত্তোলনে নতুন চর গড়ে ওঠায় নৌ-চলাচল বিঘ্নিত।
সমসাময়িক সংকট: জলবায়ু ও নগর চাপ
- জলবায়ু পরিবর্তন:বর্ষায় হঠাৎ বন্যা, শুষ্কে পানিশূন্যতা; ফ্ল্যাশ-ফ্লাডে ঢাকার দক্ষিণাঞ্চল প্লাবিত।
- নগর চাপ: কেরানীগঞ্জ-মোক্তারপুরে কংক্রিটের জঙ্গল, যেখানে একসময়ে বাঁশঝাড়-কাঁঠাল বাগান ছিল।
• শিল্পবর্জ্য আইন: পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধন ২০১০) ধারা ১২ নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপে শাস্তিযোগ্য—কিন্তু প্রয়োগ দুর্বল।

পুনরুদ্ধারের পথ: নীতি, প্রযুক্তি ও সামাজিক উদ্যোগ
| উদ্যোগ | মূল বৈশিষ্ট্য | অগ্রগতি |
| ধলেশ্বরী ড্রেজিং প্রকল্প (২০১৯-) | ৩২ কিমি খনন; নাব্যতা ২০ ফুটে তোলা | ৪৫% সম্পন্ন |
| বর্জ্য-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (কেরানীগঞ্জ) | তরল চামড়া-বর্জ্য শোধন | স্থাপনা সম্পন্ন; পূর্ণক্ষমতায় চালু নয় |
| সবুজ চর-বনায়ন কর্মসূচি | ১০ লাখ গাছ; ৫ বছরের মনিটরিং | ২.৮ লাখ গাছ বেঁচে আছে |
| ‘ধলেশ্বরী বন্ধু’ (স্বেচ্ছাসেবী) | নদী-পরিচ্ছন্নতা, স্কুলভিত্তিক সচেতনতা | প্রতি মাসে ‘ক্লিন-আপ ডে’ |
প্রযুক্তিগতভাবে রিমোট-সেন্সিং ডেটায় চর-উৎপত্তি পূর্বাভাস, আইওটি-সেন্সরে পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ—এসবই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ।
ধলেশ্বরী বাঁচলে বাঁচবে এই অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও নগরের জলনিকাশ ব্যবস্থা। দুই শতাব্দী ধরে যে জলপথ মানুষকে রুটি-রোজগার, শিল্প-বাণিজ্য ও সংস্কৃতি দিয়েছে, তা আজ মানুষের হাতেই বিপন্ন।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট