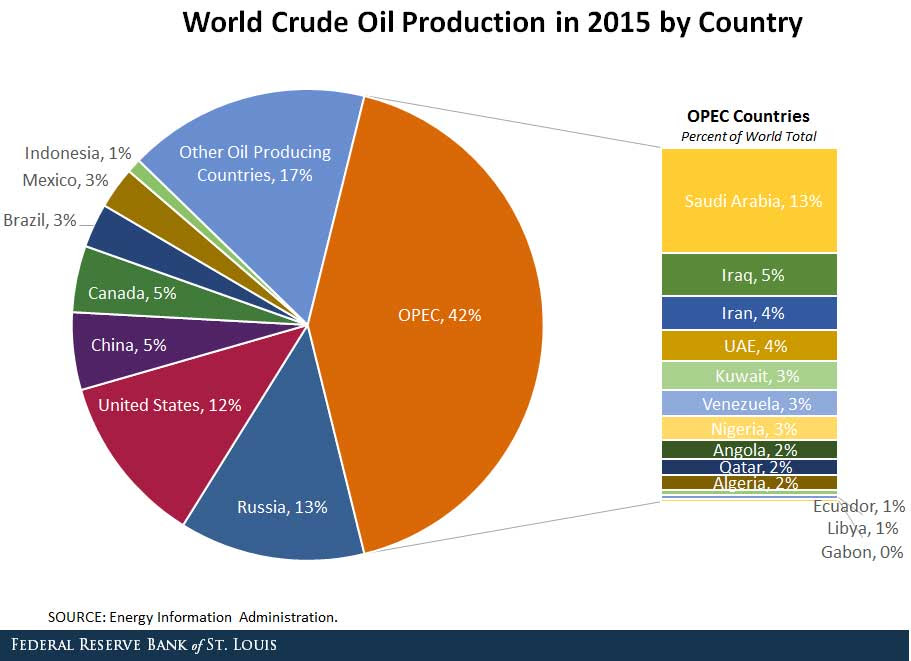বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান ও চীন দীর্ঘদিন ধরে বড় বিনিয়োগকারী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ, অবকাঠামো, শিল্প পার্ক, বন্দর, রেললাইন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল—প্রায় সব বড় প্রকল্পেই দুই দেশের বিনিয়োগের ছাপ রয়েছে। কিন্তু গত এগারো মাসের হিসাব বলছে, আগের তুলনায় জাপান ও চীনের বিনিয়োগের গতি স্পষ্টভাবেই মন্থর। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গত ১০ বছরে যে হারে বিনিয়োগ হয়েছে, সেই হার এই সময়ে দেখা যাচ্ছে না। কেন এমন হচ্ছে, তা নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক ও বিনিয়োগ বিশ্লেষকরা চিন্তিত।
বিনিয়োগের চিত্র
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাথমিক পরিসংখ্যান ও বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা)–এর তথ্য অনুযায়ী, গত ১১ মাসে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহে জাপান ও চীনের অংশ আগের তুলনায় কমেছে। জাপানের বিনিয়োগ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কিছু নতুন প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তব রূপ পায়নি। চীনের দিকেও বড় প্রকল্পের নতুন অর্থছাড় বা নির্মাণ অগ্রগতি কম দেখা যাচ্ছে। অথচ ২০১৩ থেকে ২০২২—এই ১০ বছরে বাংলাদেশে অবকাঠামো খাতে দুই দেশের মিলিত বিনিয়োগ ছিল কয়েক বিলিয়ন ডলার।

কারণসমূহ
বিনিয়োগ স্থবির হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের কারণে বাংলাদেশ সরকার ডলার খরচে কড়াকড়ি চালু করেছে। অনেক প্রকল্পের ঋণ বা কনট্রাক্টরের পেমেন্ট সময়মতো না হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা নতুন প্রকল্পে আগ্রহ হারিয়েছে।
দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। গত এক বছরে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অস্থিরতা, বিক্ষোভ, সহিংসতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার নিয়ে সমালোচনা—এগুলো বিনিয়োগকারীর আস্থায় প্রভাব ফেলেছে। বিনিয়োগকারীরা স্থিতিশীলতা চান, যাতে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প নির্বিঘ্নে চালানো যায়।
তৃতীয়ত, বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার প্রভাব। বৈশ্বিক পর্যায়ে সুদের হার বেড়ে যাওয়া, বৈদেশিক ঋণ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে জাপান ও চীন দুই দেশেই বিদেশে বিনিয়োগের পলিসি কিছুটা রক্ষণশীল হয়েছে। চীন বিশেষ করে নিজ দেশের ঋণঝুঁকিতে মনোযোগী হচ্ছে। জাপানও এশিয়ার অন্য বাজারে বিনিয়োগ বৈচিত্র্যে জোর দিচ্ছে।
চতুর্থত, প্রকল্প বাস্তবায়নের জটিলতা। বাংলাদেশে জমি অধিগ্রহণ, আমলাতান্ত্রিক দেরি, দুর্নীতি, অনুমোদন প্রক্রিয়া—সব মিলিয়ে বড় প্রকল্প সময়মতো শেষ করা কঠিন। বিনিয়োগকারীরা বারবার এসব সমস্যার সমাধান চেয়েছে।

উন্নয়নের ভবিষ্যৎ
বাংলাদেশ সরকার অবশ্য বলছে, এই ধীরগতির মানে বিনিয়োগ পুরোপুরি থেমে গেছে—তা নয়। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে জাপান ও চীনের কয়েকটি প্রকল্পে নতুন করে আলোচনা চলছে। তবে আগের মতো বিপুল অঙ্কের প্রকল্প একসঙ্গে ঘোষণা বা বাস্তবায়ন এখন আর হচ্ছে না।
অর্থনীতিবিদরা পরামর্শ দিচ্ছেন, বিনিয়োগের আস্থা ফেরাতে ডলার সংকট মোকাবিলা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রশাসনিক সংস্কার এবং সুশাসন খুবই জরুরি। না হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমতে কমতে অন্য দেশে সরে যেতে পারে, যা রপ্তানি, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির জন্য বড় ঝুঁকি হবে।
গত ১০ বছরে বাংলাদেশে জাপান ও চীনের বিনিয়োগ অর্থনীতিকে বেগ দিয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন—সব ক্ষেত্রেই দুই দেশের অর্থ ও প্রযুক্তির ছাপ রয়েছে। কিন্তু গত ১১ মাসের বিনিয়োগ প্রবাহে স্পষ্ট মন্থরতা সরকার ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক সংকেত দিচ্ছে। তাই বিনিয়োগকারীর আস্থা ফেরাতে বাস্তবসম্মত, স্বচ্ছ এবং টেকসই নীতি প্রয়োজন। অন্যথায় অর্থনৈতিক সম্ভাবনা পূরণে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়তে পারে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট