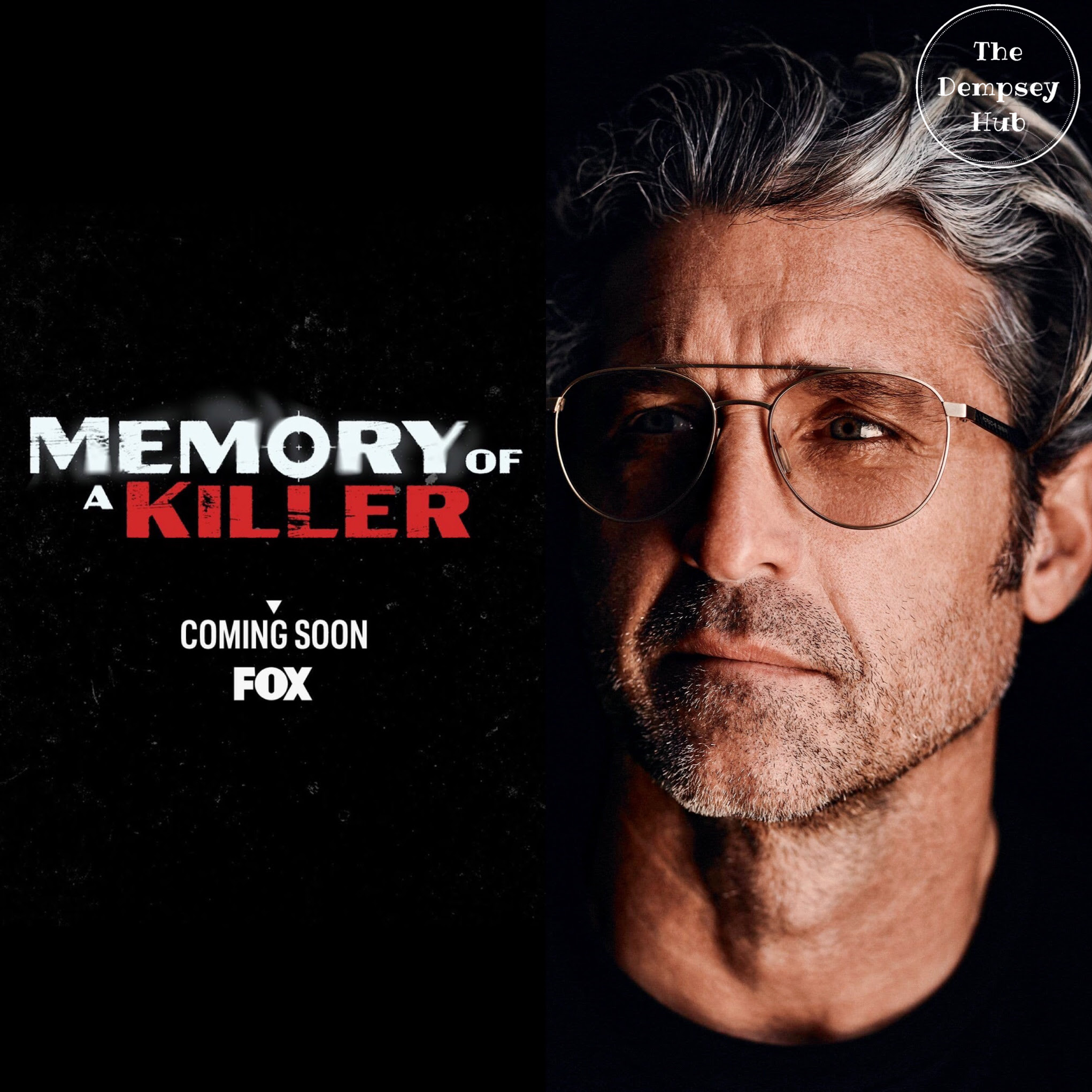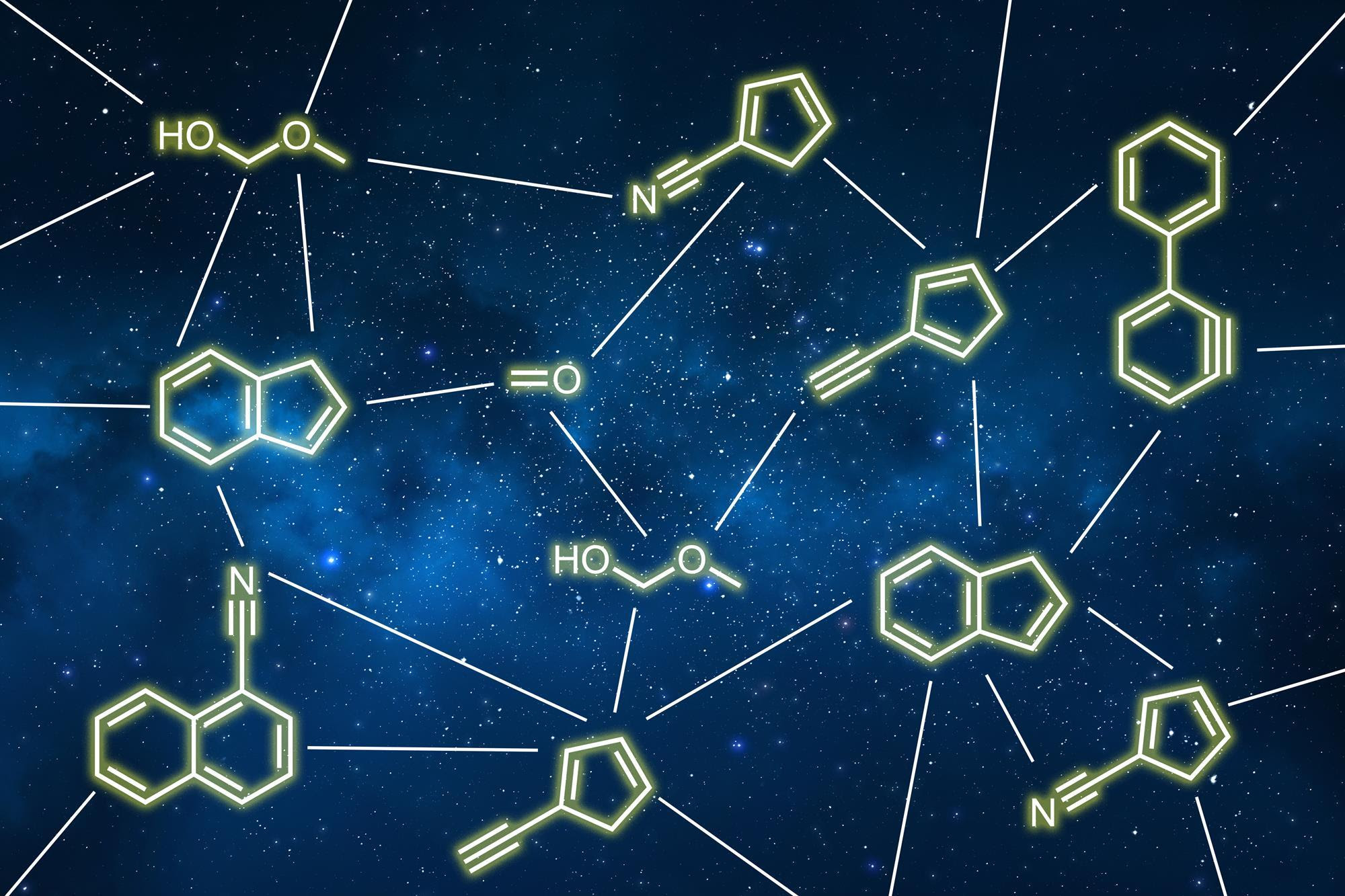চোখের জল রঙহীন বলা হলেও, বাংলাদেশে অগণিত অশ্রু নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে, দরজার আড়ালে—যেখানে কেউ তা দেখে না।
একজন মা ভোর হওয়ার আগেই জেগে ওঠেন, বুক ভরে ওঠে আতঙ্কে—কারণ ঘুম আবারও তাকে ফাঁকি দিয়েছে। এক কারখানার শ্রমিক কাঁপা হাতে অন্তহীন শিফটে কাজ চালিয়ে যান। এক কিশোরী তার ভাইবোনদের সঙ্গে হাসলেও, ভেতরে ভয়াবহ ঝড় বয়ে যায়।
এগুলো কেবল বিচ্ছিন্ন গল্প নয়, বরং মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করা মানুষের বাস্তবতা। অনেকের নির্ণয় হয়েছে, অনেকের হয়নি। তবুও সবাইকে বহন করতে হয় এক অবহেলিত বোঝা—যা সমাজ দেখে দুর্বলতা, লজ্জা কিংবা নীরবতা হিসেবে।
কিন্তু আশেপাশে হাত বাড়ানোর কেউ নেই, শোনার কান নেই, আর সহায়তার জন্য উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা নেই।
নিঃশব্দ দৈনন্দিন যুদ্ধ
পরিসংখ্যান পুরো চিত্র তুলে ধরে না, তবে কঠিন বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলে।
২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত গবেষকরা সারা দেশের হাসপাতালে ৭,৫০০ জন নারীকে নিয়ে জরিপ চালান। দেখা যায়, প্রতি চারজন গর্ভবতী বা নবমাতার মধ্যে তিনজনই বিষণ্নতা বা উদ্বেগে ভুগছেন, এবং অর্ধেকের বেশি একই সঙ্গে উভয়ের শিকার। আনন্দময় হওয়ার কথা থাকা সময়টাই অনেকের কাছে রূপ নেয় নির্ঘুম রাত, হতাশা আর ভীতিকর চিন্তায়। (সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন)

শিশু ও কিশোররাও এর বাইরে নয়। ভয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের কেও চেপে ধরে। ২০২৪ সালের মে মাসে এসএসসি ফল প্রকাশের দিনে অন্তত আটজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে—যা প্রমাণ করে, অনেকের কাছে এক টুকরো কাগজই জীবনের সমাপ্তি মনে হতে পারে। (সূত্র: ডেইলি অবজারভার)
প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও প্রায় পাঁচ জনে একজন বিষণ্নতা বা উদ্বেগে ভোগেন। কিন্তু চিকিৎসা পান খুব কমই। কারণ, খরচ বহন করা যায় না, সেবা পাওয়া যায় দূরে, অথবা সামাজিক লজ্জায় কেউ মুখ খুলতে পারেন না।
১৭ কোটির বেশি মানুষের দেশে আছেন মাত্র ২৬০ জন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আর ৫৬৫ জন মনোবিজ্ঞানী—যাদের বেশির ভাগই শহরে। ফলে গ্রামীণ বাংলাদেশ প্রায় অন্ধকারেই পড়ে থাকে।
নীরবতার কারণ
সর্বশেষ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ হয়েছিল ২০১৮ সালে। এরপর দেশ পার করেছে মহামারি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা আর জলবায়ু বিপর্যয়। এসব আঘাত মানুষের ভঙ্গুর মানসিকতাকে আরও দুর্বল করেছে। কিন্তু নতুন কোনো তথ্য নেই, কতটা গভীর হয়েছে ক্ষত, তা জানার।
যারা সাহায্য চাইতে চাইলেও বাধার মুখে পড়েন। কাউন্সেলিং মানে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া, অস্বাভাবিক খরচ আর সামাজিক কলঙ্ক—যা রোগের আগেই মানুষকে ভেঙে দেয়।

নারীরা এখানে আরও অসহায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তারা বন্দি, হতাশার কথা বললে উপহাস বা নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তরুণদের কাছে ব্যর্থতা মানে চূড়ান্ত পতন। আর দরিদ্রদের কাছে টিকে থাকাই প্রধান, মানসিক সুস্থতা সেখানে বিলাসিতা।
কাগজে-কলমে বাংলাদেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশ যুক্ত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ উদ্যোগের সঙ্গে। মানসিক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ও টেলিমেডিসিন সেবা সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নেয়নি। অধিকাংশ জেলায় কার্যকর কোনো সেবা নেই। বাজেট সীমিত, অবকাঠামো দুর্বল, সচেতনতামূলক প্রচারও বিরল। আকাঙ্ক্ষা আর বাস্তবতার ফাঁক ক্রমেই আরও জীবন গ্রাস করছে।
কী পরিবর্তন প্রয়োজন
মানসিক স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়—এটি একটি জনস্বাস্থ্য ইস্যু। একে অবহেলা করা জাতীয় ব্যর্থতা। বিশেষজ্ঞরা কিছু জরুরি পদক্ষেপের কথা বলছেন—
১. প্রতি দুই থেকে তিন বছরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ পরিচালনা।
২. সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া—কমিউনিটি সেন্টার, মোবাইল ক্লিনিক, স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে কাউন্সেলিং, এবং টেলিকাউন্সেলিং ব্যবস্থা।
৩. আরও বেশি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী ও কাউন্সেলর তৈরি ও নিয়োগ করা—বিশেষত নারী পেশাজীবীদের।
৪. স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা।
৫. গণমাধ্যম, ধর্মীয় নেতা ও সম্প্রদায়কে যুক্ত করে কলঙ্কবিরোধী প্রচার চালানো।
প্রতিটি অশ্রুত কান্না কেবল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়—এটি এক সম্মিলিত ক্ষতি।

বাংলাদেশ চাইলে নীরব থেকে যাবে, হয়ে উঠবে নিঃশব্দ মানুষের দেশ। আবার চাইলে পদক্ষেপ নিতে পারে—একটি ক্লিনিক খুলে, একটি মনোযোগী কান বাড়িয়ে, একটি জীবন রক্ষা করে।
কারণ যদি একটি জীবনও হতাশার কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনা যায়, গল্পটি বদলে যায়। আর এই পরিবর্তন শুরু হয় তখনই, যখন নীরবতা ভাঙতে শুরু করে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট