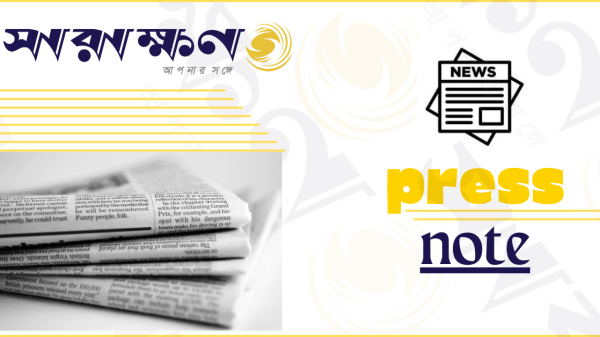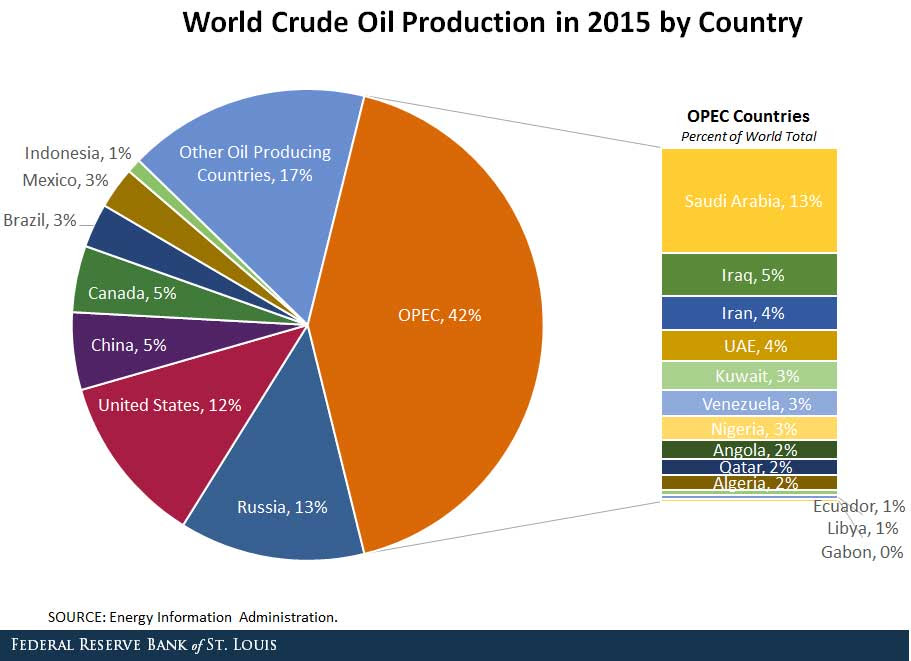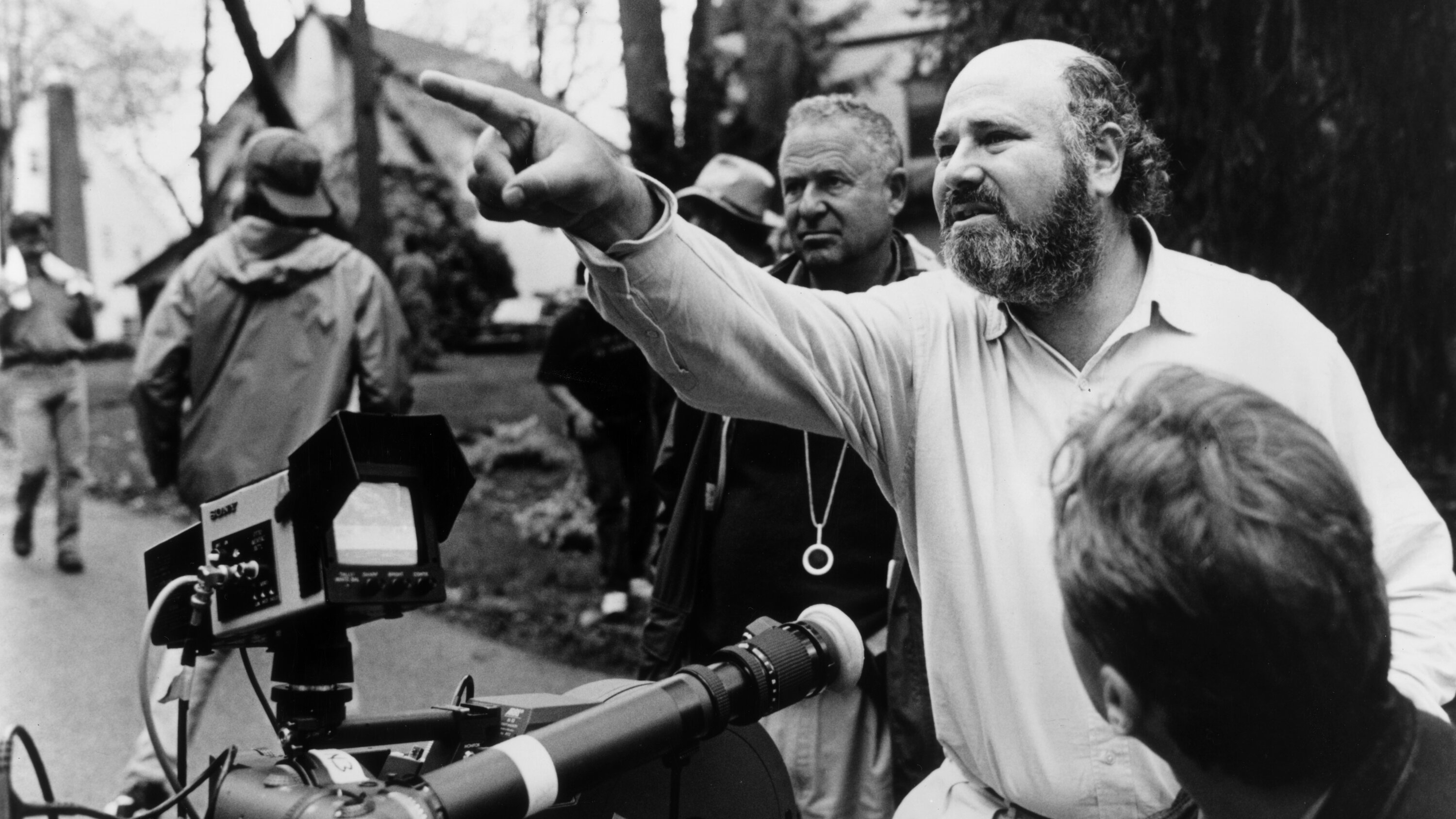সমকালের একটি শিরোনাম “বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর হওয়ার পথে ঢাকা”
রাজনীতি, রুটি-রুজি, শিক্ষা কিংবা চিকিৎসা– প্রায় সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে রাজধানী ঢাকা। প্রতিদিন এ মহানগরীতে অন্তত দুই হাজার নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে। এ কারণে দিন দিন বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে রাজধানী; নাগরিক সেবা হচ্ছে সংকুচিত। জনসংখ্যার ভারে নাগরিক সেবা এলোমেলো। যানজট, খাদ্যে ভেজাল, দূষিত বাতাস– কোনো কিছুই বাগে আসছে না। নিকট ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে উঠতে পারে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়েছে। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ঢাকা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহর।
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ‘বৈশ্বিক নগরায়ণ ধারণা-২০২৫’ প্রতিবেদনে এই অনুমান করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান জনবহুল নগর এখন ঢাকা। শীর্ষে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা। তবে যে হারে ঢাকায় জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে, তাতে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে জাকার্তাকে ছাড়িয়ে যাবে ঢাকা। তখন ঢাকা হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরী। জনসংখ্যা হবে প্রায় ৫ কোটি ২১ লাখ।
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সংজ্ঞা প্রাক্কলন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এতে বলা হয়, দ্বিতীয় স্থানে থাকা ঢাকার বর্তমান জনসংখ্যা ৩ কোটি ৬৬ লাখ। শীর্ষে থাকা জাকার্তার জনসংখ্যা ৪ কোটি ১৯ লাখ।
তবে জাতিসংঘের এই তথ্যের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যে বড় ধরনের ফারাক রয়েছে। বিবিএসের সর্বশেষ ২০২২ সালের জনশুমারি প্রতিবেদন বলছে, ঢাকার দুই সিটি মিলে জনসংখ্যা ১ কোটি ২ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮৬ জন। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি– ৫৯ লাখ ৯০ হাজার ৭২৩ জন এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৪৩ লাখ ৫ হাজার ৬৩ জন।
বিবিএসের উপাত্তে দেখা যায়, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে প্রতি বর্গকিলোমিটারে সর্বাধিক ৩৯ হাজার ৪০৬ জনের বাস। দুই সংস্থার উপাত্তে অর্ধেকেরও বেশি ব্যবধান কেন– এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ও জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ড. আমিনুল হক সমকালকে বলেন, দুটিই সঠিক। জাতিসংঘের সামাজিক পরিষদের সংজ্ঞা এবং তাদের প্রাক্কলনের ভিন্নতার কারণে বিবিএসের তথ্যের সঙ্গে তথ্যের ব্যবধান রয়েছে। জাতিসংঘ ও বিবিএস দুই সংস্থার প্রতিবেদনই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, দুই কোটি হোক আর তিন কোটি– কোনোটাই বাসযোগ্য ঢাকার জন্য উপযোগী নয়।
আজকের পত্রিকার একটি শিরোনাম”জাতীয় সংসদ নির্বাচন: জামায়াত জোটের আসন সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত”
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী সমমনা দলগুলোকে নিয়ে আসন সমঝোতার আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত করেছে। যোগ্যতা ও সম্ভাবনার বিচারে সমমনা দলগুলো থেকে প্রার্থীরা কোন কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সে হিসাবনিকাশও একেবারে শেষ পর্যায়ে। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসে না হলেও আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই আসন সমঝোতার প্রক্রিয়া শেষ করার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। সমঝোতার বিষয়ে এখনো কিছু আলোচনা বাকি আছে জানিয়ে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা তো আগেই নিজেদের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছি। এখন যেহেতু অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে… এখানে আলাপ আলোচনার অনেক বিষয় আছে।’
এখন পর্যন্ত জামায়াতসহ সমমনা আটটি দল এক হয়ে যুগপৎ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। এর মধ্যে ছয়টিই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল। জামায়াত ছাড়া অন্য দলগুলো হলো—ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই আট দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও অন্তত দুই থেকে তিনটি দল। সব মিলিয়ে ১০ অথবা ১১টি দলের মধ্যে আসন সমঝোতা হবে বলে জানা গেছে।
ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। জামায়াত ও সমমনা দলগুলোর সূত্র বলেছে, এর আগেই সমঝোতার ভিত্তিতে প্রতিটি আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে তারা। সমন্বিত কৌশলে ভোটযুদ্ধে লড়ার পরিকল্পনা করছেন দলগুলোর নেতারা। এ জন্য জনপ্রিয়তা, নেতৃত্বের সক্ষমতা ও সর্বোপরি নির্বাচনে জিতে আসার মতো ব্যক্তিরা প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন বলেন, ‘কোন দলের কোন প্রার্থী কোন জায়গায় ভালো অবস্থানে আছেন; সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা, জরিপ চলছে। যে দলের প্রার্থীই হোক না কেন, আমরা এবার জোটের সর্বোচ্চসংখ্যক প্রার্থীকে জিতিয়ে সংসদে যেতে চাই।
বণিকবার্তার একটি শিরোনাম “বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের হার বিশ্বে এখন সর্বোচ্চ”
ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ইউক্রেনে পুরোদস্তুর যুদ্ধ চলছে প্রায় চার বছর ধরে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশটিতে সর্বাত্মক হামলা করে রাশিয়া। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির ব্যাংক খাতের অবস্থাও এতটা নাজুক হয়নি, যতটা হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত। ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে দেশটির খেলাপি ঋণের হার ছিল ২৬ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৩৬ শতাংশই খেলাপি হয়ে গেছে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও প্রভাবশালী গবেষণা সংস্থার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের যে হার, সেটি এখন গোটা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এমনকি কোনো দেশের খেলাপি ঋণ ৩০ শতাংশের বেশি পাওয়া যায়নি। গত কয়েক বছর যুদ্ধবিধ্বস্ত, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দায় থাকা দেশগুলোর খেলাপি ঋণের হারও বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। আরব বসন্তের সূত্রপাত ঘটানো এবং বর্তমানে চরম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে থাকা তিউনিসিয়ার ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার এখন ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত লেবাননের খেলাপি ঋণ ২৪ শতাংশের নিচে। আর ইউক্রেনের সঙ্গে প্রায় চার বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া রাশিয়ায় খেলাপির হার মাত্র ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ। যদিও ঐতিহাসিকভাবে অলিগার্ক প্রভাবিত রাশিয়ায় খেলাপি ঋণের হার বরাবরই উচ্চ ছিল।
বিনিময় হারে চরম অস্থিরতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ অর্থনৈতিক নানা সংকটে থাকা এশিয়া, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর খেলাপি ঋণের হার এখন নিম্নমুখী। যেমন তুরস্কের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ২ দশমিক ২৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এক দশক আগে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ইউরোপের দেশ গ্রিসের খেলাপি ঋণের হার এখন ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও স্থানীয় মুদ্রার রেকর্ড পতনের মুখে থাকা আর্জেন্টিনার ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের হার ১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমেছে। যেখানে চলতি সহস্রাব্দের শুরুতেও লাতিন আমেরিকার দেশটিতে খেলাপির হার ২০ শতাংশের বেশি ছিল।
বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার এখন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় বহু গুণ বেশি। এ অঞ্চলে কেবল শ্রীলংকার খেলাপি ঋণের হারই কিছুটা বেশি—১২ দশমিক ৬ শতাংশ। যদিও অর্থনৈতিক সংকটে পড়া দেশটি তিন বছর আগে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল। অর্থনীতির পাশাপাশি চরম রাজনৈতিক সংকটেও ছিল দ্বীপরাষ্ট্রটি। কিন্তু গত তিন বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি শ্রীলংকায় অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।
মানবজমিনের একটি শিরোন “মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা লাগামহীন শোষণের শিকার”
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের ওপর ‘ব্যাপক ও পদ্ধতিগত’ শোষণ, প্রতারণা এবং বাড়তে থাকা ঋণ-দাসত্ব (ডেট বন্ডেজ) চলছে। মালয়েশিয়ায় বর্তমানে ৮ লাখের বেশি বাংলাদেশি বৈধভাবে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করছেন। দেশটির বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশিরা সংখ্যায় সবচেয়ে বড়। জাতিসংঘের পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, হাজার হাজার শ্রমিক এখনও বাংলাদেশেই আটকে আছেন বা মালয়েশিয়ায় গিয়ে শোষণের শিকার হচ্ছেন। কারণ তাদের অনেকেই সরকার নির্ধারিত ফি-এর পাঁচগুণ পর্যন্ত অর্থ দিয়ে বিদেশে গিয়েছেন। মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি এসব কথা লিখেছেন সংগঠনটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে। এতে তিনি আরও লিখেছেন, অন্য নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে মালয়েশিয়ার নিয়োগদাতাদের হাতে শ্রমিকদের পাসপোর্ট জব্দ, ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি, চুক্তি এবং প্রতিশ্রুত সুবিধার মধ্যে বৈষম্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাগুলোর পর্যাপ্ত সহায়তার অভাব। এ বিষয়টি মালয়েশিয়ায় সাধারণ ঘটনা।
যেসব শ্রমিক যথাযথ নথিপত্র ছাড়াই সেখানে থাকেন, তারা গ্রেফতার, আটক, নির্যাতন এবং মালয়েশিয়ার কঠোর ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী দেশে ফেরত পাঠানোর ঝুঁকিতে থাকেন। এই আইন অনিয়মিত প্রবেশকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ নিয়মিত ইমিগ্রেশন অভিযান চালায় এবং প্রায় ১৮,০০০ অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীকে বিভিন্ন আটকশিবিরে বন্দি করে রেখেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন মালয়েশীয় কারখানার বিরুদ্ধে আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। একইভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন ফোর্সড লেবার রেগুলেশন, যা ২০২৭ সালে কার্যকর হবে, জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্যের ওপর বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে। শ্রমিকদের ঋণদাসত্ব ও প্রতারণার মতো ঘটনা এই নতুন বিধানের আওতায় পণ্য বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারির কারণ হতে পারে।
বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারসহ অন্য শ্রমিক পাঠানো ও শ্রমিক গ্রহণকারী দেশ, এবং যেসব দেশে এসব কোম্পানির সদর দফতর- যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরাষ্ট্র ও বৃটেন- তাদের দায়িত্ব হলো যেন শ্রম অভিবাসন এমনভাবে পরিচালিত হয়, যাতে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট সব দেশকে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্রুত অভিযোগগুলো তদন্ত করতে হবে এবং কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেছেন- ‘জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন বা কোনো ধরণের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা’ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন।
মালয়েশিয়া থেকে যারা পণ্য আমদানি করেন, সেই আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের উচিত ফেয়ার লেবার অ্যাসোসিয়েশনের গাইডেন্স ফর রেসপনিসিবল রিক্রুটমেন্টকে অনুসরণ করা। এই নির্দেশনায় ক্রেতাদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে যাতে তারা ‘দায়িত্বশীল নিয়োগের খরচ’ তাদের ব্যয়ের অংশ হিসেবে ধরে এবং সরবরাহকারীরা যাতে এই খরচ ইনভয়েসে যুক্ত করে। পাশাপাশি ক্রেতাদের উচিত অভিবাসী শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার উচিত অবিলম্বে শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করা। যেসব দেশের অর্থনীতি অভিবাসী শ্রমিকদের ঘামে চলমান- তাদের সবারই উচিত দ্রুত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া, যাতে আরও নিষেধাজ্ঞা ঝুঁকি এড়ানো যায় এবং হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ কমানো যায়।

 সারাক্ষণ ডেস্ক
সারাক্ষণ ডেস্ক