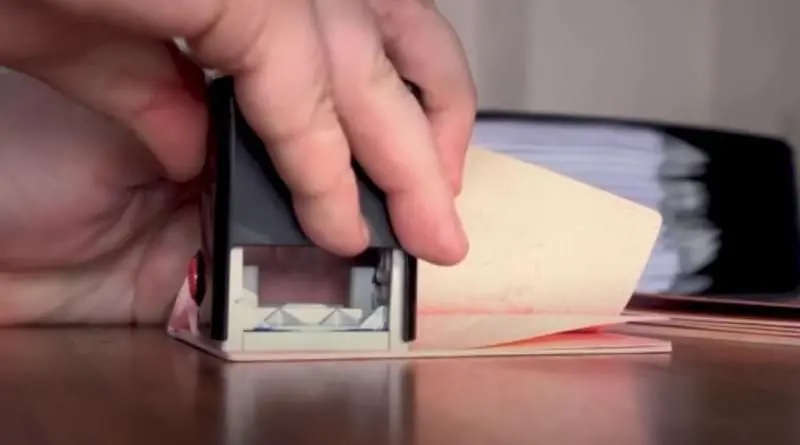সত্যি বলতে, বেশিরভাগ দিনই আমার মনে হয় সিউল কোনো শহরের চেয়ে দ্রুতগতির এক অ্যাসেম্বলি লাইনের মতো—যেখানে আমি ভুল ভঙ্গিতে পা রেখে হঠাৎ সেই লাইনের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। চারদিকে সবকিছুই চলে এক অদৃশ্য কনভেয়র বেল্টের মত দ্রুত, আর আমি যেন বিপরীত দিকে ভেসে যাওয়া কোনো ত্রুটিপূর্ণ পণ্য। গাড়িগুলো চলে না, বরং ঝাঁপিয়ে পড়ে—হঠাৎ, তীক্ষ্ণ, অনিয়মিত গতিতে—যা দেখে আমার মনে হয় হর্ন চাপিয়ে নাটকীয় প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু কোরিয়ায় হর্ন মানে সতর্কতা নয়; সেটা যেন যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা।
দরজাগুলো মানুষকে পুরোপুরি গিলে ফেলে—কেউ পেছনে দাঁড়িয়ে দরজা ধরে রাখে না। ফুটপাতজুড়ে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা কফির কাপগুলো যেন ক্লান্ত, ক্ষুদ্র সৈনিক—যারা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। পুরো পরিবেশটাই এমন এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদাসীনতার কোলাজ, যেখানে প্রতিটি ঘটনাই তুচ্ছ, কিন্তু মিলেমিশে মনে হয় সবাই যেন নিজের চারপাশে এক কঠিন, ঝকঝকে, ব্যক্তিগত ক্যাপসুল তৈরি করে বাঁচছে।
এই বিচ্ছিন্নতার বড় উৎস অবশ্যই আমাদের হাতে থাকা স্ক্রিন। আমরা এগুলোকে আধুনিক যুগের জপমালার মতো হাত দিয়ে ছুঁই—একধরনের মানসিক ভরসার জন্য। কিন্তু সমস্যা শুধু স্ক্রিন নয়; তার চেয়ে বড় হলো এই সাংস্কৃতিক মুহূর্ত, যেখানে প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তিগত ধর্মের বার্তাবাহক এবং সেই ধর্মেরই অনুসারী। যেন সমাজব্যাপী এক স্বীকৃত স্বকেন্দ্রিকতা। মেট্রোর নীরবতা শান্তি নয়—এটা এক বিশাল জনসমষ্টির নিজস্ব অন্তরসংলাপকে শব্দরোধ করে রাখার উপায়। শত মানুষের ভিড়ে থেকেও কেউ যেন কারও জন্য নেই। যেন সবাই অদৃশ্য নয়েজ-ক্যানসেলিং হেডফোন পরে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং এই নীরবতার নৃত্যে যোগ দেওয়া খুব সহজ। কোনো মানুষের সঙ্গে কথা না বলেই কিওস্ক থেকে কফি অর্ডার করা যায়। রেস্টুরেন্টে স্ক্রিন টাচ করে খাবার অর্ডার। রাতের বেলায় এক ক্লিকে কেনা জিনিসগুলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দোরগোড়ায়। কখনো কখনো সরকার পর্যন্ত ঘোষণা দেয়—মধ্যরাতের পর কেনাকাটা কমাও—যেন আকস্মিক কেনাকাটা কোনো নৈতিক অপরাধ, অথচ অর্থনীতির জন্য সেটাই মূল চালিকা শক্তি।
চারদিকে একধরনের ‘মেইন ক্যারেক্টার সিনড্রোম’। আগে ভেবেছিলাম এটা জেন-জেডদের একধরনের ব্যঙ্গাত্মক শব্দ, কিন্তু এখন মনে হয় এতে বিশাল ব্যাখ্যাশক্তি লুকিয়ে আছে। আমি চাই, তাই সেটা হওয়া উচিত। আমি অনুভব করছি, তাই তুমি মানিয়ে নাও। পৃথিবী, তুমি আমাকে মানো—কারণ আমি সব কিছুর নাজুক নায়ক।
এই আত্মকেন্দ্রিক চক্রে খুব সহজেই অন্যের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়েও প্রত্যেকেরই নিজের মতো ক্ষুধা, ভয়, গল্প আছে—যেগুলোর কোনোটাই আমরা জানি না।
এই বৈপরীত্য সবচেয়ে স্পষ্ট কোরিয়ার অদৃশ্য কিন্তু কঠোর সামাজিক কাঠামোয়। আছে একটি ভেতরের বৃত্ত—তাদের জন্য উষ্ণতা, দায়বদ্ধতা। আর আছে বাকি সবাই। তারা শীতল নয়, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত—যেন কোনো সফটওয়্যার, যার ব্যবহারবিধি কেউ কখনো লিখে রাখেনি। বিদেশি হিসেবে আপনি বুঝবেন, আপনাকে কেউ পুরোপুরি বাইরের মানুষ ভাবে না; বরং আপনি যেন মাঝখানে ঝুলে থাকা অজানা কোনো মান—যাকে সমীকরণে বসানো যাচ্ছে না। লোকজন আপনাকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না। ছোটখাটো কথা হয় না। রসিকতা ঝুঁকিপূর্ণ। আপনার অজানা থাকা অপ্রকাশিত নিয়মগুলো ধরে নেওয়া হয় স্বাভাবিক।
আর আছে তাকিয়ে থাকা। আঙুল তুলে দেখানো। ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে দেখা—যেন আপনি হয় অদ্ভুত, নয়তো আইন-শৃঙ্খলার সামান্য লঙ্ঘন। অবশ্য এই ‘সমষ্টিগত দৃষ্টি’ কোরিয়ানদের নিজেদের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়। এটা বৈষম্যমূলক নয়—সমানভাবে সবার ওপর প্রযোজ্য। কিন্তু এই অতিরিক্ত নজরের মাঝেও থাকে এক অপ্রত্যাশিত, প্রায় হতচকিত করে দেওয়া উষ্ণতা।

বাজারে এক বৃদ্ধা আমার হাত ছুঁয়ে বলেন, “ভালো করেছ”—যেন আমি কোনো বড় অর্জন করেছি। কী করলাম? দাঁড়িয়ে থাকা? শ্বাস নেওয়া? জানা নেই। কিন্তু ব্যাখ্যার চেয়ে তার সরল উচ্ছ্বাস আমাকে বেশি স্পর্শ করে। এক কিশোরী হেয়ারড্রেসার আমার মাথার আকার দেখে বিস্মিত—“এতো ছোট!”—যেন কোনো বিরল পাথর আবিষ্কার করেছে। এক অপরিচিত ব্যক্তি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করবে নাকি—সে ভাবনায় মাথা কাত করে—শেষমেশ শুধু নীরব এক মাথা নাড়ে। সেই নড়াচড়ায় থাকে অদম্য কৌতূহল আর অসহায় ভদ্রতা।
এক মোটরওয়ে সার্ভিস স্টেশনে আখরোট কেক বিক্রি করা একজন মানুষ নাটকীয় ভঙ্গিতে আমার ব্যাগে তিনটি অতিরিক্ত কেক ঢুকিয়ে দিলেন—যেন থিয়েটারের শেষ সারির দর্শকরাও যেন বুঝতে পারে তিনি কতটা উদার। কোরিয়ায় একে বলে ‘সার্ভিস’—যা চাই তার চেয়ে বেশি দেওয়ার অভ্যাস। এটা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনই কখনো কখনো অভিভূত করে। আমি মাথা নিচু করি, সম্মানসূচক ভাষা ঠিক করি—একজন সচেতন উদ্যানপালকের মতো শব্দ বাছাই করি। সেই মুহূর্তটা হয়ে ওঠে উষ্ণতার ক্ষুদ্র মরুদ্যান—এক পৃথিবীতে, যা প্রায়ই সংযোগের চেয়ে দক্ষতার দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে।
কোরিয়ানরা আমাকে সেরা আসনে বসিয়েছে, লাইনের সামনে নিয়ে গেছে, বারবিকিউতে সেরা টুকরো মাংস রেখেছে, এমনভাবে যত্ন করেছে যেন আমি কোনো বিদেশি অতিথি, যদিও আমি প্রায়ই ক্রিয়া-রূপ গুলিয়ে ফেলি। এসব আমাকে বিনয়ী করে, লজ্জা দেয়, কখনো কখনো ভীতও করে। কিন্তু এসব আচরণের কেন্দ্রে থাকে এক সরল গর্ব—সংস্কৃতির প্রতি গর্ব, খাবারের প্রতি গর্ব, আর অতিথিকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করার গর্ব।
আমি যখন ভাষা শিখতে শুরু করলাম, প্রশ্ন করলাম, ভুল করলাম—কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে—তখন এই দয়া আরও বাড়তে লাগল, যেন আলো দুটি আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ফিরছে।
দশকের পর দশক কেটে গেছে। শহর এখনও ছন্দে বাজে, গাড়ি এখনও ঝাঁপিয়ে চলে, কাপগুলো এখনও ফুটপাতে ছেড়ে রাখা ছোট্ট টিন সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এই দয়া—অরক্ষিত, অকৃত্রিম, কখনো কখনো প্রায় বিব্রতকরভাবে আন্তরিক—এটুকুই অপরিবর্তিত। এটাই এখানে থাকা শুধু সহনীয় নয়—অলৌকিক করে তোলে। মনে করিয়ে দেয়, আত্মমগ্ন মানুষের ভিড়ের মাঝেও কেউ হয়তো হঠাৎ আপনাকে তিনটি অতিরিক্ত আখরোট কেক দিয়ে দেবে—শুধুই দেওয়ার আনন্দে।

 ডেভিড এ. টিজার্ড
ডেভিড এ. টিজার্ড