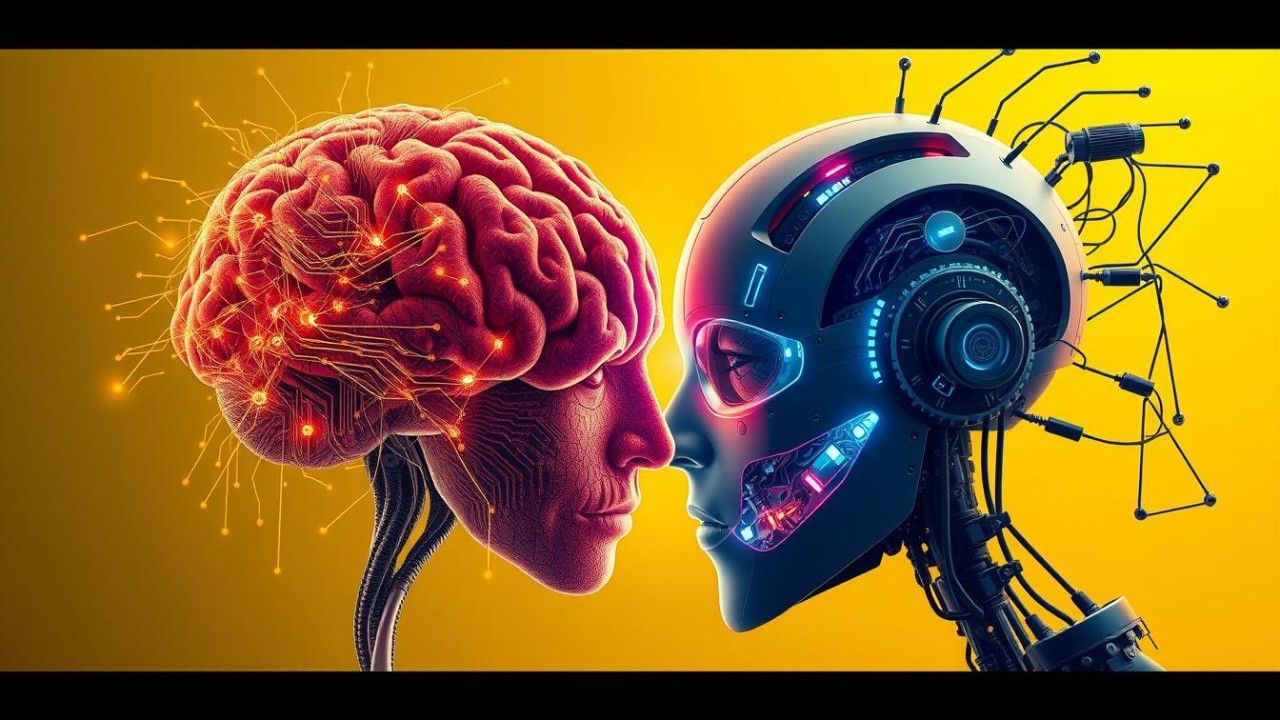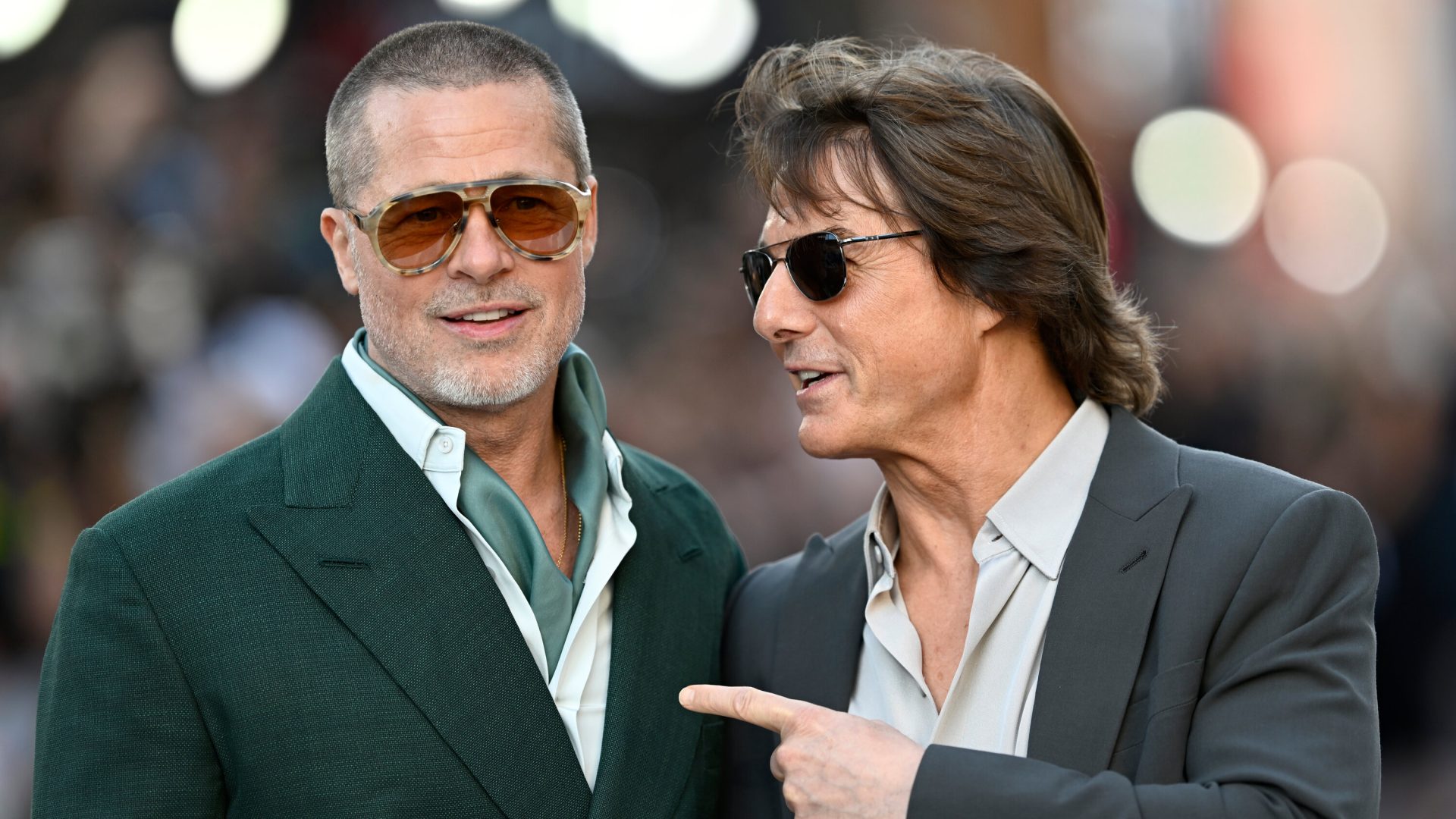তৃতীয় অধ্যায়
ভারতে নীল উৎপাদন অনেক প্রাচীন কাল থেকে হত বলে গ্রিসে ও রোমে এর নাম ‘ইন্ডিগো’ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে বিদেশি নীলকর সাহেবদের আবির্ভা? ঘটল-এরা ছিল সে যুগে দুর্ধর্ষ ভাগ্যান্বেষী। ঊনিশ শতকের ২ দশকের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপকভাবে নীলচাষ শুরু হলেও সব চাইতে বেশি জমি নীলচাষের আওতায় এসেছিল যশোর নদীয়া ও আজকের ২৪ পরগনার পূর্বাঞ্চলে।
সুন্দরবনের দক্ষিণের জমি লবণাক্ত হওয়ায় এখানে নীলচাষ করা হত না কিন্তু সুন্দরবনের উত্তরাংশের জমিতে প্রচুর নীলচাষ হত সে যুগে। ইছামতী যমুনা কপোতাক্ষ নদীতীরে অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লুই বল্লো নামে একজন ফরাসি গোন্দলপাড়াতে নীলচাষ করে প্রচুর সম্পদের মালিক হন।
পরবর্তীকালে বারাসতে মধুমুরালি পুকুরের পাশে তিনি নীলকুঠি স্থাপন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইংলন্ডে কার্পাস শিল্পের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি আমাদের দেশের নীলের চাহিদা ঐ শিল্পে বাড়তে থাকল। প্রথম থেকেই নীলচাষকে উৎসাহিত করার জন্য কোম্পানি অল্প সুদে নীলকর সাহেবদের টাকা ধার দিত। কোম্পানির পুরানো হিসাবপত্রে লক্ষ করা যায় ১৭৮৬- ১৮০৩ পর্যন্ত তারা এক কোটির ওপর টাকা নীলকর সাহেবদের অল্পসুদে অগ্রিম দিয়েছে।
এর কারণ হিসাবে কোম্পানি জানিয়েছিল-‘এই দ্রব্যটি আমাদের প্রভূত পরিমাণে লাভের উৎরূপে পরিগণিত হবে।’ ১৮১৪-১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার নীল বিশ্ববাজার দখল করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিরা নীল চাষের অত্যধিক লাভ দেখে বিভিন্ন জায়গায় তারা কুঠি তৈরি করে নীল উৎপাদন শুরু করে দিল।
১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে Court of Directors নীল উৎপাদনে এই লাভ দেখে স্থির করলেন নীলকর সাহেবদের হাতে প্রচুর টাকা আছে- সুতরাং ওদেরকে আর সাহায্য দেবার প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও নীলকর সাহেবদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে চলল। পরবর্তীকালে অনেক দেশীয় জমিদার এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ল। দেবেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে দ্বারকানাথ সম্পর্কে লিখেছেন-তখন তার হাতে হুগলি, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ জমিদারি ও নীলের কুঠি।’

 Sarakhon Report
Sarakhon Report