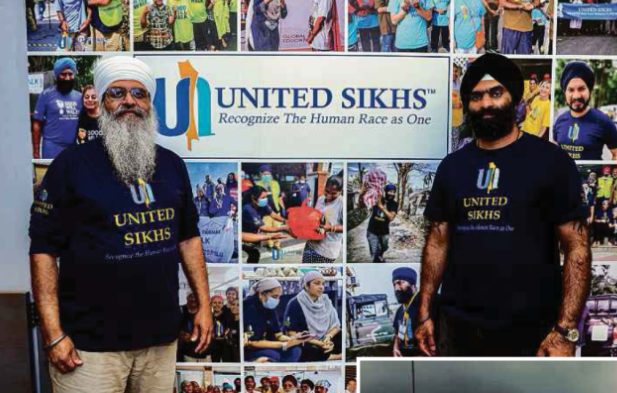স্বদেশ রায়
ট্রাম্প ও পুতিন ফোনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই মূলত ইউক্রেনের ভাগ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেলনেস্কি’র সঙ্গে ট্রাম্প পরে কথা বলেছেন। মিউনিখে আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিও নেতৃত্বে জেলনেস্কি’র সঙ্গে আলোচনা হবে। আর তাও হবে ট্রাম্প- পুতিন আলোচনার ভিত্তিতে। অন্যদিকে ইতোমধ্যে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে, সৌদি আরবে পুতিনের সঙ্গে যে মিটিং হবে সেখানে ইউক্রেনের ভাগ্য ট্রাম্প- পুতিন ফোনালাপে যা আলোচনা হয়েছে সে মোতাবেকই হবে। এখন অবধি যা বোঝা যাচ্ছে, ইউক্রেনের ভবিষ্যত রূপরেখা- রুশ ভাষাভাষিদের যে এলাকা পুতিন দখল করে নিয়েছেন, সেটা রাশিয়ার অধীনেই থাকতে পারে। অন্যদিকে ইউরোপের নিরাপত্তা এবং ইউক্রেনের স্থিতিশীলতা ছাড়াও খনিজ ও ফসলের নিরাপত্তার স্বার্থে ইউক্রেনে ন্যাটো বাহিনী হয়তো শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে নিয়োজিত হবে।
ইউক্রেনকে এই বাস্তবতায় নিয়ে এসেছে মূলত বাইডেন প্রশাসনের ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, বাইডেন তার জনগনের বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করেছেন ইউক্রেনে মূলত রাশিয়াকে অস্থিতিশীল করার জন্যে। ইউেক্রেনের নিরাপত্তা বা রাশিয়া যাতে ইউক্রেন আক্রমন থেকে বিরত হয়- সেটাকে তিনি মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে আনতে বা সে ধরনের বিশ্ব কূটনীতি গ্রহন করতে ব্যর্থ হন।

এর মূল কারণ বাইডেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উত্তর বিশ্ব-রাজনৈতিক ধারার উত্তরাধিকার। তাদের বিশ্বাসে রয়ে গেছে, কোন একটা রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তার ভেতর দিয়ে তার নিজস্ব লাভ খোঁজা বা তার প্রতিদ্বন্ধী কোন বড় রাষ্ট্রের বা বড় অর্থনীতির ক্ষতি করা বা সমস্যায় ফেলে দেয়া।
এটা মূলত সোভিয়েত- আমেরিকা দুই পরাশক্তির কোল্ড ওয়ারের সময়ের একটা গোষ্টির স্ট্রাটেজী। যার মূল লক্ষ্য সামরিকভাবে একে অপরকে দুর্বল করা। এবং সামরিকভাবে অস্থিতিশীল রেখে ওইসব দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করা।
তবে কোল্ড ওয়ার পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে একক অর্থনীতির বিশ্বে এই স্ট্রাটেজি যে বদলে গেছে, পৃথিবীর অর্থনীতিরও অনেক বেশি রূপান্তর হয়েছে, সর্বোপরি অর্থনৈতিক শক্তির অবস্থান বদলে গেছে, এটা বাইডেন প্রশাসন সঠিক পথে উপলব্দি করতে পারেনি বা করেনি। কারণ ডেমোক্র্যাটরা এক ধরনের বাম সিনড্রোমে ভুগছে। তাদের ওই অর্থে বুর্জোয়া বা ক্যাপিটালিস্ট বা মার্কেট ইকোনমিতে আস্থাশীল ও পারদর্শী নেতৃত্ব নেই।

অন্যদিকে, আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্ধি এখন এশিয়ায়। এশিয়ার অর্থনৈতিক শক্তির চরিত্র এখান থেকে দশ বছর আগেও যা ছিলো বর্তমানে তা আরো বদলে গেছে। দশ বছর আগেও এশিয়া অনেকটা পশ্চিমের প্রোডাকশন হাউস হিসেবে অর্থনৈতিক শক্তি ছিলো। এখন এশিয়া নিজেই ধীরে ধীরে নিজের পণ্যের বাজার হয়ে উঠছে। (যেমন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজার বাড়ছে চীনে ও ভারতে। বাংলাদেশের সিনথেটিক জুতোর দ্বিতীয় বড় বাজার ভারত)। অন্যদিকে ওয়ার্ল্ড পপুলেশানের ৬০% বাস করে এশিয়ায়। এই জনগনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। আবার একটি অংশের ক্রয় ক্ষমতা ইউরোপীয় বা আমেরিকান সর্বোচ্চ ক্রয় ক্ষমতার অধিকারীদের সমান।
অর্থনীতির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরাজনীতি’র চরিত্র বদলে গেছে। বিশ্ব রাজনীতির মূল স্টেকহোল্ডারও বদলে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর রাষ্ট্রনীতির সেই ধারা অর্থাত গণতন্ত্র ও তথাকথিত সোশ্যালইজমের নামে দেশে দেশে যে অস্থিতিশীলতা ছড়ানোর রাজনীতি উভয়পক্ষ করতো তা মোটেই পছন্দ করছে না বর্তমান রাজনীতির মূল স্টেক হোল্ডাররা। তারা সকলে চায় স্থিতিশীলতা। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি এগিয়ে নিতে পারে। যদিও সব সময়ই পৃথিবীতে সকল দ্বন্ধের মূলে ছিলো অর্থনীতি ও সম্পদ- তবে সেখানে বেশিক্ষেত্রে সামরিক বিষয়টিকে শক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তার পরিবর্তে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও অর্থনীতির বড় স্টেকহোল্ডার এবং তাদের নিরাপত্তা দেবার মত শক্তিই ফ্রন্টলাইনে চলে আসছে।

এ কারণে কে কোন পদ্ধতিতে দেশ চালাচ্ছে বা বিশ্বের নেতৃত্বের কোন অংশ নিচ্ছে- তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ এখন অর্থনীতি এবং অর্থনীতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় সম্পদ এক্সপ্লোর করা। এজন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনীতির স্বার্থে যেমন নিজদেশে স্থিতিশীলতা চায় তেমনি তাদের বাজার হিসেবে ব্যবহৃত, সম্পদ আহরনক্ষেত্র ও পণ্য উত্পাদনে নিয়োজিত দরিদ্র অর্থনীতির দেশগুলোতেও স্থিতিশীলতা চায়। অর্থনীতির এই নতুন ধারার প্রতিনিধি ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমান পৃথিবীর বড় অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহন করার পরে- এই স্থিতিশীলতা রক্ষার বিষয়টি আরো সরাসরি একটি পথ গ্রহন করলো। যেমন বড়শক্তি হিসেবে অর্থনীতির স্বার্থে পানামা খালের বিষয়ে সিদ্ধান্তটি আমেরিকাই নিলো। পানামা সেটা মেনে নিলো। এমনকি চীনও পানামার পেছনে গিয়ে আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো না।
চীন এই ধরনের কোন জটিলতায় ঢুকবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার “আমেরিকা গ্রেট” নীতি নিয়ে ক্ষমতাগ্রহনের পরে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিবের ফোনালাপই বিষয়টি স্পষ্ট করে। যদিও সে রিপোর্টের ভাষা অনেকে ভুল বুঝে ব্যাখা করেছে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিবকে উপদেশ দিয়েছেন, কোনরূপ সামরিক যুদ্ধের বদলে অর্থনৈতিক সহায়তায় থাকায়। আসলে কূটনৈতিক ভাষার মূল অর্থ যেমন অনেক সময় মিডিয়া ভুল ব্যখা করে নিজ নিজ স্বার্থে -তাছাড়া সারা পৃথিবী জুড়ে ভাষান্তর একটা সমস্যা। যাহোক ওই দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পরবর্তী অনান্য বক্তব্য স্পষ্ট করেছে সেখানে কোন উপদেশ ছিলো না মূলত তারা একমত হয়েছে, যত বেশি সম্ভব কূটনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করবে।

এবং একে অপরের স্বার্থের ক্ষতিকর কিছু করবে না। চীন এটা অনেকদিন থেকে চায়। গত বছরই সাউথ চায়না মর্নি পোস্টের এক কলামিস্ট একারনেই মজা করে তার কলামে লিখেছিলেন, চায়নার উল্ফ ওরিয়র ডিপ্লোম্যাটরা কি স্টেট ডিপার্টমেন্টে চলে গেছেন? বাস্তবে চায়না ধীর ধীরে তাদের উল্ফ ওরিয়র ডিপ্লোম্যাসি থেকে সরে আসছে। তারা এখন নিজেদেরকে নিয়ে আরো স্বচ্ছ ও আস্থাশীল। আর সেই স্বচ্ছ আস্থা স্পষ্ট করছে- বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতি হতে হলে তাদের আগামী পঞ্চাশ বছর কোন সরাসরি যুদ্ধে বা সংঘাতে জড়ানো যাবে না। অন্যদিকে আমেরিকার নতুন পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্যও তেমনি। তিনি বলেছেন, এক্ষেত্রে উভয়ের জন্যে উচিত কূটনীতিকভাবে বিষয়গুলো মোকাবিলা করা।
বড় শক্তিগুলো যখন নিজের অনুকূলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় সে সময়ে তারা বেলিস্টেট বা স্যাটেলাইটস্টেট গুলোর কোন মতামতের তোয়াক্কা করে না। যেমন জেলনস্কি তার দেশ ইউক্রেন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অন্য দশজনের মতো ঘটনা ঘটে যাবার পরে জানতে পারলো, তার দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ট্রাম্প ও পুতিন ফোনালাপের মাধ্যমে নিয়েছেন। সেখানে তাকে জানানো প্রয়োজন মনে করেনি ওই দুই নেতা ।

যেমন কিউবা থেকে ১৯৬২ সালে পারমানবিক মিসাইল সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতা ক্রশেভ ও আমেরিকার নেতা কেনেডির সঙ্গে আলাপের মাধ্যমেই সরিয়ে নেয়া হয়। আজকের ইউক্রেনের জেলনেস্কির থেকে হাজারগুন শক্তিশালী কিউবার নেতা ফিডেল ক্যাস্ত্রোকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার নেতা। এখানেও ন্যাটো গোষ্টিভুক্তি দেশের ও রাশিয়ার বেলিস্টেট ইউক্রেন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি জেলনেস্কিকে আগে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি আমেরিকা ও রাশিয়ার নেতা। আমেরিকা গুরুত্ব দিয়েছে তার ন্যাটো জোটসঙ্গীদের স্থিতিশীলতা ও নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ। আর রাশিয়া গুরুত্ব দিয়েছে তার দেশের স্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা। এর পরে যদি ক্রিমিয়া নিয়েও কোন নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন পড়ে সেখানকার পোর্ট ও অনান্য স্বার্থে, তাও বড় শক্তিগুলো মিলেই নেবে। সেখানে ইউক্রেনের কোন ভূমিকা থাকবে না। ক্রিমিয়া নিয়েও দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান বাস্তবতায় বদলে যেতে পারে। বদলে যাবে ইউক্রেনের সম্পদ ও স্থিতিশীলতা রক্ষার পদ্ধতি। সেখানে অতীতের মতো আমেরিকার ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের বদলে ন্যাটো বা আমেরিকার শান্তিরক্ষী বাহিনী নিয়োজিত হয়ে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিরাপত্তা দেবার পথ নিতে পারে।
অন্যদিকে আমেরিকার বিপরীতে বড় শক্তির কেন্দ্র এখন এশিয়ায় চলে এসেছে। আগামী পঞ্চাশ বছরে চীন পৃথিবীর মূল অর্থনৈতিক শক্তি হতে চায়। এর বিপরীতে ট্রাম্প প্রশাসন তার নীতি নিয়েছে আগামী একশ বছর যাতে তারা চীনকে ঠেকিয়ে নিজেদের শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখতে পারে। অর্থনৈতিক এই যুদ্ধে স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সামরিক উত্তেজনায় শক্তি ক্ষয় কমানোর জন্যে হয়তো তাইওয়ানকে না জানিয়েই আমেরিকা ও চায়না সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাইওয়ান ঘিরে সামরিক ব্যয় ও মহড়া থেকে আমেরিকা সরে আসতে পারে। অন্যদিকে চীনও তার অধিকারের সীমারেখা টানতে পারে সাউথ চায়না সিতে। এরফলে চায়নার বেলিস্টেট হিসেবে এখনও পরিচিত তাইওয়ান আরো বেশি চায়নার নিয়ন্ত্রনে চলে যাবে; অনেকখানি পূর্ণতা পাবে এক চীন নীতি। এর বিপরীতে সাউথ ইস্ট এশিয়ায় চায়নার অর্থনৈতিক স্যাটেলাইট স্টেটগুলোতে আমেরিকা আরো বেশি ব্যবসা বাড়াতে সমর্থ হতে পারে।

তবে চায়নার সঙ্গে আমেরিকার এই ব্যালান্স রক্ষার পাশাপাশি ২১ শতকে পৃথিবীর শক্তির গেইম চেঞ্জার হবে “আমেরিকা ও ইন্ডিয়ার যৌথতা” বলে এ মুহূর্তে অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মনে করছেন। কারণ, সামগ্রিক ইন্দো-প্যাসিফিক রিজিয়নে বাস করে ৫.৯ বিলিয়ন মানুষ। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান ওসান রিজিয়নে বাস করে ২. ৯ বিলিয়ন মানুষ। যেহেতু আমেরিকার বিপরীতে পৃথিবীর শক্তির অপর কেন্দ্র এখন এশিয়ায় শিফট হয়েছে। তাই আমেরিকাকে এশিয়ায় শক্তিশালী হতেই হবে। আর সে কাজ আমেরিকা- ইন্ডিয়া বন্ধুত্বই আমেরিকা ও ইন্ডিয়ার জন্যে সঠিক পথ। দুই দেশ সেদিকেই এগুচ্ছে, যা এখন স্পষ্ট। আর এ পথই তাদেরকে একুশ শতকের গেইম চেঞ্জারের ভূমিকায় নিয়ে যাবে।
এশিয়ায় আমেরিকা তার অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্যে, তার অর্থনৈতিক স্বার্থের নিশ্চয়তার জন্যে সব থেকে গুরুত্ব দেবে ইন্দো- প্যাসিফিক এলাকার স্থিতিশীলতা। সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান ওসান রিজিয়নের ২.৯ বিলিয়ন মানুষ সহ ইন্দো-প্যাসিফিক রিজিয়নের ৫.৯ বিলিয়ন মানুষের এই এলাকার অর্থনীতির স্বার্থে অভ্যন্তরীন নিরপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি সব থেকে আগে গুরুত্বপাবে। আর এ কাজের ক্ষেত্র হিসেবে তার সব থেকে বড় সহায়ক ও নিয়ামক হবে ভারত আগামী দিনে। তবে কখনও কখনও এজন্য সিদ্ধান্ত আসবে চীন ও আমেরিকার যৌথ সিদ্ধান্ত থেকে। বাদবাকি আমেরিকা ও ভারতের যৌথ সিদ্ধান্ত থেকে। মধ্যপ্রাচ্য যে দিকে যাচ্ছে সেখানেও অন্যতম নিয়ামক আমেরিকা ও ভারতের কমন ফ্রেন্ড।

সাম্প্রতিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফরে ট্রাম্প- মোদি’র যৌথ ঘোষনায় ইন্দো-প্যাসিফিকের জঙ্গীবাদের বিষয়টি এসেছে। এই ইন্দো-প্যাসিফিকের জঙ্গীবাদ চীন ও আমেরিকার সিদ্ধান্ত এবং আমেরিকা ও ভারতের সিদ্ধান্তের ওপর দমনের প্রকৃতি নির্ভর করবে। স্থিতিশীলতার বিষয়টিও সেভাবেই নির্ভর করবে। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ওসান রিজিওয়নের স্থিতিশীলতা কীভাবে রক্ষা করা হবে সেটা যেমন ইউক্রেনের বিষয়ে ট্রাম্প ও পুতিন ঠিক করেছেন তেমনি এখানেও ট্রাম্প ও মোদি ঠিক করবেন। ট্রাম্প ও মোদির ঘোষণায় পাকিস্তানের জঙ্গীবাদের বিষয়টি এসেছে।
পাকিস্তানসহ এ রিজিওয়নে একই ধরনের জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটছে অনেক দেশে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তান তার সরাসরি মদদ দিচ্ছে। এইসব জঙ্গীবাদের শরীরে যতই রঙীন পোষাক পরানো হোক না কেন , ওই পোষাকের নিচের শরীরটি অচেনা থাকে না। তাই অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে এদের বিরুদ্ধে একই ধরনের সিদ্ধান্ত আসবে বর্তমান বাস্তবতায়। আর তা মোকাবিলা করার শক্তি কখনই কোন বেলিস্টেট বা স্যাটেলাইটস্টেটের থাকে না।

এ কারণে বর্তমানের এই বাস্তবতায় পৃথিবীর দুর্বল অর্থনীতির বেলিস্টেট ও স্যাটেলাইটস্টেটগুলোর জনগন ও রাজনীতিবিদদের তাদের রাষ্ট্র চালানোর বিষয়ে আরো সজাগ ও পরিমিত বোধ সম্পন্ন হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই রপ্ত করতে হবে, কীভাবে পরিবর্তিত এই বিশ্বে নিজ নিজ অবস্থানের বড় শক্তির সঙ্গে সিমোবায়োসিস হিসেবে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এবং নিজের দেশ যেন কখনই ওই সব শক্তির জন্যে হুমকি না হয়। এর বিপরীতে গেলে এইসব বেলিস্টেটের রাষ্ট্র পরিচালকরা তাদের জনগনকে অর্থনৈতিক বিপাকে ফেলে দেবে।
বর্তমানের এই জটিল ও ক্ষমতাশালীর পৃথিবীতে কোন উম্মাদনাকে প্রশয় দেবার সুযোগ কোন রাষ্ট্রের নেই। এমনকি দূর ও নিকট অতীতে যারা আর্ন্তজাতিক ভুল স্ট্রাটেজী দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে- যেমন আফগানিস্তানসহ অনান্য দেশ- তাদের দেশের জনগনকেও এখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
লেখক: রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সম্পাদক সারাক্ষণ ও The Present World.

 Sarakhon Report
Sarakhon Report