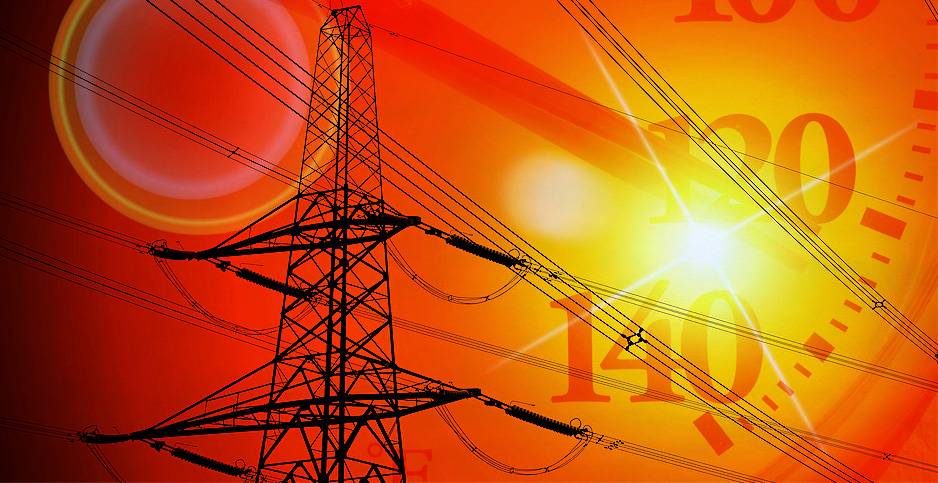সারাক্ষণ রিপোর্ট
নগরজীবনের এক অদেখা অধ্যায়
১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘গোলাপী এখন ঢাকায়’ কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি বাংলাদেশের রাজধানী শহরের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও বস্তিজীবনের তীব্র চিত্রায়ণ। পরিচালক আমজাদ হোসেন, যিনি গ্রামীন নারীর নিপীড়িত জীবন ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ চলচ্চিত্রে উপস্থাপন করেছিলেন, এবার তাঁকে শহরে নিয়ে আসেন—ঢাকায়। এই চলচ্চিত্রে গোলাপীর সংগ্রাম আরও বহুস্তরীয়, যেখানে একদিকে রয়েছে টিকে থাকার যুদ্ধ, অন্যদিকে রয়েছে সমাজের উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্তের বিভাজন, এবং সর্বোপরি একটি শোষণমুখী রাজনৈতিক কাঠামোর নির্মম প্রতিচ্ছবি।
কাহিনির পটভূমি: বস্তি, বেঁচে থাকা ও ব্যবস্থার শিকার
‘গোলাপী এখন ঢাকায়’ সিনেমায় দেখা যায় গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা এক নারী, গোলাপী, যিনি আশ্রয় খোঁজেন ঢাকার এক বস্তিতে। এই বস্তি কেবল বসবাসের জায়গা নয়—এটি এক সংগ্রামের কেন্দ্র যেখানে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই লড়াই।
গোলাপী বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়ে—কখনও গৃহকর্মী, কখনও দোকানের বিক্রয়কর্মী, কখনও আবার পথের পাশে বসে ফল বিক্রেতা। এই পটভূমির মধ্যেই উদঘাটিত হয় ঢাকার বস্তিগুলোর অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য, অপরাধচক্র, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে—রাজনৈতিক দখলদারিত্ব।

ঢাকার বস্তিজীবনের প্রতিচ্ছবি
চলচ্চিত্রে বস্তিজীবনকে তুলে ধরা হয়েছে যেন এক ধূসর বাস্তবতা। এখানে:
- ঘর মানেই চারদিকে টিন আর ছিদ্রের পলিথিন।
- চাকরি মানেই অনিশ্চয়তা।
- প্রেম মানেই সম্ভাব্য প্রতারণা।
- স্বপ্ন মানেই ভাঙনের শুরু।
বস্তির মানুষদের জীবনে কোনও নিরাপত্তা নেই। তারা পুলিশ, রাজনৈতিক ক্যাডার ও প্রভাবশালীদের হাতে জিম্মি। এই ব্যবস্থার শিকার হয় গোলাপীও—শুধু একজন নারী হিসেবে নয়, একজন প্রান্তিক মানুষ হিসেবে।
রাজনীতি: বস্তির নিয়ন্ত্রক শক্তি
চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রাজনীতির প্রভাব। বস্তিতে বসবাসকারী মানুষদের রাজনৈতিক দলের দয়া, করুণা ও শোষণের সমন্বয়ে বেঁচে থাকতে হয়।
- স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা বস্তিকে নিজেদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে।
- উন্নয়নের নামে আসে ‘উচ্ছেদ’, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয় ভোট আদায় ও জমির দখল।
- বস্তির নেতারা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় থাকেন এবং মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
গোলাপী এই রাজনীতির চক্রে প্রথমে অজ্ঞ, পরে জড়িয়ে পড়েন। একজন রাজনৈতিক কর্মী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু সেখানে প্রেম ও ক্ষমতার মিশ্রণ ঘটতে থাকে। গোলাপীর সঙ্গে এই সম্পর্ক তার জীবনে একদিকে নিরাপত্তা এনে দিলেও অন্যদিকে জন্ম দেয় আরও জটিলতা।
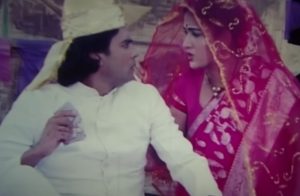
নারীর অবস্থান: পণ্য না মানুষ?
আমজাদ হোসেন এই চলচ্চিত্রে নগরের প্রান্তিক নারীর অবস্থানকে তুলে ধরেন কেবল প্রেমিক চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক সংকটের প্রতীক হিসেবে।
- নারীকে শ্রমিক হিসেবে দরকার—কিন্তু মানবিক মর্যাদার সুযোগ নেই।
- প্রেমের নামেও তার শরীর ব্যবহৃত হয়—ভালোবাসা নয়, থাকে চাহিদা।
- সমাজের চোখে সে যেন চলমান পণ্য, যার মূল্য সময় ও অবস্থানভেদে ওঠানামা করে।
এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালকের কণ্ঠে প্রতিবাদে রূপ নেয়। গোলাপীর চরিত্রে তিনি নারীর ক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং স্বপ্নের মিশ্র প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন।

শহুরে জীবনের দ্বিচারিতা
‘গোলাপী এখন ঢাকায়’ চলচ্চিত্রটি পুরোপুরি রাজনৈতিক রঙে রাঙানো না হলেও, এর ভেতরে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক বিদ্রূপ আছে। ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত শ্রেণি এখানে স্বার্থপর, কৌশলী এবং সংবেদনশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে প্রান্তিক মানুষের জীবন বেঁচে থাকার সংগ্রামে প্রতিদিনই রক্তাক্ত হয়।
চলচ্চিত্রে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রায় অনুপস্থিত—যা আমজাদ হোসেন ইচ্ছাকৃতভাবেই করেন। তিনি দেখাতে চান, সমাজে একদিকে আছে ক্ষমতাশালী শ্রেণি—আর অন্যদিকে, প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা; মাঝের সেতু ভেঙে গেছে।
নির্মাণশৈলী ও চলচ্চিত্রভাষা
চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ, সেট ডিজাইন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সবকিছুই ছিল বাস্তবভিত্তিক ও নির্মোহ। বস্তির গলি, কাদার রাস্তা, কেরোসিন বাতির আলো, ছিন্নভিন্ন পোশাক—সবকিছুতেই ছিল বাস্তবতা ও শ্রেণিচেতনার দৃঢ় প্রতিফলন।
চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানগুলো ছিল স্যাটায়ারধর্মী এবং রসবোধে ভরপুর—যা নির্মম বাস্তবতার মাঝেও একটা আলোর রেখা হিসেবে কাজ করত।

একটি রাজনৈতিক সমাজচিত্রের ভাষ্য
‘গোলাপী এখন ঢাকায়’ শুধুই বস্তির জীবনের ট্র্যাজেডি নয়, এটি হলো বাংলাদেশের রাজধানীর প্রান্তিক মানুষের জীবনের রাজনৈতিক ইতিহাস। আমজাদ হোসেন তাঁর সিনেমার ভাষায় জানান দেন—একজন গোলাপীর কাহিনি শুধু একজন নারীর কাহিনি নয়, এটি গোটা সমাজের ন্যায়বিচারহীন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।
গোলাপী ঢাকায় এসে যেমন প্রান্তিকতার মুখোমুখি হন, তেমনি তিনি প্রতিরোধও গড়ে তোলেন। পরিচালক বুঝিয়ে দেন, নারীর মুক্তি কেবল প্রেমে নয়, বা দানে নয়—বরং নিজের অবস্থানকে বোঝা, প্রতিবাদ করা, এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার মধ্যেই।
এই চলচ্চিত্র বাংলাদেশি রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার এক অনন্য দলিল হয়ে রয়ে গেছে।
‘গোলাপী এখন ঢাকায়’ ঢাকার সেই অভ্যন্তরীণ জীবনের গল্প, যা পত্রিকার শিরোনামে আসে না, কিন্তু প্রতিটি অলিতে-গলিতে প্রতিদিন লেখা হয়।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report