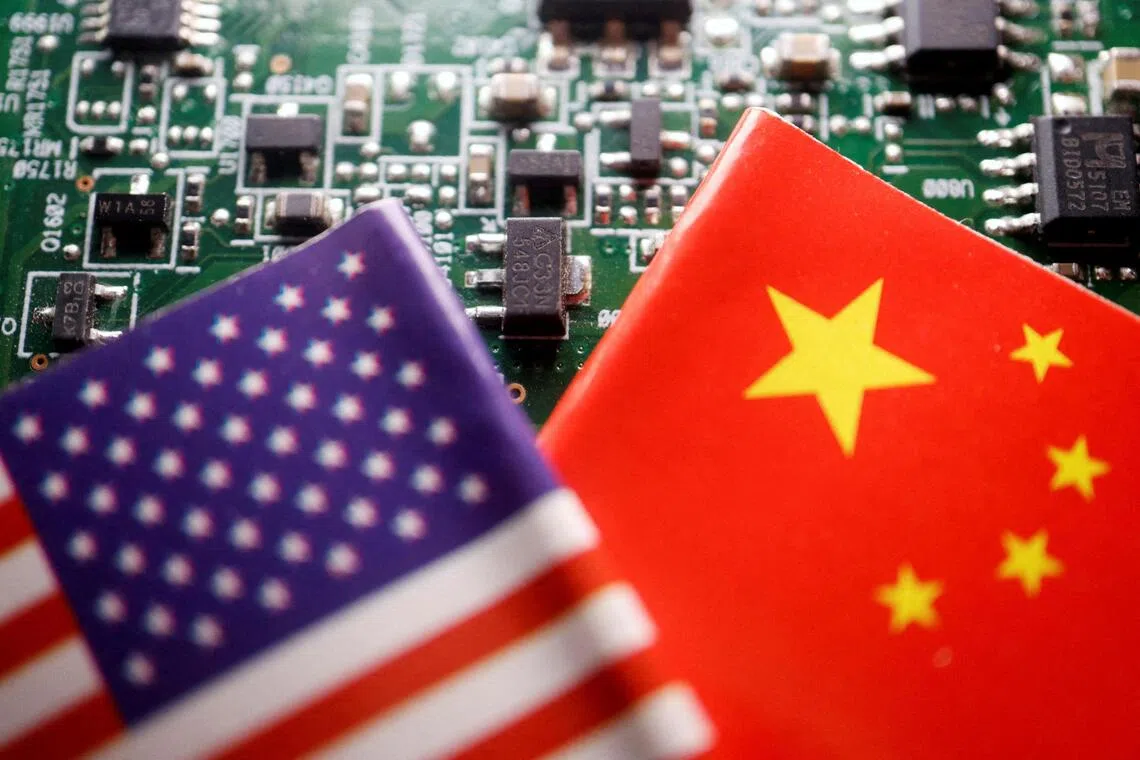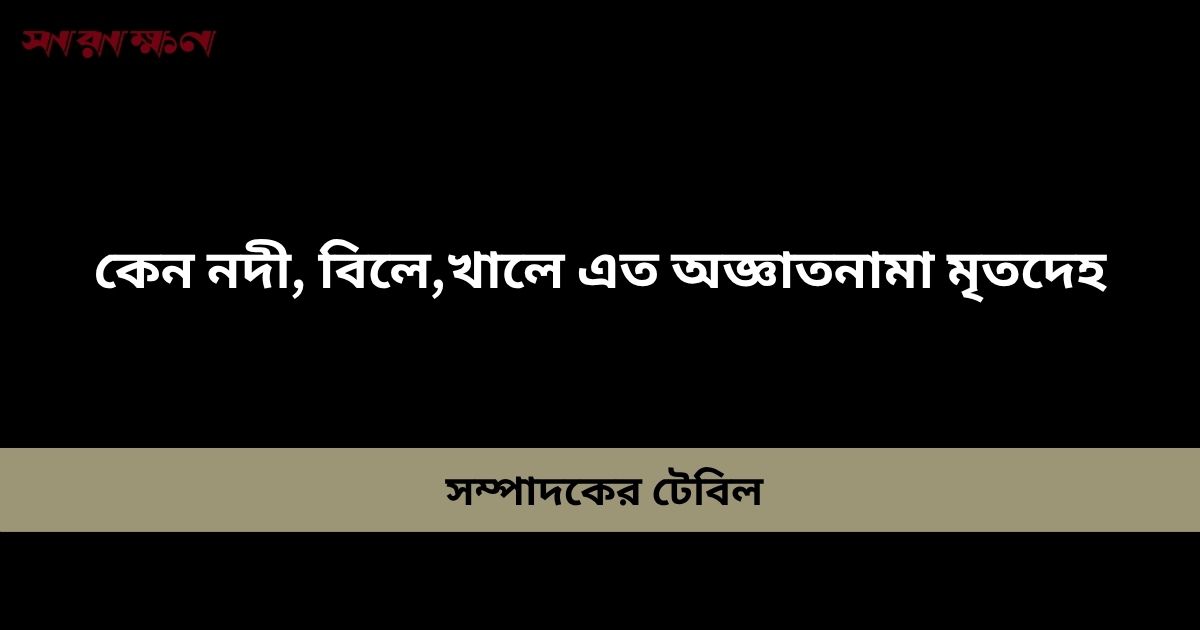পাহাড়ি ঝরনাধারা, বনভূমি আর কৃষিভূমিকে একসূত্রে গেঁথে গড়ে ওঠা মাতামুহুরী নদী (দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৮ কিমি) শুধু দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বদলায়নি, গড়ে তুলেছে এক অনন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস। আলীকদম-লামার গিরিখাঁদ পেরিয়ে নদীটি চকরিয়া উপকূলে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে—নানা আলো-আঁধারের গল্প বহন করে।
উৎস ও প্রবাহ: পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তঘেঁষা আলীকদমের দোছরি-ফাত্তারা উপনদী থেকে মাতামুহুরীর জন্ম। বানরের স্তনাকৃতির পাহাড়ি ছিদ্র দিয়ে ঝরনার মতো জল পড়ে বলেই ‘মাতা-মুহুরী’ নামের উদ্ভব—জনশ্রুতিতে সেই কাহিনি প্রচলিত। সর্পিল এ ধারা লামা, আলীকদম, চকরিয়া পেরিয়ে সমতলে নেমে আসে; মধ্যভাগে নৌপথ যুগে যুগে পণ্য ও নরম কাঠ পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল।
এক শতক আগের তীরবর্তী সভ্যতা
১৯২০-এর দশকে নদীকেন্দ্রিক জনপদের চালচিত্র ছিল ভিন্ন—পাহাড়ি ম্রো, মারমা, চাকমাদের জুম-চাষ, বাঁশ-কেন্দ্রিক হস্তশিল্প ও নৌ-বাণিজ্য ছিল মুখ্য। বাঙালি বসতির ঘনত্ব ছিল কম; নদীপাড়ে কাঠ-ভেলা ভাসিয়ে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম বন্দরে গর্জন-চাপালিশ পৌঁছত। বর্ষা-বসন্তের নৌমেলায় ইলিশ-পাবদা, পাহাড়ি লেবু-কুমড়ার হাঁকডাক ছিল নদীবাংলার প্রাণ।

বন ও প্রাণবৈচিত্র্য: সবুজ রাজ্যের ঐশ্বর্য
মাতামুহুরী-সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্টে একদা দৃষ্টিনন্দন বহুতল চিরসবুজ বন ছিল—গর্জন, চালস, জারুল, সিমুল, টুন, করই, চাম্পা ইত্যাদি সুউচ্চ বৃক্ষের ছায়ায় হাতি, সাম্বর হরিণ, কালো ভালুক, সূর্যভালুক, ইন্দো-চীনা চিতাবাঘ আর গ্রেট হর্নবিলের আবাস ছিল। পশ্চিমা হুলক গিবনে ভরপুর পাহাড় গ্রীষ্মের ভোরে আকাশ কাঁপাত। তবে শরণার্থীর বসতি ও কাঠ আহরণের চাপে বনভূমি আজ অনেকটাই স্মৃতি হয়ে গেছে।
মাতামুহুরীর মাছ ও জলজ জীবন
২০২২-এর জরিপে ওপরের পাহাড়ি ধারাজুড়ে ১৪ অর্ডারের ৯৫টি স্বাদুপানি মাছের প্রজাতি নথিভুক্ত হয়েছে—এর মধ্যে সাইক্লিড পরিবারের ১৯, ড্যানিওনিডের ১১ এবং বাগরিদের ৭ প্রজাতি। স্বর্ণ মাহশির (Tor putitora)-এর নতুন রেকর্ডসহ ১১টি অতি সংকটাপন্ন ও ১২টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। শোল, কৈ, গুলশা, শিং, পাবদার পাশাপাশি বর্ষার সময় ইলিশ ঢুকে পড়ে নিম্ন প্রবাহে।

রূপান্তরের সূচনা: সেতু, সেচ ও সরণের চাপ
পঞ্চাশের দশকে কাপ্তাই সড়ক ও সেতু নির্মাণ, সত্তরের দশকে জল-কাঠ দস্যুত্ব এবং ১৯৮৫-৮৬-তে মোহনার মুখে মুহুরী সেচ প্রকল্পের ক্লোজার ড্যাম নদীর স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটার ছন্দ পাল্টে দেয়। শুষ্ক মৌসুমে গেট বন্ধ থাকলে কৃত্রিম হ্রদ গড়ে ওঠে; বর্ষায় জোয়ারের চাপ সামলাতে হুড়মুড়িয়ে পানি ছাড়া হয়—ফলে তটভূমি ক্ষয় ও অববাহিকার ভূমি লবণাক্ত হয়ে পড়ে।
বিরূপ প্রভাব ও সঙ্কট
ড্যাম-পরবর্তী তিন দশকে খাল-নালা পলিতে ভরেছে, সেচ-নালা সঙ্কুচিত; নদীর প্রবাহশক্তি হারিয়ে গেছে। ১৯৮৬ সালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মুহুরী চর দখল-সংঘর্ষ রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করে, যা আজও এলাকাবাসীর টেকসই নদী-ব্যবস্থাপনায় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে।

আজকের নদী: ক্ষীণ স্রোতের গল্প
চকরিয়া প্রান্তে এখন বর্ষা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই নদী যেন থমকে থাকা হ্রদ; নাব্যতা কমে নৌ-যোগাযোগ প্রায় বিলুপ্ত। ওপরের অববাহিকার পাহাড়ি অংশে বছরব্যাপী বালু উত্তোলন, রাবার ক্যাম্প ও পর্যটন স্থাপনা একত্রে বনকে আঘাত করছে। ত্রিপুরা সীমান্তজুড়ে কমে আসা প্রবাহ পানির কূটনৈতিক টানাপড়েন বাড়াচ্ছে, স্থানীয়দের নিরাপদ পানির উৎস অনিশ্চিত করছে।
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা
নদীমাতৃক সভ্যতার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে গবেষকেরা তিনটি দিক জরুরি মনে করেন—
• উৎস ও জলধারা সুরক্ষা: আলীকদম-লামার উজানে যান্ত্রিক বালু উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ ও পাহাড়ি ঝরনা পুনর্জীবন।
• বন পুনর্বাসন: মাতামুহুরী-সাঙ্গু রিজার্ভে চিরসবুজ বৃক্ষরোপণ, হাতি-গিবন করিডর পুনর্গঠন।
• নদী-শাসন পুনর্বিবেচনা: ড্যামের অপারেশন পদ্ধতি আধুনিকায়ন, পলি অপসারণ ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, যাতে নদীর স্বাভাবিক স্রোত ও মাছের চলাচল বজায় থাকে।
সামষ্টিক উদ্যোগ, সীমান্ত-সমন্বয় ও জনসম্পৃক্ত বন-নদী ব্যবস্থাপনাই পারে শতবর্ষী মাতামুহুরীকে আবার জীবনদায়ী স্রোতে ফিরিয়ে আনতে—যেখানে পাহাড়ি ফেনায় মাছ লাফাবে, বনভূমি গাইবে গিবনের গান, আর উপকূলের গ্রামগুলো নিঃশ্বাস নেবে স্বচ্ছ জলে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট