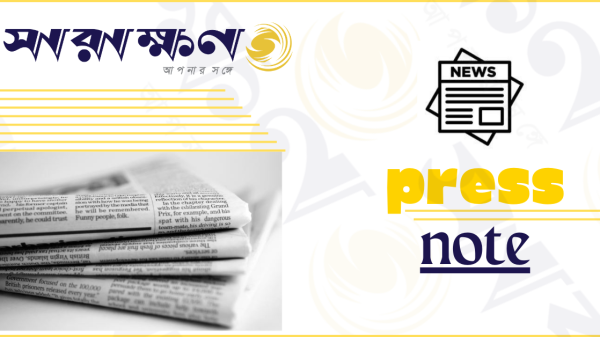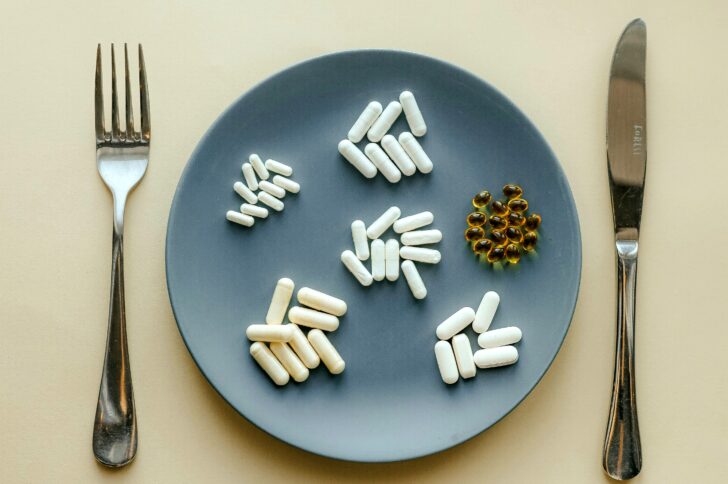ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে ভুল খবরের ধাক্কা
২০২২ সালের ১০ নভেম্বর ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে বড় ধাক্কা আসে। একটি ভেরিফায়েড টুইটার (বর্তমানে এক্স) অ্যাকাউন্ট থেকে দাবি করা হয় যে এলি লিলি নামের বিশ্ববিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি বিনা মূল্যে ইনসুলিন সরবরাহ করবে। খবরটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়—১১ হাজারের বেশি লাইক ও দেড় হাজারের মতো রিটুইট হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। এর ফলে অনলাইনে এলি লিলি নিয়ে খোঁজ বেড়ে যায় ৮০ শতাংশের বেশি। লক্ষ লক্ষ ইনসুলিন-নির্ভর রোগীর কাছে এটি আশার আলো হয়ে উঠলেও, আসল সমস্যা হলো—এটি ছিল ভুল খবর।
অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানি বিষয়টি স্পষ্ট করলেও, ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। শেয়ারমূল্য পড়ে যায় ৪ শতাংশ, বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং ইনসুলিনের দাম নিয়ে আবারও তীব্র বিতর্ক শুরু হয়।
অন্য খাতেও ভুল খবরে প্রভাব
এটি একমাত্র ঘটনা নয়। কয়েক মাস আগে ফাইজারের সিইও আলবার্ট বোরলার বক্তব্য বিকৃত করে একটি ভিডিও ছড়ানো হয়, যেখানে তাকে বলা হয়েছে—“২০২৩ সালের মধ্যে আমরা পৃথিবীর জনসংখ্যা অর্ধেক কমাব।” বাস্তবে তিনি বলেছিলেন—“আমরা ২০২৩ সালের মধ্যে ওষুধ কিনতে অক্ষম মানুষের সংখ্যা অর্ধেক কমাব।”
ভুল খবর শুধু ওষুধশিল্পেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাংক, কোকা-কোলা, ম্যাকডোনাল্ডস, ডেল্টা এয়ারলাইনস, ডিজনি, টেসলা, এমনকি ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোকেও এর আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। রাজনীতিতেও ভুল খবর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা নষ্ট করছে, বিভাজন গভীর করছে এবং ভোটের ফলাফল পর্যন্ত প্রভাবিত করছে।

ভুল খবর কেন এত বিপজ্জনক
ট্রাস্টেড ওয়েব ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮ শতাংশ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী অজান্তে ভুল খবর শেয়ার করেছেন। এমআইটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, ভুল খবর সত্য খবরের তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি হারে শেয়ার হয়। শেয়ার যত বাড়ে, খবরটি তত বেশি সত্য বলে মনে হয়।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভিডিও-এডিটিং প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের শিথিল কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের কারণে ভুল খবর ভবিষ্যতে আরও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
ভুল খবর বনাম ভুল তথ্য
ভুল তথ্য বা গুজব অনিচ্ছাকৃতভাবে ছড়ালেও, ভুল খবর ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি হয়, যাতে পাঠককে বিভ্রান্ত করা যায় এবং এটি সংবাদ আকারে ছড়িয়ে পড়ে।
প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা
কর্পোরেট খাত দীর্ঘদিন ধরে ভুল খবর মোকাবিলায় তিনটি প্রচলিত কৌশল ব্যবহার করেছে—উপেক্ষা করা, দ্রুত মুছে ফেলার চেষ্টা করা অথবা সত্য তথ্য দিয়ে প্রতিহত করা। কিন্তু এগুলো কার্যকর হচ্ছে না।

কারণ হলো—
উপেক্ষা করলে খবর আরও ছড়ায়।
মুছে ফেললেও স্ক্রিনশট বা রিপোস্টের মাধ্যমে আবার ফিরে আসে।
সত্য তথ্য দিলেও মানুষের বিশ্বাস বদলায় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে ওয়েফেয়ারের বিরুদ্ধে শিশুপাচারের অভিযোগ ছড়ায়, কোম্পানি অস্বীকার করলেও গুজব পৌঁছে যায় ৪৫ লাখ মানুষের কাছে।
এ ধরনের পরিস্থিতি “স্ট্রেইস্যান্ড ইফেক্ট” নামে পরিচিত—দমন করার চেষ্টা করলেই খবর আরও ছড়িয়ে পড়ে।
মানুষের মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক প্রভাব
মানুষ মনে করে, তারা ভুল খবর চিনতে পারে, কিন্তু অন্যরা পারে না। বাস্তবে, অন্যরা কী বিশ্বাস করছে—এটি দেখে নিজস্ব মতামতও বদলে যায়। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ ভুল খবরকে ব্যক্তিগতভাবে না মানলেও “অন্যরা বিশ্বাস করছে” ভেবে নিজের আচরণ ও সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনে।
গবেষণার ফলাফল
পরীক্ষায় দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারীদের জানানো হলেও যে খবরটি ভুল, তবু তারা বিশ্বাস করেছে অন্যরা এতে প্রভাবিত হবে। আর এই ধারণার কারণে তাদের নিজস্ব মূল্যায়নও বদলে গেছে।

কর্পোরেটদের করণীয়
ভুল খবর মোকাবিলায় শুধু তথ্য প্রকাশ নয়, “সোশ্যাল প্রুফ” বা সামাজিক প্রমাণ তৈরি করা জরুরি—অর্থাৎ দেখানো দরকার যে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডাররা, বিশেষজ্ঞরা ও সাধারণ গ্রাহকেরা ভুল খবর বিশ্বাস করছে না।
এর জন্য তিনটি কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে—
সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।
স্বচ্ছতা বজায় রাখা।
বিশ্বস্ত মিত্রদের সক্রিয় করা।
উদাহরণ ও শিক্ষণীয় বিষয়
কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে ভুল খবর ছড়ালে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা জরুরি। যেমন—ভেরো অর্গানিকস নামের একটি কাল্পনিক কোম্পানির বিরুদ্ধে ভুল ভিডিও ছড়ালে তারা সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক, সরবরাহকারী, বিজ্ঞানী ও সনদপ্রদানকারী সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে দেয়। তারা নিজেদের খামার ও উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে তুলে ধরে। গ্রাহকেরা সরাসরি অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, যা অন্যদের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।
বাস্তব উদাহরণে দেখা যায়, টাকো বেল ২০১১ সালে ভুল মামলার মুখে পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, টাকোতে ৩৫ শতাংশের কম গরুর মাংস আছে। কোম্পানি রসিকতা, বিজ্ঞাপন, ভিডিও, গ্রাহক ও কর্মচারীর অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে ভুল খবর দমন করে। কয়েক মাসের মধ্যে মামলা প্রত্যাহার হয়।
ভুল খবর মোকাবিলায় শুধু তথ্যভিত্তিক প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে সামাজিক প্রমাণ জুড়ে দেওয়া জরুরি। বিশ্বস্ত গ্রাহক, কর্মী, বিশেষজ্ঞ ও অংশীদারদের সম্পৃক্ত করে যদি প্রচলিত তথ্যভিত্তিক কৌশলের সঙ্গে সামাজিক প্রমাণ যুক্ত করা যায়, তবে ভুল খবরের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা সম্ভব।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট