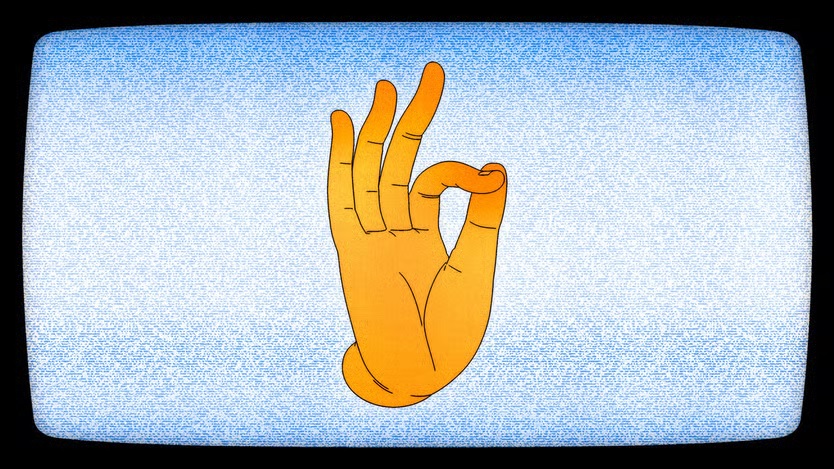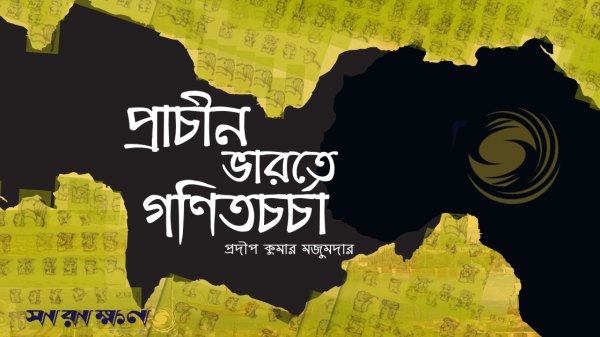আঞ্চলিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারতের শান্ত মুখ
দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে দাঁড়িয়ে যদি কেউ দূরদৃষ্টি নিয়ে তাকায়, তবে চারদিকে অস্থিরতার ছবি দেখা যাবে। উত্তর-পূর্বে নেপালে যুবসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে বৈষম্যের কারণে—রাজনীতিক পরিবারের সন্তানরা বিলাসী জীবনযাপন করছে, আর সাধারণ তরুণেরা বেকারত্বে জর্জরিত। পূর্বে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন গত বছর ক্ষমতাচ্যুত করেছে দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, যেখানে অন্যতম অভিযোগ ছিল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য সরকারি চাকরির কোটা। দক্ষিণে শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালে অর্থনৈতিক সংকটে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। পশ্চিমে পাকিস্তান আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইএমএফের শর্তে জর্জরিত।
কিন্তু এর মাঝেও ভারত যেন এক ব্যতিক্রমী স্থিতিশীলতার প্রতীক।
অর্থনৈতিক স্থিতি: অস্থিরতার ভেতরে শান্ত প্রবাহ
২০২৫ সালে ভারত একইসঙ্গে দুটি চাপে ছিল—ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধে রুশ তেল কেনার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক, এবং পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ। তবু দেশের অর্থনীতি স্থির গতিতে এগিয়েছে।
বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান যখন আইএমএফের কর্মসূচিতে জড়িয়ে পড়েছে, তখন ভারতের ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের সুদহার ৭ শতাংশের নিচে—যেখানে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার জন্য তা প্রায় ১২ শতাংশ। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৭০০ বিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ১৮ শতাংশ এবং ১১ মাসের আমদানি মেটাতে যথেষ্ট। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬–৮ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীলভাবে চলছে।

অতীতের সংকট থেকে শিক্ষিত এক ভারত
স্বাধীনতার পর ভারত একাধিকবার অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ও খরায় দেশ খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; ১৯৯১ সালে গালফ যুদ্ধ তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং প্রবাসী আয়ে ধস নামায়—সেই সময় সরকার স্বর্ণ রিজার্ভ বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়। তবে তখনকার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং এই সংকটকে সংস্কারের সুযোগে পরিণত করেন।
তিনি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দেন, মুদ্রা ভাসমান করেন এবং “লাইসেন্স রাজ” নামের জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে দেন। তার ফলেই ভারতের অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরে পায়।
“ফ্র্যাজাইল ফাইভ” থেকে আত্মনির্ভরতার পথে
২০১৩ সালে ভারত এখনও বৈশ্বিক পুঁজিবাজারের করুণার ওপর নির্ভরশীল ছিল। মর্গ্যান স্ট্যানলি তখন একে “ফ্র্যাজাইল ফাইভ”—অর্থাৎ নাজুক পাঁচ উদীয়মান অর্থনীতির একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আমেরিকার সুদের হার বাড়তেই রুপি ২০ শতাংশ পড়ে যায়।
পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ব্যাংক খাত সংস্কারে হাত দেয়, খারাপ ঋণ চিহ্নিত করে পুনর্গঠন করে, এবং দেউলিয়া আইন সংশোধন করে। ২০১৮ সালে যেখানে খেলাপি ঋণের হার ছিল ১৫ শতাংশ, ২০২৫ সালে তা নেমে এসেছে ৩ শতাংশে।

একই সঙ্গে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়েছে। মহামারির সময় বাজেট ঘাটতি ছিল ৯ শতাংশ, এখন তা ৫ শতাংশের নিচে। সরকারের লক্ষ্য ২০৩১ সালের মধ্যে ঋণ-জিডিপি অনুপাত ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশে আনা।
সেবা খাত ও তেলনীতিতে নতুন ভারসাম্য
উৎপাদন রপ্তানি প্রত্যাশা অনুযায়ী না বাড়লেও সেবা খাতে ভারতের আয় দ্রুত বেড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও ব্যবসা প্রক্রিয়া রপ্তানি এখন জিডিপির ১৫ শতাংশ, যা এক দশক আগে ছিল ১১ শতাংশ। এর ফলে বৈদেশিক পুঁজির ওপর নির্ভরতা কমেছে।
তেল আমদানির চাপও আগের তুলনায় কম। কৌশলগত তেল মজুদ, নতুন রিফাইনারি স্থাপন, রুশ তেল আমদানি এবং ২০২১ সালের ইথানল মিশ্রণ নীতি—সব মিলিয়ে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক ব্যয়ের ভার কমেছে। রুশ তেল আমদানির ফলে গত বছরই প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হয়েছে।
সামাজিক অসন্তোষ কেন দমন থাকে
ভারতের তরুণ সমাজে অসন্তোষ থাকলেও তা রাজনীতিতে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয় না। নেপালের মতো এখানেও বৈষম্যের চিত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট, কিন্তু বেশিরভাগই বলিউড তারকাদের জীবনযাপন সংক্রান্ত, যা অনেকেই প্রাপ্য সাফল্যের ফল হিসেবে মেনে নেয়।
সরকারি চাকরিতে সংরক্ষিত কোটার কারণে ক্ষোভ বাড়ছে—অর্ধেকেরও বেশি পদ সংরক্ষিত “পশ্চাৎপদ” বা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির জন্য। এর ফলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে হতাশা জন্ম নিচ্ছে, বিশেষত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বারবার ব্যর্থ তরুণদের মধ্যে।
তবু ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা যায় না। মার্চ মাসে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে যে দাঙ্গা হয়, তা ছিল ইতিহাসের এক মুসলিম সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধিকে কেন্দ্র করে, বর্তমান রাজনীতিকে নয়।
আশাবাদে টিকে থাকা এক প্রজন্ম
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অনেক ভারতীয়কে আশাবাদী করে তুলেছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির জরিপে দেখা যায়, ভারতীয়রা বর্তমানে তাদের জীবনসন্তুষ্টির মান ৪ বা ৫ হিসেবে মূল্যায়ন করলেও, পাঁচ বছর পর সেটি ৬ বা ৭ হবে বলে বিশ্বাস করেন।
দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিরতার মধ্যেও এই আশাবাদ ও অর্থনৈতিক স্থিতি ভারতের বিশেষত্ব তৈরি করেছে—একটি দেশ, যা এখনও বিশ্বাস করে, ভালো দিন আসবেই।
#India #Economy #SouthAsia #Stability #Geopolitics #SarakKhonReport

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট