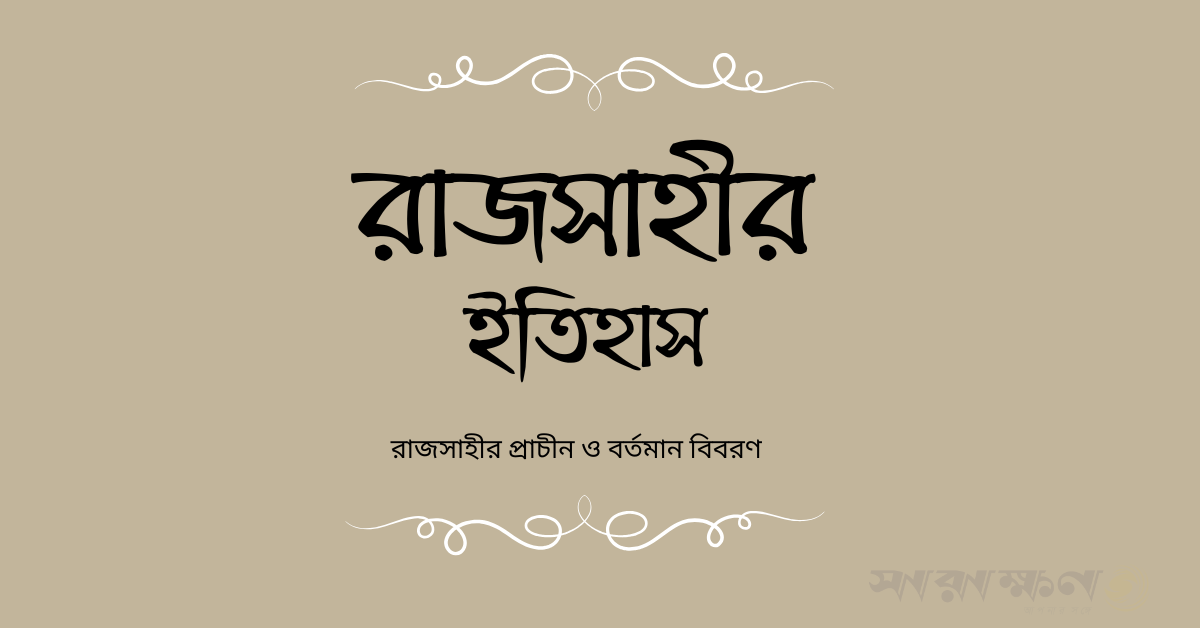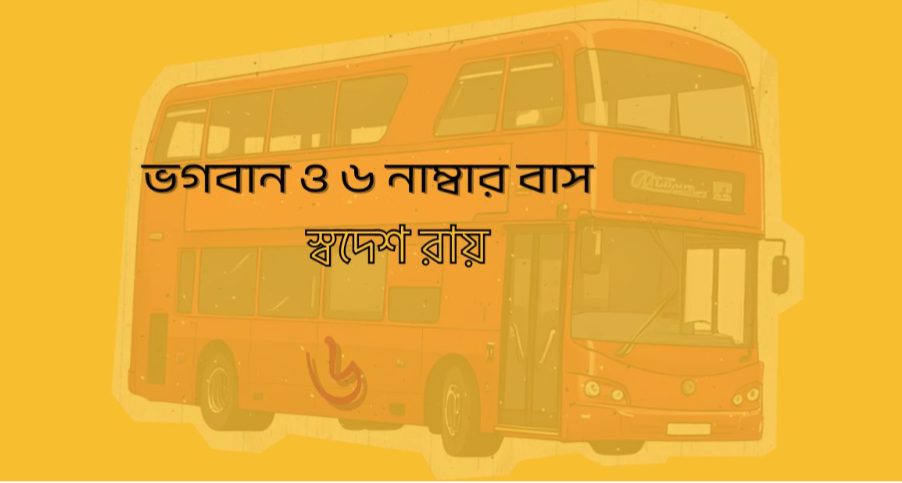চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস ও রাস্তা
যে কোন বিষয় অভ্যাস করি কিংবা অন্যের নিকট উপদেশ পাইয়া থাকি, তাহাকে শিক্ষা বলা যায়। আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুই জানিতে পারি না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রথমে মাতা পিতা, তদ্পর অন্যান্য মানবের নিকট হইতেও নানা উপায়ে ক্রমে নানা বিষয় অভ্যাস করিতে শিখি এবং উপদেশ প্রাপ্ত হই। এই নানা বিষয় এবং নানা উপদেশ বহুবিধ ভাষায় ও গ্রন্থে শিখিবার প্রয়োজন হয়। যেমন আহার না করিলে শরীর ক্রমে পুষ্ট, কান্তিযুক্ত ও বলশালী হয় না, তেমনই নানাবিধ বিষয়ের শিক্ষা ও উপদেশ লোক প্রমুখাৎ ও নানা ভাষার গ্রন্থে প্রাপ্ত না হইলে মানবের মানসিক প্রবৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট, মার্জিত বা কার্যক্ষম হয় না। অভ্যাস ও উপদেশের বলে মানব সংসারে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হয়। শিখিবার ইচ্ছা মানব হহৃদয় মাত্রেই নিহিত রহিয়া আছে। সুতরাং কোন না কোন প্রকার শিক্ষা মানব প্রাপ্ত হয়। তবে কাল ও অবস্থা ভেদে সকল মানব সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কেহ সংস্কৃত ভাষায়, কেহ গ্রিক ভাষায়, কেহ লাটিন ভাষায়, কেহ ইংরাজি ভাষায়, কেহ দর্শন শাস্ত্রে, কেহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে, কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্রে, কেহ অঙ্ক শাস্ত্রে, কেহ সাহিত্যে, কেহ কৃষি বিদ্যায়, কেহ শিল্পকার্যে, কেহ স্থাপত্য বিদ্যায়, কেহ যুদ্ধ বিদ্যায়, কেহ সঙ্গীত বিদ্যায় পণ্ডিত হয়। এইরূপে মানবের শিক্ষা।
এই স্বাভাবিক শক্তি বলে পুরাকালে পিতা মাতা বালক বালিকাদের সমানভাবে লেখাপড়া, জ্ঞান, ধর্ম ও নীতি শিখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। মধ্য এশিয়া হইতে একদল আর্য জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে। এই আর্য জাতিরা ভারতবর্ষের আদিমবাসীদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। এই আর্য জাতির ভাষা সংস্কৃত। আর্য সন্তানেরা, ধর্ম, নীতি, রাজকার্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, যুদ্ধ বিদ্যা, সকল বিষয়ই বেশ ভাল জানিতেন এবং সংস্কৃত ভাষায় সকল বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এই সংস্কৃত একটি অতি প্রাচীন পবিত্র সম্পূর্ণ ভাষা। একজন ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে কিরূপ উচ্চ আসন দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত অংশে পরিচয় পাওয়া যাইবে।’ সংস্কৃত অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। “সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বজ্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। পুরাকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ভারতের দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, সাহিত্য, বেদবেদান্ত প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার বলে আর্য ঋষিরা ভারতকে আচার, ব্যবহার, ধর্ম, নীতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসনে উপনীত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ঋষি ও পণ্ডিতেরা আদিকাল হইতে ঐ দেব ভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন। অতএব আদিম নিবাসীরাও ঐ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বেদ হইতে মনু পর্যন্ত, মনু হইতে পুরাণ পর্যন্ত, পুরাণ হইতে তান্ত্রিক সময় পর্যন্ত, তান্ত্রিক সময় হইতে বৌদ্ধদের সময় পর্যন্ত, যেমন আচার, ব্যবহার, ধর্ম, নীতি ও সভ্যতার পরিবর্তন হয়, তেমনই সংস্কৃত ভাষারও বিস্তর পরিবর্তন হয়। অশোক রাজার রাজত্ব সময়ের একশত বৎসরেরও অধিককাল পরে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষা রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে প্রচলিত হয়। ঐ প্রাকৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলা ভাবার সৃষ্টি হইবার সময় হইতে বা উহার ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব হইতেই সংস্কৃত ভাষা সর্বসাধারণের ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল না। তখন কথোপকথন আদি সংস্কৃত ভাষায় রহিত হইয়া তৎসময়ের প্রচলিত ভাষায় কথোপকথন আদি হইতে লাগিল। এখন বাংলা ভাষাতেই কথোপকথন আদি সম্পন্ন হয়।
এমন দুর্দিনে ভারত যবনাক্রান্ত হইলে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চারও হ্রাস হইতে লাগিল। সংস্কৃত ভাষার চর্চার হ্রাসে বঙ্গদেশে বাংলা ও যাবনিক রাজভাষার চর্চার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশ যবনাক্রান্ত হওয়ার পরেও পাঠানাদিগের রাজত্বকালে বাংলার সাহিত্য, দর্শন, নীতি ও ধর্ম শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা চণ্ডীদাসের ‘পদাবলী’, বিদ্যাপতির কবিত্ব, বসুবংশ গুণরাজ খাঁর “শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিজয়,” রূপ সনাতনের ধর্মভাব ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন, “চিন্তামণি দীধিতি” প্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় শাস্ত্র বিচারের প্রাধান্য, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রেম-ভক্তির তরঙ্গ, বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবত”, কৃষ্ণদাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃত”, উদয়নাচার্য ভাদুড়ি, পুরন্দর বসু ও পরমানন্দ রায়ের কুলশাস্ত্র প্রণয়নে প্রকাশ পাইতেছে এবং আজিও বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ ভাব আর অধিক দিন স্থায়ী রহিল না। ক্রমে বঙ্গদেশ যবনের পদানত। রাজ দরবারে যবন ভাষারই প্রাধান্য। সুতরাং বঙ্গবাসীরা বিশেষত কায়স্থেরা নিজ নিজ সন্তানকে মুসলমান রাজদরবারের কর্মোপযোগী করিবার জন্য যবন ভাষা শিক্ষা দিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। যবন ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সন্তানেরা যবন ভাবাপন্নও হইতে লাগিলেন এবং মুসলমান ও কায়স্থের হস্তেই পারসি ভাষায় (যবন ভাষা) রাজকার্য নির্বাহের ভার অর্পিত হইতে লাগিল। রাজসাহী বঙ্গদেশের অন্তর্গত; সুতরাং রাজসাহীতেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইল।”
বলা যমে ক্যাস ও ও দয় কাল পারে কেহ কেহ দ্যায়
পড়া, আর্য সায়, জন কি হয়া র্ষের চার, তন। বস্তর
সেনবংশীয় রাজাদের সময়েও রাজসাহীতে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেবল সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা হইত। মুসলমান রাজত্বকালেও যাহারা মুসলমান রাজদরবারে দাসত্ব করিবার প্রয়াসী হইতেন অথবা মুসলমান রাজদরবারের সংস্রবে থাকিবার আবশ্যক মনে করিতেন অথবা কোন কারণে বাধ্য হইতেন, তাহারা সংস্কৃত, বাংলা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার একটি শাখা বিশেষ।” এই বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা সম্ভূত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বাংলা ভাষা বর্তমান কালের ন্যায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল না। সংস্কৃত, মৈথিল, কান্যকুব্জ, হিন্দি, পারসি প্রভৃতি মিশ্রিত বাংলাই বেশি প্রচলিত ছিল। রাজসাহীতে রাজা, জমিদারের বাসই বেশি। অতএব রাজভাষা শিক্ষা দেওয়ারই বেশি প্রয়োজন হইয়া উঠে। তথাপি ইংরাজ রাজত্ব সময় পর্যন্তও রাজসাহীতে বহুবিধ সংস্কৃত “চতুষ্পাঠী” ছিল। সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঁঠিয়া, নাটোর ও দিঘাপতিয়া বংশের রাজাদের রাজত্ব সময়ে তাহাদের রাজ্যে বিস্তর “চতুষ্পাঠী” ছিল এবং ঐ চতুষ্পাঠীগুলি রক্ষার জন্য রাজারা বহু অর্থ ও ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার নির্দশন এখনও রাজসাহীতে এবং অন্যান্য জেলার অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে। ইহা কথিত আছে যে রাজসাহী প্রদেশের চতুষ্পাঠী রক্ষার জন্য মহারাণী ভবানী বৃত্তি দান করিয়া যান এবং এই দান স্থির রাখিবার জন্য জেলার কালেক্টর সাহেবের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, বার্ষিক রাজস্বের সহিত রাণীর বার্ষিক বৃত্তিদানের টাকা সংযোজিত হইল। বৃত্তিদানের টাকার সহিত নির্ধারিত রাজস্ব মহারাণী ভবানী কালেক্টর সাহেব সমীপে বার্ষিক দাখিল করিবেন এবং কালেক্টর সাহেবযোগে চতুষ্পাঠীয় পণ্ডিতগণ নির্ধারিত বৃত্তি পাইবেন। এই প্রকারে মহারাণীর জমিদারির রাজস্ব বর্ধিত হারে নির্ধারিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সে সকল চতুষ্পাঠী প্রায় না থাকায় এবং চতুষ্পাঠীর আদি পণ্ডিতের উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকায় বা অন্য কোন কারণে মহারাণী ভবানীর প্রদত্ত বৃত্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইবে।
এই সময় সাধারণ বাংলা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে “সরকার” (যাহারা পরে “গুরুমহাশয়” বলিয়া পরিচিত) জমিদারি ও মহাজনী কার্যনির্বাহ উপযোগী শিক্ষা দিতেন। জমিদারের পাটওয়ারী, আমিন, শুমারনবীশ, জমানবীশ প্রভৃতিও পাঠশালার কার্যও নির্বাহ করিতেন। শুরুমহাশয়ের মাসিক ও টাকার বেশি আয় ছিল না। স্বতন্ত্র পাঠশালা গৃহ ছিল না। গুরুমহাশয় নিজগৃহে, কি কোন চণ্ডীমণ্ডপে, কি কাহার বৈঠকখানায় পাঠশালার কার্য নির্বাহ করিতেন। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার ন্যায় রাজসাহীতে প্রকৃত উপযুক্ত “গুরুমহাশয়ের” পাঠশালার প্রথা প্রচলিত ছিল না। এ প্রণালীর শিক্ষা রাজসাহীতে নিতান্ত কম ছিল।
উপরের লিখিত চতুষ্পাঠীতে দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞনিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং কোন কোন স্থানে বেদ বেদান্ত পড়ান হইত। সেকালের রাজসাহীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পুঠিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা বৎসাচার্য, রাজা কংসনারায়ণের আদিপুরুষ পুরুষোত্তম বেদান্তী এবং তাহার সহোদর কুল্লুকভট্ট’ ও উদয়নাচার্য ভাদুড়ির পাণ্ডিত্যে রাজসাহীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কুল্লুক স্বকৃত মন্বার্থ মুক্তাবলী নামক টীকায় কেবল যে তাহার বৃদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও স্থির গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এমন নহে। একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশান্তর্গত টীকাকারগণ মধ্যে কুল্লুককে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। ইহা রাজসাহী প্রদেশের পক্ষে অসীম গৌরবের কথা। এস্থলে আর কতকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের গুণকীর্তন করা প্রয়োজন বোধ করিলাম। যে যে পণ্ডিতগণ রাণী ভবানী প্রদত্ত দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হইতেছেন তাহারও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট