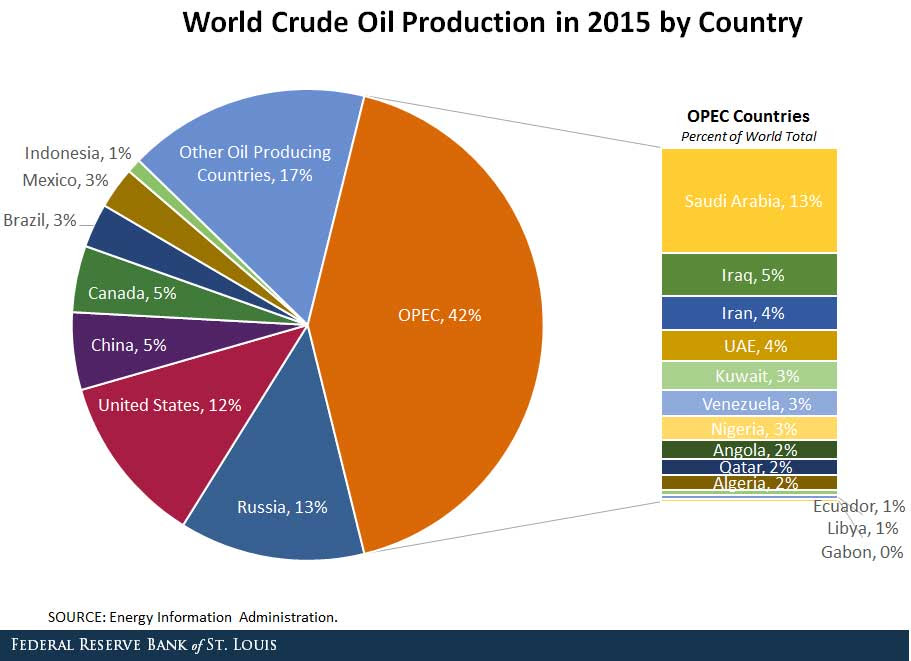একটি টাইফুনের ভারী বৃষ্টিতে জুলাইয়ে ফিলিপাইন্সের পাম্পাঙ্গায় জলমগ্ন রাস্তা। দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বীমা কভারেজের ঘাটতি—যাকে ‘প্রোটেকশন গ্যাপ’ বলা হয়—এখন বড় উদ্বেগ।
বর্তমান জলবায়ু নীতিগুলো এভাবেই চলতে থাকলে ২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে, যা বিশ্বের বহু অঞ্চলে জীবনযাত্রার মানকে খারাপ করে দেবে। শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বন্যা, উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ ও খরার কারণে বৈশ্বিক জিডিপি ক্ষতি ৮ শতাংশের বেশি হতে পারে।
পরবর্তী আর্থিক সংকটের বীজ ইতিমধ্যেই বপন হয়ে গেছে। তা নীরবে প্রবৃদ্ধিকে দুর্বল করছে, ঋণ বাড়াচ্ছে এবং ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া ডেকে আনা ধাক্কা তৈরি করছে। এই চালিকাশক্তি কী? জলবায়ু পরিবর্তন।
এশিয়া ২০৭০ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সর্বোচ্চ ১৭ শতাংশ—এবং শতাব্দীর শেষে ৪১ শতাংশ পর্যন্ত—হারাতে পারে, যদি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণহীন থাকে; এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে এমন সতর্কতা দেওয়া হয়।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঝুঁকি বিশেষভাবে তীব্র। টাইফুন, বন্যা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম গরমে অঞ্চলটি অত্যন্ত উন্মুক্ত; একই সঙ্গে বহু অর্থনীতি কৃষি, মৎস্য ও পর্যটনের মতো জলবায়ু-সংবেদনশীল খাতে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল—বললেন হাউডেন নামের বীমা ব্রোকিং প্রতিষ্ঠানের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্য বিভাগের প্রধান ড্যানিয়েল ফেয়ারওয়েদার।

তিনি যোগ করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ তীব্র তাপের মুখে পড়বে, যা শ্রম উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য নিরাপত্তাকে দুর্বল করবে। এসব কোনো নতুন কথা নয়। তবে আর্থিক খাত এখন বুঝতে শুরু করেছে ঝুঁকির ব্যাপ্তি কতটা বিশাল—এবং নতুন বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে এগুলো কত গভীর, প্রাতিস্বিক (সিস্টেমিক) ও দ্রুত বেড়ে চলেছে।
ফেয়ারওয়েদারের ভাষায়, “জলবায়ু পরিবর্তন প্রাতিস্বিক আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে; সেগুলো যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড় সংকটে পরিণত হতে পারে।”
তার মতে, একাধিক চাপ একসঙ্গে এসে দেশগুলোর ধাক্কা মোকাবিলার সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে। উৎপাদনশীলতা হ্রাস ও দুর্যোগজনিত ক্ষতিতে জিডিপি সংকুচিত হতে পারে। অভিযোজন ব্যয় বাড়তে থাকলে সার্বভৌম ঋণমান (ক্রেডিট রেটিং) কমে যেতে পারে। খাদ্য ও জ্বালানির দামে ধাক্কা উঠে ভোক্তা ও বাজার অস্থির হতে পারে। আর এখন, কিছু অঞ্চলে বীমা-অযোগ্যতা (আনইনশিওরেবিলিটি) বাড়ায় সম্পদের দামে ঝুঁকি দেখা দিয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাড়তে থাকা আর্থিক ঝুঁকি
ব্যাংকারদের উদ্বেগ বাড়ছে।ওসিবিসি ব্যাংকের গ্রুপ ইএসজি রিস্ক অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটির প্রধান চ্যং বি লেং বলেন, “আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে বর্তমান ও বাড়তে থাকা প্রাতিস্বিক ঝুঁকি হিসেবে দেখি। অতিরিক্ত ঘনঘন ও তীব্র চরম আবহাওয়া জীবন, ব্যবসা ও অবকাঠামোতে ব্যাঘাত ঘটায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এর মানে হলো সম্পদের অবমূল্যায়ন ও ঋণমানের অবনমনের ঝুঁকি।”
তিনি দ্য স্ট্রেইটস টাইমসকে বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য দুটি প্রধান জলবায়ু ঝুঁকি স্পষ্ট। প্রথমটি বন্যা-ঝুঁকি—কারণ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বড় অংশই নিম্নাঞ্চলীয়, ঘনবসতিপূর্ণ উপকূলে কেন্দ্রীভূত। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো দেশে বন্যার ঘনত্ব ইতিমধ্যেই বেড়েছে, এবং এসব ঘটনা বৃহত্তর আঞ্চলিক অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। “এসব ঝুঁকি কমাতে নীতিমূলক পদক্ষেপ ও অভিযোজন কৌশল দরকার,” তিনি বলেন।
দ্বিতীয়টি হলো রূপান্তর-ঝুঁকি (ট্রানজিশন রিস্ক)। ২০৫০ সালের মধ্যে নিট-শূন্য নির্গমন অর্জন করতে হলে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও তেল-গ্যাস উৎপাদনসহ জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদ থেকে দ্রুত সরে আসতে হবে। সমস্যাটি হলো, এ খাতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ হয়েছে, এবং এশিয়ায় বহু সম্পদের আয়ুষ্কাল শেষ হতে এখনও বহু বছর বাকি। শক্তি দক্ষতার কড়াকড়ি ও কার্বনের দামে বৃদ্ধি ঘটিয়ে জলবায়ু প্রশমন সফল হলে উল্টোটাই হতে পারে—জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অনেক বিনিয়োগ আর্থিকভাবে অকার্যকর বা ‘স্ট্র্যান্ডেড অ্যাসেট’-এ পরিণত হতে পারে। এতে ওই খাতে ঋণ এক্সপোজার থাকা ব্যাংকগুলোর জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রধান শক্তির উৎস হিসেবে কয়লা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করলে গভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে—খনি বন্ধে কর্মসংস্থান হারানো, স্থানীয় অর্থনীতি ও জীবিকার ওপর ঢেউ-তোলা প্রভাবসহ—বলেন চ্যং। একই সঙ্গে, নতুন প্রযুক্তি ও রেট্রোফিটিংয়ে মূলধনী বিনিয়োগ এবং স্বল্প-কার্বন বিকল্পের প্রতিযোগিতার কারণে ব্যবসার খরচও বাড়বে।
সিঙ্গাপুরে জলবায়ু-ভিন্ন এক পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কাজ চলছে—উন্নত ড্রেনেজ, উপকূল রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, ভবন নকশা ও শীতলীকরণ ব্যবস্থার জ্বালানি দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে।
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অবকাঠামো ও রিয়েল এস্টেটের জন্য বড় হুমকি; তাই উপকূল সুরক্ষার উপায় নিয়ে সরকারের চলমান গবেষণা এবং ইস্ট কোস্টে ‘লং আইল্যান্ড’-এর মতো পরিকল্পিত বিনিয়োগ চলছে।
পরোক্ষ ঝুঁকিগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। খাদ্য ও অন্যান্য কাঁচামালের জন্য বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর সিঙ্গাপুরের নির্ভরতা তাকে চরম আবহাওয়াজনিত বিঘ্নের মুখে ফেলে। এ কারণেই দেশটি সরবরাহকারী ও উৎস অঞ্চল বৈচিত্র্য করছে, আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব জোরদার করছে, এবং দেশীয় উৎপাদন ও জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করছে। তবু খামখেয়ালি আবহাওয়া সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। চ্যং বললেন, “খরা পানির যোগান ও খাদ্য প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে, ফলে দামের অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।”
আরও ঝুঁকি আছে। সিঙ্গাপুরের ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিদেশেও বড় বিনিয়োগে যুক্ত। বিদেশে জলবায়ুজনিত দুর্যোগ বা স্ট্র্যান্ডেড অ্যাসেট সিঙ্গাপুরের আর্থিক ব্যবস্থায় পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে—ইঙ্গিত দিলেন ফেয়ারওয়েদার।

নতুন ঝুঁকি: বীমা-অযোগ্যতা ও ব্যাংক-অযোগ্যতা
এখন দিগন্তে বড় এক আর্থিক ঝুঁকি—বীমা খাত সামনের সারিতে। আবহাওয়াজড়িত দুর্যোগ থেকে ক্ষতি ক্রমেই বাড়ছে। ফেয়ারওয়েদার বলেন, “বীমার সামর্থ্য ও প্রাপ্যতা বিশ্বজুড়েই চাপের মধ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াও এর বাইরে নয়।” এটি বড় সমস্যা, কারণ দুর্যোগকালে বীমা একধরনের সামাজিক সুরক্ষা—আর বীমা ছাড়া ব্যাংক ঋণ দেয় না।
২০২৪ সালে বৈশ্বিক বীমা ক্ষতির ৯০ শতাংশের বেশি—মোট ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের—কারণ ছিল আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ; তার মধ্যে ১৪০ বিলিয়ন ডলার ছিল বীমা-কভার্ড—জানিয়েছে রিইনশিওরার মিউনিখ রি। বছরটি শিল্পের জন্য খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। কিন্তু এই সংখ্যার আড়ালে আরেকটি উদ্বেগজনক চিত্র আছে—দরিদ্র দেশগুলোর বীমা কভারেজের ঘাটতি, বা ‘প্রোটেকশন গ্যাপ’। মিউনিখ রি-এর হিসেবে, ১৯৮০ সাল থেকে এশিয়া-প্যাসিফিকে আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে; এর মাত্র প্রায় ১০ শতাংশ বীমার আওতায় ছিল।
উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের টাইফুন ইয়াগি ফিলিপাইন্স, দক্ষিণ চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, লাওস ও মিয়ানমারের অংশে ভয়াবহ বন্যা ঘটায়—সামগ্রিক ক্ষতি ১৪ বিলিয়ন ডলার, কিন্তু বীমা-কভার্ড ক্ষতি ছিল মাত্র ১.৬ বিলিয়ন ডলার—বলেছে মিউনিখ রি।
ধনী দেশগুলো—যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের মতো—এখন ক্রমবর্ধমান বিপর্যয়ক্ষতি সামাল দিতে বীমা প্রিমিয়াম তীব্রভাবে বাড়াচ্ছে, কখনও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় (বনানলে, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ে ঝুঁকিপূর্ণ) কভারেজ দিতেই পিছিয়ে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় টানা ভয়াবহ বনানল, বন্যা ও সাইক্লোনের পর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রিমিয়াম বেড়ে কিছু অঞ্চলে বীমা কার্যত অপ্রাপ্য হয়ে গেছে; আনুমানিক ৭০ শতাংশ ব্যবসা আন্ডারইনশিওরড—হাউডেনের হিসাব।

যুক্তরাষ্ট্রে কভারেজের ঘাটতি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে—সেনেট বাজেট কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর শেলডন হোয়াইটহাউসের প্রকাশিত এক গবেষণায় গৃহবীমায় জলবায়ু-চালিত সংকটের ছবি উঠে এসেছে। ২০১৮–২০২৩ সময়কালে ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও ডিসির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন গৃহমালিকদের জন্য বীমা পাওয়া কঠিন করে তুলছে এবং বাড়ির মূল্য কমাচ্ছে—যা বহু আমেরিকানের প্রধান আর্থিক সম্পদকে ক্ষয় করছে। এর রয়েছে সামষ্টিক আর্থিক অভিঘাত। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ‘ফার্স্ট স্ট্রিট’ নামের জলবায়ু আর্থিক ঝুঁকি প্রতিষ্ঠান অনুমান করে, জলবায়ু-ঝুঁকির কারণে আগামী ৩০ বছরে অপরিবর্তিত রিয়েল এস্টেট মূল্যে সম্ভাব্য ১.৪৭ ট্রিলিয়ন ডলার হ্রাস ঘটতে পারে।
এতে কমিউনিটি ‘খালি হয়ে যাওয়ার’ ঝুঁকিও আছে। ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল ফেব্রুয়ারিতে সেনেটের এক কমিটিতে সাক্ষ্যে বলেন, “আরও ১০–১৫ বছর পরে এমন অঞ্চল দেখা যাবে যেখানে আপনি মর্টগেজ পাবেন না, সেখানে এটিএম থাকবে না, ব্যাংকের শাখাও থাকবে না”—অর্থাৎ ব্যাংক ও ব্যবসা উচ্চ জলবায়ু-ঝুঁকির এলাকা থেকে সরে যাবে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মূল সমস্যা হলো স্থায়ী বীমা-ঘাটতি। এর অর্থ, জলবায়ু পরিবর্তনের বাড়তি ব্যয় স্থানীয় জনগণ ও সরকারের কাঁধে পড়ছে। তবে ঘনঘন ভয়াবহ আবহাওয়ার আর্থিক ধাক্কা অন্তত কিছুটা কমাতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এগুলো কোনো জাদু সমাধান নয়, কিন্তু সহায়ক।
ফেয়ারওয়েদার বলেন, ‘প্যারামেট্রিক’ বীমা—যেখানে পূর্বনির্ধারিত সূচক (যেমন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বাতাসের বেগ) ট্রিগার হলেই অর্থ ছাড় হয়—প্রোটেকশন গ্যাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে তড়িৎভাবে জরুরি প্রয়োজনের টাকা পৌঁছে দেওয়া যায়।
সিঙ্গাপুরের মোনেটারি অথরিটি (এমএএস) অঞ্চলের সহায়তায় রিইনশিওরেন্স সক্ষমতা বাড়াতেও কাজ করছে; যেমন ইনসুরেন্স-লিঙ্কড সিকিউরিটিজ। সিঙ্গাপুরে ৩০টিরও বেশি ‘ক্যাটাস্ট্রফি বন্ড’ ইস্যু হয়েছে—যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এশিয়ার বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ কভার করে—মোট কভারেজ ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি।
সিঙ্গাপুর ‘সাউথইস্ট এশিয়া ডিজাস্টার রিস্ক ইনসুরেন্স ফ্যাসিলিটি’রও অংশ—বিশ্বব্যাংকের অংশীদারিত্বে আসিয়ান+৩-এর একটি উদ্যোগ—যার লক্ষ্য জলবায়ু ধাক্কার বিরুদ্ধে অঞ্চলের আর্থিক সক্ষমতা জোরদার করা। তবু সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও পুনরাবৃত্ত বন্যার ঝুঁকিতে থাকা সম্পদের ‘বীমা-অযোগ্যতা’ও বড় হুমকি—যা সহনশীলতা ও ঝুঁকি-হ্রাসে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আরও জোরালো করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ঝুঁকি স্পষ্ট করছে
এ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো জলবায়ু-জনিত আর্থিক ঝুঁকি বোঝা, হালনাগাদ করা ও কমানোর চেষ্টা করছে। তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো দৃশ্যপট-পরিকল্পনা—আগাম চেয়ে দেখা, কোন নীতি ও বিনিয়োগে কী সমন্বয় আনতে হবে যাতে ভৌত (ফিজিক্যাল) ও রূপান্তর-ঝুঁকি কমে এবং সম্ভাব্য সুযোগগুলো ধরা যায়। ১৪৭ সদস্যবিশিষ্ট ‘নেটওয়ার্ক ফর গ্রিনিং দ্য ফিনান্সিয়াল সিস্টেম’ (এনজিএফএস)—যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা যুক্ত—জলবায়ু-ঝুঁকির দৃশ্যপট পরীক্ষায় অগ্রণী।
২০২৪ সালে এনজিএফএস হালনাগাদ দৃশ্যপট প্রকাশ করে। সাতটি দৃশ্যপট রয়েছে—সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী (২০৫০ সালে নিট-শূন্যের লক্ষ্য) থেকে শুরু করে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক (খণ্ডিত বিশ্ব, জলবায়ু পদক্ষেপে দীর্ঘ বিলম্ব) পর্যন্ত। বর্তমান নীতিগুলো ২১০০ সালে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার পথেই—যা বহু অঞ্চলে বসবাসের পরিস্থিতি খারাপ করবে। শতকের মাঝামাঝি বন্যা, উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ ও খরায় বৈশ্বিক জিডিপি ক্ষতি ৮ শতাংশ ছাড়াতে পারে।
নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ভবন–শিল্প–পরিবহন বিদ্যুতায়ন, কার্বন সংরক্ষণ ও অপসারণ, এবং অর্থনীতিজুড়ে জ্বালানি দক্ষতায় বড় বিনিয়োগ এসব ঝুঁকি অনেকটাই কমাতে পারে।
এমএএস—যাকে অঞ্চলের ‘রেফারেন্স’ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়—আর্থিক খাতের জলবায়ু-সহনশীলতা জোরদারে কাজ করছে এবং পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যাশা নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জলবায়ু দৃশ্যপট বিশ্লেষণ ও স্ট্রেস টেস্ট করতে উৎসাহিত করা। এমএএস আঞ্চলিক নির্গমন ও জলবায়ু ঝুঁকি কমাতে সবুজ বিনিয়োগও জোরদার করছে। সিঙ্গাপুরের ‘ফিন্যান্সিং এশিয়াস ট্রানজিশন পার্টনারশিপ’—যার লক্ষ্য সর্বোচ্চ ৫ বিলিয়ন ডলার তোলা—সম্প্রতি ‘গ্রিন ইনভেস্টমেন্টস পার্টনারশিপ’-এর অধীনে প্রথম ক্লোজ সম্পন্ন করেছে; এর অর্থ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সৌরশক্তিসহ নানা সবুজ বিনিয়োগে তহবিল যাবে।

নির্গমন না কমালে রেহাই নেই
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সব প্রয়াসের পরও বড় ঝুঁকি রয়ে গেছে—সরকার ও বেসরকারি খাতের যৌথ পদক্ষেপের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনও প্রভাবের পরিধি ও জরুরিতা-সাপেক্ষে যথেষ্ট নয়।
উদাহরণ হিসেবে, এখন পরিষ্কার জ্বালানিতে বিনিয়োগ বছরে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার—নিট-শূন্য লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় ৪.৫ ট্রিলিয়নের অর্ধেকেরও কম। সিঙ্গাপুরের জলবায়ু-কার্যক্রম বিষয়ক রাষ্ট্রদূত রবি মেনন সাম্প্রতিক এক ভাষণে বলেন, এশিয়ায় বছরে কমপক্ষে ৮০০ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি রয়েছে।
জাতিসংঘ বলছে, এ দশকের শেষের আগেই নির্গমন অনেক বেশি মাত্রায় কমাতে হবে। ঝুঁকি আমরা জানি—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃশ্যপট, জলবায়ু বিজ্ঞানী ও বীমা শিল্পের ঝুঁকি বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত মানচিত্রায়ন করছেন এবং হালনাগাদ দিচ্ছেন।
আরও শক্তিশালী প্রশমন ও অভিযোজন নীতিমালা করপোরেটগুলোর অর্থায়ন মডেলকে বিবর্তিত হতে বাধ্য করতে পারে—ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়া, প্রবৃদ্ধির উৎস বৈচিত্র্য করা এবং সহনশীল অবকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে।
আসন্ন দিনগুলোতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে হালনাগাদ জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনার ঢল নামবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্যারিস চুক্তির অধীন এসব ‘ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন’ দেখাবে—বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত—এবং তার ওপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

 ডেভিড ফগার্টি
ডেভিড ফগার্টি