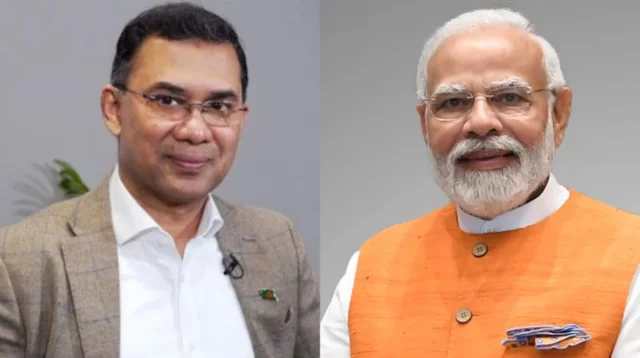নতুন প্রজন্মের মূল্যবোধের পালাবদল
দক্ষিণ সিউলের এক রৌদ্রোজ্জ্বল ফ্ল্যাটে ২৫ বছর বয়সী চো সাং-হুন বসে আছেন ল্যাপটপের সামনে, চাকরির তালিকা একের পর এক স্ক্রল করছেন— যেন নিজের ভবিষ্যৎকে পর্দার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন।
দেশের সেরা স্কুলগুলোর শিক্ষা পেয়েও তিনি আজ দ্বিধাগ্রস্ত। কোন কাজ তাঁর জন্য উপযুক্ত হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তাই এখন এশিয়ার কোটি তরুণের জীবনের প্রতিচ্ছবি, যারা নিঃশব্দে বদলে দিচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংজ্ঞা।
চো বলেন, “আমি যেকোনো কাজ নিতে পারব না। আমাকে বুঝতে হবে, কোন কাজটা আমার জন্য সঠিক।”
বছরের পর বছর ধরে প্রতিযোগিতার এই দৌড়ে তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছে কঠোর পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ এবং ইন্টার্নশিপের ধাপ। তবুও তিনি নিজেকে বলেন “দ্বিতীয় হাতের নবীন”—একটি শব্দ যা কোরিয়ানরা ব্যবহার করেন সেই তরুণদের জন্য, যারা সিস্টেমে প্রবেশের আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।
চো আরও বলেন, “আমাদের বাবা-মায়ের প্রজন্মে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করলেই বড় কোম্পানিতে চাকরি পাওয়া সহজ ছিল, অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক। এখন আর তা নেই।”
দক্ষিণ কোরিয়া: ‘কেবল বিশ্রামে থাকা’ প্রজন্ম
যে দেশ কঠোর কর্মসংস্কৃতি ও নির্মম শিক্ষাব্যবস্থার জন্য পরিচিত, সেই দক্ষিণ কোরিয়াই এখন দেখছে এক নতুন প্রজন্মের ধীরগতি ও ক্লান্তি।
২০২১ সালের এক জরিপে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক তরুণ বিশ্বাস করেন না যে তাঁরা সামাজিকভাবে উন্নতি করতে পারবেন। চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত ৪ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি কোরিয়ান নিজেদের “শুধু বিশ্রামে থাকা” হিসেবে বর্ণনা করেছেন—এক দশকে এই সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ।
অনেকে এখন একা বসবাস বা ‘হঞ্জক’ জীবনযাপন বেছে নিচ্ছেন—আংশিক সময়ের কাজ করছেন, আর ফাঁকে নিজেদের শখ পূরণ করছেন।২৬ বছর বয়সী রেস্তোরাঁ কর্মী লি সাং-ওয়ান বলেন, “আমি প্রচলিত কোনো কোম্পানিতে কাজ করতে চাই না। আমি শুধু এতটুকু উপার্জন করতে চাই যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে পারি, ঘুরতে পারি, নিজের মতো করে জীবন কাটাতে পারি।”
কোরিয়া শ্রম গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা কিম ইউ-বিন বলেন, “এখনকার তরুণরা চাকরিতে স্বাধীনতা ও নমনীয়তা খোঁজে। আগের প্রজন্ম চাইত স্থায়িত্ব ও আয়।”
তবে কাঠামোগত সমস্যার কারণেও অনেক তরুণ তাদের পছন্দের চাকরি পাচ্ছেন না। কিম বলেন, “দক্ষিণ কোরিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকের হার অত্যন্ত বেশি, কিন্তু যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির সংখ্যা সীমিত।”
এমনকি যারা নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন, তারাও বেকার। ২০২১ সালে বেকার তরুণদের অর্ধেকই ছিলেন ডিগ্রিধারী, অথচ ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে কর্মীর ঘাটতি রয়ে গেছে।

জাপান: ‘উদাসীন আলোকিত’ প্রজন্ম
জাপানে বছরের পর বছর অর্থনৈতিক স্থবিরতা তরুণদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক নীরব আত্মসমর্পণ। এই প্রজন্মকে বলা হয় “সাতোরি সেদাই”—অর্থাৎ “আলোকপ্রাপ্ত প্রজন্ম”, যারা বস্তুগত সাফল্যের চেয়ে মানসিক শান্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
তারা আর গাড়ি, বিদেশ ভ্রমণ বা বিলাসী জীবন চায় না। বরং খোঁজে ছোট ছোট আনন্দ—কনভিনিয়েন্স স্টোরের কফি, এনিমে দেখা, বা স্থিতিশীল কিন্তু নিরুত্তেজনাপূর্ণ কাজ।
ইয়োকোহামার ২৮ বছর বয়সী শিক্ষক মাতসুবোকুরি বলেন, “আমি ছোট ছোট দৈনন্দিন সুখকে গুরুত্ব দিই। টাকা বা মর্যাদার জন্য নিরন্তর পরিশ্রম নয়, বরং একটু স্বস্তিতে বাঁচাটাই আমার লক্ষ্য।”
টোকিওর ২৫ বছর বয়সী রিও ইয়ামামোতো নিজেকে বলেন “ফ্রিটার”—অর্থাৎ আংশিক সময়ের অনিয়মিত চাকরিজীবী। তিনি বলেন, “যত বেশি উপরে উঠবেন, তত কম সময় পাবেন নিজের জন্য। সময়মতো অফিস থেকে বের হওয়াটাই আমাদের একমাত্র স্বাধীনতা।”
চুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী ইজুমি তসুজি বলেন, “এখন এমন এক সময় চলছে, যখন প্রত্যেকে নিজের মতো করে বাঁচার পথ বেছে নিচ্ছে।”
জাপানে প্রায় ১৪ লাখ তরুণকে ‘ফ্রিটার’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তসুজি বলেন, “এটি আত্মসমর্পণ নয়, বরং অভিযোজন—তারা নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে চায়।”
সরকার অতিরিক্ত কাজের সময় সীমিত করা, পার্ট-টাইম কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে পার্ট-টাইম কর্মীদের স্থায়ী চাকরিতে রূপান্তরিত করতে।
চীন: ‘লেট ইট রট’ প্রজন্মের ক্লান্তি
চীনে “তাং পিং” বা “শুয়ে থাকা” শব্দটি প্রথম ভাইরাল হয় ২০২১ সালে—যখন এক তরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন যে অতি দীর্ঘ কর্মঘণ্টা ও জীবনযাপনের চাপে শুয়ে পড়াই প্রতিরোধের সম্মানজনক উপায়।
এই ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে লাখ লাখ তরুণের মধ্যে, যারা ৯টা থেকে ৯টা, সপ্তাহে ছয় দিন কাজের সংস্কৃতিতে বন্দী। পরে এর চেয়েও হতাশ একটি শব্দ জনপ্রিয় হয়—“বাই লান” বা “পচে যেতে দাও”—যা বোঝায় সম্পূর্ণ ক্লান্তি ও উদাসীনতা।

২৫ বছর বয়সী ছাত্র স্যু রুইইয়াং বলেন, “চীনে এখন কঠোর পরিশ্রম ফল দেয় না। তাই আমি তাং পিং অনুসরণ করি—আমার কোনো বড় লক্ষ্য নেই।”
চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১৯৯২ সালের ১৪ শতাংশ থেকে কমে গত বছর মাত্র ৫ শতাংশে নেমেছে। কর্মসংস্থান কমেছে, মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। ফলে তরুণরা বলছেন, পরিশ্রম করেও তারা বাড়ি কেনার সামর্থ্য রাখেন না।
সরকার এই মনোভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। তরুণদের পুনরায় কাজে ফিরিয়ে আনতে ভর্তুকি ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু হতাশা এখন অনলাইনে রসিকতা ও মিমের আকারে টিকে আছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া: বেঁচে থাকার লড়াই
পূর্ব এশিয়ার তরুণরা যখন মানসিক ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়ছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লড়াই আরও মৌলিক—বেঁচে থাকার।
ফিলিপাইনে তরুণদের মতে, সাফল্য মানে এখন কেবল টিকে থাকা। এক ছাত্র বলেন, “আমি যতই পরিশ্রম করি না কেন, যদি সিস্টেম একই থাকে, কিছুই বদলাবে না।”
জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ তরুণ এখন বিদেশে কাজ করতে চায়। ২০২৪ সালে বিদেশে পাঠানো রেমিট্যান্স ফিলিপাইনের জিডিপির ৯ শতাংশে পৌঁছেছে।
থাইল্যান্ডে শিক্ষায় বা কর্মসংস্থানে যুক্ত নয় এমন তরুণের সংখ্যা ২০২৩ সালে ১৪ লাখে পৌঁছেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ১৫–২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৬ শতাংশ—যা জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ।
এই অঞ্চলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন টিকে থাকার সংগ্রামে রূপ নিয়েছে। একসময় যে নিয়ম ছিল—পড়াশোনা করে ভালো চাকরি মানেই উন্নতি—তা আজ ভেঙে পড়েছে।

নতুন প্রজন্মের বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ
আজকের তরুণদের এই মনোভাব আসলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাফল্যেরই উত্তরাধিকার। কোরিয়ান শ্রম বিশেষজ্ঞ কিম বলেন, “তাদের বাবা-মায়েরা দ্রুত উন্নতির যুগে সম্পদ গড়েছেন, তাই সন্তানরা কাজ না করলেও পরিবারে ভরসা আছে।”
চীনে এটি অতিরিক্ত কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কোরিয়ায় চাকরি থেকে সরে আসা, জাপানে সংযমী জীবনের আনন্দ, আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিছক বেঁচে থাকার লড়াই।
চীনের সমাজবিজ্ঞানী মিয়াও জিয়া বলেন, “মানুষ কাজ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে, একদিন সাফল্য পাবে। কিন্তু এখন তরুণরা দেখছে, সেই সুযোগ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই তারা ‘শুয়ে পড়ছে’—প্রতিরোধের এক নীরব উপায়ে।”
সাফল্যের পুরনো সংজ্ঞা ভেঙে যাচ্ছে
এশিয়ার তরুণ প্রজন্ম আজ প্রশ্ন তুলছে—কঠোর পরিশ্রমের প্রতিদান কি সত্যিই মেলে? পুরনো সাফল্যের সংজ্ঞা কি আর টিকে আছে?
কেউ স্বাধীনতা বেছে নিচ্ছে, কেউ মানসিক শান্তি, কেউ কেবল টিকে থাকার পথ। তাদের এই নীরব প্রতিবাদই ইঙ্গিত দিচ্ছে—এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এক নতুন যুগের দিকে এগোচ্ছে।

 সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট রিপোর্ট
সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট রিপোর্ট