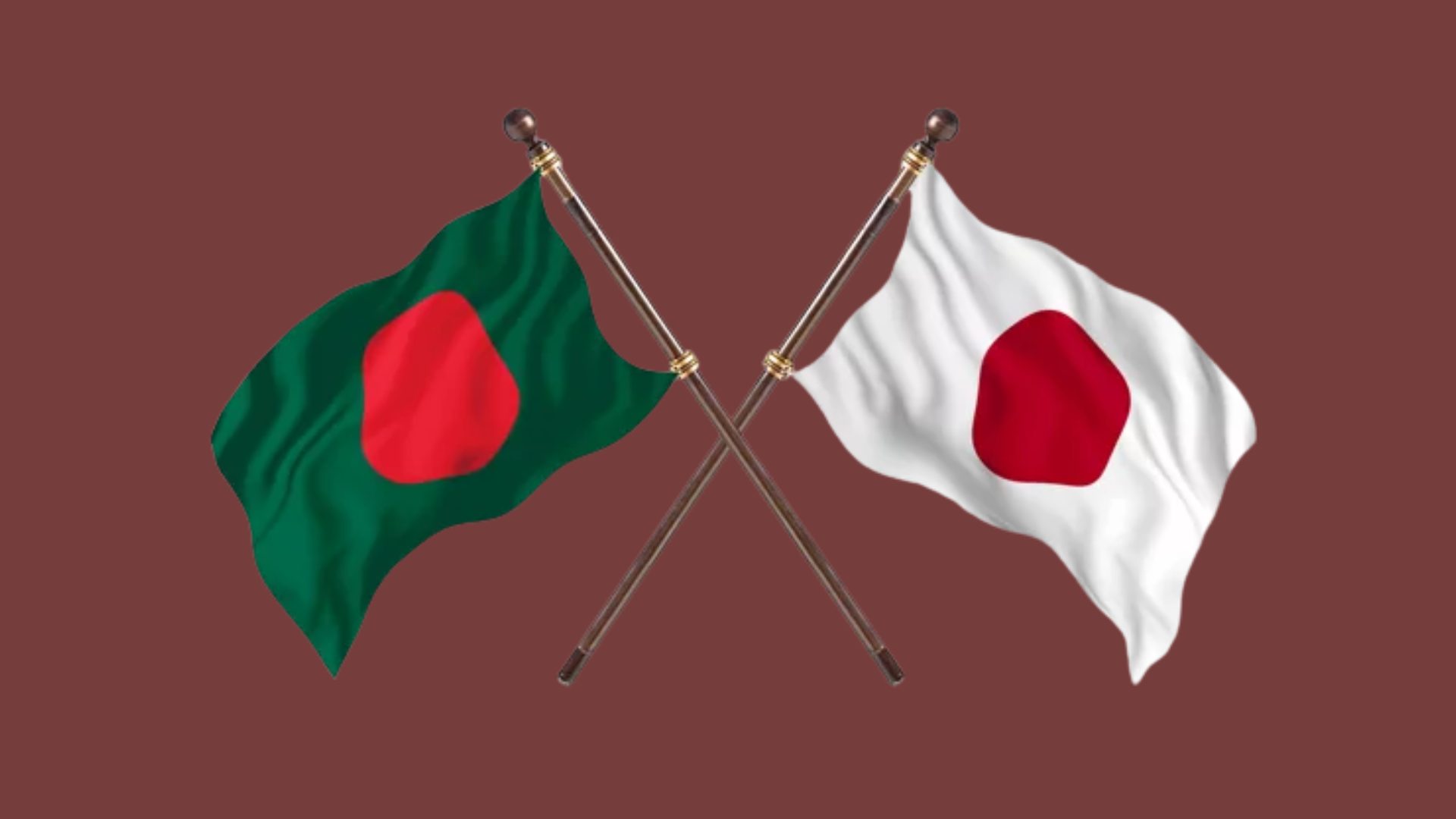চিত্রকলার ইতিহাসে ক্লদ মোনে শুধু একজন শিল্পী নন—তিনি আলো, জল ও রঙের মধ্যকার সম্পর্কের জাদুকর। ১৯০৮ সালে যখন তিনি প্রথম ভেনিসে যান, তখন তার বয়স প্রায় ৬৮। এর আগে তিনি লন্ডন, গিভেরনি কিংবা নরম্যান্ডির প্রকৃতি এঁকেছেন, কিন্তু ভেনিসের দীপ্ত জলের ছায়া-আলো তাকে মুগ্ধ করেছিল এক অনন্যভাবে। সেই মুগ্ধতার ফলেই জন্ম নেয় তার বিখ্যাত ভেনিস সিরিজ—৩৭টি পেইন্টিং যা আজও আলো ও জলের কবিতার মতো প্রতিভাত।
মোনের ভেনিস যাত্রা
১৯০৮ সালের অক্টোবরে মোনে ও তার স্ত্রী অ্যালিস হোশেদে ইংরেজ শিল্পসমর্থক মেরি হান্টারের আমন্ত্রণে ভেনিসের পালাজ্জো বারবারোতে অবস্থান করেন। সেই সময় অনেক ইউরোপীয় শিল্পী—জেমস ম্যাকনিল হুইসলার, জন সিঙ্গার সার্জেন্ট, এমনকি এদুয়ার মানেও—এই শহরের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মোনে প্রথমে ভেনিসে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পৌঁছানোর পর শহরের শরতের কুয়াশা ও জলের প্রতিফলন তাকে বিমোহিত করে।
তিনি সেখানে প্রায় দুই মাস অবস্থান করেন এবং আঁকেন ৩৭টি পেইন্টিং—যেগুলো আংশিকভাবে খোলা আকাশের নিচে ‘en plein air’ এবং পরে গিভেরনির স্টুডিওতে সম্পন্ন করেছিলেন। এসব চিত্রে জল ও আলোর সম্পর্কের প্রতি তার আগ্রহ নতুন মাত্রা পায়।

‘মনে অ্যান্ড ভেনিস’ প্রদর্শনী
ব্রুকলিন মিউজিয়ামে শুরু হওয়া ‘Monet and Venice’ প্রদর্শনীটি মোনের মৃত্যুর শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে তার ১৯টি ভেনিস পেইন্টিং, সঙ্গে আরও কিছু সমকালীন শিল্পীর কাজ, আলোকচিত্র, পোস্টকার্ড ও আধুনিক মাল্টি-স্ক্রিন ভিডিও ইনস্টলেশন।
এই প্রদর্শনী যৌথভাবে আয়োজন করেছে ব্রুকলিন মিউজিয়াম ও সান ফ্রান্সিসকোর ফাইন আর্টস মিউজিয়ামস। কিউরেটর হিসেবে ছিলেন লিসা স্মল ও মেলিসা বুরন, যিনি বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে কর্মরত। এটি ১৯১২ সালের পর প্রথমবারের মতো এককভাবে মোনের ভেনিস সিরিজকে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রদর্শনী।
প্রদর্শনীর প্রথম অংশ
প্রবেশমুহূর্তে দর্শকদের স্বাগত জানায় বিশাল ভিডিও প্রজেকশন—ভেনিসের খাল, গির্জা, প্রাসাদ ও গৃহস্থালির দৃশ্য। পরবর্তী অংশে রয়েছে মোনের আঁকা স্থানগুলোর মানচিত্র, তার স্ত্রীর পাঠানো পোস্টকার্ড ও ভেনিস গাইডবুক।
জন সিঙ্গার সার্জেন্টের আঁকা ১৮৯৯ সালের একটি ম্লান আলোছায়ার ঘরোয়া দৃশ্য এখানে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যা মোনে ও তার স্ত্রীর অবস্থানকৃত পালাজ্জো বারবারোর পরিবেশের আভাস দেয়ার মতো।

ভেনিসে রঙ ও স্থাপত্যের জটিলতা
মোনের “দ্য রেড হাউস” (১৯০৮) রঙের উজ্জ্বল সংলাপ—সিনাবার লাল, লেবু-হলুদ ও নীল-সবুজের ভারসাম্য। অন্যদিকে “ভেনিস, পালাজ্জো দারিও” (১৯০৮) স্টুডিওতে কাজের ঘনত্ব ও নিখুঁত কাঠামো প্রকাশ করে।
ভেনিসের স্থাপত্য মোনের চিত্রে নতুন বিন্যাস এনেছিল। গিভেরনিতে তিনি যেখানে জলের উপর ফুলের বিস্তীর্ণ ছাপ আঁকতেন, সেখানে ভেনিসে তিনি জল ও স্থাপত্যের সমতল ফ্যাসাদকে আয়তাকার বিন্যাসে সাজিয়েছিলেন। প্রতিটি আয়তক্ষেত্রে রঙের ভিন্ন তাপমাত্রা ও ভিন্ন ছন্দ।
“পালাজ্জো দারিও”-তে ভবনের গোলাপি-সবুজ প্রতিফলন ও জানালার নীলাভ আভা একসঙ্গে এক সুরেলা ভারসাম্য তৈরি করে।
শেষ গ্যালারিতে মোনের নান্দনিক চূড়ান্ততা
শেষ গ্যালারিতে দর্শক দেখতে পান “পালাজ্জো কন্তারিনি” ও “পালাজ্জো দা মুলা”-এর চিত্রগুলো। এখানে জলের রঙের কম্পন ভবনের জানালায় প্রতিফলিত হয়ে তৈরি করেছে আলো-জলের জ্যামিতিক সিম্ফনি।
“পালাজ্জো দুকালে” দেখা যায় দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে—গন্ডোলা থেকে এবং সান জর্জিও মাজিওর দ্বীপ থেকে। একটিতে স্থাপত্য যেন রঙে বিলীন হয়ে যায়, অন্যটিতে নীল পাথুরে তীররেখা জলীয় প্রতিফলনের সঙ্গে সংলাপে লিপ্ত হয়।
মোনের জলে-আলোর অনুরাগ
প্রদর্শনীর একটি অংশ মোনের জলের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী অনুরাগকে তুলে ধরেছে। ১৮৭০-৮০ দশকের নরম্যান্ডি ও সীন নদীর চিত্রে দেখা যায় ঢেউয়ের তীব্র গতিশীলতা, যা পরে ‘ওয়াটার লিলিস’ সিরিজে পরিণত হয়।
আরও কয়েকটি চিত্রে তিনি বিষয়বস্তুর পরিবর্তে বাতাস ও আলোর মধ্যবর্তী ‘পরিবেশ’ আঁকতে চেয়েছেন—যেমন লন্ডনের কুয়াশায় সূর্যালোকের প্রতিফলন নিয়ে তার নীলচে-কমলাভ চিত্রটি।
ভেনিসে অন্যান্য শিল্পীর প্রভাব
মোনের সঙ্গে প্রদর্শনীতে রয়েছে ক্যানালেত্তো, করো, টার্নার, হুইসলার ও সার্জেন্টের কাজ। টার্নারের জলরঙে আলো যেন কাগজে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, হুইসলারের খোদাইয়ের রেখা সূক্ষ্ম ও আবেগপূর্ণ, আর সার্জেন্টের জলধারার দৃশ্যগুলো আলোয় ঝলমল। এমনকি সার্জেন্টের বোন এমিলিও এখানে ফ্রারি চার্চের অভ্যন্তরের এক সাধারণ জলরঙ এনেছেন।

সবচেয়ে বিস্ময়কর সংযোজন—জন রাসকিনের আঁকা সান মার্কোর নিখুঁত স্থাপত্যবিস্তার।
ভেনিসে ফিরে না আসার আক্ষেপ
প্রদর্শনীর শেষ অংশে মোনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকা “পালাজ্জো দুকালে,” “সান জর্জিও,” ও “সান্তা মারিয়া দেলা সালুতে”-র দৃশ্য দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রতিটি চিত্রে রঙ, আলো ও দৃষ্টিকোণের সূক্ষ্ম পার্থক্য চোখে ধরা পড়ে।
দর্শক অবচেতনেই অনুভব করেন—মোনে যদি আবার ভেনিসে ফিরতেন, তবে হয়তো আরও কিছু অপার্থিব সৃষ্টি আমাদের হাতে থাকত।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট