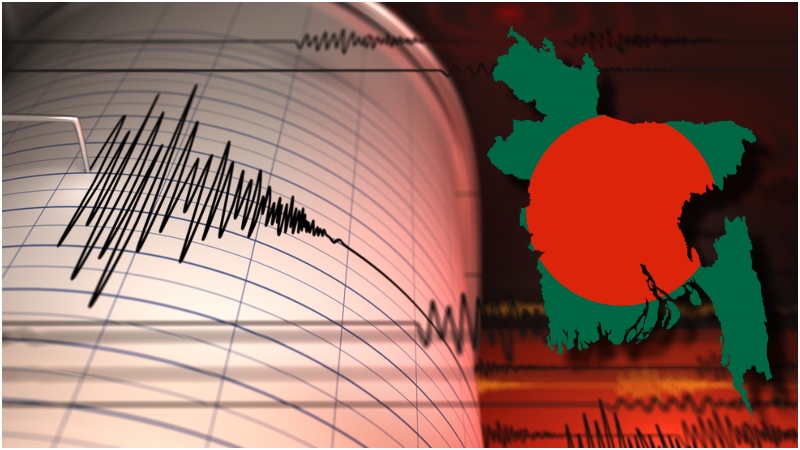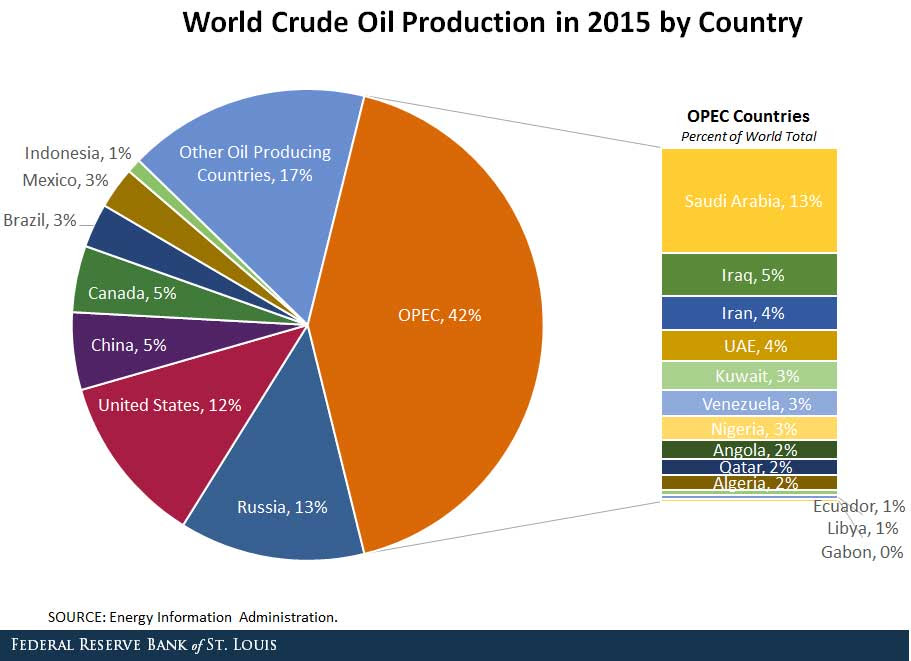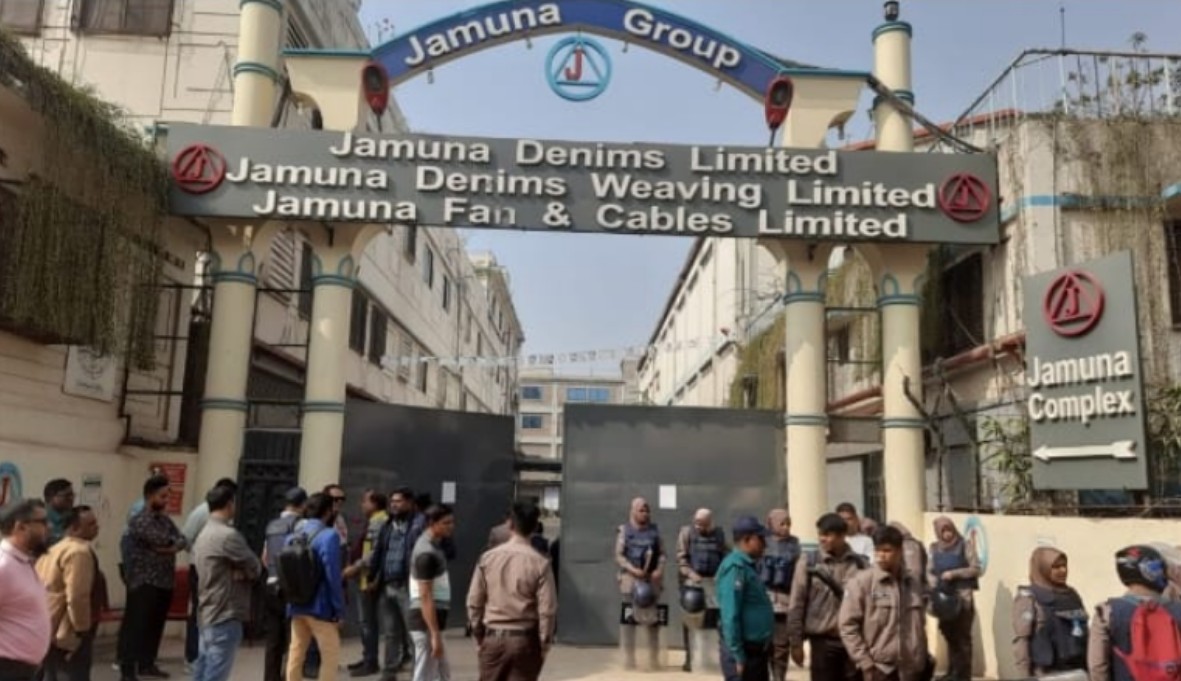বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও টেকটনিক অবস্থান এই ভূখণ্ডকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রেখেছে। হিমালয় পাদদেশ, ইন্দো-বার্মা আর্ক ও সক্রিয় ফল্টলাইনের মাঝে অবস্থান—এমন একটি ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প-সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে। গত দুইশত বছরে কয়েকটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আমাদের জনজীবন, স্থাপত্য, নদীনালা, ভূভাগের বিন্যাস এমনকি রাজনীতি পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। সেই বড় বড় কম্পনগুলো এবং তাদের পরবর্তী অভিঘাতই এই প্রতিবেদন।
১৮৯৭ সালের মহাভূমিকম্প: ‘গ্রেট আসাম কোয়েক’–এর ছায়া বাংলাদেশে
১২ জুন, ১৮৯৭। রিখটার স্কেলে প্রায় ৮.১ থেকে ৮.৭ মাত্রার এই ভূমিকম্প ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালীগুলোর একটি। উপকূল থেকে ময়মনসিংহ–সিলেট অঞ্চল পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়। পুরান ঢাকার অসংখ্য ইটের দালান ধসে পড়ে, তৎকালীন রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলেও ব্যাপক কাঠামোগত ক্ষতি হয়।
পরবর্তী অভিঘাত
- নদীর গতিপথ বদলে যায়—মেঘনা ও তার শাখাগুলোর গভীরতা-প্রবাহ পরিবর্তিত হয়।
- রেলের লাইন বেঁকে যায়, সেতু বসে যায়।
- হাজার হাজার ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ে, খাদ্য ও নিরাপদ পানি সংকট দেখা দেয়।
- দীর্ঘ সময় ধরে পরভূমিতে ধস ও ফাটল থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন দেখা যায়।
১৯১৮ সালের শিলিগুড়ি ভূমিকম্প: উত্তরবঙ্গে নতুন দাগ
১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ সালের ভূমিকম্পটি মাত্রায় ৭.৬ হলেও এর প্রভাব ছিল বিস্তৃত। মূল উপকেন্দ্র ছিল শিলিগুড়ি, কিন্তু তত্কালীন পূর্ববঙ্গও ব্যাপকভাবে কেঁপে ওঠে।
পরবর্তী অভিঘাত
- দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর কাঁচা ঘর ধসে পড়ে।
- ধান ও পাটক্ষেতের জমিতে দীর্ঘ ফাটল সৃষ্টি হয়, কৃষি উৎপাদন দীর্ঘস্থায়ী ধাক্কা খায়।
- নদীভাঙন কয়েকগুণ বেড়ে যায়, বিশেষত তিস্তা ও ধরলার দুই তীর পরিবর্তিত হয়।
১৯৩০ সালের ধুবরি ভূকম্প: সিলেটের শিলাঘর কেঁপে ওঠা
৩ জুলাই, ১৯৩০। মাত্রা ছিল প্রায় ৭.১। উপকেন্দ্র ছিল ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ধুবরি, যা বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কাছেই।
পরবর্তী অভিঘাত
- সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে ব্যাপক কাঠামোগত ক্ষতি।
- বহু জমিদার বাড়ি ও পুরনো সুরমা তীরবর্তী স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে গোলযোগ দেখা দেয়—অনেক কূপের পানি শুকিয়ে যায়, আবার রাতারাতি নতুন জলাধার সৃষ্টি হয়।
১৯৫০ সালের আসাম ভূমিকম্প: পাহাড়ের বুক থরথর
১৫ আগস্ট, ১৯৫০ সালের ৮.৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি ছিল ২০ শতকের অন্যতম শক্তিশালী কম্পন। যদিও কেন্দ্র ছিল ভারতীয় আসামের তাওয়াং–মিশমি অঞ্চল, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এর প্রভাব ছিল বিধ্বংসী।
পরবর্তী অভিঘাত
- সিলেট শহর ও আশপাশের হাওর-বিল অস্থির হয়ে ওঠে; নৌপথ ভেঙে যায়।
- পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।
- ভূমিকম্পের পর মাসের পর মাস আফটারশক মানুষকে ঘরছাড়া করে রাখে।
১৯৯৭ সালের চট্টগ্রাম পাহাড়ি ভূমিকম্প: আধুনিক সময়ের সতর্কবার্তা
২২ নভেম্বর, ১৯৯৭। মাত্রা ৬.১—কিন্তু উপকেন্দ্রের নৈকট্যের কারণে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ভয়াবহ ক্ষতি দেখা দেয়।
পরবর্তী অভিঘাত
- চট্টগ্রামের বহু বহুতল ভবন ফাটলধরা অবস্থায় পড়ে।
- খাগড়াছড়ি–রাঙামাটিতে বড় আকারের ভূমিধস ঘটে; বহু গ্রামবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- এই ভূমিকম্প দেশজুড়ে বিল্ডিং কোড নিয়ে গুরুতর আলোচনার জন্ম দেয়।
২০০৪ সালের সুমাত্রা ভূমিকম্প: ঢাকাও কেঁপে উঠেছিল
২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪। মাত্রা ৯.১—বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভূমিকম্প। যদিও উপকেন্দ্র দূরে সুমাত্রায়, বাংলাদেশে উপকূলসহ পুরো দেশ জুড়ে দীর্ঘ সময় কম্পন অনুভূত হয়।
পরবর্তী অভিঘাত
- কক্সবাজারে পানির স্তর অসমভাবে ওঠানামা করে; সামুদ্রিক ঢেউ অস্বাভাবিক হয়।
- উপকূলীয় কুতুবদিয়ায় ভাঙন বাড়ে।
- জাতীয় পর্যায়ে সুনামি প্রস্তুতি পরিকল্পনার সূচনা ঘটে।
২০০৫ ও ২০১৫ সালের হিমালয় ভূমিকম্প: আমাদের কাঠামো কতটা নিরাপদ?
২০০৫ সালের কাশ্মীর ভূমিকম্প ও ২০১৫ সালের নেপাল ভূমিকম্প—দুটি বড় কম্পনই বাংলাদেশের ভবন-নিরাপত্তা বিষয়ে নতুন প্রশ্ন তোলে।
পরবর্তী অভিঘাত
- ঢাকার হাজারো ভবনে ফাটল দেখা যায়, বিশেষত পুরান ঢাকা ও গুলিস্তান–পল্টন এলাকায়।
- জরুরি উদ্ধারব্যবস্থা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ে।
- বহু সরকারি ও বেসরকারি অফিস ভবনে রেট্রোফিটিং নিয়ে উদ্যোগ শুরু হয়।
বাংলাদেশ: এখনো ঝুঁকির মুখে কেন?
বাংলাদেশ তিনটি প্রধান ফল্টলাইনের ওপর অবস্থিত—ডফলা ফল্ট, ত্রিপুরা ফল্ট ও কলকাতা–ময়মনসিংহ শিয়ার জোন। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন, ইন্দো-বার্মা আর্কে বিশাল মাত্রার শক্তি আটকে আছে, যা ভবিষ্যতে বড় ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে।
নগর ঘনত্ব, অবৈধ নির্মাণ, দুর্বল বিল্ডিং কোড-অনুসরণ, এবং নদীভাঙনের বাড়তি প্রবণতা এই ঝুঁকিকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।
গত ২০০ বছরের ভূমিকম্পগুলো আমাদের শুধু কাঠামোগত ক্ষতিই শেখায়নি—প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাও দেখিয়েছে। ইতিহাস বলে, বড় কম্পন ফিরে আসে বারবার; প্রশ্ন শুধু—আমরা কতটা প্রস্তুত?
#বাংলাদেশভূমিকম্প #ইতিহাস #সারাক্ষণ_রিপোর্ট #FeatureStory

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট