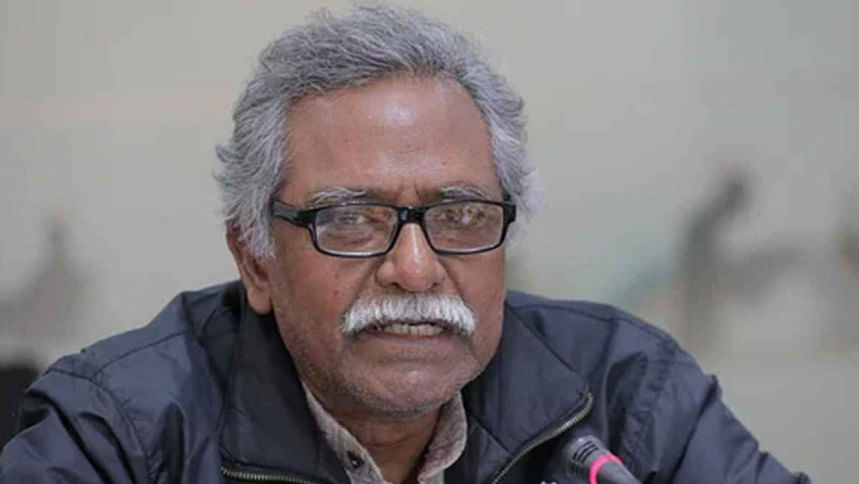যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগে দাবি করেছিলেন যে তিনি একদিনের মধ্যেই রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারেন। এখন আলোচনা বাস্তবেই আসন্ন মনে হচ্ছে, আর ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা এ নিয়ে স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন।
এই সপ্তাহে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বুধবার ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং এর পর ঘোষণা করেন যে শান্তি আলোচনা “তাৎক্ষণিকভাবে” শুরু হবে। (পরে সেদিনই ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে তিনি ও পুতিন শীঘ্রই সৌদি আরবের মাটিতে সাক্ষাৎ করতে পারেন।) পুতিনের সঙ্গে কথা বলার পর ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন—যিনি পরে জানান, ইউক্রেনকে বাইরে রেখে কোনো শান্তিচুক্তি হলে তা তারা মেনে নেবে না। একই দিন, ব্রাসেলসে ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ইউক্রেনকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। এ ছাড়া তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পর রাশিয়া দখল করা সব ভূখণ্ড ফিরে পাওয়ার ইউক্রেনের লক্ষ্য “অবাস্তব।”
ইউরোপজুড়ে এই ঘটনার পর স্পষ্ট অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে। দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এ হেনরি ফয়, ফেলিসিয়া শোয়ার্টজ ও ক্রিস্টোফার মিলার লেখেন, এই খবরে ইউরোপ “স্তম্ভিত” হয়ে পড়েছে। তাদের বিশ্লেষণে বলা হয়, ইউরোপীয় কর্মকর্তারা ভয় পাচ্ছেন, যুদ্ধ-পরবর্তী নিরাপত্তা ও পুনর্গঠনব্যয় তাদেরই বহন করতে হবে। এদিকে জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস অভিযোগ করেছেন যে আলোচনার আগেই ট্রাম্প প্রশাসন মস্কোর কাছে ছাড় দিতে শুরু করেছে। সিএনএনের স্টিফেন কলিনসন মনে করেন, পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের এই ফোনকলে ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিন্যাস চিরতরে পাল্টে যেতে পারে—বিশেষত যেহেতু আগে থেকেই ইউরোপে শঙ্কা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে তাদের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণ থেকে সরে যাবে।
কলিনসন লেখেন, “যে কোনো আমেরিকানের বয়স এখন অন্তত পঞ্চাশের কোঠায় হলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপরীতে ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কে মনে করতে পারেন। এখন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপে নয়, এশিয়ায়। কাজেই, নাৎসিদের পরাজয়ের ৮০ বছর পরও কেন ইউরোপ নিজস্ব প্রতিরক্ষার ভার নেয়নি, এই প্রশ্ন তোলা ট্রাম্পের পক্ষে স্বাভাবিক।” সিএনএনের নিক প্যাটন ওয়ালশ লিখেছেন, এই মুহূর্তটির জন্যই পুতিন অপেক্ষা করছিলেন: যাতে তিনি ইউক্রেনের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন এবং ইউরোপের ক্ষমতার ভারসাম্য ট্রাম্পের সঙ্গে একান্তে ঠিক করে নিতে পারেন—জেলেনস্কিকে বাইরে রেখেই।

অনেক ইউরোপীয় নেতার “দুঃস্বপ্নের” মতো পরিস্থিতি হলো “ইউক্রেন ও ইউরোপীয়দের মাথার ওপর দিয়ে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো গোপন চুক্তি।” ফিনান্সিয়াল টাইমস-এ লেখা এক কলামে ল্যা মন্ড-এর সম্পাদকীয় পরিচালক সিলভি কফম্যান জানিয়েছেন, ইউরোপ কিভাবে ইউক্রেনের পাশে অবস্থান নেবে, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন না থাকলে সে বিতর্ক প্রবল হয়ে উঠেছে। “যদি ইউরোপ আলোচনার টেবিলে আসন পেতে চায়,” কফম্যান লিখেছেন, “তবে সবার আগে তাদের এমন কিছু রাখতে হবে যা আলোচনা ও বাস্তবায়নের পর্যায়ে ইউরোপের স্বার্থ নিশ্চিত করবে।”
দ্য ইকোনমিস্ট-এ বলা হয়েছে, ট্রাম্প হয়তো এমন কিছু পদক্ষেপ নেবেন যা ইউরোপীয় সরকারের কাছে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে: “তার অদ্ভুত কৌশল সত্ত্বেও … কিছু পর্যবেক্ষক আশা করছেন যে তার উপদেষ্টারা শেষ পর্যন্ত তাকে প্রচলিত নীতির দিকে নিয়ে যাবেন। ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দূত কার্ট ভলকার মনে করেন, পুতিনের সঙ্গে ‘উষ্ণ কথাবার্তায়’ ট্রাম্প হয়তো তাকে উদ্দীপ্ত করতে চান, আবার চাপও দিতে চান। পরে সেদিন ট্রাম্প নিজেই বলেছিলেন ‘আমি ইউক্রেনের পক্ষেই আছি।’ … তবু ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা স্পষ্টতই হতাশার সুরে বলছেন, পরিবেশ এখন অনেক বেশি অন্ধকারময়।”
সম্ভাব্য পরিণতি: ইউরোপীয় সেনা মোতায়েন ও অস্ত্রবিরতি?
আলোচনা শেষ পর্যন্ত যেদিকেই গড়াক না কেন, ওয়াশিংটন পোস্ট-এর কলামনিস্ট ডেভিড ইগনেশিয়াস বলছেন, ফলাফল দিয়েই ট্রাম্পকে বিচার করা হবে।
কিন্তু এক চুক্তির রূপরেখা কেমন হতে পারে? আর ট্রাম্প প্রশাসন এখন কী ভাবছে? স্পষ্টতই, ট্রাম্প ইউরোপের উপর বেশি দায়িত্ব চাপাতে চান। ব্রাসেলসে হেগসেথ বলে এসেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে সেনা পাঠাবে না, তবে “ইউরোপীয় কিংবা নন-ইউরোপীয় সৈন্যদের” শান্তিরক্ষী হিসেবে পাঠানোর সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। যদি কখনো তা হয়, হেগসেথের মতে, সে মিশন যেন “নাটোর (ন্যাটো) নয়, অন্য কোনো কাঠামোর অধীনে” পরিচালিত হয়।
“হেগসেথের বক্তব্য মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়,” ইগনেশিয়াস লিখেছেন। “ইউরোপে ‘ট্রিপওয়্যার বাহিনী’ মোতায়েনের ধারণা নভেম্বর থেকেই ট্রাম্প ও তার উপদেষ্টারা ন্যাটো মিত্রদের জানাচ্ছিলেন। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো এমন বাহিনী পাঠাতে রাজি বলেও শোনা গেছে, সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি. টেলর জুনিয়রের ভাষ্য অনুযায়ী। … ট্রাম্প ও হেগসেথের বক্তব্য একসঙ্গে পড়লে বোঝা যায়, তারা এমন এক যুদ্ধবিরতি বা সিজফায়ারের কথা ভাবছেন, যেখানে প্রায় ৬০০ মাইল দীর্ঘ বর্তমান সামনের লাইনটি দ্বিধাবিভক্তির সীমানা হিসেবে স্বীকৃত হবে। হেগসেথ উল্লেখ করেছেন, ‘সেই যোগাযোগরেখার ওপর আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ জোরদার করতে হবে।’ কোরিয়া যুদ্ধের অবসানে যে সাময়িক বিভাজন-রেখা টানা হয়েছিল, এ পদ্ধতিকে অনেকটা সেইরকম মনে হচ্ছে—যেখানে ‘ডিমিলিটারাইজড জোন’-এর একপাশে দক্ষিণ কোরিয়া বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।”

মূল্যবান খনিজ সম্পদ আলোচনার কেন্দ্রে
ইউক্রেনকে সহায়তা অব্যাহত রাখবেন কি না—তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ট্রাম্প বলছেন, কিয়েভ যেন যুক্তরাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সরবরাহ করে। এগুলো হল দূর্লভ ধাতু, যা ব্যাটারি ও ইলেকট্রনিকস পণ্যে ব্যবহৃত হয়। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ কনস্টাঁ মেয়ে লিখেছেন, “ইউক্রেনের কাছে এগুলো হলো এমন এক ‘চাল’, যা তারা ট্রাম্পের কাছে আর্থিক ও সামরিক সহায়তার বিনিময়ে ব্যবহার করতে চায়। আর ট্রাম্পের কাছে এগুলো কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে দীর্ঘদিন পরিশোধযোগ্য এক ধরন বিল।”
ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স রিভিউ-তে আমান্ডা কোউকলি দেখিয়েছেন যে এখন জেলেনস্কি “ডিলের কৌশল রপ্ত করছেন,” কারণ তিনিও এই প্রস্তাবকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। আসলে, জেলেনস্কি অক্টোবরে যে “বিজয় পরিকল্পনা” উপস্থাপন করেছিলেন, সেখানে মিত্রদের জন্য “ক্রিটিক্যাল রিসোর্সের যৌথ সুরক্ষা” বিষয়ে একটি বিশেষ চুক্তির কথা আছে, যার মধ্যে রয়েছে উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্পে ব্যবহৃত দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থের যৌথ বিনিয়োগ ও ব্যবহার। কোউকলি লেখেন, “ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেনের সামরিক সহায়তার খরচ নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন রয়েছে, আর তিনি যে দ্রুত কোনো সমাধান পেতে চান—এমনকি যদি তার মানে হয় ইউক্রেনের বড় অঞ্চল রাশিয়ার দখলে চলে যাওয়া—এটা কারও অজানা নয়। এ অবস্থায় মূল্যবান খনিজ এলাকা ছেড়ে দেওয়া যে কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে, সেই যুক্তি ব্যবহার করে জেলেনস্কি এখন এক নতুন মাত্রার বক্তব্য দিচ্ছেন।”
অনেকেই অবশ্য এই ধারণার বিরোধিতা করছেন। কিইভ ইন্ডিপেনডেন্ট-এ এক মতামতে ইউক্রেনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী দমিত্র কুলেবা বলেছেন, মূল্যবান খনিজ পদার্থের বিনিময়ে ওয়াশিংটনের সাহায্য চাওয়া মানে ১৯১৮ সালে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙেরির সঙ্গে ইউক্রেনের চুক্তির পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেয়—যেখানে শস্য, চর্বি, মাংস ও তেল দিয়ে সুরক্ষা কেনার চেষ্টা হয়েছিল। “ওই চুক্তিতে ইউক্রেনীয় পিপলস রিপাবলিক (ইউপিআর) বলশেভিকদের কবল থেকে ক্ষমতা ফিরে পেলেও পরে দেখা গেল জার্মান সমর্থন মূল্য দিতে হচ্ছে অনেক,” কুলেবা লেখেন। “জার্মান কর্তৃপক্ষ তখন মনে করল, তাদের উপস্থিতি ছাড়া ইউক্রেন চলে না। তারা ইউপিআর সরকারকে হটিয়ে হেটম্যান পাভলো স্কোরোপাডস্কিকে ক্ষমতায় বসাল, যিনি ইউক্রেনের সংসদ পাস করা সব আইন বাতিল করে দিলেন।” এখনকার পরিস্থিতিকে কুলেবা দেখছেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হিসেবে। “শত বছর আগে যেমন ছিল, এখনো সেটাই ঘটছে—শুধু এই পার্থক্য যে জার্মানির জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র, আর শস্যের জায়গায় লিথিয়াম। চর্বির জায়গায় গ্রাফাইট। … কিন্তু এক শতাব্দী আগের মতো এখন আর আমাদের সুরক্ষায় কোনো সেনাবাহিনী পাঠানোর প্রতিশ্রুতি নেই—না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, না ন্যাটো। অথচ ওয়াশিংটনের এই সম্পদগুলো দরকার।”

 Sarakhon Report
Sarakhon Report