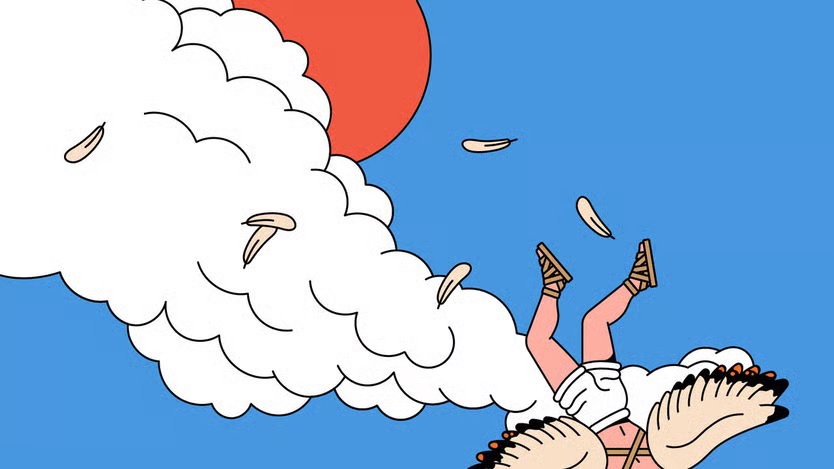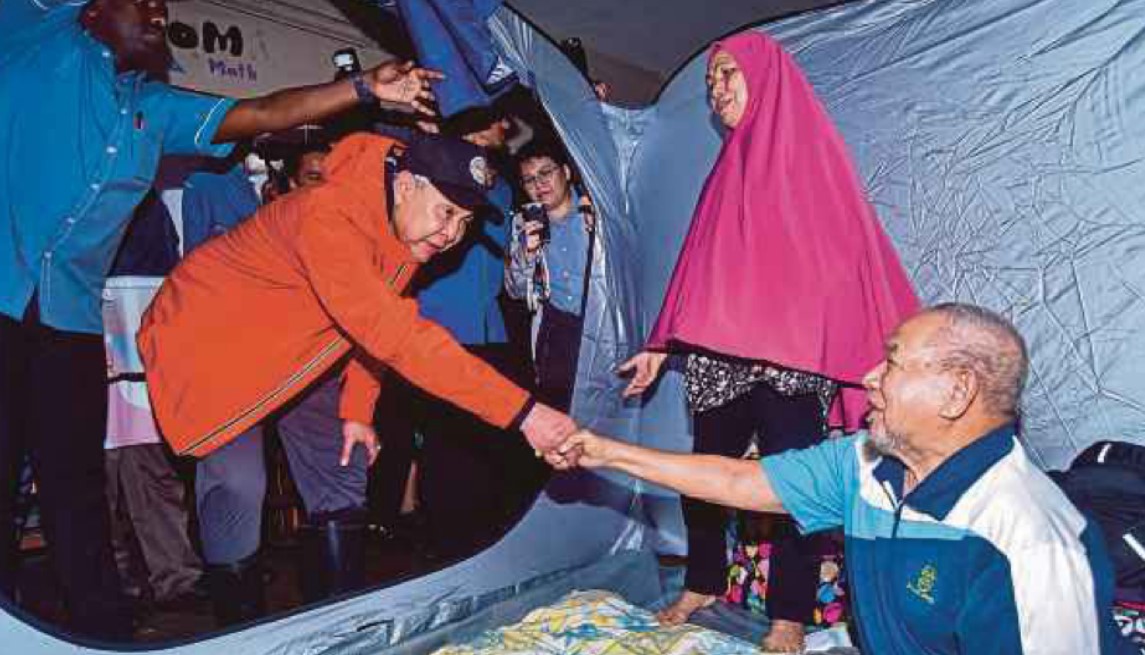ইউরোপীয় কর্মকর্তারা এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন, যা ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্ব দিয়ে আসছিলেন: যুক্তরাষ্ট্র আর ইউক্রেন বা গোটা ইউরোপের নিরাপত্তার প্রধান রক্ষক হয়ে থাকতে চাইছে না।
কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, বিষয়টি আরও চরম: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি জোট সম্পর্কের ইতি টানতে চলেছেন এবং এর বদলে রাশিয়ার পক্ষে ঝুঁকছেন।
সাম্প্রতিক সময়ে, ট্রাম্প রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেন নিয়ে আলোচনা থেকে ইউরোপ ও ইউক্রেনকে বাদ দিয়েছেন, এমনকি ইউক্রেনকে রাশিয়ার অংশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথাও বলেছেন। পাশাপাশি তিনি ক্রেমলিনের প্রচারের সুর মিলিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকিকে “স্বৈরশাসক” বলে অভিহিত করেছেন, মিথ্যাভাবে দাবি করেছেন যে ইউক্রেনই রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছে, এবং প্রকাশ্যে জেলেন্সকিকে চাপে ফেলে সমঝোতায় আসতে না পারলে দেশটি হারিয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। (জেলেন্সকি নিজে বলছেন, ট্রাম্প বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের বুদবুদের মধ্যে বাস করছেন।) ট্রাম্প আরও বলেছেন যে রাশিয়াকে আবার জি৭ গোষ্ঠীতে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত—যেখান থেকে ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখলের কারণে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।
এ বিষয়টি আসলে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে পুনর্গঠনের একটি চেষ্টা, বলছেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স-এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যাপক পিটার ট্রুবোউইটজ। জার্মানির ডয়েচে ভেলে-র নিকোল ফ্রলিশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “আমি মনে করি ট্রাম্পের কাছে এটি এক ধরনের নাটকীয় মোড় আনতে পারে—রাশিয়াকে শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ফের কাছে টেনে আনা পুরোপুরি বড় কোনো মঞ্চায়নের মতো। এটি দুঃসাহসী, নাটকীয়, অপ্রত্যাশিত, এবং এটাই তার আসল লক্ষ্য। ভূরাজনৈতিক দিক থেকে তিনি মনে করেন, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ইউরোপের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে, কারণ ইউরোপ অনেকাংশে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। সেইসঙ্গে, ট্রাম্পের দৃষ্টিতে, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন চীনের ওপর প্রভাব বিস্তারের একটি সুযোগ খুলে দিতে পারে। অন্যদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নিজস্ব লক্ষ্য আছে—যদিও তা আলাদা—তবু দুজনেই ইউক্রেন নিয়ে আলোচনা থেকে সুযোগ নিতে চাইছেন, যা আসলে যুদ্ধের চেয়েও বড় পরিসরে ভূকৌশলগত চাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।”
ফরেন পলিসি পত্রিকায় একটি মতামত প্রবন্ধে, যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক নীতিগত উপদেষ্টা গার্ভান ওয়ালশ কিছুটা ভিন্নভাবে লিখেছেন, “ট্রাম্পের এই উদ্যোগ ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা চুক্তির প্রতিধ্বনি, যেখানে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট এবং সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন সম্মত হন যে পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাববলয়ে থাকবে।”
ইউরোপের দ্বিধা
এর প্রভাব কী হতে পারে ইউরোপের ওপর? প্রথমত, বর্তমান পরিস্থিতি “অতিবাস্তব” বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর ফারাহ স্টকম্যান। তিনি লিখেছেন, “ইউরোপীয়রা এখন দেখছেন যে তারা এমন এক বিদেশি শক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, যা আর আগের মতো ব্যবহার করছে না। আগে যে আমেরিকা উদার গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে জোরালো অবস্থান নিত, এখন তা থেকে সরে গিয়ে মিত্রদেরও ধাক্কা দিচ্ছে।”
এ পরিস্থিতিতে ইউরোপ হয় নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনভাবে দাঁড়াবে, নয়তো যুক্তরাষ্ট্র যদি ফের নিঃশর্তভাবে ন্যাটোর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, সেক্ষেত্রে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে—এমন মত দিয়েছেন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস-এর লিয়ানা ফিক্স। ফরেন পলিসিতে গার্ভান ওয়ালশ যুক্তি দেখিয়েছেন, “ট্রাম্প প্রশাসন সমগ্র মার্কিন জনগণকে এককভাবে প্রতিফলিত করে না।” তাই ইউরোপীয় নেতারা এমন মার্কিন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব ও আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে পারেন, যারা ট্রাম্পের বিশ্বপরিকল্পনার সঙ্গে একমত নন।
অন্যদিকে আরেকটি ফরেন পলিসি প্রবন্ধে সিঙ্গাপুরের সাবেক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক কিশোর মাহবুবানি লিখেছেন, ইউরোপের উচিত এখনই ইঙ্গিত দেওয়া যে তারা ন্যাটো থেকে বেরিয়ে এসে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে যেতে পারে। তিনি লেখেন, “দুই হাজার বছরের ভূরাজনৈতিক ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র কি পক্ষ পরিবর্তন করছে?
ইউরোপীয় কর্মকর্তারা এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন, যা ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্ব দিয়ে আসছিলেন: যুক্তরাষ্ট্র আর ইউক্রেন বা গোটা ইউরোপের নিরাপত্তার প্রধান রক্ষক হয়ে থাকতে চাইছে না।
কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, বিষয়টি আরও চরম: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি জোট সম্পর্কের ইতি টানতে চলেছেন এবং এর বদলে রাশিয়ার পক্ষে ঝুঁকছেন।
সাম্প্রতিক সময়ে, ট্রাম্প রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেন নিয়ে আলোচনা থেকে ইউরোপ ও ইউক্রেনকে বাদ দিয়েছেন, এমনকি ইউক্রেনকে রাশিয়ার অংশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথাও বলেছেন। পাশাপাশি তিনি ক্রেমলিনের প্রচারের সুর মিলিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকিকে “স্বৈরশাসক” বলে অভিহিত করেছেন, মিথ্যাভাবে দাবি করেছেন যে ইউক্রেনই রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছে, এবং প্রকাশ্যে জেলেন্সকিকে চাপে ফেলে সমঝোতায় আসতে না পারলে দেশটি হারিয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। (জেলেন্সকি নিজে বলছেন, ট্রাম্প বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের বুদবুদের মধ্যে বাস করছেন।) ট্রাম্প আরও বলেছেন যে রাশিয়াকে আবার জি-৭ গোষ্ঠীতে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত—যেখান থেকে ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখলের কারণে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।
এ বিষয়টি আসলে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে পুনর্গঠনের একটি চেষ্টা, বলছেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স-এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যাপক পিটার ট্রুবোউইটজ। জার্মানির ডয়েচে ভেলে-র নিকোল ফ্রলিশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “আমি মনে করি ট্রাম্পের কাছে এটি এক ধরনের নাটকীয় মোড় আনতে পারে—রাশিয়াকে শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ফের কাছে টেনে আনা পুরোপুরি বড় কোনো মঞ্চায়নের মতো। এটি দুঃসাহসী, নাটকীয়, অপ্রত্যাশিত, এবং এটাই তার আসল লক্ষ্য। ভূরাজনৈতিক দিক থেকে তিনি মনে করেন, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ইউরোপের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে, কারণ ইউরোপ অনেকাংশে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। সেইসঙ্গে, ট্রাম্পের দৃষ্টিতে, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন চীনের ওপর প্রভাব বিস্তারের একটি সুযোগ খুলে দিতে পারে। অন্যদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নিজস্ব লক্ষ্য আছে—যদিও তা আলাদা—তবু দুজনেই ইউক্রেন নিয়ে আলোচনা থেকে সুযোগ নিতে চাইছেন, যা আসলে যুদ্ধের চেয়েও বড় পরিসরে ভূকৌশলগত চাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।”
ফরেন পলিসি পত্রিকায় একটি মতামত প্রবন্ধে, যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক নীতিগত উপদেষ্টা গার্ভান ওয়ালশ কিছুটা ভিন্নভাবে লিখেছেন, “ট্রাম্পের এই উদ্যোগ ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা চুক্তির প্রতিধ্বনি, যেখানে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট এবং সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন সম্মত হন যে পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাববলয়ে থাকবে।”
ইউরোপের দ্বিধা
এর প্রভাব কী হতে পারে ইউরোপের ওপর? প্রথমত, বর্তমান পরিস্থিতি “অতিবাস্তব” বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর ফারাহ স্টকম্যান। তিনি লিখেছেন, “ইউরোপীয়রা এখন দেখছেন যে তারা এমন এক বিদেশি শক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, যা আর আগের মতো ব্যবহার করছে না। আগে যে আমেরিকা উদার গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে জোরালো অবস্থান নিত, এখন তা থেকে সরে গিয়ে মিত্রদেরও ধাক্কা দিচ্ছে।”
এ পরিস্থিতিতে ইউরোপ হয় নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনভাবে দাঁড়াবে, নয়তো যুক্তরাষ্ট্র যদি ফের নিঃশর্তভাবে ন্যাটোর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, সেক্ষেত্রে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে—এমন মত দিয়েছেন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস-এর লিয়ানা ফিক্স। ফরেন পলিসিতে গার্ভান ওয়ালশ যুক্তি দেখিয়েছেন, “ট্রাম্প প্রশাসন সমগ্র মার্কিন জনগণকে এককভাবে প্রতিফলিত করে না।” তাই ইউরোপীয় নেতারা এমন মার্কিন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব ও আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে পারেন, যারা ট্রাম্পের বিশ্বপরিকল্পনার সঙ্গে একমত নন।
অন্যদিকে আরেকটি ফরেন পলিসি প্রবন্ধে সিঙ্গাপুরের সাবেক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক কিশোর মাহবুবানি লিখেছেন, ইউরোপ উচিত এখনই ইঙ্গিত দেওয়া যে তারা ন্যাটো থেকে বেরিয়ে এসে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে যেতে পারে। তিনি লেখেন, “দুই হাজার বছরের ভূরাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের শেখায়, সব মহাশক্তিই প্রথমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে, প্রয়োজনে মিত্রদের স্বার্থ ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে না। ট্রাম্প এখন তার দেশকে সামনে রেখেই কাজ করছেন। ইউরোপের উচিত শুধু তাকে দোষারোপ না করে একই পথ অনুসরণ করা। আপাতদৃষ্টিতে অকল্পনীয় এই পথ—স্বাধীন ভূরাজনৈতিক অভিনেতা হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করা, যারা নিজেদের স্বার্থকে সর্বোচ্চে রাখবে—গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। হতে পারে তখন ট্রাম্প ইউরোপকে কিছুটা সম্মান করবে।”
যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপ ছেড়ে যাওয়া বা তাদেরকে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া সত্যি উদ্দেশ্যও হতে পারে; আবার এটি হতে পারে চাপের কৌশল—“মিত্রদের কাছ থেকে সামরিক ব্যয় বা অন্য কোনো সুবিধা আদায়ের চেষ্টা,” লিখেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর জিউজেপে স্পাটাফোরা। তিনি বলেন, “ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন বাস্তবে পরিণত হওয়ার পথে।… হয়তো শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা এই দুই ধারার মিশ্রণ হবে। ইউরোপীয়রা শুধুমাত্র একতরফা কোনো ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে পারবে না। কিছু দেশ হয়তো বেশি করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে বা অন্য উপায়ে ট্রাম্পকে তুষ্ট করার চেষ্টা করবে, কিন্তু প্রশাসনের উদ্দেশ্য যদি সত্যিই ইউরোপ থেকে সরে যাওয়া হয়, তবে তা যথেষ্ট হবে না। সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য ইইউকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল গড়ে তুলতে হবে। এর কেন্দ্রে থাকবে শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রতিরোধশক্তির বিকাশ, যা মার্কিন পিছু হটার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে।”
গাজা এবং ‘জনসংখ্যা স্থানান্তরের বেদনাদায়ক ইতিহাস’
গাজা উপত্যকা “নিয়ে নেওয়া” এবং ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুত করার পরিকল্পনা করছেন ট্রাম্প—এমন খবরে বিভিন্ন আরব সরকার বিকল্প পরিকল্পনা তৈরির চেষ্টা করছে বলে নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্যাট্রিক কিংসলি ও ভিভিয়ান জানিয়েছেন। “মিশর, জর্ডান, সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিরা শান্তভাবে একত্রে কাজ করে গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি ভিন্ন প্রস্তাব তৈরির চেষ্টা করছেন, যেখানে আরব দেশগুলো গাজা পুনর্গঠনের জন্য তহবিল ও নজরদারির দায়িত্ব নেবে, তবে সেখানকার বাসিন্দাদের সরিয়ে না নিয়ে তাদের স্বদেশেই রাখবে, যাতে ভবিষ্যতে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকে,” কূটনীতিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়। মিশরের তৈরি পরিকল্পনায় মূলত গাজা পুনর্গঠন করা হবে, কিন্তু সেখানকার ফিলিস্তিনিদের মিশর বা জর্ডানে স্থানান্তর করা হবে না, যেমনটি ট্রাম্প উল্লেখ করেছেন।
এটি গাজার বাসিন্দাদের জন্য স্বস্তির বিষয়—যারা ধ্বংসস্তূপের মাঝেও নিজ ভূমিতে থাকার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কমপ্যাক্ট পত্রিকায় লেখা এক নিবন্ধে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের পিএইচডি প্রার্থী হিদার পেনাটজার লিখেছেন, বলপূর্বক স্থানচ্যুতি বা “জনসংখ্যা স্থানান্তর” সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না। “আধুনিক কালের রাজনীতিতে এমন স্থানচ্যুতির উদাহরণ আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো বিপরীত ফল দেয়। ইতিহাস বলে, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তব সমস্যার সমাধান কম করে, বরং নতুন সংকটের সৃষ্টি করে।”
তিনি উল্লেখ করেন, স্টালিনের সময় ভল্গা অঞ্চলের জার্মান জনগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়ায় পাঠানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে নাৎসিদের স্লাভ জনগোষ্ঠীকে হটানোর পরিকল্পনা কিংবা ১৮৩০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের “ইন্ডিয়ান রিমুভাল অ্যাক্ট”-এর উদাহরণ। আরেক ধরনের স্থানচ্যুতি হলো “জনসংখ্যা বিনিময়,” যেখানে দুই দেশ পারস্পরিক সমঝোতায় বড় জনগোষ্ঠীকে ‘বিনিময়’ করে। পেনাটজার বলেন, “উদাহরণস্বরূপ, সাম্রাজ্য-পরবর্তী যুগে লিগ অব নেশন্স বেশ কয়েকটি দেশকে জাতিগতভাবে একজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে জনগোষ্ঠী বিনিময়ের চেষ্টা করেছিল।… ১৯২৩ সালে গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে প্রায় ২০ লাখ মানুষ (গাজার বর্তমান জনসংখ্যার সমান) আদিবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তবে ইতিহাস বলে, এরকম প্রকল্পগুলো সবসময় অস্থিতিশীলতা ডেকে আনে। ভৌগোলিক অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে অভ্যন্তরীণ সংঘাত শুরু হওয়ার প্রবল ঝুঁকি তৈরি হয়।”
সব মহাশক্তিই প্রথমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে, প্রয়োজনে মিত্রদের স্বার্থ ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে না। ট্রাম্প এখন তার দেশকে সামনে রেখেই কাজ করছেন। ইউরোপের উচিত শুধু তাকে দোষারোপ না করে একই পথ অনুসরণ করা। আপাতদৃষ্টিতে অকল্পনীয় এই পথ—স্বাধীন ভূরাজনৈতিক অভিনেতা হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করা, যারা নিজেদের স্বার্থকে সর্বোচ্চে রাখবে—গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। হতে পারে তখন ট্রাম্প ইউরোপকে কিছুটা সম্মান করবে।”
যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপ ছেড়ে যাওয়া বা তাদেরকে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া সত্যি উদ্দেশ্যও হতে পারে; আবার এটি হতে পারে চাপের কৌশল—“মিত্রদের কাছ থেকে সামরিক ব্যয় বা অন্য কোনো সুবিধা আদায়ের চেষ্টা,” লিখেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর জিউজেপে স্পাটাফোরা। তিনি বলেন, “ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন বাস্তবে পরিণত হওয়ার পথে।… হয়তো শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা এই দুই ধারার মিশ্রণ হবে। ইউরোপীয়রা শুধুমাত্র একতরফা কোনো ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে পারবে না। কিছু দেশ হয়তো বেশি করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে বা অন্য উপায়ে ট্রাম্পকে তুষ্ট করার চেষ্টা করবে, কিন্তু প্রশাসনের উদ্দেশ্য যদি সত্যিই ইউরোপ থেকে সরে যাওয়া হয়, তবে তা যথেষ্ট হবে না। সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য ইইউকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল গড়ে তুলতে হবে। এর কেন্দ্রে থাকবে শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রতিরোধশক্তির বিকাশ, যা মার্কিন পিছু হটার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে।”
গাজা এবং ‘জনসংখ্যা স্থানান্তরের বেদনাদায়ক ইতিহাস’
গাজা উপত্যকা “নিয়ে নেওয়া” এবং ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুত করার পরিকল্পনা করছেন ট্রাম্প—এমন খবরে বিভিন্ন আরব সরকার বিকল্প পরিকল্পনা তৈরির চেষ্টা করছে বলে নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্যাট্রিক কিংসলি ও ভিভিয়ান জানিয়েছেন। “মিশর, জর্ডান, সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিরা শান্তভাবে একত্রে কাজ করে গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি ভিন্ন প্রস্তাব তৈরির চেষ্টা করছেন, যেখানে আরব দেশগুলো গাজা পুনর্গঠনের জন্য তহবিল ও নজরদারির দায়িত্ব নেবে, তবে সেখানকার বাসিন্দাদের সরিয়ে না নিয়ে তাদের স্বদেশেই রাখবে, যাতে ভবিষ্যতে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সম্ভাবনা উন্মুক্ত থাকে,” কূটনীতিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়। মিশরের তৈরি পরিকল্পনায় মূলত গাজা পুনর্গঠন করা হবে, কিন্তু সেখানকার ফিলিস্তিনিদের মিশর বা জর্ডানে স্থানান্তর করা হবে না, যেমনটি ট্রাম্প উল্লেখ করেছেন।
এটি গাজার বাসিন্দাদের জন্য স্বস্তির বিষয়—যারা ধ্বংসস্তূপের মাঝেও নিজ ভূমিতে থাকার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কমপ্যাক্ট পত্রিকায় লেখা এক নিবন্ধে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের পিএইচডি প্রার্থী হিদার পেনাটজার লিখেছেন, বলপূর্বক স্থানচ্যুতি বা “জনসংখ্যা স্থানান্তর” সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না। “আধুনিক কালের রাজনীতিতে এমন স্থানচ্যুতির উদাহরণ আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো বিপরীত ফল দেয়। ইতিহাস বলে, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তব সমস্যার সমাধান কম করে, বরং নতুন সংকটের সৃষ্টি করে।”
তিনি উল্লেখ করেন, স্টালিনের সময় ভল্গা অঞ্চলের জার্মান জনগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়ায় পাঠানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে নাৎসিদের স্লাভ জনগোষ্ঠীকে হটানোর পরিকল্পনা কিংবা ১৮৩০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের “ইন্ডিয়ান রিমুভাল অ্যাক্ট”-এর উদাহরণ। আরেক ধরনের স্থানচ্যুতি হলো “জনসংখ্যা বিনিময়,” যেখানে দুই দেশ পারস্পরিক সমঝোতায় বড় জনগোষ্ঠীকে ‘বিনিময়’ করে। পেনাটজার বলেন, “উদাহরণস্বরূপ, সাম্রাজ্য-পরবর্তী যুগে লিগ অব নেশন্স বেশ কয়েকটি দেশকে জাতিগতভাবে একজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে জনগোষ্ঠী বিনিময়ের চেষ্টা করেছিল।… ১৯২৩ সালে গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে প্রায় ২০ লাখ মানুষ (গাজার বর্তমান জনসংখ্যার সমান) আদিবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তবে ইতিহাস বলে, এরকম প্রকল্পগুলো সবসময় অস্থিতিশীলতা ডেকে আনে। ভৌগোলিক অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে অভ্যন্তরীণ সংঘাত শুরু হওয়ার প্রবল ঝুঁকি তৈরি হয়।”

 Sarakhon Report
Sarakhon Report