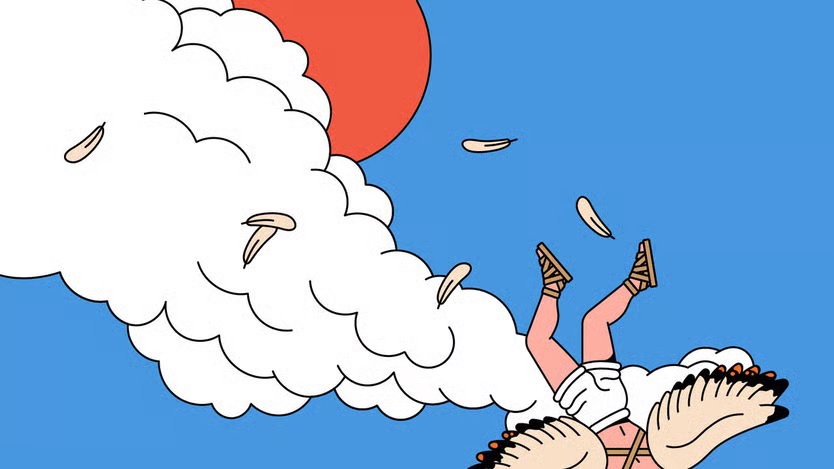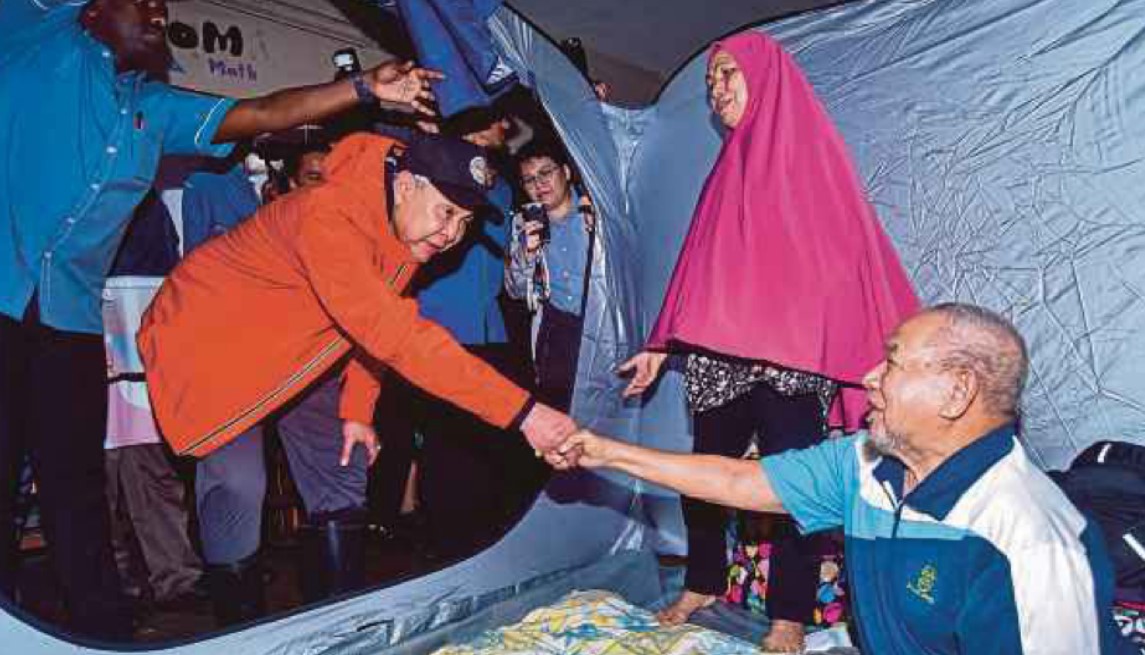মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত নাজুক। গাজা, লেবানন, সুদান, সিরিয়া ও লিবিয়ায় দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতি, সেই সঙ্গে ২০১০-এর দশকে উত্থান ও পতন ঘটানো আইএসের খেলাফত—এসব মিলিয়ে গোটা অঞ্চল কার্যত বিধ্বস্ত। সাম্প্রতিক ফরেন অ্যাফেয়ার্স পত্রিকায় কার্নেগি মিডল ইস্ট সেন্টারের মাহা ইয়াহইয়া উল্লেখ করেছেন যে, এই অঞ্চলে শক্তিশালী পুনর্গঠন পরিকল্পনা এখন জরুরি।
এই মুহূর্তে অবশ্য এক বিশেষ পুনর্গঠন পরিকল্পনা বেশি আলোচিত হচ্ছে, যা মূলত গাজার যুদ্ধকবলিত পরিস্থিতি ঘিরে: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বপ্নমতো “গাজাকে অধিগ্রহণ করে” ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুত করা, তারপর একে নতুন “রিভিয়েরা”য় পরিণত করা। মাহা ইয়াহইয়ার মতে, এই ভাবনা অবাস্তব—মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অনেকেরই পরবর্তী গাজার রূপরেখা এমন এক এলাকা, যা হয় ফিলিস্তিনশূন্যভাবে জাতিগতভাবে পরিশুদ্ধ করা হবে অথবা শাসনহীন কোনো রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে রাখা হবে, যা আশ্চর্যজনকভাবে স্থিতিশীল থাকবে!
আরব বিশ্ব থেকেও কিছু পাল্টা প্রস্তাব উঠছে, তবে ইয়াহইয়া মনে করেন, সেটি যথেষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বড় আকারের পরিকল্পনা—ইসরায়েল-সৌদি আরব সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ কিংবা ইরানকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দুর্বল করা—সবই খোদ অঞ্চলের জন্য অপ্রতুল। ইয়াহইয়ার যুক্তি, মধ্যপ্রাচ্যকে সত্যিকারের স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যেতে হলে মার্শাল পরিকল্পনার মতো একটি বৃহৎ উদ্যোগ দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনার অধীনে শুধু অর্থপুষ্টি নয়, সেই অর্থের ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছিল পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার উপায়ে, যা শেষ পর্যন্ত ইউরোপকে অর্থনৈতিকভাবে একীভূত করে ও দীর্ঘ সময় ধরে শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে এখন বহুমুখী ক্ষোভ ও আঞ্চলিক-বৈরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব মেটানোর প্রয়োজন রয়েছে, ইয়াহইয়া মনে করেন। শুধু অর্থের সংস্থান নয়, দরকার এর সুচিন্তিত ব্যবহার, একই সঙ্গে রাজনৈতিক কাঠামো ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি লিখেছেন, “স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে, যুদ্ধবিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্যকে অবশ্যই পথ বদলাতে হবে। শক্তিধর দেশগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বৈরিতা শুধুমাত্র আড়াল না করে সেটি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হবে। খণ্ডিত সমাজগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ তৈরি করতে হবে। জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে এবং অন্তর্বর্তী ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। পুনর্গঠনকে আরও বিস্তৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির অংশ করে তুলতে হবে। ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করে এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো আনতে হবে। একই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন বা অন্তত ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণের উপায় বের করতে হবে। না হলে বিশ্ব যতই অর্থ ঢালুক না কেন, এই অঞ্চল ভাঙাচোরা অবস্থাতেই থেকে যাবে।”
যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী
রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দরকষাকষি সাম্প্রতিক সময়ে জোরদার হয়েছে। সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় এই দুই পক্ষ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আলোচনা চালাচ্ছে, যখন একই সময়ে ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির বিরোধিতায় নেমেছেন।
এই আলোচনার অন্তর্নিহিত কারণ বেশ জটিল। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যাপক পিটার ট্রুবোভিটস ডয়েচে ভেলেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ-সংক্রান্ত এই আলোচনাকে ট্রাম্প ব্যবহার করতে চান যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি পুনর্গঠনের একটি ক্ষেত্র হিসেবে, যেখানে ওয়াশিংটন মস্কোর কাছাকাছি আসবে এবং ইউরোপ থেকে কিছুটা দূরে সরে যাবে।
তবে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান-পুনর্বিন্যাসের বাইরে, লে মন্ড পত্রিকার কলামে সিলভি কফম্যান লিখেছেন যে, রাশিয়া-ইউক্রেন কোনো যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যমাত্রাই আসলে যথেষ্ট নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। ২০১৪–২০১৫ সালে মিনস্কে হওয়া চুক্তির পরও ইউক্রেন ও ইউরোপ রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল।
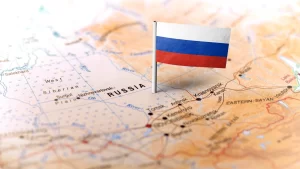
অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, পুতিনের প্রত্যাশা পূর্ব ইউক্রেনকে একীভূত করে নেওয়ার চেয়েও বড় কিছু। যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া আলোচনায় তাই উত্থাপিত হবে ন্যাটোর সম্প্রসারণ রোধ, ইউরোপের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামো পুনর্বিন্যাস সহ নানা বড় শর্ত। ২০২২ সালে পূর্ণমাত্রার আক্রমণের আগে পুতিন ন্যাটোর কাছে যে খসড়া চুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, তাতে জোটের সম্প্রসারণ বন্ধ করে ১৯৯৭ সালের মে মাসের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া ইত্যাদি বড় বড় দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব দাবি না মানলে অর্থবহ কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো কঠিন—সম্প্রতি কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের থমাস গ্রাহাম এমনটাই যুক্তি দিয়েছেন। ট্রাম্পের পক্ষে এসব শর্ত মেনে নিয়ে সাফল্যের মোড়কে উপস্থাপন করা মোটেই সহজ হবে না।
ইতালীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইস্তিতুতো আফ্ফারি ইন্টারনাজিওনালির গবেষক রিকার্দো আলকারো সম্প্রতি লিখেছেন, “রাশিয়া পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে, আসন্ন আলোচনাকে তারা মূলত তাদের পুরোনো লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে চায়—যে লক্ষ্য তারা ইউক্রেনের সঙ্গে বিরোধের ‘মূল কারণ’ বলে মনে করে: স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ন্যাটো-কেন্দ্রিক যে ইউরোপীয় নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে উঠেছে, সেটিকে দুর্বল করা; নিজেদের সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো ও ইইউ-এর সম্পৃক্ততা কমানো; আর ইউক্রেনকে ইউরো-আটলান্টিক প্রক্রিয়ায় না ঢুকতে দেওয়া। পুতিনের ধারণা, ইউক্রেনের ভূখণ্ড কেটে নেওয়া, স্থায়ীভাবে সামরিক নিরপেক্ষ রাখা, নিরস্ত্রীকরণ এবং তথাকথিত ‘ডি-নাজিফিকেশন’ (অর্থাৎ জেলেনস্কির সরকার ফেলে রুশপন্থি শক্তিকে ক্ষমতায় আনা) ছাড়া এটি সম্ভব নয়।”
ফরাসি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনস্টিট্যু ফ্রঁসেজ দে রিলাসিয়ঁ আন্তেরনাসিওনালের তরফে দিমিত্রি মিনিক সম্প্রতি একটি বিশ্লেষণপত্রে লিখেছেন, “ট্রাম্পের লক্ষ্য কী? দ্রুত কোনো চুক্তি করেই ‘শান্তির দূত’ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, এমন এক নেতায় পরিণত হওয়া যাকে মস্কো উপেক্ষা করতে পারবে না। পুতিনের লক্ষ্য কী? ইউক্রেনকে রাজনৈতিকভাবে তার অধীনস্থ বানানো—যেটা এখনো মনে হয় ট্রাম্প পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বাস্তবে কোনো চুক্তি করতে হলে খুব দ্রুতই তাকে এটি বুঝতে হবে। পুতিন মিনস্কের সময় যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে এবারও পশ্চিমাদের ‘কু-চুক্তি’তে যুক্ত করতে চাইবেন যাতে ইউক্রেনকে মেনে নেওয়া অসম্ভব এমন শর্ত মানতে বাধ্য করা যায়। এই কৌশলে তিনটি লক্ষ্য পূরণ হবে: কিয়েভকে দুর্বল করা, পশ্চিমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং ইউক্রেনের জনগণের মধ্যে পশ্চিমাদের প্রতি ক্ষোভের জন্ম দেওয়া।”

ঈশ্বর-ভাবাপন্ন পর্যায়ে পৌঁছানোর দৌড়
চলতি মাসে নিউ স্টেটসম্যানের প্রচ্ছদ নিবন্ধে ব্রুনো মাকাইস লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সক্ষমতা অর্জনের প্রতিযোগিতা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, “এ বছরই অসংখ্য বুদ্ধিমান এআই এজেন্ট তৈরি হবে … আমাদের দৈনন্দিন কাজ (যেমন সূচি তৈরি, ফ্লাইট ও হোটেল বুকিং, কেনাকাটা বা দর-কষাকষি) এমনকি আরও বৃহৎ পরিসরে কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে এসব এজেন্ট। এদের ভিত্তি হবে সেই ‘ফাউন্ডেশনাল মডেল’, যা এক ধরনের ভার্চুয়াল জগতের মতো। সেটাই হল আসল বড় পুরস্কার। … কল্পনা করুন, এমন একটা সময়, যখন সত্যিই বিশ্বময় এক ‘সুপার বুদ্ধিমত্তা’ বা ‘গ্লোবাল ব্রেইন’ সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ইচ্ছেমতো কোনো বিশেষ নীতি বা লক্ষ্য প্রবেশ করানো যেতে পারে, এবং সেটি এমনভাবে সুগভীরভাবে লুকিয়ে রাখা সম্ভব যে, এই সিস্টেম তৈরি করা ছাড়া অন্য কেউ জানতেই পারবে না যে এর ভেতরে অন্য কোনো অভিসন্ধি ঢোকানো আছে। … একে বলা যেতে পারে একধরনের অদৃশ্য শাসনব্যবস্থা … প্রতিপক্ষ যেন কেবল ভিডিও গেম খেলছে, আর আপনি সেই গেমের কোড লিখে দিচ্ছেন।”

 Sarakhon Report
Sarakhon Report