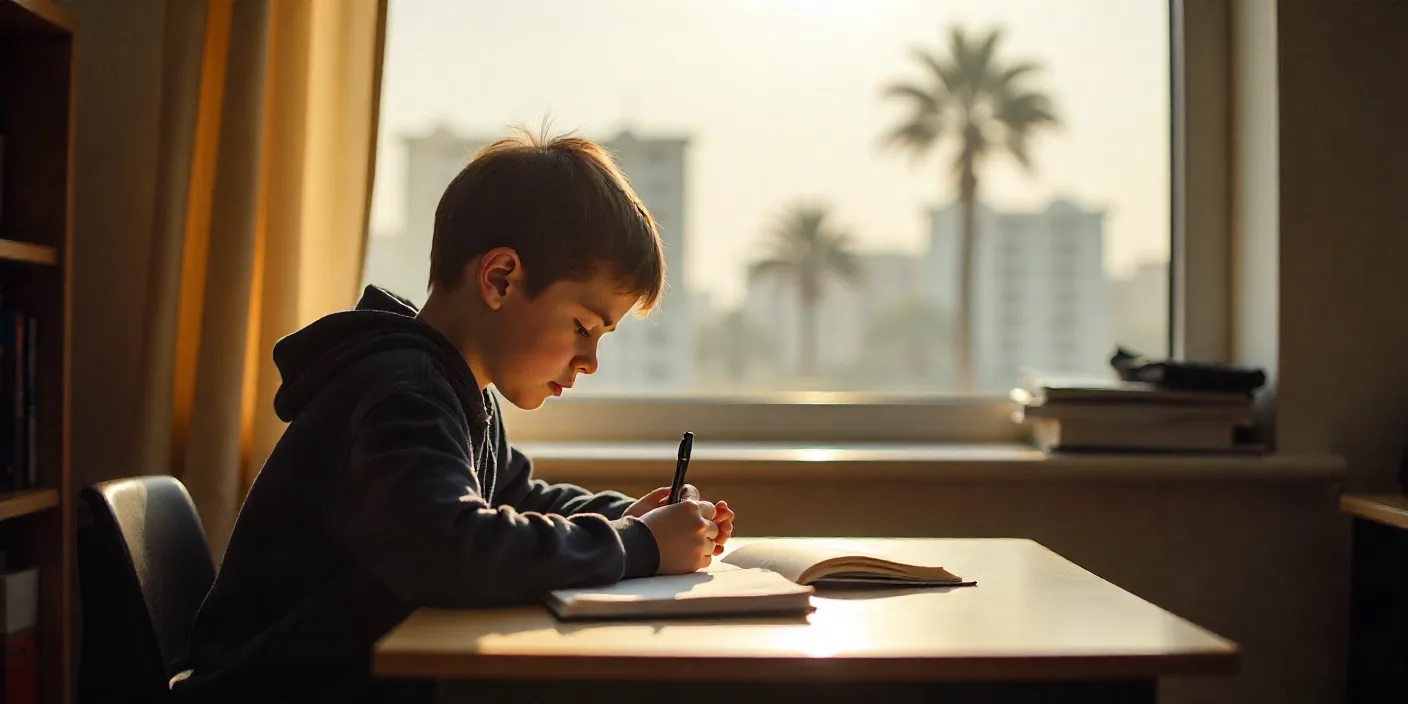গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কারের প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার অন্যতম অংশ রাজনীতিতে নারীর অর্থপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের বিষয়টি আলোচনায় নেই। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের প্রধান দুই দলের শীর্ষ পদে আছেন নারী, সরকার পরিচালনায় তিন দশকেরও বেশি সময় ছিলেন তারা; এরপরও রাজনীতিতে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি।
সরকারের নিবন্ধন পাওয়ার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু এরপরও নির্ধারিত ৩৩ শতাংশ বা তার কাছাকাছি নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি কোনো দল।
জুলাই-অগাস্টের আন্দোলনের সময় রাজপথে নানা শ্রেণি-পেশার নারীর অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশ্লেষকরা বলছেন, আন্দোলনে নারীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে রাস্তায় নামতে উদ্বুদ্ধও করেছে।
কিন্তু আন্দোলনে নারীর উপস্থিতি যত স্পষ্ট ছিল, অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব অতটা জোরালো নয়।
পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করা নতুন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিয়েও অসন্তোষের খবর গণমাধ্যমে এসেছে।
এরইমধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার-হেনস্তার একের পর এক ঘটনা আলোচনায় আসায় শঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাজনীতিবিদ, বিশ্লেষকসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ।
নারীর নিরাপত্তা নিয়েই যেখানে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সেখানে তাদের রাজনীতি চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়েও সন্দেহ তৈরির যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশে নারী নেতৃত্ব
বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষ পদে নারীর উপস্থিতি গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে।
১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর দলের ভেতরে অসন্তোষের সূত্র ধরে বিএনপির একাংশ খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে আনার পরিকল্পনা করে। ১৯৮২ সালের একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে খালেদা জিয়া বিএনপিতে যোগ দেন এবং ১৯৮৪ সালে দলের চেয়ারম্যান পদে আসেন।
এদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের ছয় বছর পর ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। দলের একতা ধরে রাখতে শেখ মুজিবের পরিবারের সদস্য হিসেবেই তাকে আনা হয় এই পদে।
শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এখনও দলীয় প্রধানের পদেই আছেন।
জাতীয় পার্টির নেতৃত্বেও রওশন এরশাদের একটি ভূমিকা আছে, যিনি দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের স্ত্রী।
১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি গঠনের পর থেকে ২০১৯ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দলের প্রধান ছিলেন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তার মৃত্যুর পর দলের নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয় মি. এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ ও ভাই গোলাম মোহাম্মদ কাদেরের মধ্যে। সেই দ্বন্দ্ব এখনও শেষ না হলেও ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর সংসদে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বিরোধী দলীয় প্রধানের পদে ছিলেন রওশন এরশাদ।
এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুযায়ী দলে নারীর ৩৩ শতাংশ উপস্থিতি নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা অর্জন করতে পারেনি কোনো দল।
দলের শীর্ষে নারী থাকলেও আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোর কোনোটিই দলে নারীদের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই বলে বার বার আলোচনায় এসেছে।
তবে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, “জামায়াতে ইসলামে ৪৩ শতাংশ নারী সদস্য, আর বাকি ৫৭ ভাগ পুরুষ। কাজেই নির্বাচন কমিশনের যে শর্ত তার বেশি আমরা অর্জন করেছি।”
আবার বিশ্লেষকদের অভিমত, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের যে পরিমাণ অংশগ্রহণ দেখা যায় তাও মূলত আলঙ্করিক। তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা হয় এবং অনেকেই পদপদবী পান পরিবারতন্ত্র বা অর্থের দাপটে। সত্যিকার অর্থে নারীর অংশগ্রহণ কম।
কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা বেগম আলপনা বলেন, “সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কাছে নারীরা জিম্মি।”
“পুরুষশাষিত সমাজের যে নেতারা, তারা যেখানে সবকিছুর জন্য দায়ী, তারা নিজেদের স্বার্থে কাজ করে। নারীরা সংসদে আছেন, জেলা-উপজেলায় আছেন, ইউনিয়ন পরিষদে আছেন, কিন্তু তারা কি সবার সহযোগিতা পান? আমরা ঘরে যেরকম, বাইরেও সেরকম।”

রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের বাস্তবতা কী––এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, এটা একবারেই নেই তেমনটা নয়। কিন্তু ঢালাওভাবে এই অভিযোগ সত্য নয়।
তিনি বলেন, “আমাদের জেলা ও উপজেলা কমিটিতে আমরা চেয়েছি ৩৩ শতাংশ নারীর কোটা পূর্ণ করতে। আমরা চাচ্ছি তৃণমূল থেকে নারীরা আসবে। কিন্তু উপজেলায় বা ডিস্ট্রিক্টে যখন কমিটি করে তারা আর দেখে না তৃণমূল থেকে কে আসলো। তারা ঘরের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে এটাকে নিয়ে আসে। কারও বোন, কারও বৌ। এটা কেন্দ্র থেকে হয় না।”
তিনি আরও বলেন, “সাধারণ মহিলা যারা রাজনীতি করতে চায়, তাদের ব্যাপারে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটার পরিবর্তন হয় নাই। সেখানে এখনও বাধাগ্রস্ত হচ্ছি আমরা। কমিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে মনে করে এই যে মহিলাকে দেবো, তার পরিবর্তে এখানে আমার অনুগত একটা ছেলে চলে আসবে, সেই ছেলে বেশি উপযুক্ত– এই চিন্তাধারা থেক আমরা বের হতে পারি নাই।”
বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র ছিল ও আছে, এরকম অভিমত জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফওজিয়া করিম ফিরোজ বলছেন, “পরিবারতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আওয়ামী লীগ চলে যাওয়ার পরেও কিন্তু (নেতৃত্বের ক্ষেত্রে) শেখ পরিবারের সদস্যদের কথাই শোনা যায়। যারা শেখ পরিবারের বাইরে আছে তাদের নাম কিন্তু শোনা যাচ্ছে না।”
“আর বিএনপি তো পরিবারতন্ত্রের ভেতরই আছে, বের হতে পারে নাই। জাতীয় পার্টিও পরিবার থেকে বের হতে পারে নাই। রাজা-রানীর ছবি দেখে এসেছি সারা জীবন, আমরা এটা থেকে বের হতে পারি নাই।”
ফওজিয়া করিম ফিরোজ অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনেরও সদস্য।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলছিলেন, “পরিবারতন্ত্র এখনও একটা ফ্যাক্টর বাংলাদেশের রাজনীতিতে। এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে অর্থভিত্তিক রাজনীতি।”
তিনি বলেন, কিছু কিছু গবেষণার সময় দেখা গেছে, নারীরা দাবি করেছেন পরিবারতন্ত্রের বাইরেও তারা অর্থ খরচ করতে পারেননি বলে “নমিনেশন বাণিজ্যে তারা সুবিধা করতে পারেননি”।
“নিয়ম ছিল দলগুলোর সব পর্যায়ের কমিটিতে শতকরা ৩৩ নারী থাকতে হবে। কিন্তু আনফরচুনেটলি দুই থেকে তিন পার্সেন্টও আছে কিনা সন্দেহ আছে। আওয়ামী লীগে একটু বেশি হতে পারে, বিএনপিতে একটু কম, জাতীয় পার্টির কথা নাই বা বললাম। নতুন যে রাজনৈতিক দল এনসিপি সেখানেও নারীর খুব বেশি উপস্থিতি আমরা দেখছি না। ভবিষ্যতে তারা কতটুকু (৩৩ শতাংশ) পূরণ করবে, এখন বলা কঠিন,” বলেন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন।

কোটা নাকি যোগ্যতা?
১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (২০১৩ সালে প্রতিস্থাপিত) অনুযায়ী, সব রাজনৈতিক দলের সদস্যপদে ও সব কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা ছিল। ২০২০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনের কথাও বলা হয়েছিলো।
তবে কোনো দলই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করায় ২০৩০ সালের মধ্যে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আরপিও সংস্কারের প্রস্তাব পাঠায় নির্বাচন কমিশন।
এদিকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন খাতের সংস্কারে যেসব সংস্কার কমিশন গঠন করে, তার মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশন নারীর জন্য সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত আসন তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এর পরিবর্তে ৪০০ আসনের সংসদে নারীর জন্য ১০০ আসন সংরক্ষিত রাখা জনগণের সরাসরি ভোটে সেখানে নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার বিধান রেখেছে।
তবে কোনো সংস্কার কমিশনেই রাজনৈতিক দলের নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে কেনো সুপারিশ বা পরামর্শ নেই।
একদিকে রাজনৈতিক দলের ওপর নারী সদস্য রাখার বিষয়ে কোনো চাপ না থাকা, আবার অন্য দিকে সরাসরি ভোটে নারীর জন্য আসন রাখা–– এই দুইয়ের মাঝখানে ভারসাম্যহীনতার কোনো জায়গা তৈরি হচ্ছে কিনা সে প্রশ্নও সামনে আসছে।
এ বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলছেন, “এটা অবশ্যই কনসার্নের (চিন্তার) বিষয়। সংস্কার কমিশনগুলোর রিপোর্টে ঐকমত্য তৈরির আগে অনেকগুলো বিষয় ঠিক (সংশোধন) করতে হবে।”
বাংলাদেশের জনসংখ্যায় নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে বেশি। সেই অনুপাতে রাজনৈতিক দলে নারীর ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের ধারণা ঠিক কিনা এই প্রশ্ন তিনি বলেন, “জনসংখ্যার অনুপাতে এটা যথেষ্টই কম বলে মনে করি আপাত দৃষ্টিতে।”
“আমরা চাই এমন একটা সময় আসুক যখন শতাংশের হিসাবে রিপ্রেজেন্টেশন (প্রতিনিধিত্ব) ঠিক করতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না …। কিন্তু এখনও আমরা দেখছি নারীদের সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য নারীদেরই কথা বলতে হচ্ছে। শতাংশ হিসেবে ডিসাইড করে না দিলে নারীদের আর সামনে পাওয়া যাচ্ছে না রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না হলে পার্সেন্টেজ করেও আসলে খুব বেশিদিন এটা (নারীর প্রতিনিধিত্ব) টেকানো যাবে না।”
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “যোগ্যতার ভিত্তিতে না এনে শুধু নারী বলেই রাজনীতিতে আনতে হবে আমরা এটার বিরোধী। এর ফলে আরও বেশি বৈষম্যের সুযোগ তৈরি হয়। ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব এটার ক্ষেত্রেও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নারীদের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।”
এ বিষয়ে আইনজীবী ফওজিয়া করিম ফিরোজ বলছিলেন, “নারীরা পুরুষের চাইতে সংখ্যায় বেশি বাংলাদেশে। তারপরও তাদের প্রতিনিধিত্ব নাই সংখ্যার হিসাবে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর কারণ মানসিকতার পরিবর্তন হয় নাই।”
তবে তিনি মনে করেন, কোটা তৈরি করে নয়, বরং রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীকে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দেওয়াটাই বেশি জরুরি।
৩৩ শতাংশ কোটা রাখার বাধ্যবাধকতা রাখা উচিত না-এই অভিমত জানিয়ে আফরোজা বেগম আলপনা বলছেন, “যেখানে কোটা থাকবে সেখানেই স্বজনপ্রীতি থাকবে, দুর্নীতি থাকবে, অর্থের খেলা থাকবে। যার যোগ্যতা নাই তাকে এনে বসিয়ে দেবে। বরং সমাজের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে, সমাজের মানুষ চেনে-জানে এমন মানুষকেই রাজনীতিতে জায়গা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।”
বিএনপির সেলিমা রহমান বলছেন, “একটা মেয়েকে রাজনীতির দর্শন বুঝে কাজ করতে হবে। নারী বলে নিয়ে নিলাম, সে কিছুই বুঝলো না, একটু পুতুলের মতো থাকলো সেটা তো করা যাবে না। সেজন্যই নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।”
শুধু নিয়মের জন্য রাখা নয়, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীদের সুযোগ করে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলছেন, নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলকেই আলটিমেটলি সংষ্কারের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
“তারাই প্রার্থী দেবে, গণতন্ত্রের চর্চা তাদের মাধ্যমে আসবে। সংস্কার কমিশন তো সাময়িক, ফলে এটা রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্টের ওপর নির্ভর করে। তবে অতীতে আমরা অনেকবার দেখেছি তারা এরকম নানা আশ্বাস দিয়ে পরে আর পূরণ করেনি। তাই সদিচ্ছাটা প্রয়োজন।”

নিরাপত্তাহীনতায় শঙ্কার জায়গা বেড়েছে
গত সাত মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের হেনস্তা-অপদস্তের বিভিন্ন ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
‘তৌহিদি জনতার’ নাম করে নারীদের ফুটবল খেলা বন্ধ করা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দান, নারীদের পোশাক নিয়ে বা প্রকাশ্যে তাদের ধূমপান করা নিয়ে মোরাল পুলিসিং এর অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনাকে সমর্থন করতেও দেখা গেছে অনেককে।
এরকম পরিস্থিতিতে মিছিলে-রাজপথে নারীর অংশগ্রহণ, তাদের রাজনীতি চর্চা নিয়েও উদ্বেগের জায়গা তৈরি হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ বিবিসি বাংলাকে বলেন, “বাংলাদেশে নারীরা প্রতিবারই বিভিন্ন আন্দোলনে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, এরপর শাসকগোষ্ঠীর দিক থেকে তাদের পণ্য হিসেবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা পাল্টায়নি।”
“জুলাই আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে নারীদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু আট তারিখের (আটই অগাস্ট) পরে আমরা সবচেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত সময়ে আছি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত হয়েছি আমরা নারীরা।”
নারীদের হেনস্তার নানা ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, “আজ যারা নতুন বন্দোবস্তের কথা বলছেন তাদের অনেককেই দেখেছি এসব ঘটনায় প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখতে। ফলে বাংলাদেশ যে প্রত্যাশার দিকে হাঁটছে না, প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে হাঁটছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।”
তবে তিনি এটাও বলেন, “আশার কথা হচ্ছে যে নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে তাদের রুখে দেওয়ার শক্তি কারোরই নেই। ফলে নারীদের প্রতিই আমাদের আস্থা আছে।”
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “নিরাপত্তা তো নাগরিক হিসেবে আমার অধিকার। সরকারের পক্ষ থেকে এটা নিশ্চিত করার কথা। আমরা এত যে অধিকারের কথা বলি সেটার জন্য এবং দেশের জন্য এই পরিস্থিতি (নিরাপত্তাহীনতা) ক্ষতিকর।”
পাঁচই অগাস্ট জামায়াতেরও অনেক নারী সদস্য শাহবাগে ছিলেন উল্লেখ করে জামায়াত নেতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেন, “নারীর রাজনীতি করার অধিকার আছে, ইসলামও এক্ষেত্রে বাধা দেয় না। কিন্তু নারী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণে কিছুটা তো নৈতিক ঝুঁকি থাকে। নৈতিক অবক্ষয় যাতে না হয় সেরকম একটা পরিস্থিতি আমাদের তৈরি করা দরকার।”
সেলিমা রহমান বলেন, “পাঁচই অগাস্টের পরে আমরা ভেবেছিলাম, যেহেতু আমাদের মেয়েরা এখন অনেক যোগ্য ও উপযুক্ত, আন্দোলনেও তারা ছিলেন, তাদের জন্য একটা জায়গা তৈরি হবে। কিন্তু এরপরে যে অরাজকতা…ধর্ষণ, মব জাস্টিস, যাকে তাকে যেখানে সেখানে অপমান করা, জোর করে মামলা প্রত্যাহার করা এগুলো কী নির্দেশ দিচ্ছে? সরকারই বা চুপ কেন? নারীরা কী করে মুক্ত ভবিষ্যতে রাজনীতি করবে? কীভাবে তারা অংশগ্রহণ করবে?”
বিবিসি নিউজ বাংলা

 Sarakhon Report
Sarakhon Report