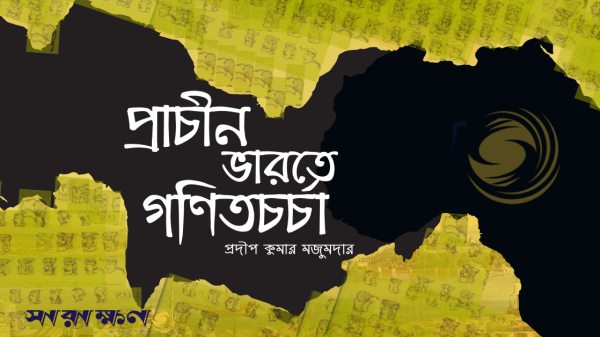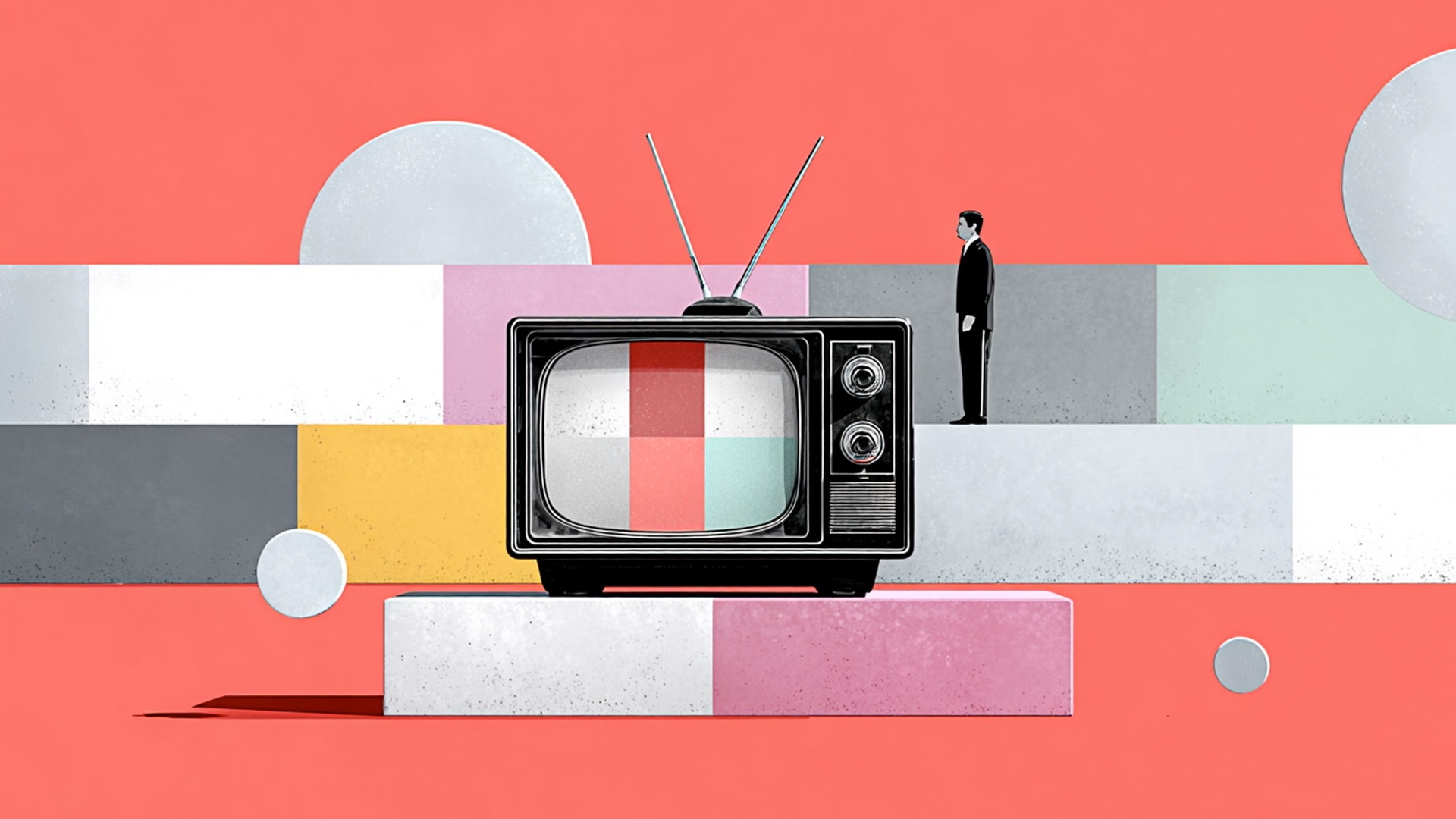বাংলাদেশে চলমান মব ভায়োলেন্সের ঘটনা শুধু তাৎক্ষণিক নৃশংসতা নয়, বরং এটি একটি গভীর রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকটের প্রতিফলন। এর পেছনে রয়েছে বহুস্তর বিশৃঙ্খলা, দণ্ডমুক্তি, ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। চলুন এই সংকটের মূল দিকগুলো পর্যালোচনা করি।
নাগরিক কর্তৃত্ব দুর্বল, আইনের শাসন দুর্বলতর
সেনাপ্রধানের বক্তব্য প্রতীকীভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, প্রতিদিনের আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব পুলিশের হাতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ সদস্যরা নিজেই পর্যাপ্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। অনেক সময় তারা মানসিক ট্রমার মধ্যে রয়েছেন—বিশেষ করে মব ভায়োলেন্সে নিহত সহকর্মীদের বিচার না পাওয়ার কারণে। ফলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও তারা ঝুঁকি নিতে ভয় পান, কারণ কোনো ন্যায়বিচার বা প্রতিরক্ষা তাঁদের জন্য নিশ্চিত নয়।
রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বলয়
বাংলাদেশের অনেক সহিংসতার পেছনে রয়েছে দলীয় ছত্রছায়া। স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, সংসদ সদস্য বা ছাত্র সংগঠনের নেতারা অনেক সময় এই সহিংস গোষ্ঠীগুলোকে ‘প্রয়োজনে ব্যবহারের উপকরণ’ হিসেবে দেখেন। এদের অনেকেই দলের যুব সংগঠন বা ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত। ফলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বিচারহীনতার সংস্কৃতি
বাংলাদেশে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিচারহীনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে:
- অতীতের শিক্ষকদের ওপর হামলা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক হামলাগুলোর বেশিরভাগই বিচারবহির্ভূত থেকে গেছে।
- প্রাথমিক পর্যায়ের হামলাকারীদের কয়েকজনকে হয়তো গ্রেপ্তার করা হয়, তবে মূল পরিকল্পনাকারীরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।
- দলীয় প্রচারণার মাধ্যমে এমনভাবে প্রচার চালানো হয়, যাতে ভুক্তভোগীদের দোষী করে তোলা হয়, ফলে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং প্রতিবাদ স্তিমিত হয়।
ছাত্র-যুব গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ব্যবহার
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলো ‘মাঠের সৈনিক’ হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের অপরাধকে “আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া” হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এই গোষ্ঠীগুলো প্রায়শই ক্যাম্পাসে অঘোষিত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং যেকোনো ভিন্নমতকে দমন করতে সক্ষম হয়।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার সংকট
মব ভায়োলেন্সের বহু ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ ক্যাম্পাসে ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রায়শই সাবধানী বা নিরুৎসাহী আচরণ করে, কারণ রাজনৈতিক চাপ বা প্রতিশোধের ভয় কাজ করে। সাময়িক বহিষ্কার একধরনের প্রতীকী পদক্ষেপ, যেখানে স্থায়ী বহিষ্কার বা আইনগত ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত।

এই সহিংসতাকারীদের পৃষ্ঠপোষক কারা?
- স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী, যারা তাদের এলাকায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এই গোষ্ঠী ব্যবহার করে।
- সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীরা, যারা এদেরকে দলীয় শক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করেন।
- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, যারা রাজনৈতিক শিবিরের অনুগ্রহ বজায় রাখতে চায়।
- পুলিশ কর্মকর্তারা, যাঁরা অনেক সময় অভিযোগ নিতে পারেন না বা প্রতিশোধমূলক মামলার শিকার হন।
এরা কি আইনের ঊর্ধ্বে?
বাস্তবতা হলো—হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই তারা আইনের ঊর্ধ্বে। কারণ:
- বেশিরভাগ হামলাকারী গ্রেফতার এড়ায় বা দ্রুত জামিন পেয়ে যায়।
- দলের অভ্যন্তরে তাদের “সাহসিকতা” হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।
- তারা পুনরায় সহিংসতায় জড়ায়, শাস্তি না পেয়ে বারবার একই কাজ করে।
- অনেকে আবার ছাত্র ও যুব সংগঠনের মধ্যে পদোন্নতি পায়।

কী করা জরুরি?
-
- আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে দলমত নির্বিশেষে।
- রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।
- পৃষ্ঠপোষকদের নাম প্রকাশ করতে হবে—জনসমক্ষে লজ্জিত করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির প্রভাব বন্ধ করতে হবে।
- বিশেষ সংকটকালে সেনা বা আধাসামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
উপসংহার
সেনাপ্রধানের বক্তব্য যতই তাৎপর্যপূর্ণ হোক, যদি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকে, তবে তা শুধু প্রতীকী উচ্চারণেই রয়ে যাবে। রাজনৈতিক দণ্ডমুক্তির সংস্কৃতি যতদিন ভাঙা না যায়, এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য পৃষ্ঠপোষকদের জবাবদিহির আওতায় না আনা যায়, ততদিন মব ভায়োলেন্স একটি ভয়ের অস্ত্র, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও প্রতিশোধের মাধ্যম হিসেবেই থেকে যাবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট