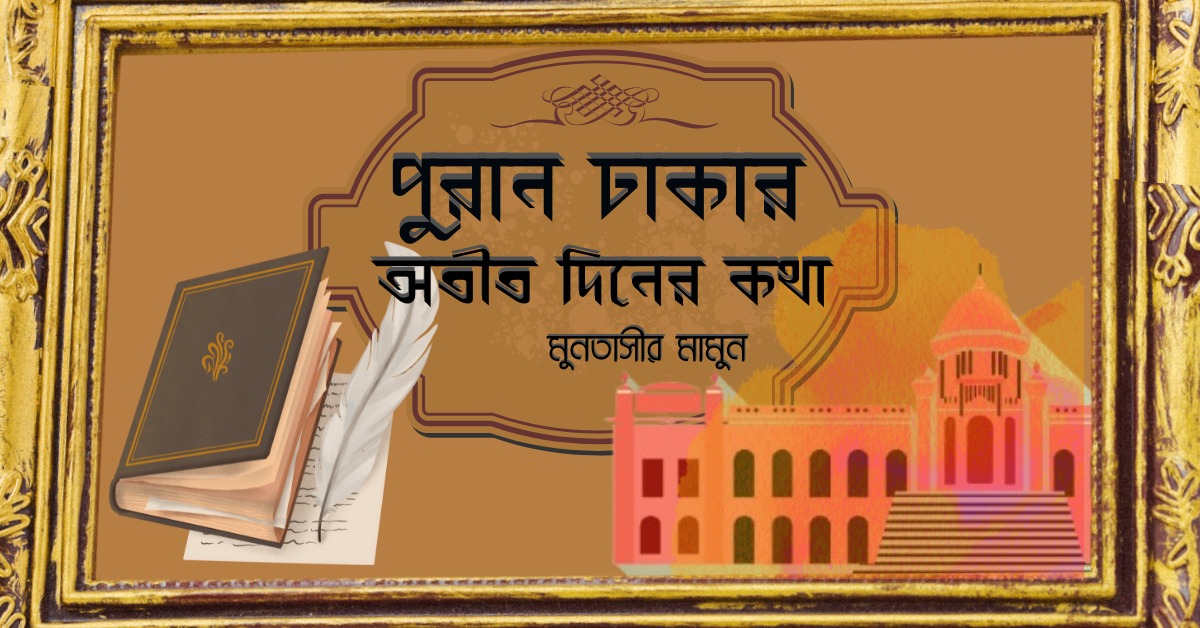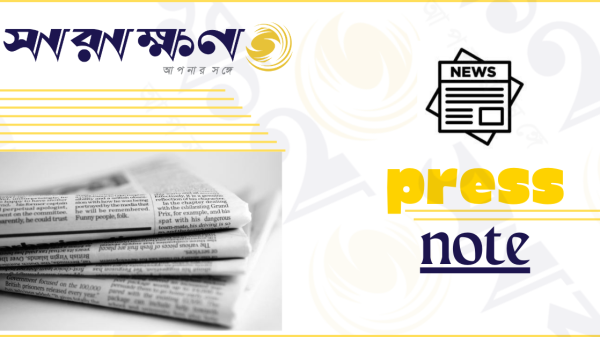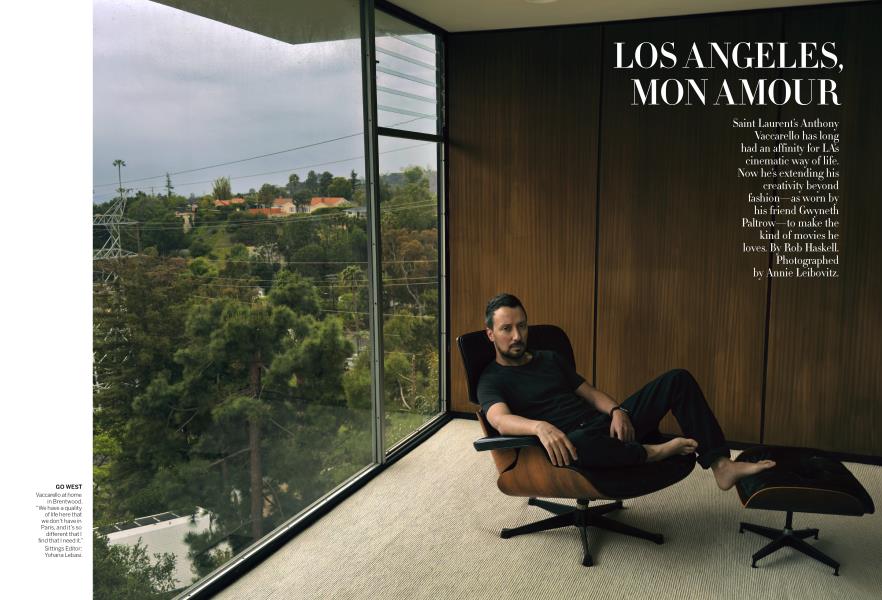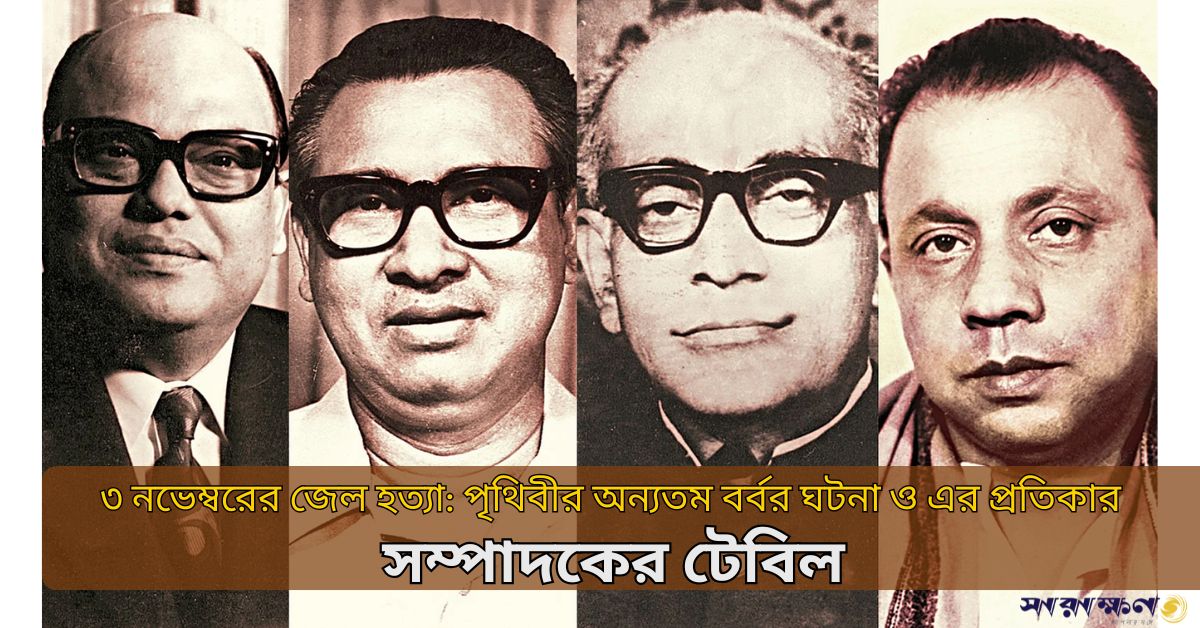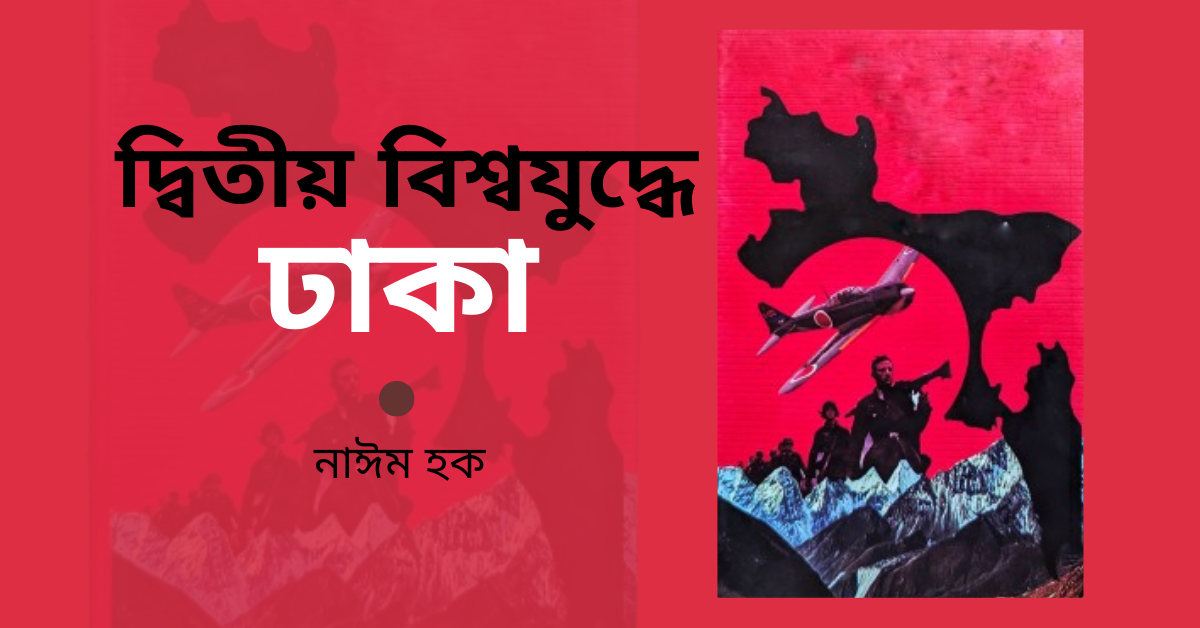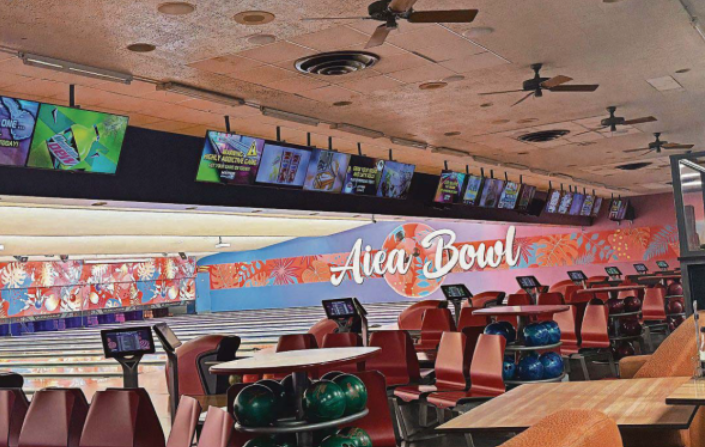বিশ্ববাণিজ্যের বাজারে চীন ও জাপান যুগের পর যুগ ধরে তাদের হস্তনির্মিত কাঠ, মাটি (ক্লে) এবং সিরামিক পুতুল রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এই শিল্প শুধু তাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে না, বরং সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বাহক হিসেবেও আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হচ্ছে।
বাংলাদেশেও একসময় ছিল এমনই সমৃদ্ধ পুতুলশিল্প। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মাটি, কাঠ, ঘাস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে অসাধারণ নকশার পুতুল তৈরি করতেন। এসব পুতুল ছিল শুধু শিশুদের খেলার সামগ্রী নয়—তাদের রঙ, নকশা, আকার ও ঐতিহ্যে ফুটে উঠত গ্রামের জীবনের কাহিনী, লোককথা এবং শিল্পচেতনা।
দুঃখজনকভাবে, বহু কারিগর দেশভাগের সময় ও পরে ভারতে চলে গেছেন। ফলে বাংলাদেশের পুতুলশিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। এখন প্রশ্ন—আমরা কি আবারও এই ঐতিহ্যকে জাগিয়ে তুলতে পারি? বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি? জাপান-চীনের উদাহরণ কি আমাদের কোনো পথ দেখাতে পারে?
চীন ও জাপানের পুতুলশিল্প: সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

চীনের কেস স্টাডি
চীনের জিয়াংসি, ফুজিয়ান, গুয়াংডং প্রদেশে বিশেষ করে সিরামিক এবং ক্লে ডল তৈরির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।
- তারা আধুনিক ডিজাইন ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সমন্বয়ে পণ্য তৈরি করে।
- সরকারের সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও রপ্তানির বাজার খুঁজে পাওয়ার উদ্যোগে শিল্পটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।
- পর্যটন খাতেও এই পুতুল একটি গুরুত্বপূর্ণ সুভেনিয়র।
জাপানের কেস স্টাডি
জাপানের কাঠের পুতুল (কোকেশি) বহু শতাব্দীর পুরানো।
- এগুলো হাতে খোদাই করা হয় এবং নান্দনিক রঙে আঁকা হয়।
- পর্যটক ও সংগ্রাহকেরা এগুলো কিনে নেন উচ্চ মূল্যে।
- সরকার ও বেসরকারি খাত স্থানীয় কারিগরদের সহায়তা করে, প্রদর্শনী আয়োজন করে এবং বিদেশি বাজারে পরিচিত করে তোলে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্য: একসময়কার গৌরব
বাংলাদেশে মাটির পুতুলের ইতিহাস শত বছরের বেশি পুরোনো।
- মাটি, কাঠ, শণ বা ঘাসের পুতুলে গ্রামীণ জীবনের দৃশ্য ফুটে উঠত।
- হিন্দু কারিগরদের মধ্যে এই শিল্পটি ছিল বংশপরম্পরায়।
- নবরাত্রি, দুর্গাপূজা, মেলা ও গ্রামীণ হাটে এগুলো বিক্রি হতো।
- ঢাকায় কার্জন হল, পল্টন ও দেশি মেলাতেও এই পুতুল পাওয়া যেত।
কিন্তু দেশভাগের পর এই কারিগরদের বড় অংশই ভারত চলে যায়। নতুন প্রজন্ম আর এই কাজ শিখতে চায়নি। বাজার, পৃষ্ঠপোষকতা ও আধুনিকীকরণের অভাবে শিল্পটি ক্ষয়িষ্ণু হয়।
হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের কারণ
- জনগোষ্ঠী পরিবর্তন: হিন্দু কারিগরদের চলে যাওয়া।
- প্রযুক্তির অভাব: আধুনিক ছাঁচ, রঙ ও গ্লেজিং প্রযুক্তি নেই।
- বাজার হারানো: স্থানীয় মেলা ও গ্রামীণ বাজার কমেছে।
- বিনিয়োগের অভাব: সরকার বা বেসরকারি খাত আগ্রহী নয়।
- প্রশিক্ষণহীনতা: নতুন প্রজন্ম শিখতে চায় না এবং শেখানোর ব্যবস্থা নেই।
সম্ভাবনা: কী করে আবারও গড়ে তোলা যায় এই শিল্প?

স্থানীয় কারিগরদের খুঁজে বের করা ও সংরক্ষণ
এখনো কিছু এলাকায় (যেমন মাদারীপুর, ফরিদপুর, নওগাঁ, দিনাজপুর) ছিটেফোঁটা পুতুল তৈরি হয়। তাদেরকে সরকারি বা এনজিও সহায়তায় সংগঠিত করা যায়।
কারিগরি প্রশিক্ষণ
আধুনিক নকশা, রঙ ও ছাঁচ ব্যবহারের কৌশল শেখানো। সিরামিক, কাঠ ও ক্লে—প্রতিটি শাখায় আলাদা দক্ষতা গড়ে তোলা।
ডিজাইন ও ব্র্যান্ডিং
বাংলাদেশের নিজস্ব লোককাহিনি, নকশা ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য তুলে ধরা। বিদেশি বাজারের জন্য স্টাইলিশ, শৌখিন ও সংগ্রাহক-যোগ্য পুতুল তৈরি করা।
রপ্তানি সংযোগ
- ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম (Amazon, Etsy) ব্যবহার করে বিদেশে বিক্রি।
- সরকারের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) এর সহায়তায় বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ।
- পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে হোটেল, এয়ারপোর্ট ও গিফট শপে পুতুল রাখা।

নীতিগত সহায়তা
শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ঋণ, ভর্তুকি, প্রদর্শনী ও বাজার-সংযোগ সুবিধা প্রদান।
সম্ভাব্য বৈদেশিক মুদ্রা আয়
চীন ও জাপানের অভিজ্ঞতা বলছে, বছরে কোটি কোটি ডলার আসে এই শিল্প থেকে। বাংলাদেশ শুরুতে ছোট পরিসরে ১–৫ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে। ধীরে ধীরে ২০–৫০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে।
বাংলাদেশের পুতুলশিল্প শুধু বাণিজ্যিক নয়, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। আজ যখন চীন ও জাপান তাদের ঐতিহ্য রক্ষা করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, তখন আমাদেরও দরকার সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা।
কারিগরদের খুঁজে বের করা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক ডিজাইন, সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ—সব মিলিয়ে সঠিক উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশও একদিন তার পুতুলশিল্প দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট