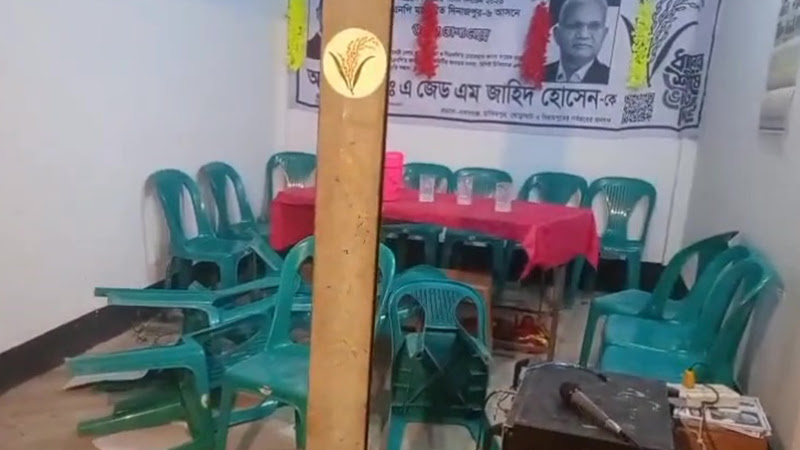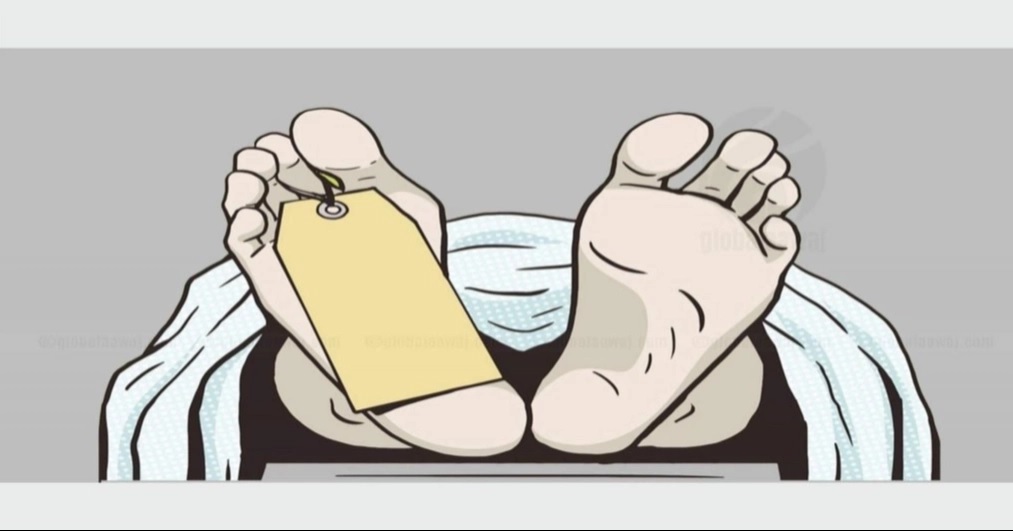ভূমিকা
বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের স্বাস্থ্যসেবার সংকটের কথা নতুন নয়। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট, বেসরকারি সেবার ব্যয়বহুলতা আর যাতায়াতের সমস্যার কারণে গ্রামের মানুষ প্রায়ই চিকিৎসা বঞ্চিত থাকে। এই শূন্যতায় এগিয়ে আসেন তথাকথিত “খালি পায়ের ডাক্তার”— যারা প্রাতিষ্ঠানিক এমবিবিএস ডাক্তার নন, তবে নিজেরা শিখে, প্রশিক্ষণ নিয়ে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে গ্রামের মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেন। এদের জীবনযাপন সাদামাটা, খাবার খরচ কম, সন্তানদের পড়াশোনার সংগ্রাম, আর সমাজের কাছে সম্মান ও বিতর্ক—সব মিলে এক বৈচিত্র্যময় গল্প।
খালি পায়ের ডাক্তার কে?
“খালি পায়ের ডাক্তার” বলতে এমন মানুষকে বোঝানো হয় যাদের ফরমান মেডিকেল ডিগ্রি নেই, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়, ওষুধ বিতরণ, এমনকি ছোটখাটো অস্ত্রোপচার পর্যন্ত করে থাকেন। অনেকে এনজিও থেকে প্রশিক্ষণ নেন, আবার কেউ কাউকে দেখে বা কোন ডাক্তারে চেম্বারে কাজ করে শিখে নেন। সরকার বা স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের স্বীকৃতি দেয় না, তবে বহু গ্রামে এরা একমাত্র ভরসা।

ডাক্তার আবদুল জলিলের গল্প
শুরুর জীবন
বরিশালের মুলাদী উপজেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম আবদুল জলিলের। বাবা ছিলেন ছোট কৃষক। অভাবের কারণে অষ্টম শ্রেণীর পর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। এরপর গ্রামেই এক স্থানীয় “কম্পাউন্ডারের” দোকানে সহকারী হিসেবে কাজ শিখতে শুরু করেন। সেখানেই প্রথম ওষুধ চিনলেন, ইনজেকশন শিখলেন।
চিকিৎসার অভিজ্ঞতা
দশ বছর ধরে গ্রামের গলিপথ ধরে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে সেবা দেন জলিল। হেঁটে যাওয়া তাঁর অভ্যাস—পাকা স্যান্ডেল বা জুতো কেনার সামর্থ্য নেই সব সময়। শুরুর দিকে গরিব কৃষক পরিবারগুলা ওষুধের দামও দিতে পারত না। তিনি লিখে দেন বাজার থেকে সস্তা জেনেরিক ওষুধের নাম। কখনো টাকা না নিয়েই চিকিৎসা করেছেন।
জীবিকা ও খরচ
জলিল মাসে গড়ে ৫-৬ হাজার টাকা রোজগার করেন। খরচ সামলাতে সস্তা চাল, ডাল, আলু-পটল—এই তাঁর খাদ্যতালিকা। মাছ-মাংস উৎসবে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ২ কক্ষের কাঁচা ঘর। তাঁর দুই ছেলে স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়ে, বেসরকারি স্কুলে টিউশন করানো সম্ভব হয়নি।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা
প্রথম দিকে ‘কাচা ডাক্তার’ বলে অনেকে উপহাস করত। এখন গ্রামের বয়স্করা বলেন—“ডাক্তার সাহেব আসছেন”। গ্রামের ধনী লোকজন কখনো যান সরকারি হাসপাতালে, কিন্তু দরিদ্ররা জলিলকেই ডাকেন। তিনি ডায়রিয়া, জ্বর, চর্মরোগ, ব্যথা-বেদনা থেকে স্যালাইন দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ করেন।
বগুড়ার হাসিনা খাতুনের গল্প
জীবন সংগ্রাম
হাসিনা খাতুন বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার এক নারী “খালি পায়ের ডাক্তার”। স্বামী দিনমজুর ছিলেন, যক্ষায় মারা যান। এক মেয়েকে নিয়ে সংসার। স্বামীর মৃত্যুর পর এনজিও’র স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ নেন। ছোট এক বক্সে কয়েকটি ওষুধ, ব্যান্ডেজ, স্যালাইন নেন—এটাই তাঁর ‘চেম্বার’।

স্বাস্থ্যসেবা
হাসিনা গ্রামের ৬-৭ কিলোমিটার এলাকা হেঁটে হেঁটে ঘুরে সেবা দেন। প্রসূতি মায়েদের প্রাথমিক সেবা, গর্ভকালীন পরামর্শ, শিশুর জ্বর, সর্দি, ডায়রিয়া চিকিৎসা, টিকা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা—সবই করেন তিনি। অনেক নারী তাঁর কাছে স্বাচ্ছন্দ্যে আসেন, কারণ এলাকার সরকারি হাসপাতালে নার্সও নেই।
জীবনযাপন
হাসিনার খাদ্য মান বেশ সাদামাটা। সকালে ভাতের মাড় আর মরিচ-লবণ, দুপুরে চাল-ডাল, মাঝে মাঝে সবজি। মেয়েকে স্কুলে রেখেছেন অনেক কষ্টে। বই খাতা কিনতে এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়েছেন।
সম্মান ও সমালোচনা
প্রথম দিকে গ্রামের কিছু প্রভাবশালী হাসিনা খাতুনকে ‘মেয়েলি ডাক্তার’ বলে তুচ্ছ করতেন। অনেকে বলত, “মেয়ে হয়ে ডাক্তারি শিখে কি হবে?” কিন্তু এখন গ্রামের বাচ্চাদের মায়েরা ওকেই ডাকেন। প্রয়োজনে রাতের বেলাতেও দৌড়ে যান প্রসূতি মায়ের বাড়ি।

খালি পায়ের ডাক্তারদের চ্যালেঞ্জ
সরকারি স্বীকৃতির অভাব
এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও সরকারি মেডিকেল বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন নেই। ফলে সরকারিভাবে ‘ডাক্তার’ নয়। আইনি ঝুঁকি থেকে যায়।
ওষুধ কেনার সামর্থ্য
দরিদ্র রোগীরাও টাকা দিতে পারে না, আবার নিজেরাও বড় ওষুধের স্টক রাখতে পারে না।
প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা
নতুন রোগ বা জটিল রোগ চেনা-জানা নেই। কখনো ভুল চিকিৎসার ঝুঁকি থেকে যায়।

সমাজে সম্মানের সংকট
অনেকে “কাচা ডাক্তার”, “ঝাড়ফুঁকওয়ালা” বলে হেয় করে।
অভাবী জীবনযাপন
জীবনযাপনের মান খুবই নিম্ন। ভালো খাবার, পোশাক, সন্তানদের শিক্ষা—সবই চ্যালেঞ্জ।
কেন এরা গুরুত্বপূর্ণ?
বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের জন্য এরা সত্যিকারের লাইফলাইন। যেখানে ১০-১৫ কিমি দূরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাক্তার থাকে না, থাকে না নার্স—সেখানে জলিল বা হাসিনা খাতুনের মতো মানুষই একমাত্র ভরসা। তাঁরা টিকাদান কর্মসূচি, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য—সব ক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগের অনানুষ্ঠানিক সহযোদ্ধা।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতিতে এখনো এই “খালি পায়ের ডাক্তার”দের জন্য বিশেষ নীতি নেই। অথচ এরা প্রমাণ করেছেন, শিখে, ভালোবাসা দিয়ে, নিজের জীবন কষ্টে ফেলে মানুষকে সেবা করা যায়। সরকার চাইলে এদের সীমিত পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এতে দেশের কোটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা আরও সহজলভ্য হবে।
খালি পায়ের ডাক্তার মানে শুধু ডাক্তার নয়—একজন গ্রামীণ সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, অভিভাবক। তারা মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার আলো।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট