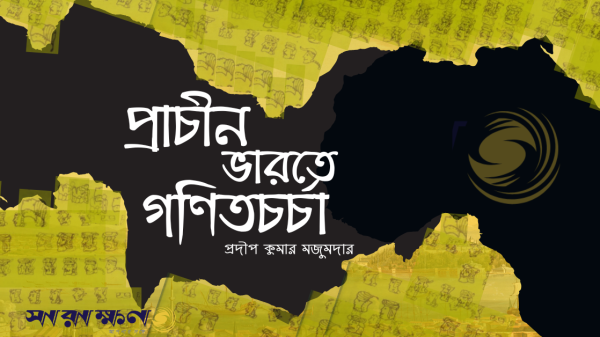বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা যখন আবার ক্যাম্পাসে ফিরছেন, তখন Nature পত্রিকায় আরেকটি সংস্কৃতি-যুদ্ধ-ধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যা নিজেদেরকে একাডেমিক সমালোচনা বলে দাবি করছে। “বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপনিবেশমুক্ত করো, শুধু বৈচিত্র্য আনাই যথেষ্ট নয়” শিরোনামের ওই প্রবন্ধে বিভিন্ন শাখার আটজন গবেষক ঘোষণা করেছেন যে “পশ্চিমা বিজ্ঞান” আসলে “উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের” ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মতে, বিজ্ঞানের কাজ আর নিরপেক্ষভাবে সত্যের অনুসন্ধান নয়—তারা একে নিছক এক মিথ্যা ধারণা বলে উড়িয়ে দেন—বরং তা হওয়া উচিত আবেগপ্রবণ, “বর্ণবাদবিরোধী” প্রচেষ্টা, যেখানে শাস্ত্রগুলোকে “উপনিবেশমুক্ত” করা হবে এবং “আদিবাসী গবেষণা পদ্ধতি”কে উৎসাহ দেওয়া হবে। গবেষকরা এমনকি “citation justice” নামের এক ধারণাও সামনে এনেছেন, যেখানে গ্রন্থতালিকা পর্যন্ত জাতি, লিঙ্গ ও যৌনতার ভিত্তিতে সাজানো হবে।
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অদ্ভুত সব শব্দচাতুরী বের হওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার বিষয়টি সামনে এসেছে এক সংকটময় সময়ে। ট্রাম্প প্রশাসন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসহনীয় ভয়াবহ ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় প্রশাসনকে রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানের জন্য চাপ প্রয়োগের অভিযোগ করেছে। কিন্তু সমস্যার মূল জায়গা কিংবা সংস্কারের ক্ষেত্রটি অধ্যাপকদের লাউঞ্জ কিংবা ওভাল অফিস নয়। এটি আসলে বোর্ডরুমে।
আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রিত হয় রিজেন্ট বা ট্রাস্টিদের মাধ্যমে। সাধারণত বোর্ড সদস্যরা খ্যাতিমান ও গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা মানুষ, যাদের কাজকর্মে দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যখনই তারা বুদ্ধিবিরোধী আন্দোলন, রাজনীতিকরণ বা ক্যাম্পাসে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন, তখনই চোখ বুজে থেকেছেন।

অধিকাংশ ট্রাস্টির স্বভাবই হলো লড়াই না করে সমঝোতা তৈরি করা। তারা এমন অনুষ্ঠান উদযাপন করতে চান, যা শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের একত্র করে—যেমন হোমকামিং বা সমাবর্তন। খুব কম মানুষই বোর্ডে যোগ দেন বুদ্ধিবৃত্তিক সীমা রক্ষার জন্য বা কঠিন প্রশ্ন করে সমালোচনা আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। অনেকে বৃত্তি তহবিলে বড় অঙ্কের অর্থ দান করেন, অন্যরা নস্টালজিয়ায় ভর করে তাদের নিজের কলেজজীবনের স্মৃতিকে লালন করেন। বিনিময়ে তারা শুধু ফুটবল ম্যাচের টিকিট বা সন্তান-নাতি-নাতনিদের ভর্তির সময় কিছুটা সহানুভূতিশীল দৃষ্টি প্রত্যাশা করেন। তাদের সময় ও অর্থ আছে, এবং সদিচ্ছা থেকে তারা “ফিরিয়ে দিতে” চান। লড়াই করতে আসেননি।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, চরমপন্থীরা ইতিমধ্যেই এই লড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছে—এখন দায়িত্বশীল কারও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই ধরনের কাজ আদৌ কি টেনিউরের জন্য যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
একাডেমিক পদোন্নতি ও রাজনীতিকরণ
প্রশ্ন উঠছে—এ ধরনের সক্রিয়তামূলক গবেষণা কি কারও সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী, সেখান থেকে পূর্ণ অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা দেয়, বেতন বৃদ্ধিসহ? সবচেয়ে মৌলিক পর্যায়ে, পেশাগত সময় এভাবে ব্যয় করলে কি অধ্যাপকেরা শিক্ষাদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন? শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ নিয়ম হলো প্রকৃত গবেষণা করার জন্য এ ধরনের ছাড় দেওয়া।

Nature-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের এই অতি-উদারপন্থী লেখকেরা ব্যতিক্রম নন। মানবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ বহুদিন ধরেই বিষ ছড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা বিজ্ঞানকেও কলুষিত করতে শুরু করেছে। ২০২০ সালে জনস্বাস্থ্য গবেষকেরা গির্জা ও নার্সিং হোম বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কোভিড মোকাবিলায়। কিন্তু এই একই বিজ্ঞানীদের অনেকে আবার জর্জ ফ্লয়েড স্মরণে ব্যাপক বিক্ষোভ সমর্থন করেছিলেন। আবার মনোবিজ্ঞানী সমিতিগুলো নিজেদের গবেষণার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে লিঙ্গ-সংক্রান্ত অস্বস্তি (gender dysphoria) নিয়ে। কারও কারও মতে, শিশুদের অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য অস্ত্রোপচারও সমর্থনযোগ্য।
যেসব ট্রাস্টি নীরব থাকেন যখন মানদণ্ড ভেঙে পড়ে, তারা নিজেদের কাপুরুষ মনে করেন না। তারা মনে করেন, চারপাশে ছড়ানো পচন তাদের হাতের বাইরে। “শেয়ার্ড গভর্নেন্স”—যেখানে বোর্ড ও প্রেসিডেন্টরা অধ্যাপকদের ছাড়া পাঠ্যক্রম এক-তরফাভাবে ঠিক করতে পারেন না—ভালো একটি নীতি। কিন্তু বাস্তবে তা মানে দাঁড়িয়েছে, সবচেয়ে আমলাতান্ত্রিকভাবে সক্রিয় অধ্যাপকরা (যাদের মতামত আসলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে না) পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছেন, অথচ বোর্ড সদস্যদের কোনো অনুমোদন বা প্রকৃত ধারণাই নেই।
বোর্ডগুলোর করণীয়
গুরুতর বোর্ডগুলোর প্রথম কাজ হলো সৎভাবে স্বীকার করা: উচ্চশিক্ষায় সবকিছু স্বাভাবিক নয়, এবং সমাধানের অংশ হতে হবে তাদেরও।
সব কলেজে সমাধান একরকম হবে না। একটি খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে জমি-অনুদানপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রকৌশল কলেজের চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতি নিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বোর্ডের দায়িত্ব হলো তাদের প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র মিশন স্পষ্ট করা ও তা রক্ষা করা। এর জন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে শত্রুতা করার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ অধ্যাপকই তথাকথিত “‘ওয়োক’ (woke) বিপ্লব”-এর সমর্থক নন। বোর্ড আসলে সবার হয়ে কথা বলার জন্যই আছে, যারা প্রতিষ্ঠানের মিশনে বিশ্বাসী এবং প্রতিষ্ঠার মূলনীতির প্রতি বিশ্বস্ত।

বোর্ডের দুটি তাৎক্ষণিক ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। প্রথমত, ক্যাম্পাসকে রাজনৈতিকীকরণমুক্ত করা। বক্তৃতা ও নিয়োগ—উভয়ের ক্ষেত্রে এমন নীতি নির্ধারণ করা, যা বুদ্ধিবৃত্তিক বৈচিত্র্য বাড়ায়। আমেরিকান উচ্চশিক্ষা বিশ্বের সেরা—কিন্তু চরমপন্থা ও অতিরিক্ত রাজনীতিকরণ তা বিপদের মুখে ফেলছে।
দ্বিতীয়ত, কী অর্থায়ন করা হবে, এবং কেন, তা নির্ধারণ করা। আগের বছরের বাজেট হুবহু পুনরাবৃত্তি করা নেতৃত্ব নয়। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচের দুই-তৃতীয়াংশই কর্মী ব্যয়। তাহলে প্রতিটি বিষয়ে, মূল পাঠ্যক্রমে এবং নির্বাচনী কোর্সে পড়ানো শেখানোর খরচ কত? এটি কি ক্রেডিট-আওয়ার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা যায়? আর গবেষণার ক্ষেত্রে: প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের গবেষণায় ভর্তুকি দিচ্ছে, এর পরিমাপযোগ্য ফলাফল কী, এবং কেন?
কিছু অধ্যাপক, যারা কখনও জবাবদিহি জানেন না, তারা স্বচ্ছতার দাবি শুনে একে একাডেমিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে আখ্যা দেবেন। একেবারে বাজে কথা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ও মনোযোগ সীমিত। বোর্ড সদস্যরা যদি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে না পারেন যে তারা কী অর্থায়ন করছেন, কী ভর্তুকি দিচ্ছেন—এবং কী ধরনের বুদ্ধিবিরোধী অযথা কর্মকাণ্ড সহ্য করছেন—তাহলে তারা তাদের কাজ ঠিকমতো করছেন না।
বেন সাসে: প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্ট এবং নেব্রাস্কার মার্কিন সিনেটর (২০১৫–২০২৩)।

 বেন সাসে
বেন সাসে