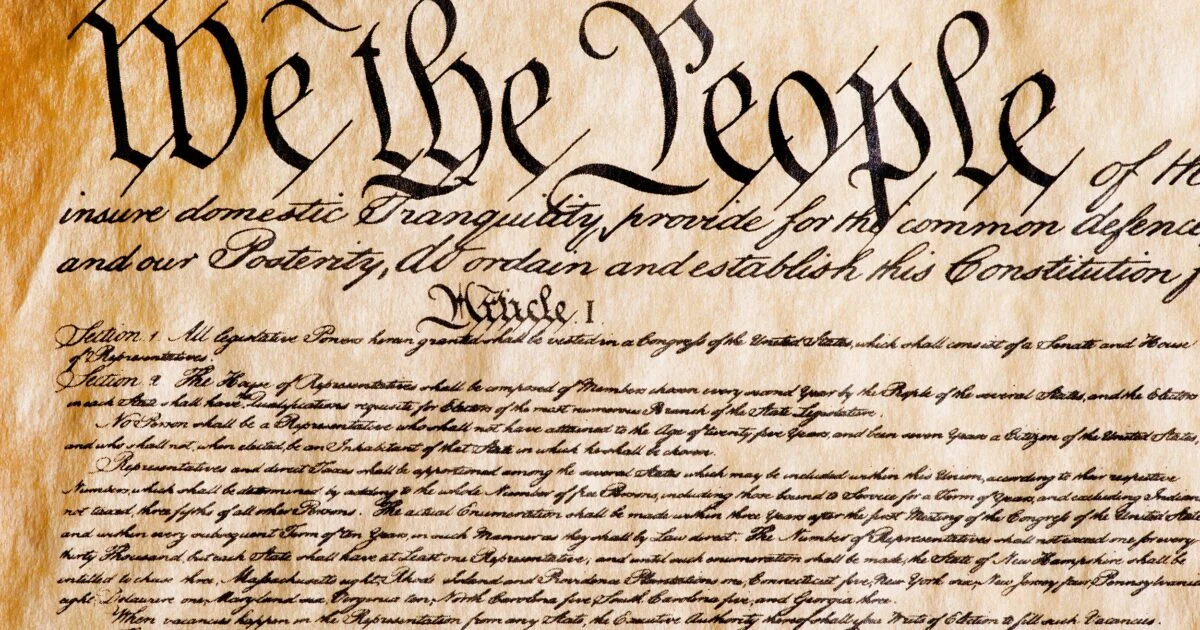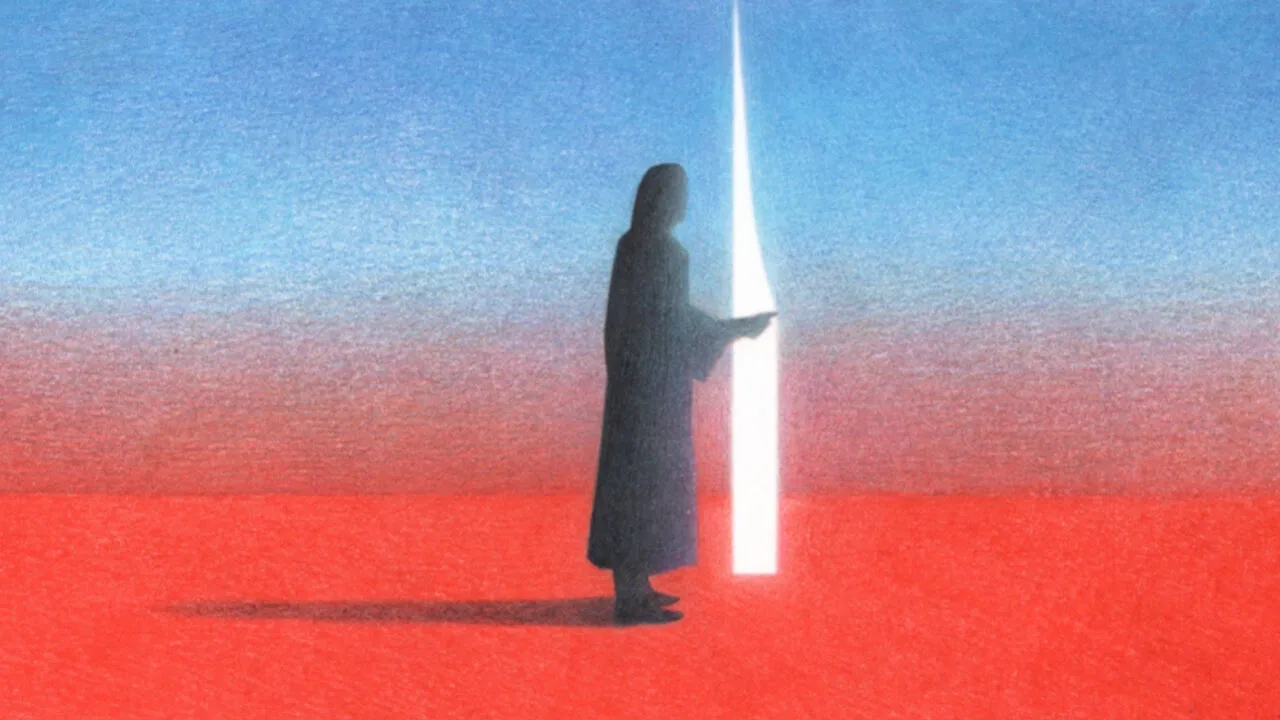প্রেক্ষাপট
ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন রাজনৈতিক মতামতের কারণে অভিবাসীদের কারাগারে পাঠিয়েছে এবং বিচার ছাড়াই সন্দেহভাজন মাদক ব্যবসায়ীদের হত্যা করেছে। ট্রাম্প এক পর্যায়ে বলেছেন, “আমি যা চাই তা করার অধিকার আমার আছে।” তবু তিনি সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা করেননি। ইতিহাস বলে দেয় কেন—১৭৮৯ সালে কনফেডারেশনের আর্টিকেল বদলে বর্তমান সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রায় ১২ হাজার সংশোধনী প্রস্তাবিত হয়েছে, অথচ অনুমোদিত হয়েছে মাত্র ২৭টি—অর্থাৎ ০.২৫ শতাংশেরও কম।
জিল লেপোরের বই
হার্ভার্ডের অধ্যাপক ও নিউইয়র্কারের লেখক জিল লেপোর তার বই We the People–এ যুক্তি দেখিয়েছেন যে আমেরিকার সংবিধান এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে, কারণ এটি পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে—যা সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায়ের পরিপন্থী। টমাস জেফারসন বিশ্বাস করতেন প্রতি ১৯ বছর অন্তর একটি নতুন সংবিধান সভা হওয়া উচিত। তিনি জেমস ম্যাডিসনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন, “এক প্রজন্মের মানুষের আরেক প্রজন্মকে বাঁধার অধিকার নেই।”
আর্টিকেল V ও তার সীমাবদ্ধতা
ম্যাডিসন এত ঘনঘন সভার বিপদ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন, তাই প্রস্তাব দেন আর্টিকেল V–এর, যা অনুযায়ী কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ এবং অঙ্গরাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ সম্মত হলে সংবিধান সংশোধন সম্ভব। ১৮শ শতকে এটি অর্জন করা সম্ভব হলেও বর্তমানে এটি বিশ্বের অন্যতম কঠিন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।
সংশোধনের ইতিহাস
আর্টিকেল V “ঘুমন্ত দৈত্য” হলেও যুদ্ধ ও বড় অস্থিরতার সময়ে সক্রিয় হয়েছে—যেমন গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দাসপ্রথা বিলোপ ও নাগরিক অধিকার প্রসারে। তবে ১৮০৪ থেকে ১৮৬৫ এবং ১৮৭০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত কোনো সংশোধনী অনুমোদিত হয়নি। সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আসে ১৯৭১ সালে, যখন ভোটের বয়স কমিয়ে ১৮ করা হয়। এরপর থেকে সংশোধনী প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে আমেরিকা এখনো টিকে আছে ইলেক্টোরাল কলেজের মতো পুরোনো ব্যবস্থার ওপর, যা জনপ্রিয় ভোটে হারা পাঁচজনকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে। একই সাথে আজীবন মেয়াদী ফেডারেল বিচারক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে আদালতকে রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট করে তুলেছে। এমনকি সিনেটে ওয়াইওমিংয়ের একজন ভোটারের প্রভাব ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটারের চেয়ে ৬৮ গুণ বেশি—এরও কোনো সমাধান নেই।
জলবায়ু পরিবর্তন ও সীমাবদ্ধতা
লেপোর মনে করেন, আর্টিকেল V–কে নতুন করে কার্যকর না করলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে যাবে। তবে অতিরিক্ত সংশোধনের বিপদও রয়েছে। ব্রাজিল ১৯৮৮ সালের পর থেকে ১৩০টির বেশি সংশোধনী এনেছে, যার ফলে বাজেট ভারী হয়েছে এবং জনআস্থা নষ্ট হয়েছে। মেক্সিকো শত বছরে ৭৩৭টি সংশোধনী এনেছে, যা একই ধরনের অস্থিরতা তৈরি করেছে।
তুলনামূলক দৃষ্টান্ত
জার্মান সংবিধান ১৯৪৯ সাল থেকে প্রায় ৬০ বার সংশোধিত হয়েছে। অনেকের মতে এটি একটি ভারসাম্যের উদাহরণ, যেখানে আইন পরিবর্তনের সুফল ও অস্থিরতার খরচকে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। আমেরিকায় যেহেতু সংশোধন কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাই আদালতের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে সংবিধান।
আদালতের ভূমিকা
এটি সংবিধানকে সর্বোচ্চ আদালতের নয় বিচারকের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট নাগরিক স্বাধীনতা সম্প্রসারণে বহু সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে “অরিজিনালিজম” নামে পরিচিত পদ্ধতি—যা বর্তমান ডানপন্থি সংখ্যাগরিষ্ঠদের পছন্দ, অথচ লেপোরের মতে সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রেত নয়—সংবিধানকে রক্ষণশীল দিকেই ঠেলে দিয়েছে।
ভবিষ্যতের প্রশ্ন
লেপোর লিখেছেন, হয়তো একদিন আমেরিকানরা আবার সংশোধন শেখবে, কিংবা একেবারে নতুন সংবিধান তৈরি করবে। তবে বইটিতে কীভাবে তা সম্ভব হবে সে বিষয়ে কোনো রূপরেখা নেই। একই সাথে, বিদ্যমান সংবিধানের জায়গায় কী আসা উচিত সে সম্পর্কেও নির্দেশনা অনুপস্থিত। অথচ এই সংবিধানই আমেরিকাকে ১৩ অঙ্গরাজ্য থেকে ৫০–এ, দাস সমাজ থেকে মুক্ত সমাজে, মহাদেশীয় শক্তি থেকে বৈশ্বিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে।
We the People মেরামতের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নয়। তবে এটি আমেরিকানদের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার ইতিহাস তুলে ধরে, যারা সময়ের সাথে তাদের প্রজাতন্ত্রকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছে।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট