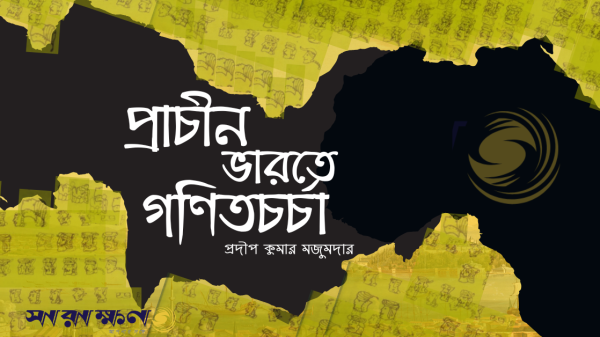ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মে মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রথমে এই বিভাজন ছিল কেবল কূটনৈতিক স্তরে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে, তিনি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ ঠেকিয়েছেন। কিন্তু নয়াদিল্লি বিষয়টি আমলে নেয়নি। পরে পরিস্থিতি তীব্র হয়, যখন ওয়াশিংটন ভারতের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে এবং শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করে।
নয়াদিল্লি তার অসন্তোষ প্রকাশ করলেও সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। ভারত এখনো বুঝতে হিমশিম খাচ্ছে কেন ট্রাম্প প্রশাসন এভাবে চাপ দিচ্ছে, যদিও ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রকাশ্যে একে অপরকে ভালো বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি অসন্তোষ দেখাতে ভারত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছে। আগস্টে মোদি সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সম্মেলনে যোগ দিতে তিয়ানজিন যান, যা ছিল সাত বছরে তার প্রথম চীন সফর। সেখানে তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ আলাপ করেন। পুতিন বছরের শেষের আগে ভারত সফরের পরিকল্পনা করেছেন। অন্যদিকে মোদি বারবার ভারতের কৌশলগত স্বয়ম্ভরতার প্রতিশ্রুতি জোর দিয়ে বলেছেন।

তবে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করার সময় নয়াদিল্লি কৌশল সাবধানে সাজিয়েছে। চীন সফরের স্পর্শকাতরতা হ্রাস করতে মোদি এর আগে জাপান সফর করেন, যা এক ধরনের কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা। তিয়ানজিনে তিনি সদস্য ও পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রগুলোর উপস্থিতিতে হওয়া এসসিও প্লাস বৈঠকে যোগ দেননি। বেইজিংয়ে জাপানবিরোধী যুদ্ধজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেডেও তিনি থাকেননি।
হয়তো যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী ভাবমূর্তি এড়ানোর জন্য নয়াদিল্লি মস্কোর প্রস্তাবিত চীন-রাশিয়া-ভারত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও সম্মত হয়নি। সেপ্টেম্বরে ব্রাজিল যখন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতি নিয়ে বিশেষ ব্রিকস ভার্চুয়াল সম্মেলন আয়োজন করল, তখন ভারত কেবল পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠায়।
নয়াদিল্লি জাপান ও ইউরোপের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার চেষ্টা করছে, হয়তো ওয়াশিংটনের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল নিয়ে নতুন করে আগ্রহ জাগাতে এবং ট্রাম্প প্রশাসনকে ‘সঠিক পথে’ ফেরাতে।
তবে এতে ট্রাম্প প্রশাসনের উসকানি আরও বাড়তে পারে। এরই মধ্যে এক মার্কিন সিনেটর এমন একটি আইন প্রস্তাব করেছেন যাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো যারা সেবা আউটসোর্স করে তাদের ওপর কর আরোপ করা হয়। এতে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আউটসোর্সিং খাত বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে।
ভারত এখনো বাইডেন যুগের বাস্তবতায় আটকে আছে। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করে আসার পর মোদি সরকার দেখছে যে, ওয়াশিংটনের সেই বিশেষ সুবিধা আর তারা পাচ্ছে না।
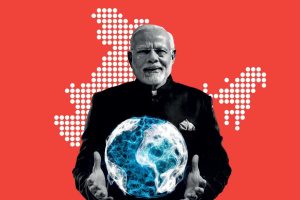
নয়াদিল্লি আসলে ভুল হিসাব করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র-চীন কৌশলগত প্রতিযোগিতা কীভাবে গড়ে উঠবে। ওয়াশিংটন চীনের ভারসাম্য রক্ষায় অংশীদার চাইলেও সেই অংশীদার যে ভারত হবে, তা নিশ্চিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতের উত্থান জাপান বা জার্মানির মতো নয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় জনসংখ্যার দেশ, যাদের প্রবাসী অভিজাত শ্রেণি গভীরভাবে অ্যাংলো-স্যাক্সন বিশ্বে প্রভাবশালী—এমন একটি দেশের উত্থান ওয়াশিংটনকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আফসোস করছে যে তারা তাদের গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে চীনের উত্থান সহজতর করেছিল। আরেকটি এশীয় শক্তির উত্থান ঘটিয়ে তারা কি একই ভুল করবে? অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাচস উল্লেখ করেছেন: “অনেকে ভেবেছিল ভারত হবে চীনের বিকল্প। যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং ভারতকে চীনের সাপ্লাই চেইনের জায়গায় বসাবে।” কিন্তু তিনি বলেন, এটি অবাস্তব চিন্তা, কারণ “যুক্তরাষ্ট্র যেমন এখন চীন থেকে বিপুল রপ্তানি অনুমোদন করে না, তেমনি ভারত থেকেও তা অনুমোদন করবে না।”
ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো বড় শক্তির উত্থান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অগ্রহণযোগ্য। কল্পনা করুন, যদি জার্মানি ও জাপান ঠান্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন করতে না দিত, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কতটা নেতিবাচক হতো।
যদি নয়াদিল্লি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হয়ে অধীনস্থ ভূমিকায় যেতে রাজি না হয়, তবে ওয়াশিংটন তার উত্থান মেনে নেবে না।

চীনকে ঘিরে ওয়াশিংটনের কৌশলে সহযোগীর অভাব নেই—বরং ট্রাম্প অতিরিক্ত জোটের প্রতিই সন্দেহপ্রবণ। কিন্তু তাদের প্রয়োজন এমন অংশীদার, যারা সক্ষম এবং ইচ্ছুকভাবে বেইজিংয়ের মুখোমুখি হবে। নয়াদিল্লির না সেই সক্ষমতা আছে, না সেই উদ্দেশ্য।
৭ মে, ভারত-পাকিস্তান বিমান সংঘর্ষের প্রথম দিনে নয়াদিল্লি ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে তার সামরিক শক্তি প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, চীনের ভৌগোলিক নৈকট্য ভারতের মনে সবসময় এই আশঙ্কা জাগায় যে, কোনো একদিন যুক্তরাষ্ট্র-চীন গোপনে মীমাংসায় পৌঁছাতে পারে।
অনেক সময় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র না হওয়ায় নয়াদিল্লি ওয়াশিংটনের কাছে অবিশ্বস্ত অংশীদার। কিন্তু এমনকি যদি নয়াদিল্লি রাজি থাকেও, ওয়াশিংটন তাকে মিত্র হিসেবে নেবে না। ভারতের সঙ্গে জোট গড়তে হলে চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা আসবে, যার খরচ হবে বিপুল।
মনে রাখা উচিত, ২০২১ সালে যখন ভারত করোনাভাইরাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ঢেউয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, তখনো বাইডেন প্রশাসন ভ্যাকসিন তৈরির কাঁচামাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। পরে কেবল আংশিকভাবে সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছিল।

 লিন মিনওয়াং
লিন মিনওয়াং